মুক্তমনায় (www.mukto-mona.com) এক বছর আগে বিবর্তনীয় মনোবিজ্ঞান নিয়ে একটা সিরিজ শুরু করেছিলাম; শুরু করেছিলাম একটা ‘বড়দের জোক’ মানে প্রাপ্তবয়স্ক কৌতুক দিয়ে। কৌতুকটা এইরকম।
এক আধ-পাগলা ব্যাটা (ধরা যাক তার নাম মন্টু মিয়া) সারাদিন পাড়ায় ঘুরে ঘুরে গুলতি দিয়ে জানালার কাঁচ ভাঙত। এটাই তার নেশা। কিন্তু বাপ, তুই নেশা করবি কর তোর নেশার চোটে তো পাড়া-পড়শির ঘুম হারাম। আর তা হবে নাই বা কেন! কাশেম সাহেব হয়তো ভরপেট খেয়েদেয়ে টিভির সামনে বসেছেন, কিংবা হয়তো বিছানায় যাওয়ার পাঁয়তারা করছেন, অমনি দেখা গেল দড়াম করে বেডরুমের কাঁচ ভেঙে পড়লো। শান্ত কখনো বা সকালে উঠে প্রাতঃকৃত্য সারার নাম করে বাবা-মার কাছ থেকে লুকিয়ে চাপিয়ে বাথরুমে গিয়ে কমোডে উপবেশনপূর্বক একটা বিড়ি ধরিয়ে একখান সুখটান দেবার উপক্রম করেছে অমনি গুলতির চোটে বাথরুমের কাঁচ ছত্রখান। নরেন্দ্রবাবু সকালে উঠে এক রৌদ্রস্নাত দিন দেখে ‘আজি এ প্রভাতে রবির কর…’ কবিতার চরণ আবৃত্তি করতে করতে জানালা দিয়ে চাঁদমুখোনি বাড়িয়ে দিয়েছেন, অমনি এক ক্ষুদ্র ইষ্টকখণ্ড ‘আসিয়া জানালা তো ভাঙিলোই, তদুপরি কপালখানিও বেঢপ আকৃতিতে ফুলিয়া উঠিলো।
কাহাতক আর পারা যায়। পাড়া পড়শিরা একদিন জোট বেঁধে শলাপরামর্শ করে মন্টু মিয়াকে বগলদাবা করে শহরের পাশের পাগলা গারদে দিয়ে আসলো।
সে এক হিসেবে ভালোই হলো। এখন আর বলা নেই কওয়া নেই হঠাৎ করে কারো জানালার কাঁচ ভেঙে পড়ে না। কাশেম সাহেব ভরপেট খেয়ে টিভির সামনে বসতে পারেন, শান্ত বাবাজি হাগনকুঠিতে গিয়ে নিবিষ্ট মনে গিয়ে বিড়ি টানতে পারে, আর নরেন্দ্রবাবুও রবিঠাকুরের কবিতা শেষ করে জীবনানন্দ দাশেও সেঁধিয়ে যেতে পারেন, কোনো রকমের বাধা-বিপত্তি ছাড়াই। জীবন জীবনের মতো চলতে থাকে নিরুপদ্রপে।
আর অন্য দিকে মন্টু মিয়ার চিকিৎসাও ভালোই চলছে। প্রতিদিন নিয়ম করে তাকে ঔষধ পথ্য খাওয়ানো হচ্ছে, রেগুলার সাইকোথেরাপি দেওয়া হচ্ছে, সমাজ জীবন নিয়ে এন্তার জ্ঞানও দেয়া হচ্ছে। মানুষ সম্পর্কে আর সমাজ সম্পর্কে দায়িত্ববোধ গড়ে তোলা হচ্ছে। আর মন্টু মিয়ার দায়িত্ব নিয়েছেন দেশের বিখ্যাত বিশেষজ্ঞ ড. আজিম। তো এই উন্নত চিকিৎসা আর পরিবেশ পেয়ে মন্টু মিয়ার মনও ধীরে ধীরে পরিবর্তিত হয়ে উঠলো। এখন আর জানালার কাঁচ দেখলেই মন্টু মিয়ার হাত আগের মতো নিশপিশ করে না। জব্দ করা গুলতির জন্য মন কেমন কেমন করে উঠে না। নিয়ম করে খায় দায়, বই পড়ে, ব্যায়াম করে আর সমাজ আর জীবন নিয়ে উচ্চমার্গীয় চিন্তা করে। অসুস্থতার কোনো লক্ষণই আর মন্টু মিয়ার মধ্যে নেই! দিন যায়, মাস যায়, বছর যায়…
বহুদিন ধরে চিকিৎসার পর একদিন সুবে সাদিকে ডাক্তার সাহেব মন্টু মিয়ার কেবিনে এসে বললেন,
– “মন্টু মিয়া, তুমি সম্পূর্ণ সুস্থ।”
-”তাই? এইটা তো খুবই ভালো সংবাদ দিলেন স্যার। আমি তো ভাবতেছিলাম এই পাগলা গারদ থেকে কোনোদিন ছাড়াই পামু না আর।” মন্টু মিয়ার চোখে বিস্ময়।
– “কী যে বলো! আমাদের চিকিৎসার একটা ফল থাকবে না!”– ডাক্তার সাহেবের ভরাট গলায় একধরনের আত্মপ্রসাদের ছাপ।
– “তা তো বটেই। আপনাগো অনেক ধন্যবাদ ডাক্তার সাহেব। আপনারা সবাই মিল্লা আমার জন্য যা করলেন… ”।
– “না না কী যে বলেন। আপনার নিজের প্রচেষ্টা ছাড়া কী আর এ অসাধ্য সম্ভব হতো নাকি! ” বিনয়ের অবতার সেজে গেলেন ডাক্তার সাহেব। তারপর হাতের স্টেটসকোপ দিয়ে নাড়ি দেখলেন, রক্তের চাপ পেলেন স্বাভাবিক মাত্রায়। জিব বের করিয়ে চোখের পাতা টেনে ধরে নীচ-উপর করলেন কোনো অস্বাভাবিকতাই পেলেন না। আরও কিছু ছোটখাটো পরীক্ষা সেরে নিলেন। একজন স্বাভাবিক মানুষের যা যা লক্ষণ পাওয়া উচিত তাই পেলেন ডাক্তার সাহেব। ডাক্তার আজিম বুঝলেন তার চিকিৎসায় মন্টু এখন পুরোপুরি সুস্থ। অযথা আর হাসপাতালে আটকে রাখার কোনো মানে হয় না। তাকে রিলিজ করে দেওয়ার যাবতীয় কাগজপত্র হাতে নিলেন সই করবেন বলে। এই কাজটা একদমই ভালো লাগে না ড, আজিমের। সামান্য একটা রিলিজ, অথচ হাজারটা কগজপত্র, হাজার জায়গায় সই। কাগজগুলোতে চোখ বুলিয়ে একটা একটা করে সই-এর দায়িত্ব সেরে নিচ্ছেন ডাক্তার সাহেব। ফাঁকে ফাঁকে মন্টু মিয়ার সাথে কথোপকথন চালাচ্ছেন, যাতে যতদূর সম্ভব বিরক্তি থেকে মুক্ত থাকতে পারেন।
“তা হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেয়ে কী করবে মন্টু মিয়া? সোজা বাসায় চলে যাবে?”
– “হোটেলে? কেন? ভালো করে খাওয়া দাওয়া করবে বুঝি? তা করতেই পার। হাসপাতালের ঘাস পাতা খেতে খেতে অরুচি ধরে গেছে নিশ্চয়।”
– হোটেলটায় নাকি মদ-টদ আর সাথে আরও কিছু জিনিস পাওয়া যায় সস্তায়। ভাবতেছি অনেকদিন …
– হ্যাঁ হ্যাঁ তা তো বটেই। আরে এত লজ্জা পাচ্ছ কেন। ফুর্তি করার এটাই তো বয়স। হ্যাঁ, ওখানে শুধু মদই পাওয়া যায় না, সাথে নাকি সুন্দর সুন্দর মেয়েও পাওয়া যায়… মানে এই আমি শুনেছি আর কী…
(ড, আজিম যে সেসব উদ্ভিন্নযৌবনা মধুমক্ষিকার লোভে প্রায়শই বাসার নাম করে নিষাদে সেঁধিয়ে যান, আর দীর্ঘ সময় পরে মাঝরাতে বাসায় গিয়ে বউকে আলিঙ্গন করে বলেন…আজকেও ফিরতে ফিরতে অনেক রাত হয়ে গেল, বুঝলে এত কাজ থাকে… এই ব্যাপারটা এক্ষণে মন্টু মিয়ার কাছ হইতে চাপিয়া যাওয়াই শ্রেয় মনে করিলেন ড. আজিম)।
– ‘হ স্যার ওগো জিনিস ভালা। আমি জানি।‘
— ‘তো এতদিন পর এরকম একটা চান্স…নিশ্চয় অনেক আমোদ ফুর্তি করবে।
– ‘হ স্যার। লটের সব থেইক্যা সুন্দর মাইয়াডারে ভাড়া করুম। লগে এক বোতল কেরু’।
‘বাহ তারপর?’ ডাক্তার সই করার কথা ভুলে মন্টু মিয়ার দিকে চাইলেন। কেরুর প্রতি ড, আজিমের বিন্দুমাত্র আকর্ষণ না থাকলেও (তিনি আবার বিদেশি মদ ছাড়া কিছু মুখে দেন না), নারীদেহের প্রতি তার অন্তহীন আকর্ষণ। মন্টু মিয়া হোটেলে গিয়ে কী করবেন, তা ভেবেই তিনি রোমাঞ্চিত হয়ে উঠতে লাগলেন।
– “তারপর আর কী! একটা রুম বুক দিমু। টেকা পয়সা যা আছে তাতে চইলা যাইব’।
‘টাকা পয়সা যে তোমার আছে তা ত জানি। কিন্তু তুমি রুমে গিয়ে কী করবে? ডাক্তার সাহেবের আর তর সয় না।
‘রুমে গিয়া দরজাটা ভালো মতো লক করমু আগে। তারপর মাইয়াডারে বিছানায় বহাইয়া কেরুর বোতল খুইলা দিমু চুমুক। তারপর আস্তে ধীরে মাইয়াডার দিকে আগামু…।
– “তারপর, তারপর?’ ডাক্তার সাহেবের শিরদাঁড়া খাড়া হয়ে উঠছে।
— ‘তারপর স্যার…মাইয়াডার কাপড় আস্তেধীরে খুলতে শুরু করমু। তারপর…’
— ‘তারপর?’ ডাক্তার সাহেব উত্তেজনায় পারলে একেবারে দাঁড়িয়ে যান।
— তারপর ব্রাটা খুইলা লমু..
— “হ্যাঁ, তারপর? তারপর কী করবে?’ ড. আজিম এবারে চেয়ার ছেড়ে দাঁড়িয়ে যান।
– “তারপর স্যার, ওই ব্রাটার ইলস্টিকটারে গুলতি বানায়া হোটেলের জানালার সমস্ত কাঁচ ভাঙ্গুম!
– ‘কী!!!!’ ড, আজিম মাথায় হাত দিয়ে চেয়ারে বসে পড়লেন।
ছোটবেলায় শোনা এই ‘বড়দের’ জোকটা ‘ফালতু’ মনে হলেও এর মর্মার্থ কিন্তু ব্যাপক। এতে আমাদের মানব মনের এক অন্তহীন প্রকৃতিকে তুলে ধরা হয়েছে। এই বড়দের ‘ঈশপের গল্পের মর্মার্থ হলো কারো কারো মাথার ক্যারা এমনই যে, যত চেষ্টাই করা হোক না কেন সেই ক্যারা কোনো রকমেই বের করে ফেলা যায় না। যত সাইকোথেরাপিই দেয়া হোক না কেন, দেখা যায় আবার সুযোগ পেলেই এবাউট টার্ন করে রোগী। আমি ‘সমকামিতা কি প্রকৃতিবিরুদ্ধ’[৪] নামে একটি সিরিজ লিখেছিলাম (পরে এটি শুদ্ধস্বর থেকে বই আকারে প্রকাশিত হয়[৫]), সেখানে বহু দৃষ্টান্ত হাজির করে দেখিয়েছিলাম যে, সমকামিতার ব্যাপারটা অনেক ক্ষেত্রেই স্রেফ পরিবেশনির্ভর নয়, বরং ‘বায়োলজিকালি হার্ডওয়্যার্ড’। একটা সময় ছিল যখন, সমকামিতাকে ঢালাওভাবে মনোরোগ বা বিকৃতি বলে ভাবা হতো। ভাবা হতো সমকামিতা বোধ হয় কিছু বখে যাওয়া মানুষের বেলাল্লাপনা ছাড়া আর কিছু নয়। আজকের দিনে সেই ধারণা (অন্তত পশ্চিমে) অনেকটাই পাল্টেছে। এ প্রসঙ্গে জানানো যেতে পারে যে, ১৯৭৩ সালের ১৫ই ডিসেম্বর American Psychiatric Association (বহু চিকিৎসক এবং মনোবিজ্ঞানীদের সমন্বয়ে গড়ে ওঠা সংগঠন) বিজ্ঞানসম্মত আলোচনার মাধ্যমে একমত হন যে সমকামিতা কোনো নোংরা ব্যাপার নয়, নয় কোনো মানসিক ব্যধি। এ হলো যৌনতার স্বাভাবিক প্রবৃত্তি। ১৯৭৫ সালে American Psychological Association একইরকম অধ্যাদেশ দিয়েছিলেন। সকল আধুনিক চিকিৎসকই আজ এ বিষয়ে একমত।
বিবর্তনীয় মনোবিজ্ঞান কী?
–বিবর্তনীয় মনোবিজ্ঞান মূলত বিজ্ঞানের দুটো চিরায়ত শাখাকে একীভূত করেছে; একটি হচ্ছে বিবর্তনীয় জীববিজ্ঞান (Evolutionary Biology) এবং অন্যটি বৌদ্ধিক মনোবিজ্ঞান (Cognitive Psychology)। বৌদ্ধিক মনোবিজ্ঞান থেকে আমরা জানতে পারি যে, আমাদের মানসপট নির্মাণে দীর্ঘদিনের এক জটিল পরিকল্পনার ছাপ আছে। আবার বিবর্তনীয় জীববিজ্ঞান বলে যে, জীবদেহের এই ‘জটিল পরিকল্পনা’ বলে যেটাকে মনে হয় সেটা আসলে ডারউইন বর্ণিত ‘প্রাকৃতিক নির্বাচন’ এবং কিছু ক্ষেত্রে যৌনতার নির্বাচনের ফলাফল। কাজেই, এই দুই শাখার মিশ্রণে গড়ে উঠা বিবর্তনীয় মনোবিজ্ঞানের উপসংহার হচ্ছে আমাদের জটিল মানসপটও উদ্ভূত হয়েছে দীর্ঘদিনের বিবর্তনীয় পথ পরিক্রমায় প্রাকৃতিক নির্বাচন এবং যৌনতার নির্বাচনকে পুঁজি করেই।
মন্টু মিয়ার পাগলামো কিংবা সমকামিতাই কি ‘ক্যারা মাথার’ কেবল একমাত্র উদাহরণ? না তা মনে করা ভুল হবে। আমাদের চারপাশে চোখ মেললেই আমরা মানবপ্রকৃতির এ ধরনের আরও মজার মজার উদাহরণ দেখতে পাব। একই রকম কিংবা প্রায় একই রকম পরিবেশ দেয়ার পরও অভিভাবকেরা লক্ষ করেন তাদের কোনো বাচ্চা হয় মেধাবী, অন্যটা একটু শ্লথ, কেউ বা আবার অস্থির, কেউ বা চাপা স্বভাবের, কেউ বা কোমল কেউ বা হয় খুব ডানপিটে। কেউ বা স্কুলের লেকচার থেকে চটপট অঙ্কের সমস্যাগুলো বুঝে ফেলে, কেউ বা এ ধরনের সমস্যা দেখলেই পালিয়ে বাঁচে, কিংবা মাস্টারের বেতের বাড়ি খেয়ে বাসায় ফেরে। ছোটবেলা থেকেই কেউ পিয়ানোতে খুব দক্ষ হয়ে উঠে, কেউ বা রয়ে যায় তাল কানা। কেউ বা খেলাধুলায় হয় মহা চৌকস, কারো বা ব্যাটে বল লাগতেই চায় না। কেউ ছোটবেলা থেকেই গল্প-কবিতা লেখায় খুব পারদর্শী হয়ে উঠে, তার কেউ সাহিত্য শব্দটা উচ্চারণ করতে গেলেই দাঁত খুলে আসে কিংবা একটা চার লাইনের কবিতা লিখতে গেলেই কলম ভেঙে পড়ে। এ ধরনের ব্যাপারস্যাপারের সাথে আমরা সবাই কমবেশি পরিচিত।
কাজেই, আমরা কিছু উদাহরণ পেলাম যেগুলো হয়তো অনেকাংশেই পরিবেশনির্ভর নয়। অন্তত পরিবেশ নিয়ন্ত্রণ করে আমরা সেগুলোর প্রকৃতি রাতারাতি বদলে দিতে পারি না। আইনস্টাইনকে শিশু বয়সে আর্জেন্টিনা বা ব্রাজিলে বড় করলেই কি তিনি ম্যারাডোনা বা পেলে হয়ে উঠতে পারতেন? তা কিন্তু হলফ করে বলা যাবে না। তার মানে ভালোবা উপযুক্ত পরিবেশ দেয়ার পরও বাঞ্ছিত ফলাফল আমরা পাই না বহু ক্ষেত্রেই। তখন কপাল চাপড়ানোই সার হয়। কিন্তু তার মানে কিন্তু এটা মনে করা ভুল হবে যে, জীবন গঠনে পরিবেশের কোনো প্রভাব নেই। অবশ্যই আছে। জীবন গঠনে পরিবেশের ভূমিকা যে অনস্বীকার্য, সেটা তো আমরা ছোটবেলা থেকেই জানি। সে জন্যই প্রত্যেক পিতামাতা তার সন্তানকে একটা ভালো পরিবেশ দিয়ে বড় করতে চান। শিশুর মানসপটে পরিবেশের প্রভাব আছে বলেই ভালো একটা পরিবেশ প্রদানের জন্য কিংবা ভালো একটা স্কুলে বাচ্চাকে ভর্তি করানোর জন্য অভিভাবকেরা অহর্নিশি চিন্তিত থাকেন। তারপরও কি তারা সবসময় প্রত্যাশিত ফল পান? মুনির ঘরে কি শনি জন্মায় না? কিংবা আলিমের ঘরে জালিম? জন্মায় জন্মায়। এই আমার উদাহরণটাই ধরুন। আমার মা ছোটবেলা থেকে কত করে চাইল তার ছেলেটার যেন ধর্মেকর্মে মতি থাকে, সবার সাথে যেন ভালো ব্যবহার করি, কারো সাথে যেন ঝগড়া ফ্যাসাদে না জড়াই। তা আর হলো কই! ধর্মকর্ম আর আমার ধাতে সইলো না। মুনাফেকের খাতায় অচিরেই নাম উঠে গেল আমার। সাত বছর বয়সে আমি ঘোষণা দিয়ে বললাম–”মন্দিরের প্রসাদ যেন। আমাকে না খাওয়ানো হয় কক্ষনো’। আমাদের পাড়ার (মা-বাবার দৃষ্টিতে) সবচেয়ে অপছন্দের আর বখে যাওয়া ছেলেটার সাথে মিশতে শুরু করে দিলাম। আমার মা। নীরবে চোখের জল ফেলেন- “কী কুক্ষণে যে এইটারে পেটে ধরেছিলাম!” অথচ এমন কি হবার কথা ছিল? ভালো পরিবেশের কোনো অভাব ছিল না আমার …
পাঠকদের মাথায় নিশ্চয়ই প্রশ্ন উঁকি দিতে শুরু করেছে পরিবেশই যদি মানবপ্রকৃতি গঠনের একমাত্র নিয়ামক না হয়ে থাকে, তাহলে আর বাকি থাকে কী? বাকি থাকে একটা খুব বড় জিনিস। আজকের দিনের বিজ্ঞানীরা বলেন, মানবপ্রকৃতি গঠনে পরিবেশের প্রভাব যেমন আছে, তেমনি আছে আরেকটা জিনিসের প্রভাব। সেটা হচ্ছে বংশাণু বা ‘জিন’। মানুষের প্রকৃতি বিশ্লেষণে ‘জিন’কে নিয়ে আসায় অনেকের চোখই হয়তো কপালে উঠে যাবে। ভুরু কুঁচকে যেতে পারে কারো কারো। তবে আমি এ প্রবন্ধে দেখানোর চেষ্টা করব যে, পরিবেশ এবং “জিন’ মানবপ্রকৃতি গঠনে কোনোটার প্রভাবই কোনোটার চেয়ে কম নয়। আমরা প্রায়শই সন্তানদের দেখিয়ে বলি–ছেলেটা বাপের মতোই বদরাগী হয়েছে, কিংবা বলি মেয়ে হয়েছে মার মতোই সুন্দরী। চোখগুলো দেখেছ কী রকম টানা টানা?’ এগুলো কিন্তু আমরা এমনি এমনি বলি না। বহুদিনের অভিজ্ঞতা থেকেই এগুলো বলি, আর সেজন্যই এই উপমাগুলো আমাদের সংস্কৃতিতে এমনিভাবে মিশে গেছে। কেবল শারীরিক সৌন্দর্য নয়, আবেগ, অনুরাগ, হিংসাত্মক কিংবা বদরাগী মনোভাব এমনকি ডায়াবেটিস কিংবা হৃদরোগের ঝুঁকি পর্যন্ত আমরা বংশপরম্পরায় বহন করি ‘জেনেটিক তথ্য হিসেবে আমাদের অজান্তেই। বাবার হৃদরোগের উপসর্গ থাকলে ছেলেকেও একটু বাড়তি সচেতন হতে পরামর্শ দেন আজকের ডাক্তারেরা। কার্ব আর রেড মিট ছেড়ে দিতে বলেন। পরিবারে কারো ডায়াবেটিস থাকলে কিংবা কাছের কোনো আত্মীয়ের দেহে এ রোগ বাসা বেঁধে থাকলে অন্যান্যরাও নিয়মিত ‘সুগার চেক’ করা শুরু করে দেন। এগুলো কিন্তু আমরা সবাই জানি। শারীরিক গঠন কিংবা রোগ-বালাইয়ের ক্ষেত্রে তাও না হয় মানা যায়, কিন্তু মানুষের চরিত্র গঠনে ‘জিন’-এর প্রভাব থাকতে পারে, এ ব্যাপারটা মেনে নিতে অনেকেরই আপত্তি ছিল, এখনও আছে বহুজনেরই। আর আপত্তি আছে বলেই আমরা জ্ঞানের ক্ষেত্রটিকে পরিষ্কার দুইভাগে ভাগ করে। ফেলেছি– জীববিজ্ঞান আর সমাজবিজ্ঞান নামের অভিধায়। প্রাণিদেহের এবং সর্বোপরি মানুষের শারীরিক গঠন, দৈহিক বৈশিষ্ট্য, মিউটেশন ইত্যাদি নিয়ে গবেষণা করবেন জীববিজ্ঞানীরা, আর সমাজসংস্কৃতি আর মানুষের মন নিয়ে গবেষণা করবেন জীববিজ্ঞানীরা আর সমাজসংস্কৃতি আর মানুষের মন নিয়ে গবেষণা করবেন সমাজবিজ্ঞানীরা কিংবা মনোবিজ্ঞানীরা। এ যেন দুই স্বতন্ত্র বলয়। জীববিজ্ঞানের আহৃত গবেষণা সম্পর্কে সমাজবিজ্ঞানীরা নীরব থাকবেন। আবার সমাজিক বিজ্ঞানীদের বিভিন্ন সামাজিক গবেষণা সম্পর্কে জীববিজ্ঞানীরা উদাসীন থাকবেন। এটাই চিরন্তন নিয়ম হয়ে গিয়েছে যেন। কিন্তু এই বিভেদ কি যৌক্তিক? এই দুই বলয়ের মধ্যে কী কোনোই সম্পর্ক নেই? আধুনিক চিন্তাবিদরা কিন্তু বলেন, আছে। খুব ভালোভাবেই সম্পর্ক আছে। আসলে সংস্কৃতি বলি, কৃষ্টি বলি, দর্শন বলি, কিংবা সাহিত্য–এগুলোকিন্তু মানবমনের সম্মিলিত প্রকাশছাড়া আর কিছুনয়। আবার মানব মন কিন্তু মানব মস্তিষ্কেরই (Human brain) অভিব্যক্তি, যেটাকে হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক স্টিভেন পিঙ্কার তার ‘হাউ মাইন্ড ওয়ার্কস’ বইয়ে খুব সহজভাবে ব্যাখ্যা করেছেন এই বলে– Mind is what the brain does’। আর এ কথা তো সবারই জানা যে, দীর্ঘকালের বিবর্তনীয় প্রক্রিয়াতেই তৈরি হয়েছে মানব বংশাণু যা আবার মস্তিষ্কের গঠনের অবিচ্ছেদ্য নিয়ামক। কাজেই একধরনের সম্পর্ক কিন্তু থেকেই যাচ্ছে। আমরা চাইলেও আর সামাজিক আচার-ব্যবহার কিংবা মানবপ্রকৃতি বিশ্লেষণে জীববিজ্ঞানকে সমাজবিজ্ঞান থেকে আজকে আলাদা করে রাখতে পারি না। এ ব্যাপারটাই স্পষ্ট করেছেন জন ব্রকম্যান তার সাম্প্রতিক সায়েন্স এট এজ’ (২০০৮) বইয়ের ভূমিকায়
Connection do exist: our arts, our philosophies, our literature are the product of human minds interacting with one another, and the human mind is a product of human brain, which is organized in part by the human genome and has evolved by the physical process of evolution.
মানবপ্রকৃতি বিশ্লেষণে জিন বা বংশাণুকে গোনায় ধরা উচিত–এ ব্যাপারটি প্রথম স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করেন এডওয়ার্ড ও উইলসন তার বিখ্যাত “সামাজিক জীববিজ্ঞান (Sociobiology) নামক পুস্তকে[৬]। সে সময় উইলসনের গবেষণার বিষয় ছিল পিঁপড়ে এবং পিঁপড়েদের সমাজ। পিঁপড়েদের চালচলন গতিবিধি এবং সমাজব্যবস্থা নিয়ে অনেকদিন ধরেই ভদ্রলোক রিসার্চ করছিলেন। ১৯৭১ সালে তিনি এ নিয়ে একটি সুন্দর একাডেমিক বইও লিখেছিলেন ‘দ্য ইনসেক্ট সোসাইটি’ নামে। ১৯৭৫ সালের ‘সোশিওবায়োলজি’ বইটিতেও তিনি পিঁপড়েদের আকর্ষণীয় জীবনযাপন আর সমাজের নানা রকমের গতিবিধিই মূলত ব্যাখ্যা করছিলেন। তিনি যদি সেখানেই থেমে যেতেন, তবে কোনো সমস্যা ছিল না। কিন্তু তিনি সেখানে থেমে না গিয়ে শেষ অধ্যায়ে তার ধ্যানধারণা একেবারে মানবসমাজ পর্যন্ত নিয়ে যান। পরে সেই ধারণাকে উইলসন আরও বিস্তৃত করেন তার পরবর্তী ‘মানবপ্রকৃতি নিয়ে’ (১৯৭৮) নামের বইয়ে[৭]। তিনি বলেন আজকে আমরা যাদের আধুনিক মানুষ নামে অভিহিত করি, সেই হোমোস্যাপিয়েন্স প্রজাতিটির মূল মানসপটের বির্নিমাণ আসলে ঘটেছিল অনেক আগে যখন তারা বনে-জঙ্গলে শিকার করে আর ফলমূল কুড়িয়ে জীবনযাপন করত। একটু লক্ষ করলেই দেখা যাবে, সেই আদি স্বভাবের অনেক কিছুই এখনও আমরা আমাদের স্বভাবচরিত্রে বহন করি–যেমন বিপদে পড়লে ভয় পাওয়া, দল বেঁধে বিপদ মোকাবেলা করা, অন্য জাতি-গোত্রের সাথে যুদ্ধে জড়িয়ে পড়া, সবার আগে নিজের পরিবারের বা গোত্রের নিরাপত্তা নিয়ে চিন্তিত হওয়া ইত্যাদি। এগুলোর সাথে এখন যুক্ত হয়েছে বর্তমান সভ্যতার জটিল সাংস্কৃতিক উপাদান। এই জিন এবং সাংস্কৃতিক উপাদানের সুষম মিশ্রণেই গড়ে উঠে মানবপ্রকৃতি, যাকে উইলসন তার বইয়ে চিহ্নিত করেন ‘জিন-কালচার সহবিবর্তন’ (Gene-culture coevolution) নামে।
যখন অধ্যাপক উইলসনের বইটি প্রকাশিত হয়, তা একাডেমিয়ায় তুমুল বিতর্কের জন্ম দেয়। সমাজবিজ্ঞানীরা অধ্যাপক উইলসনের কাজকে দেখেছিলেন তাদের গবেষণার ক্ষেত্রে অযাচিত হস্তক্ষেপ হিসেবে। আর তাছাড়া সামাজিক ডারউইনিজম আর ইউজিনিক্সের দগদগে ঘা তখনো মানুষের মন থেকে শুকোয়নি। মানবপ্রকৃতি ব্যাখ্যা করতে গিয়ে ‘জিন’ বা বংশাণুকে নিয়ে আসায় উইলসনকে অভিযুক্ত হতে হয় নিও-সোশাল ডারউইনিস্ট অভিধায়। অভিযোগ করা হয় উইলসন নিজের জাতিবিদ্বেষী মনোভাবকে বিজ্ঞানের মোড়কে পুরে উপস্থাপন করতে চাচ্ছেন। উইলসনের বিরুদ্ধে সবচেয়ে সোচ্চার ছিলেন সে সময়কার ‘আদর্শবাদী চিন্তাবিদেরা। তাদের অধিকাংশই অর্থনৈতিক বিশ্লেষণ ছাড়া অন্য কোনো বিশ্লেষণ দিয়ে মানবপ্রকৃতিকে ব্যাখ্যা করার প্রয়াসকে মেনে নিতে বরাবরই অনাগ্রহী ছিলেন। science for the People নামের বাম ভাবাদর্শে দীক্ষিত একটি সংগঠন উইলসনের বিরুদ্ধে সে সময় সোচ্চার হয়ে ওঠে। ১৯৮৪ সালে রিচার্ড লেওনটিন, স্টিফেন রোজ এবং লিওন কামিন-এই তিন মাস্কেটিয়ার্স ১৯৮৪ সালে ‘নট ইন আওয়ার জিনস’ বইয়ে উইলসন এবং অন্যান্য সামাজিক জীববিজ্ঞানীদের আক্ষরিক অর্থেই তুলোধুনো করেন। তারা তাদের বইয়ে দেখানোর চেষ্টা করেন যে, বিজ্ঞান এখন জাত্যাভিমানী পশ্চিমা পুঁজিবাদি সমাজের প্রোপাগান্ডা মেশিনে পরিণত হয়েছে, আর উইলসন সেই বৈষম্যমূলক ‘পুঁজিবাদী বিজ্ঞান’কে প্রমোট করছেন। তারা উইলসনের জমজ নিয়ে পরীক্ষা, পরিগ্রহণ পরীক্ষা প্রভৃতির উপর পদ্ধতিগত আক্রমণ পরিচালনা করেন, শুধু তাই নয় তাদের মার্কসবাদী দার্শনিক বিশ্বাস থেকে প্রস্তাব করেন জীববিজ্ঞানেও মার্ক্সবাদের মতো ‘দ্বান্দ্বিক বা ডায়লেক্টিকাল পদ্ধতি অনুসরণ করা উচিত। এ নিয়ে অধ্যাপক রিচার্ড লেওনটিন একটি বইও লেখেন সে সময়—ডায়লেক্টিকাল বায়োলজিস্ট নামে।
এর প্রতিক্রিয়ায় বিবর্তনবাদী জীববিজ্ঞানী রিচার্ড ডকিন্স ১৯৮৫ সালে রিচার্ড লেওনটিন, স্টিফেন রোজ এবং লিওন কামিনের কাজের তীব্র সমালোচনা করে তাদের বইকে ‘স্কুল, আত্মাভিমানী, পশ্চাৎমুখী এবং ক্ষতিকর হিসেবে আখ্যায়িত করে ‘নিউ সায়েন্টিস্ট’ পত্রিকায় একটি প্রবন্ধ[৮] লেখেন। অধ্যাপক ডকিন্স অভিযোগ করেন যে, লেওনটিনরা নিজস্ব দার্শনিকভিত্তি থেকে মদদপুষ্ট হয়ে সামাজিক জীববিজ্ঞানীদের উপর যে সমস্ত অভিযোগ করেছেন এবং যেভাবে ভিত্তিহীন আক্রমণ পরিচালনা করেছেন তা স্ট্রম্যান হেত্বাভাস[৯] দোষে দুষ্ট। তিনি বলেন, বিজ্ঞানের কাজ হচ্ছে প্রকৃতির রহস্য উদঘাটন করা, কোনো ‘বৈষম্যমূলক পুঁজিবাদ’কে প্রমোট করা নয়।
সোশিওবায়োলজি বইটি প্রকাশের তিন দশক পরে আজ এ কথা নির্দ্বিধায় বলা যায়, উইলসন সামাজিক বিবর্তনবাদ নিয়ে যে কাজ শুরু করেছিলেন তা মৌলিক ছিল নিঃসন্দেহে। উইলসন সেই কাজটিই করেছিলেন যেটি ডারউইন পরবর্তী যে কোনো জীববিজ্ঞানীর জন্য হতে পারে মাইলফলক। তখন তিনি বিতর্কের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হলেও পরে অনেকেই তার কাজের গুরুত্ব অনুভব। করতে পেরেছিলেন। উইলসন মানবপ্রকৃতি নিয়ে তার ব্যতিক্রমধর্মী কাজের কারণে দু-দুবার পুলিৎসার পুরস্কার পেয়েছিলেন। শুধু তাই নয় উইলসন যে কাজটি সামাজিক জীববিজ্ঞানকে এখন দেখা হয় বিবর্তনের সাম্প্রতিক গবেষণার অন্যতম সজীব একটি শাখা হিসেবে, যা পরবর্তীতে আরও পূর্ণতা পেয়েছে বিবর্তনীয় মনোবিজ্ঞান (Evolutionary Psychology) নামের ভিন্ন একটি নামে। উইলসনের সোশিওবায়োলজি বইটির পর বিবর্তনীয় মনোবিজ্ঞানের জগতে অন্যতম উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হলো রিচার্ড ডকিন্সের ‘স্বার্থপর জিন’ (১৯৭৬) নামের অনন্যসাধারণ একটি বই[১০]। এই বইয়ের মাধ্যমে দকিন্স সুস্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করলেন কেন জেনেটিক দৃষ্টিভঙ্গি থাকা আমাদের জন্য খুবই প্রয়োজনীয়। তিনি তার বইয়ে দেখালেন যে, আমরা আমাদের এই দেহের পরিচর্যা নিয়ে যতই চিন্তিত থাকি না কেন দেহ কিন্তু কোনো প্রতিলিপি তৈরি করে না; প্রতিলিপি তৈরি করে বংশাণু বা জিন। তার মানে হচ্ছে আমাদের দেহ কেবল আমাদের জিনের বাহক (vehicle) হিসেবে কাজ করা ছাড়া আর কিছুই করে না। আমাদের খাওয়া-দাওয়া, হাসিকান্না, উচ্ছ্বাস, আনন্দ, সিনেমা দেখা, খেলাধুলা বা গল্প করা আমাদের দেহ যাই করুক শেষ পর্যন্ত ‘অত্যন্ত স্বার্থপর’ভাবে জিনকে রক্ষা করা আর জিনকে পরবর্তী প্রজন্মে পৌঁছে দেয়াতেই উদ্দেশ্য খুঁজে নিতে বাধ্য করে, বিবর্তনীয় দৃষ্টিকোণ থেকে জীবনের কোনো ‘উদ্দেশ্য যদি থেকে থাকে তবে সেটাই সে উদ্দেশ্য। মা বাবারা যে সন্তানদের সুখী দেখতে পাওয়ার জন্য পারলে জানটুকু দিয়ে দেয়–এটা কিন্তু জৈবিক তাড়না, আরও পরিষ্কার করে বললে জিনগত তাড়না থেকেই ঘটে। শুধু মানুষ নয় অন্য যে কোন প্রাণীর মধ্যেই সন্তানদের প্রতি অপত্য স্নেহ প্রদর্শন কিংবা সন্তানদের রক্ষা করার জন্য মা বাবারা সর্বোচ্চ ত্যাগ স্বীকার করে। অর্থাৎ, নিজের দেহকে বিনষ্ট করে হলেও পরবর্তী জিনকে রক্ষা করে চলে। পরবর্তী জিন রক্ষা না পেলে নিজের দেহ যত সুষম, সুন্দর, শক্তিশালী আর মনোহর কিংবা নাদুসনুদুস হোক না কেন, বিবর্তনের দিক থেকে কোনো অভিযোজিত মূল্য নেই। এক ধরনের ইঁদুর আছে যারা শুধু সঠিক সঙ্গী খুঁজে জিন সঞ্চালন করার জন্য বেঁচে থাকে। যৌনমিলনের পর পরই পুরুষ ইঁদুরটিমৃত্যুবরণ করে। অথচ এই মৃত্যুকূপের কথা জেনেও পুরুষ ইঁদুরটি সকল নিয়ে বসে থাকে ‘সর্বনাশের আশায়। এক প্রজাতির ‘ক্যানিবাল’ মাকড়শা আছে যেখানে স্ত্রী মাকড়শাটি যৌনমিলনের পর পরই পুরুষ মাকড়শাটিকে খেয়ে ফেলে। সাক্ষাৎ এই মৃত্যুর কথা জেনেও দেখা গেছে পুরুষ মাকড়শাগুলো জিন সঞ্চালনের তাড়নায় ঠিকই তাড়িত হয়। অর্থাৎ, দেহ এবং জিনের সংঘাত যদি উপস্থিত হয় কখনো সে সমস্ত বিরল ক্ষেত্রগুলোতে দেখা গেছে জিনই জয়ী হয় শেষপর্যন্ত। আমাদের দেহে ‘জাংক ডিএনএ’ কিংবা ‘সেগ্রেগেশন ডিস্টরশন জিন’-এর উপস্থিতি সেই সত্যটিকেই তুলে ধরে যে শরীরের ক্ষতি করে হলেও জিন অনেক সময় নিজেকে টিকিয়ে রাখে অত্যন্ত ‘স্বার্থপরভাবেই। এই বইয়ের মাধ্যমেই আসলে জীববিজ্ঞানীরা সমাজ এবং জীবনকে ভিন্নভাবে দেখা শুরু করলেন। পরার্থিতা, আত্মত্যাগ, দলগত নির্বাচনের মতো যে। বিষয়গুলো আগে বিজ্ঞানীরা পরিষ্কার করে ব্যাখ্যা করতে পারতেন না, সেগুলো আরও বলিষ্ঠভাবে জীববিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যাখ্যা করতে পারলেন তারা। তবে তার চেয়েও বড় যে ব্যাপারটি ঘটল, সেটা হলো মানবসমাজের বিভিন্ন সামাজিক প্যাটার্ন ব্যাখ্যা করার নতুন এক দুয়ার খুলে গেল জীববিজ্ঞানীদের জন্য। সেজন্যই ‘রিচার্ড ডকিন্সঃ কীভাবে একজন বিজ্ঞানী আমাদের চিন্তাভাবনার গতিপথকে সমূলে বদলে দিল’ নামের একটি বইয়ে তার সমসাময়িক বিজ্ঞানী এবং দার্শনিকেরা বলেছেন[১১], ডারউইনেরঅরিজিন অব স্পিশিজ–এরপর কোনো জীববিজ্ঞানীর লেখা বই যদি মানসপট এবং দৃষ্টিভঙ্গিকে পরিবর্তন করার ক্ষমতা রাখে, তো সেটি ডকিন্সের সেলফিশ জিন। এ ব্যাপারে ২০০১ সালে প্রকাশিত “সামাজিক জীববিজ্ঞানের সাফল্য নামের গ্রন্থে জন অ্যালকের মন্তব্যটি অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক।
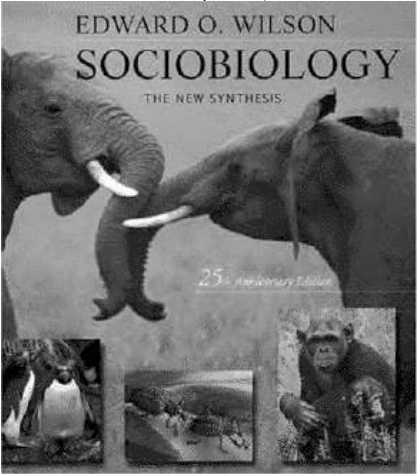
‘প্রাণিজগতের আচরণ নিয়ে বর্তমান গবেষণার ক্ষেত্রে কেউ ‘সোশিওবায়োলজি কিংবা সেলফিশ জিন শব্দগুলো নিয়ে বেশি কথা বলার কিংবা নতুন করে ব্যাখ্যা করার প্রয়োজনবোধ করেন না কারণ এগুলো এখন বিজ্ঞানের অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়ে গিয়েছে’।
ডারউইন ১৮৫৯ সালে যখন তার সেই বিখ্যাত গ্রন্থ অরিজিন অব স্পিশিজ লিখেছিলেন, তখন তিনি পুরো বইটিতে মানুষের বিবর্তন নিয়ে তেমন কোনো উচ্চবাচ্য করেননি। হয়তো অনাকাঙ্ক্ষিত বিতর্ক এড়াতে গিয়েই এই কৌশল নিয়েছিলেন ডারউইন, যদিও বইয়ে মানবসমাজ এবং বিবর্তন নিয়ে সুস্পষ্ট ইঙ্গিত দিয়েছিলেন এই বলে–”Light will be thrown on the origin of man and history। এবং একই প্যারাগ্রাফে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন–In the distant future… Psychology will be based on a new foundation.’
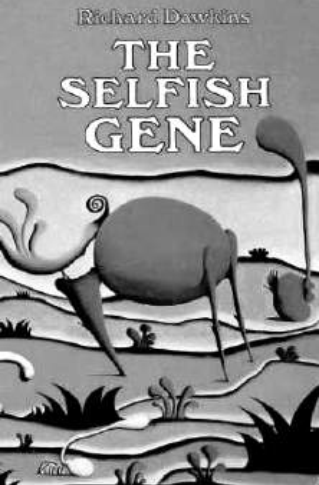
মজার ব্যাপার হলো–ডারউইন যেমন তার অরিজিন অব স্পিশিজ বইয়ে মানববিবর্তন নিয়ে আলোচনা করে ‘বিতর্কিত হতে চাননি, ঠিক। তেমনি তার একশ বছরেরও পরে বই লিখতে বসে ডকিন্স এবং উইলসনরাও তাদের হাটু কাঁপুনি থামাতে পারেননি। তারাও তাদের বইয়ে মানবসমাজ নিয়ে খুব বেশি আলোচনা করে ‘বিতর্ক’-এর কেন্দ্রবিন্দুতে আসতে হয়তো চাননি। ডকিন্সের ‘সেলফিশ জিন’ সুস্থ বৈজ্ঞানিক যুক্তি এবং আলোচনায় ভরপুর, কিন্তু প্রায় পুরোটাই তিনি সীমাবদ্ধ রেখেছিলেন নিম্নস্তরের প্রাণিজগতের ক্ষেত্রে। উইলসন তার ৫২৬ পৃষ্ঠার ঢাউস আকারের বইটির পুরোটুকুতেই পিঁপড়া আর পোকামাকড় নিয়েই পড়ে ছিলেন, মানুষ নিয়ে কথা বলেছিলেন শেষ ২৮ পৃষ্ঠায় এসে। তারপরও ডারউইন যেমন বিতর্ক এড়াতে পারেননি, আধা মানুষ আর আধা বানরের কার্টুনের কেরিক্যাচার হজম করতে হয়েছে, ঠিক তেমনি ডারউইনের উত্তরসূরীদের নানা ধরনের কটুক্তি হজম করতে হচ্ছে ডারউইনেরই ভবিষ্যদ্বাণী— ‘সাইকোলজি উইল বি বেসড অন এ নিউ ফাউন্ডেশন’-কে পূর্ণতা দিতে গিয়ে।
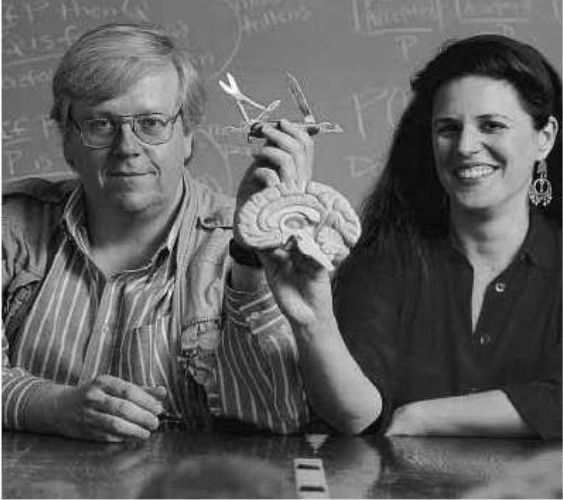
তবে আধুনিক ‘বিবর্তন মনোবিদ্যা’র জন্ম এদের কারো হাতে হয়নি, এর জন্ম হয়েছে মূলত এক সেলিব্রিটি দম্পতি জন টুবি (নৃতত্ত্ববিদ) এবং লিডা কসমাইডস (মনোবিজ্ঞানী)–এর হাত দিয়ে। তারা ১৯৯২ সালে ‘অভিযোজিত মনন’ নামে যে বইটি লেখেন সেটিকে আধুনিক বিবর্তনীয় মনোবিজ্ঞানের ভিত্তিমূল হিসেবে বিবেচনা করা হয়[১৩]। তারা এই বইয়ের মাধ্যমে প্রথমবারের মতো সমাজবিজ্ঞানের প্রমিত মডেলকে (standard social science model, সংক্ষেপে SSSM) প্রশ্নবিদ্ধ করেন এবং সামাজিক বিবর্তন এবং সংস্কৃতির বিভিন্ন রূপরেখা জৈববিজ্ঞানীয় দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যাখ্যা করেন। এই দৃষ্টিকোণটিকে আজ অনেকেই অভিহিত করছেন ‘মনের নতুন বিজ্ঞান’ (the new science of the mind) নামে। যারা জন টুবি এবং লিডাকসমাইডসের এই নতুন বিজ্ঞানের সাথে পরিচিত হতে চান, তারা অন লাইনে ‘Evolutionary Psychology: A Primer’[১৪] প্রবন্ধটি পড়ে নিতে পারেন (আমাদের মুক্তমনা সদস্য শিক্ষানবিস জন টুবি এবং লিডা কসমাইডসের প্রবন্ধটি নিজস্ব বিশ্লেষণ সহযোগে অনুবাদ করেছেন। তার অনুবাদটি রাখা আছে মুক্তমনায়[১৫])। জন টুবি আর লিডা কসমাইডস লেখাটিতে বিবর্তনীয় মনোবিজ্ঞানের মূলনীতি হিসেবে কতগুলো সূত্রেরও প্রস্তাব করেন। সেগুলো হলো–
প্রথম সূত্রঃ মস্তিষ্ক একটি ভৌত যন্ত্র যা অনেকটা কম্পিউটারের মতো কাজ করে। এর বর্তনীগুলো পরিবেশ উপযোগী স্বভাব তৈরি করে।
দ্বিতীয় সূত্রঃ প্রাকৃতিক নির্বাচনের মাধ্যমে আমাদের স্নায়বিক বর্তনীগুলো গড়ে উঠেছে। বিবর্তনের ইতিহাসে আমাদের পূর্বপুরুষেরা যেসব সমস্যার সম্মুখীন হয়েছিল সেগুলো সমাধান করার জন্যই প্রাকৃতিক নির্বাচন কাজ করেছে।
তৃতীয় সূত্রঃ আমাদের মনন বা চেতনাকে হিমশৈলের চূড়ার সাথে তুলনা করা যেতে পারে। হিমশৈলের বেশিরভাগ অংশই থাকে পানির নীচে লুকানো, ঠিক তেমনি আমাদের মনের মধ্যে যা কিছু ঘটে তার অধিকাংশই গোপন থাকে। সুতরাং চেতনা আমাদের এই বলে বিভ্রান্ত করতে পারে যে, মস্তিষ্কের বর্তনী বোধ হয় খুব সরল। আমরা প্রত্যহ যেসব সমস্যার সম্মুখীন হই সেগুলো সমাধান করা আপাতদৃষ্টিতে সহজ মনে হলেও প্রকৃতপক্ষে তার জন্য অনেক জটিল স্নায়বিক বর্তনীর জটিল যোগসাজোশের প্রয়োজন পড়ে।
চতুর্থ সূত্রঃ প্রতিটি অভিযোজনগত সমস্যা সমাধানের জন্য পৃথক পৃথক স্নায়বিক বর্তনী আছে। প্রতিটি বর্তনী কেবল নিজ কাজ করার জন্যই বিশেষায়িত।
পঞ্চম সূত্রঃ আমাদের আধুনিক করোটির ভিতরে বাস করে আদিম প্রস্তরযুগের মস্তিষ্ক[১৬]।
শিকারি–সংগ্রাহক পরিস্থিতি এবং সাভানা অনুকল্প
বিবর্তনীয় মনোবিজ্ঞান মনে করে প্রায় ৬ মিলিয়ন বছর আগে শিম্পাঞ্জি থেকে আলাদা হওয়ার পর সেখান থেকে শুরু করে আজ থেকে দশ হাজার বছর পর্যন্ত আমরা মানুষেরা মূলত বনে জঙ্গলেই কাটিয়েছি। সেই সময় থেকে শুরু করে আধুনিক সময়কাল বিবর্তনের পঞ্জিকায় হিসেব করলে খুবই ক্ষুদ্র একটা সময়। আর কৃষি কাজের উদ্ভব কিংবা তারো পরে শিল্প বিপ্লব ইত্যাদি তো আরও তুচ্ছ। সঠিকভাবে বলতে গেলে, মানুষ শিকারি সংগ্রাহক ছিল প্লাইস্টোসিন যুগের পুরো সময়টাতে: ২৫ লক্ষ বছর পূর্ব থেকে ১২,০০০ বছর পূর্ব পর্যন্ত। ‘হোমো’ গণ এর উদ্ভবের সময়কালটাও ২৫ লক্ষ বছর পূর্বের দিকে। তার মানে মানুষের ২৫ লক্ষ বছরের বিবর্তনের ইতিহাসে ৯৯% সময়ই তারা ছিল শিকারি-সংগ্রাহক। অর্থাৎ, ইভলুশনারি স্কেলে মানুষেরা মানব সভ্যতার শতকরা নিরানব্বই ভাগ সময়টাই বনে জঙ্গলে আর ফলমূল শিকার করে কাটিয়েছে। কাজেই আমাদের মস্তিষ্কের মূল নিয়ামকগুলো হয়তো তৈরি হয়ে গিয়েছিল তখনই, সে সময়কার বিশেষ কিছু সমস্যা মোকাবেলার জন্য আজকের দিনের অত্যাধুনিক সমস্যাগুলোর জন্য নয়। এখনও অনেকেই মাকড়শা, তেলাপোকা কিংবা টিকটিকি দেখলে আঁতকে উঠে, কিন্তু বাস ট্রাক দেখে সেরকম ভয় পায় না। এটা বিবর্তনের কারণেই ঘটে বলে মনে করা হয়। বনে-জঙ্গলে দীর্ঘদিন কাটানোর কারণে বিষধর কীটপতঙ্গকে ভয় পাওয়ার স্মৃতি আমরা নিজেদের অজান্তেই বহন করি। সেজন্যই লিডা কসমাইডস এবং জন টুবি আধুনিক মানুষকে সংজ্ঞায়িত করতে গিয়ে বলেন–আমাদের আধুনিক করোটির ভিতরে বাস করে আদিম প্রস্তরযুগের মস্তিষ্ক।
এই আধুনিক করোটির ভিতরে আদিম প্রস্তরযুগের মস্তিষ্ক বাস করার ব্যাপারটাকে বিবর্তনীয় মনোবিজ্ঞানে ‘সাভানা অনুকল্প’ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। এই প্রিন্সিপলটির মূল কথা হলো[১৭]—
মানব মস্তিষ্কের মডিউলগুলো যখন তৈরি হয়েছিল, তখন আধুনিক সমাজের বিদ্যমান উপকরণগুলোর অনেকগুলোই ছিল না। ফলে আধুনিক পরিস্থিতি মোকাবেলার জন্য আমাদের মস্তিষ্ক সম্পূর্ণ প্রস্তুত নয়, বরং মস্তিষ্কে অনেকাংশেই রাজত্ব করে আদিম পরিবশের উপজাতসমূহ।
১৯৯৪ সালে রবার্ট রাইট নামে একজন গবেষক একটি গুরুত্বপূর্ণ বই লিখলেন ‘মরাল এনিমেল’ নামে[১৮]। বিবর্তনীয় মনোবদ্যার উপর একটি পূর্ণাঙ্গ বই। এই বইয়ের লেখক প্রথমবারের মতো ‘সাহস করে’ ডারউইনের বিবর্তনের আলোকে মনোবিজ্ঞানকে ব্যাখ্যা করতে উদ্যোগী হন। শুধু তাই নয়, ডারউইনের জীবন থেকে অজস্র দৃষ্টান্ত হাজির করে দেখালেন, ভদ্র, সৌম্য, লাজুক স্বভাবের ডারউইনও শেষ পর্যন্ত আমাদের মতোই জৈব তাড়নায় তাড়িত একধরনের ‘এনিমেল’ ছাড়া আর কিছুই ছিলেন না। রবার্ট রাইটের বইটির পর এই বিষয়ে গণ্ডা গণ্ডা বই লেখা হয়েছে, এখনও হচ্ছে। গবেষকেরা এই ‘মনের নতুন বিজ্ঞান নিয়ে প্রতিনিয়ত গবেষণা করে যাচ্ছেন। গবেষকদের মধ্যে স্টিভেন পিঙ্কার, ডেভিড বাস, হেলেন ফিশার, জিওফ্রি মিলার, রবিন বেকার, ম্যাট রিডলী, ভিক্টর জন্সটন, সাতোসি কানাজাওয়া, ডনাল্ড সায়মন্স সহ অনেকেই আছেন। বিবর্তনীয় মনোবিজ্ঞানের বিভিন্ন আকর্ষণীয় বিষয় উপজীব্য করে বিগত কয়েক বছরে বিজ্ঞানী এবং গবেষকেরা লিখেছেন ‘হাও মাইন্ড ওয়ার্ক্স’[১৯], ‘এন্ট এন্ড দ্য পিকক’[২০], ‘দ্য রেড কুইন’[২১], ‘এনাটমি অব লাভ’[২২] ‘মেটিং মাইন্ড’[২৩], স্পার্ম ওয়ার্স[২৪] সহ অসংখ্য জনপ্রিয় ধারার বই। এছাড়া সফল টিভি প্রোগ্রামের মধ্যে আছে ‘দ্য সায়েন্স অব সেক্স’, ‘জেন্ডার ওয়ার্স’ ইত্যাদি। ইংরেজিতে বিবর্তন মনোবিজ্ঞান নিয়ে প্রচুর কাজ হলেও বাংলাভাষায় এ নিয়ে লেখা একদমই চোখে পড়ে না। মুক্তমনায় আমার সিরিজটির আগে এ নিয়ে কোনো পূর্ণাঙ্গ বিশ্লেষণও চোখে পড়েনি আমার। আমার এ সিরিজটি প্রকাশিত হবার পর অপার্থিব, বন্যা, স্বাধীন, পৃথিবী, বিপ্লব পাল, সংসপ্তক, মুহম্মদ (শিক্ষানবিস) সহ অনেকেই এনিয়ে আলোচনা করেছেন, প্রবন্ধও লিখেছেন অনেকেই।
বিবর্তনীয় মনোবিজ্ঞান নামের সাম্প্রতিক এই শাখাঁটি তাহলে আমাদের কী বলতে চাচ্ছে? সাদামাটাভাবে বলতে চাচ্ছে এই যে, আমাদের মানসপটের বিনির্মাণে দীর্ঘদিনের বিবর্তনীয় প্রক্রিয়ার একটি ছাপ থাকবে, তা আমরা যে দেশের, যে সমাজের বা যে সংস্কৃতিরই অন্তর্ভুক্ত হই না কেন। ছাপ যে থাকে, তার প্রমাণ আমরা দৈনন্দিন জীবনের অনেক কিছুতেই কিন্তু পাই। মিষ্টিযুক্ত কিংবা চর্বিযুক্ত খাবার আমাদের শরীরের জন্য খারাপ, কিন্তু এটা জানার পরও আমরা এ ধরনের খাবারের প্রতি লালায়িত হই। সমাজ-সংস্কৃতি নির্বিশেষেই এটা ঘটতে দেখা যায়। কেন? বিবর্তনীয় মনোবিজ্ঞানীরা বলেন, একটা সময় মানুষ জঙ্গলে থাকত, খুব কষ্ট করে খাবারদাবার সংগ্রহ করতে হতো। শর্করা এবং স্নেহজাতীয় খাবার এখনকার মতো এত সহজলভ্য ছিল না। শরীরকে কর্মক্ষম রাখার প্রয়োজনেই এ ধরনের খাবারের প্রতি আসক্তি তৈরি হয়ে গিয়েছিল। তখন তো আর কারো জানার উপায় ছিল না যে, হাজার খানেক বছর পর মানুষ নামের অদ্ভুত এই ‘আইলস্যা’ প্রজাতিটি ম্যাকডোনাল্ডসের বিগ-ম্যাক আর হার্শিজ হাতে নিয়ে কম্পিউটারের সামনে বসে বসে ব্লগ আর চ্যাট করে অফুরন্ত অলস সময় পার করবে আর গায়ে গতরে হোঁদল কুতকুতে হয়ে উঠবে। কাজেই খাবারের যে উপাদানগুলো একসময় ছিল আদিম মানুষের জন্য শক্তি আহরণের নিয়ামক কিংবা ঠান্ডা থেকে বাঁচার রক্ষাকবচ, আজকের যান্ত্রিক সভ্যতার যুগে সেগুলোর মাত্রাতিরিক্ত ব্যবহার হয়ে উঠেছে তাদের জন্য মরণ-বিষ। কিন্তু এগুলো জেনেও আমরা আমাদের লোভকে সংবরণ করতে প্রায়শই পারি না; পোলাও বিরিয়ানি কিংবা চকলেট বা আইসক্রিম দেখলেই হামলে পড়ি। আমাদের শরীরে আর মনে বিবর্তনের ছাপ থেকে যাওয়ার কারণেই এটি ঘটে।

এ ধরনের আরও উদাহরণ হাজির করা যায়। আমরা (কিংবা আমাদের পরিচিত অনেকেই) মাকড়শা, তেলাপোকা কিংবা টিকটিকি দেখলে আঁতকে উঠি। কিন্তু বাস ট্রাক দেখে সেরকম ভয় পাই না (উপরে শিকারি-সংগ্রাহক পরিস্থিতি ব্লক দ্রষ্টব্য)। অথচ কে না জানে, প্রতি বছর তেলাপোকার আক্রমণে যত মানুষ না মারা যায়, তার চেয়ে ঢের বেশি মানুষ মরে ট্রাকের তলায় পড়ে। অথচ ট্রাককে ভয় না পেয়ে আমরা ভয় পাই নিরীহ তেলাপোকাকে। এটাও কিন্তু বিবর্তনের কারণেই ঘটে। বনে-জঙ্গলে দীর্ঘদিন কাটানোর কারণে বিষধর কীটপতঙ্গকে ভয় পাওয়ার স্মৃতি আমরা নিজেদের অজান্তেই আমাদের জিনে বহন করি। সে হিসেবে, বাস ট্রাকের ব্যাপারগুলো আমাদের জন্য অপেক্ষাকৃত নতুন, তাই এগুলোকে ভয় পাওয়ার কোনো স্মৃতি আমরা এখনও আমাদের জিনে (এখনও) তৈরি করতে পারিনি। সেজন্যই বোধ হয় বিবর্তনীয় মনোবিজ্ঞানের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা লিডা কসমিডস এবং জন টুবি আধুনিক মানুষকে সংজ্ঞায়িত করতে গিয়ে বলেন—‘our modern skull house a stone age of mind’।
বিবর্তনীয় মনোবিজ্ঞান : চেনা সমীকরণের ভুলে যাওয়া অংশটুকু
মানুষের প্রকৃতি গঠনে পরিবেশ এবং জিন দুইয়েরই জোরালো ভূমিকা আছে। পরিবেশের যে ভূমিকা আছে সেটা সবারই জানা। বড় বড় সমাজবিজ্ঞানী থেকে শুরু করে রাজনীতিবিদ, শ্রমিক, শিক্ষক, অভিভাবকসহ সবাই পরিবেশের গুরুত্বের কথা জানেন। কিন্তু সেই তুলনায় মানবপ্রকৃতি গঠনের পেছনে যে জিনেরও জোরালো ভূমিকা আছে সেটা কিন্তু বহু লোকেই জানে না। সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক অঙ্গনে তো বটেই, এমনকি শিক্ষায়তনেও ব্যাপারাটা উহ্যই ছিল এতদিন। এখন সময় পাল্টেছে। বিবর্তনীয় মনোবিজ্ঞানীরা আকর্ষণীয় গবেষণায় প্রতিদিনই হারিয়ে যাওয়া অংশের খোঁজ পাচ্ছেন। এই বইয়ে পরিবেশ এবং জিন নিয়ে কমবেশি আলোচনা করা হলেও, প্রাজ্ঞ পাঠকদের দৃষ্টি এড়াবে না যে, অনাদরে উপক্ষিত অংশটির উপরেই বেশি জোর দেয়ার চেষ্টা করা হয়েছে, এবং তা করা হয়েছে সঙ্গত কারণেই। আমার মতে জিন তথা জৈববিজ্ঞানের অংশটুকু আমাদের অতি চেনা সমীকরণের ‘ভুলে যাওয়া অংশ। আধুনিক গবেষণার নিরিখে নতুন নতুন তথ্য আমরা জানতে পারছি, তা বস্তুনিষ্ঠভাবে বাঙালি পাঠকদের কাছে তুলে ধরাই এই বইয়ের মূল উদ্দেশ্য।
যে কথাটি এই বইয়ে বারে বারে আসবে তা হলো, বিবর্তন মনোবিদ্যা শুধু নতুন দৃষ্টিভঙ্গি থেকে সমাজ এবং জীবনকে ব্যাখ্যা করছে না, সেই সাথে সামাজিক বিজ্ঞানের বহু প্রচলিত অনুকল্প এবং ধারণাকেও প্রশ্নবিদ্ধ করে ফেলেছে। সারমর্ম করলে ব্যাপারগুলো দাঁড়াবে অনেকটা এরকম–
ক)মানুষ বিচ্ছিন্ন কিছু নয়, জীবজগতেরই অংশঃ বিবর্তন মনোবিজ্ঞানের প্রথম স্বীকার্যই হচ্ছে মানুষকে জীবজগতেরই অংশ হিসেবে চিন্তা করা। যতই অস্বস্তি লাগুক। আমাদের শুনতে, জীববিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে মানুষ এক ধরনের পশু বৈ আর কিছু নয়[২৬]। তার মানে কিন্তু এই নয় যে মানবসমাজে কোনো অনন্য বৈশিষ্ট্য নেই। নিশ্চয় আছে। সে জন্যই তো মানুষ আলাদা একটি প্রজাতি। কুকুর, বিড়াল, হাতি, গরিলা যেমন আলাদা প্রজাতি, ঠিক তেমনি মানুষও একটি প্রজাতি। আর মানুষের মতো সব প্রজাতিতেই অনন্য বৈশিষ্ট্য খুঁজলে পাওয়া যাবে। মেরুভল্লুকের লোমশ শরীর, মৌমাছিদের ফুল থেকে মধু আহরণের ক্ষমতা, কুকুরের ঘ্রাণ শক্তি কিংবা চিতা বাঘের ক্ষীপ্রতা নিঃসন্দেহে তাদের নিজ নিজ প্রজাতির জন্য অনন্য বৈশিষ্ট্য। সেই বৈশিষ্ট্যগুলো আমরা জৈববৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ থেকেই ব্যাখ্যা করি। অথচ মানবপ্রকৃতিকে ব্যাখ্যা করতে গেলেই জীববিজ্ঞান বাদ দিয়ে কেবল সামাজিক মডেলগুলোর শরণাপন্ন হন সমাজবিজ্ঞানীরা। এমন একটা ভাব যে, মানুষ অন্য প্রাণিজগৎ থেকে আলাদা বা বিচ্ছিন্ন কিছু, জীববিজ্ঞান এখানে অচল। না, এই দৃষ্টিভিঙ্গিটিকেই ভুল বলে মনে করেন সামাজিক জীববিজ্ঞানী এবং বিবর্তন মনোবিজ্ঞানীরা। বিখ্যাত সামাজিক জীববিজ্ঞানী পিয়ারি এল ভ্যান দেন বার্গি (Pierre L. van den Berghe) সেজন্যই বলেন–
নিঃসন্দেহে আমরা অনন্য। কিন্তু আমরা স্রেফ অনন্য হবার জন্য অনন্য নই। বৈজ্ঞানিকভাবে চিন্তা করলে প্রতিটি প্রজাতিই আসলে অনন্য, এবং তাদের অনন্য বৈশিষ্ট্যগুলো পরিবেশের সাথে অভিযোজন করতে গিয়ে দীর্ঘদিনের বিবর্তনের ফলশ্রুতিতেই উদ্ভূত হয়েছে।
মানবসমাজের কিছু অনন্য বৈশিষ্ট্য কিংবা জটিলতা বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও মানুষ শেষ পর্যন্ত জীবজগতেরই অংশ। অথচ, সমাজবিজ্ঞানের প্রচলিত প্রমিত মডেল মানুষকে অন্য প্রাণিজগৎ থেকে একেবারেই আলাদা করে ফেলে দেখার পক্ষপাতি। অতীতে বহু সমাজবিজ্ঞানীই জৈবিক ব্যাখ্যার মাধ্যমে মানবসমাজের গতি প্রকৃতি ব্যাখ্যার ব্যাপারে অনাসক্তি এবং ক্ষেত্রবিশেষে তীব্র আপত্তি উত্থাপন করেছেন। গবেষক এলিস লী দাবি করেছেন জৈবিক ব্যাখ্যার ব্যাপারে সমাজবিজ্ঞানীদের অনীহা, বিরক্তি এবং ভীতি যেটাকে এলিস ‘বায়োফোবিয়া’ বলে আখ্যায়িত করেছেন, ধীরে ধীরে শাখাঁটির পতন ডেকে আনছে[২৭]।
খ) মানব মস্তিষ্ক স্বর্গীয় কিছু নয়, বিবর্তন প্রক্রিয়ারই উপজাত: প্রতিটি জীব সেটা মানুষই হোক আর তেলাপোকাই হোক, কতগুলো কর্মক্ষম অংশের (functional parts) সমাহার। জীবের অভ্যন্তরীণ অঙ্গ, যেমন হৃৎপিণ্ড, ফুসফুস, চোখ, রক্ত, হাড়, মাংশপেশী, যকৃত, চামড়া, অন্ত্র, জননগ্রন্থি সবগুলোরই আলাদা কাজ আছে।

বলা বাহুল্য, আধুনিক চিকিৎসাবিদ্যা পুরোটাই দাঁড়িয়ে আছে এই কর্মক্ষম অংশগুলোর কাজকে আলাদাভাবে দেখার এবং সঠিকভাবে বিশ্লেষণের উপরেই। বিবর্তনীয় মনোবিজ্ঞানের পরিভাষায় বিভিন্ন অঙ্গের আলাদা কাজ করার ক্ষমতাকে বলে অভিযোজন বা এডাপ্টেশন। আর এই অভিযোজন ঘটে ‘প্রাকৃতিক নির্বাচন নামে একটি ধীর স্থির এবং দীর্ঘকালীন একটি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে। বিবর্তনীয় মনোবিজ্ঞানের মতে প্রাকৃতিক নির্বাচন দেহের অন্যান্য অঙ্গের বিকাশে যেভাবে প্রভাব রেখেছে, ঠিক সেরকমভাবেই প্রভাবিত করেছে মস্তিষ্ককে এবং এর সাথে জড়িত স্নায়বিক বর্তনীকেও। কাজেই মস্তিষ্ককেও বিবর্তনের উপজাত হিসেবেই দেখতে হবে, চিন্তা করতে হবে অভিযোজনের মিথস্ক্রিয়ার সমন্বিত প্রতিরূপ হিসেবেই[২৮]।
সমাজবিজ্ঞানীদের একটা বড় অংশই ভুলভাবে মনে করেন বিবর্তন বোধ হয় ঘাড়ের কাছে এসে থেমে গেছে, এর উপরে আর উঠেনি[২৯]। বিবর্তন মনোবিজ্ঞান নিয়ে গবেষণারত বিজ্ঞানীরা সমাজবিজ্ঞানীদের এই দৃষ্টিভঙ্গিকে একেবারেই ভুল মনে করেন। মানুষের হাতের আঙুল কিংবা পায়ের পাতা তৈরিতে যদি প্রাকৃতিক নির্বাচন এবং যৌনতার নির্বাচনসহ বিবর্তনের নানা প্রক্রিয়াগুলো ভূমিকা রেখে থাকে, মস্তিষ্ক তৈরির ব্যাপারেও এটি ভূমিকা রাখবে এটাই স্বাভাবিক। বিবর্তনীয় মনোবিজ্ঞানীরা বিবর্তনের যে সূত্রগুলোশরীরের অন্যান্য অঙ্গপ্রত্যঙ্গের গঠন এবং অভিব্যক্তি প্রকাশের জন্য সত্যি মনে করেন, সেগুলো মস্তিষ্কের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া বোঝার জন্যও ব্যবহার করতে চান। তারা (যৌক্তিকভাবেই) মনে করেন, বিবর্তন কখনোই ঘাড়ের কাছে হঠাৎ করেই এসে শেষ হয়ে যায়নি, বরং উঠে গেছে একদম উপর পর্যন্ত।
গ) মানবপ্রকৃতি কোনো ব্ল্যাঙ্ক স্লেট নয়: সমাজবিজ্ঞানীদের একটা বড় অংশ মানবপ্রকৃতিকে একটি ব্ল্যাঙ্ক স্লেট বা তাবুলা রাসা (Tabula rasa) হিসেবে দেখতে পছন্দ করেন[৩০]। তারা মনে করেন, প্রতিটি মানুষ একটা স্বচ্ছ স্লেটের মতো প্রকৃতি নিয়ে জন্মায়, আর তারপর মানুষ যত বড় হতে থাকে তার চারপাশের পরিবেশ ও পারিপার্শ্বিকতার মাধ্যমে ঐ স্বচ্ছ স্লেটে মানুষের স্বভাব ক্রমশ লিখিত হতে থাকে। কিন্তু বিবর্তন মনোবিজ্ঞান সংক্রান্ত বেশ কিছু সাম্প্রতিক গবেষণায় সমাজবিজ্ঞানীদের এই স্বতঃপ্রবৃত্ত বিরুদ্ধে বেশ কিছু জোরালো প্রমাণ পাওয়া গেছে। এ নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা করা হয়ছে এই বইয়ের দ্বিতীয় অধ্যায়ে। সেজন্যই জীববিজ্ঞানী উইলিয়াম হ্যামিলটন জোরের সাথে বলেন[৩১], “The tabula of human nature was never rasa and it is now being read”।
ঘ) মানবপ্রকৃতি এবং সংস্কৃতি বংশাণু এবং পরিবেশের মিথস্ক্রিয়ার ফলাফল : এই বইয়ের একটি গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা ব্যাপৃত হয়েছে পরিবেশ নির্ণয়বাদ বনাম বংশাণু নির্ণয়বাদকে কেন্দ্র করে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সমাজবিজ্ঞানীর যেহেতু ধরেই নেন যে, মানবপ্রকৃতি অনেকটা ব্ল্যাঙ্ক স্লেটের মতো, তাই তারা কেবল পরিবেশ এবং সামাজিকীকরণের উপরই জোর দেন, অস্বীকার করেন বংশগতি সংক্রান্ত যে কোনো উপাত্তকে যা মানবপ্রকৃতিকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। কিন্তু এই বইয়ে আধুনিক বিজ্ঞানের সাম্প্রতিক গবেষণা থেকে প্রাপ্ত তথ্যের আলোকে দেখানো হয়েছে যে, জেনেটিক এবং সাংস্কৃতিক উপাদানের সুষম মিশ্রণেই মূলত গড়ে উঠে মানবপ্রকৃতি। মানবপ্রকৃতি গঠনে জিন বা বংশাণুর প্রভাব যেমন আছে, তেমনি আছে পরিবেশের। তাই সম্পূর্ণ বংশাণুনির্ণয়বাদী হওয়া কিংবা সম্পূর্ণ পরিবেশ নির্ণয়বাদী হওয়াটা চরম এবং ভুল অবস্থান, এবং প্রায় সকল ক্ষেত্রেই। পাঠকেরা বইয়ের দ্বিতীয় এবং তৃতীয় অধ্যায়ে এ নিয়ে চিন্তার উদ্রেককারী গুরুত্বপূর্ণ কিছু আলোচনার সন্ধান পাবেন বলে আশা করছি।
প্রতিটি অধ্যায়েই উপরে উল্লিখিত বিষয়গুলো নানাভাবে উঠে আসবে, দেখানোর চেষ্টা থাকবে যে, মানবপ্রকৃতি আসলে জিন-কালচার কোএভুলুশনেরই ফল, এবং এ দুয়ের সুষম সংমিশ্রণ। কিন্তু সেখানে যাওয়ার আগে গুরুত্বপূর্ণ যে কয়েকটি হেত্বাভাস (fallacy) নিয়ে সতর্ক থাকা দরকার, তা নিয়ে একটু আলোচনা প্রয়োজন।
বিবর্তনীয় মনোবিজ্ঞান : যে হেত্বাভাসগুলো নিয়ে সতর্ক থাকা প্রয়োজন
কী বনাম উচিত এর হেত্বাভাস (“Is” vs. “Ought” fallacy): এই বইটি পড়লে পাঠকেরা মানবপ্রকৃতির সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশের একটা প্যাটার্নের ব্যাখ্যা পাবেন বেশিরভাগ জায়গাতেই। কিন্তু তার মানে এই নয় যে, সেই প্যাটার্নটাই আপনার আমার সবার জন্যই প্রযোজ্য, কিংবা সেটাই সর্বোত্তম। কেন সমাজ বা মানবপ্রকৃতির বড় একটা অংশ কোনো একটা নির্দিষ্ট ছকে আবদ্ধ থাকে সেটা বিবর্তনীয় মনোবিজ্ঞানের সাহায্যে ব্যাখ্যা করা যায়, সমাজ কী রকম হওয়া উচিত তা নয়। আরও পরিষ্কার করে বললে বিবর্তন কোনো অথোরিটি দাবি করে না। কাজেই বিবর্তনের মাধ্যমে পাওয়া তথ্য কেউ ব্যক্তিগত জীবনে কিংবা সমাজে প্রয়োগ করার ঔচিত্যের আহ্বান জানালে সেটা নিঃসন্দেহে একটি ভ্রান্তি বা হেত্বাভাস হবে। কী বনাম উচিত এর কুযুক্তিকে হেত্বাভাস হিসেবে সর্বপ্রথম তুলে ধরেন আঠারো শতকের বিখ্যাত স্কটিশ দার্শনিক এবং ইতিহাসবিদ ডেভিড হিউম[৩২]।
প্রাকৃতিক হেত্বাভাস (Naturalistic fallacy): আগেই বলেছি, এই বইয়ে বহু জৈবিক প্যাটানের প্রাকৃতিক ব্যাখ্যা পাবেন পাঠকেরা। কিন্তু কোনো কিছু প্রাকৃতিক হলেই সেটা ‘ভালো’ এরকম সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়াটা একটি বড় ধরনের ভ্রান্তি। যেমন, বিবর্তনের মাধ্যমে আমরা একটা প্রাকৃতিক ব্যাখ্যা পাই কেন পুরুষদের মন মানসিকতা প্রতিযোগিতামূলক হয়ে বেড়ে উঠেছে, কিংবা কেন তারা অপেক্ষাকৃত সহিংস আর কেন মেয়েরা গড়পড়তা পুরুষদের চেয়ে জৈবিকভাবে বেশি স্নেহপরায়ণ। কিন্তু তার মানে কেউ যদি মনে করেন যে, তাহলে মেয়েরা কেবল গৃহস্থালির কাজ করবে, শিশু আর তার স্বামীপ্রভুর যত্ন-আত্তি করবে, আর ছেলেরা বাইরে ডাণ্ডাগুটি মেরে বেড়াবে সেটা হবে একটি প্রাকৃতিক হেত্বাভাসের উদাহরণ। আমরা জানি এই বাংলাতেই এমন একটা সময় ছিল যখন বাল্যবিবাহ করা ছিল ‘স্বাভাবিক’ (রবীন্দ্রনাথ, বঙ্কিম সহ অনেকেই বাল্যবিবাহ করেছিলেন। আর মেয়েদের বাইরে কাজ করা ছিল ‘প্রকৃতি বিরুদ্ধ। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত মেয়েদের বাইরে কাজ করার বিপক্ষে একটা সময় যুক্তি দিয়ে বলেছিলেন এই বলে-
যেমন করেই দেখ প্রকৃতি বলে দিচ্ছে যে, বাইরের কাজ মেয়েরা করতে পারবে না। যদি প্রকৃতির সেরকম অভিপ্রায় না হতো, তা হলে মেয়েরা বলিষ্ঠ হয়ে জন্মাতো। যদি বল, পুরুষদের অত্যাচারে মেয়েদের এই দুর্বল অবস্থা হয়েছে, সে কোনো কাজেরই কথা নয়।
অর্থাৎ, রবীন্দ্রনাথের যুক্তি এখন মানতে গেলে কপালে টিপ দিয়ে, হাতে দু-গাছি সোনার বালা পরে গৃহকোণ উজ্জ্বল করে রাখা রাবীন্দ্রিক নারীরাই সত্যিকারের ‘প্রাকৃতিক। আর শত সহস্র আমিনা, রহিমারা যারা প্রখর রোদ্দুরে কিংবা বৃষ্টিতে ভিজে ইট ভেঙে, ধান ভেনে সংসার চালাচ্ছে, কিংবা পোশাক শিল্পে নিয়োজিত করে পুরুষদের পাশাপাশি ঘামে শ্রমে নিজেদের উজাড় করে চলেছে তারা সবাই আসলে প্রকৃতি বিরুদ্ধ’ কুকর্মে নিয়োজিত কারণ, প্রকৃতিই বলে দিচ্ছে যে, বাইরের কাজ মেয়েরা করতে পারবে না। বাংলাদেশের অখ্যাত আমিনা, রহিমাদের কথা বাদ দেই, নাসার মহাজাগতিক রকেট উৎক্ষেপন থেকে শুরু করে মাইনিং ফিল্ড পর্যন্ত এমন কোনো ক্ষেত্র নেই যেখানে মেয়েরা পুরুষদের পাশাপাশি আজ কাজ করছেন না। তাহলে? তাহলে আর কিছুই নয়। নিজের যুক্তিকে তালগাছে তোলার ক্ষেত্রে প্রকৃতি’ খুব সহজ একটি মাধ্যম, অনেকের কাছেই। তাই প্রকৃতির দোহাই পাড়তে আমরা ‘শিক্ষিত জনেরা’ বড্ড ভালোবাসি। প্রকৃতির দোহাই পেড়ে আমরা মেয়েদের গৃহবন্দি রাখি, জাতিভেদ বা বর্ণবাদের পক্ষে সাফাই গাই, অর্থনৈতিক সাম্যের বিরোধিতা করি, তেমনি সময় সময় সমকামী, উভকামীদের বানাই অচ্ছুৎ। কিন্তু যারা যুক্তি নিয়ে একটু আধটু পড়াশোনা করেছেন তারা জানেন যে, প্রকৃতির দোহাই পাড়লেই তা যুক্তিসিদ্ধ হয় না। বরং প্রকৃতির কাঁধে বন্দুক রেখে মাছি মারার অপচেষ্টা জন্ম দেয় এক ধরনের কুযুক্তি বা হেত্বাভাসের (logical fallacy)। ইংরেজিতে এই হেত্বাভাসের পুঁথিগত নাম হলো—‘ফ্যালাসি অব ন্যাচারাল ল’ বা ‘অ্যাপিল টু নেচার’[৩৪]। এমনি কিছু ‘অ্যাপিল টু নেচার’ হেত্বাভাসের উদাহরণ দেখা যাক–
১। মিস্টার কলিন্সের কথাকে এত পাত্তা দেওয়ার কিছু নেই। কলিন্স ব্যাটা তো কালো। কালোদের বুদ্ধি সুদ্ধি একটু কমই হয়। কয়টা কালোকে দেখেছ বুদ্ধি সুদ্ধি নিয়ে কথা বলতে? প্রকৃতি তাদের পাঁঠার মতো গায়ে গতরে যেটুকু বাড়িয়েছে, বুদ্ধি দিয়েছে সেই অনুপাতে কম। কাজেই তাদের জন্মই হয়েছে শুধু কায়িক শ্রমের জন্য, বুদ্ধিবৃত্তির চর্চার জন্য নয়।
২। মারামারি, কাটাকাটি হানাহানি, অসাম্য প্রকৃতিতেই আছে ঢের। এগুলো জীবজগতের স্বভাবজাত বৈশিষ্ট্য। কাজেই আমাদের সমাজে যে অসাম্য আছে, মানুষের উপর মানুষের যে শোষণ চলে তা খারাপ কিছু নয়, বরং ‘কমপ্লিটলি ন্যাচারাল’।
৩। প্রকৃতি বলে দিচ্ছে যে, বাইরের কাজ মেয়েরা করতে পারবে না। যদি প্রকৃতির সেরকম অভিপ্রায় না হতো, তা হলে মেয়েরা বলিষ্ঠ হয়ে জন্মাতো।
৪। সমকামিতা প্রকৃতিবিরুদ্ধ। প্রকৃতিতে তুমি কয়টা হোমোসেক্সয়ালিটির উদাহরণ দেখেছ?
৫। প্রকৃতিতে প্রায় প্রতিটি প্রজাতিতেই বহুগামিতা দৃশ্যমান, কাজেই মানবসমাজে বহুগামিতা গ্রহণ করে নেওয়াই সমীচীন।
উপরের উদাহরণগুলো দেখলে বোঝা যায়, ওতে যত না যুক্তির ছোঁয়া আছে, তার চেয়ে ঢের বেশি লক্ষনীয় ‘প্রকৃতি’ নামক মহাস্ত্রকে পুঁজি করে পাহাড় ঠেলার প্রবণতা। এমনি উদাহরণ দেওয়া যায় বহু। আমি আমার সমকামিতা (২০১০) বইয়ে[৩৫] এ ধরনের বহু প্রাকৃতিক হেত্বাভাসের উল্লেখ করেছিলাম। সেগুলো এই বইয়ের জন্যও প্রযোজ্য। প্রাকৃতিক হেত্বাভাসের ব্যাপারটি হেত্বাভাস হিসেবে সর্বপ্রথম তুলে ধরেন বিশশতকের প্রথমভাগে ইংরেজ দার্শনিক জর্জ এডওয়ার্ড মুর[৩৬]।
নৈতিক হেত্বাভাস (Moranistic fallacy): নৈতিক হেত্বাভাস হচ্ছে প্রাকৃতিক হেত্বাভাসের ঠিক উলটো। এর প্রবক্তা হার্ভাডের মাইক্রোবায়োলজিস্ট বার্নাড ডেভিস[৩৭]। এই ধরনের ভ্রান্তি যারা করেন, তারা ‘উচিত’কে ‘কী’ দিয়ে প্রতিস্থাপনের চেষ্টা করেন। কোনো কিছু নৈতিকভাবে সঠিক বলে মনে হলেই সেই ব্যাপারটাকে প্রাকৃতিক মনে করাটাই এই ভ্রান্তির মোদ্দাকথা। যেমন, ‘ধর্ষণ করা অনৈতিক, ফলে প্রকৃতিতে জীবজগতে কোথাও ধর্ষণ নেই’–এটা একটি নৈতিক হেত্বাভাসের উদাহরণ। কিংবা কেউ যদি বলেন, “মানবসমাজের শিক্ষায়তনে কোনো ধরনের বৈষম্য লালন করা হয় না, ফলে প্রকৃতিতেও কোনো ধরনের বৈষম্য নেই’–এটাও নৈতিক হেত্বাভাসের উদাহরণ হবে।
এই বইয়ে যতদূর সম্ভব এ ধরনের হেত্যুভাসগুলো এড়িয়ে চলার চেষ্টা করা হয়েছে। এই বইয়ের উদ্দেশ্য কেবল নির্মোহ বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণে দেখানো কীভাবে প্রকৃতি কিংবা সমাজের বিভিন্ন প্যাটার্ন কাজ করে, কিন্তু সমাজ কিংবা প্রকৃতি কেমন হওয়া উচিত তা নিয়ে কোনো মতামত দেয়া হয়নি। আমার প্রত্যাশা থাকবে আমার এই বইয়ের পাঠকেরাও এই বই থেকে কোনো ধরনের বৈধতাসূচক কোনো সিদ্ধান্তে উপনীত হবার আগে উপরের হেত্বাভাসগুলোকে স্মরণ করবেন।
“ভালোবাসা কারে কয়” বই সম্পর্কিত আপনার মন্তব্যঃ