প্রাচীনকাল থেকেই ঈশ্বরের প্রতি অগাধ আনুগত্য এবং ধর্ম বিশ্বাসকেই মানুষের নৈতিক চরিত্র গঠনের একমাত্র অবলম্বন বলে মনে করা হয়েছে। পাশ্চাত্য বিশ্বে গোঁড়া খ্রিস্টধর্মের অনুসারীরা সংগঠিত হয়ে অনেক আগে থেকেই মগজ ধোলাই করতে শুরু করেছে এ কথা প্রচার করে যে, ধর্মগ্রন্থগুলো আর তাদের ঈশ্বরই একমাত্র নৈতিকতা বিষয়ে শেষ কথা বলবার অধিকার রাখে। ধর্মগ্রন্থগুলোতে যেভাবে পথ দেখানো হয়েছে, সেগুলো অন্ধভাবে অনুসরণ করাই হল নৈতিকতা[৯৩]। আমাদের দেশি সংস্কৃতি তো আবার এগুলোতে সবসময়ই আবার আরও একধাপ এগিয়ে। অনেক বাসায় দেখেছি সেই ছেলেবেলা থেকেই ছোট ছেলে মেয়েগুলোর মাথা বিগড়ে দিয়ে বাংলা শেখার আগেই বাসায় হুজুর রেখে আরবি পড়ানোর বন্দোবস্ত করানো হয়, নয়ত হরি-কীর্তন শেখানো হয় আর নৈতিক চরিত্র গঠনের মূলমন্ত্র হিসেবে তোতা পাখির মতো আওরানো হয় নীরক্ত বাক্যাবলী- ‘অ্যাই বাবু, এগুলো করে না। আল্লাহ কিন্তু গোনাহ দিবে। ছোটবেলা থেকেই এইভাবে নৈতিকতার সাথে ধর্মের খিচুড়ি একসাথে মিশিয়ে এমনভাবে ছেলে-পিলেদের খাওয়ানো হয় যে তারা বড় হয়েও আর ভাবতেই পারে না যে ধর্ম মানা ছাড়াও কারো পক্ষে ভালো মানুষ হওয়া সম্ভব। কিন্তু সত্যিই কি ধর্মের সাথে নৈতিক চরিত্র গঠনের কোনো বাস্তব যোগাযোগ আছে? নামাজ, রোজা, হজ্জ, যাকাত, কৃষ্ণলীলা, তবলিগ জামাত ইত্যাদির মাধ্যমে গণ মানুষের নৈতিকতা উন্নয়নের যতই চেষ্টা করা হোক না কেন, সারা পৃথিবী জুড়ে ধর্মের নামে মারামারি, হানাহানি, হিংসা, শোষণ, নির্যাতন, দারিদ্র্য আর সন্ত্রাসের বিস্তার দেখে বোঝা যায়। যে ঈশ্বরে বিশ্বাস আসলে কোনো বিশাল অনুপ্রেরণা হয়ে মানুষের মধ্যে কথনোই কাজ। করে নি। কারণটা অতি পরিষ্কার। ঈশ্বরে বিশ্বাসের মাধ্যমে মরালিটি বা নৈতিকতা অর্জনের চেষ্টা করা আসলে সোজা পথে ভাত না গিলে কানের চারিদিকে হাত ঘুরিয়ে ভাত খাওয়ার মতন। প্রত্যেক ধর্মই বলছে বিধাতা ভালো মানুষকে পুরস্কৃত করেন আর পাপী-তাপী-নীতিহীনদের শাস্তি দেন। বোঝাই যায়, পুরস্কারের লোভটাই এখানে মুখ্য। নৈতিকতা বাদ দিয়ে অন্য যেকোনো উপায়ে আল্লাহকে তুষ্ট করে পুরষ্কার বগলদাবা করতে পারলে কোনো বান্দাই আর নৈতিকতার ধার ধারবে না। একটু ঠাণ্ডা মাথায় চিন্তা করলেই বোঝা যায় যে, রাম-নাম, হরিবোল, পাঁঠা বলি, কোরবানি, নামাজ, হজ্জ, কোরআন তেলাওয়াত, পূজা, যজ্ঞ এই সমস্ত ব্যাপার-স্যাপারগুলোর মাধ্যমে মানুষ আসলে নৈতিকতার কোনো ধার না ধেরে বিধাতার তুষ্টি লাভের প্রচেষ্টাতেই মত্ত। মানুষের প্রতি আর সমাজের প্রতি যাদের অবজ্ঞা আর প্রবঞ্চনা বেশি, তারাই কিন্তু বেশি-বেশি ‘আল্লা-আল্লা’ করে। হাজী সেলিমের মতো লোকের হজ্জ করার প্রয়োজনটা পড়ে বেশি, এরশাদের ‘আলহাজ্জ্ব হওয়ার শখ হয় প্রবল। কারণ ধর্মেই রযেছে সমস্ত আ-কাজ, কু-কাজ করেও পার পাবার ঢালাও ব্যবস্থা। মক্কা, জেরুজালেম, পুরী, বারানসী, তিরুপতি, এসব পবিত্র স্থান দর্শনে রয়েছে জীবনের সব পাপ ধুয়ে গিয়ে পরকালে স্বর্গবাসী হওয়ার নিশ্চিত গ্যারান্টি। কোটি টাকার চোরাকারবারী তাই ধুম-ধাম করে পূজা-যজ্ঞ করে নয়ত, শেষ বয়সে এলাকায় মন্দির গড়ে দেয় বেহেশতে একটা প্লট বুকিং দেবার আশায়।
উপরন্ত, যুক্তি আর বিজ্ঞানের অগ্রগতির সাথে সাথে সমাজ সচেতন মানুষ আজ বুঝতে শিখেছে যে, ঈশ্বর এক অর্থহীন অলীক কল্পনা মাত্র। রাহুল সাংকৃত্যায়নের ভাষায় ‘অজ্ঞানতার অপর নামই হলো ঈশ্বর। কাজেই অজ্ঞানতাকে পুঁজি করে ঈশ্বর নামক মিথ্যা-বিশ্বাসের মূলা ঝুলিয়ে মানুষের নৈতিক চরিত্র গঠনের কাহিনি আজ অনেকের কাছেই ‘শিশুতোষ গল্প’ ছাড়া আর কিছু নয়। বার্ট্রান্ড রাসেল তার ‘হোয়াই আই অ্যাম। নট আ খ্রিস্টান’ গ্রন্থে বলেন[৯৪]–
‘ধর্ম সম্পর্কে দু ধরনের আপত্তি করা যায়-বৌদ্ধিক এবং নৈতিক। বৌদ্ধিক আপত্তি অনুসারে বলা যায় যে, কোনো ধর্মকেই ধ্রুব সত্য বলে মেনে নেওয়ার কোনো যৌক্তিক কারণ নেই এবং নৈতিক আপত্তি অনুসারে বলা যায় ধর্মের উপদেশগুলো এমন সময় থেকে উঠে এসেছিল যখন মানুষ বর্তমান যুগের থেকেও অনেক নিষ্ঠুর ছিল। ফলে দেখা যাচ্ছে এই উপদেশগুলো অমানবিকতাকে চিরন্তন করবার জন্যই তৈরি। যদি এই চিরন্তন ব্যাপারটি গ্রহণে মানুষকে বাধ্য না করা হতো, তবে মানুষের নৈতিক বিবেকবোধ বর্তমানে আরো অনেক উন্নত হতো।’
ইন্টারনেটে লেখালিখি করতে গিয়ে ধার্মিকদের নানা (কু) যুক্তির সাথে পরিচয়ের তিক্ত অভিজ্ঞতা আমার রয়েছে। একবার এক ওযেব সাইটের জন্য বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ থেকে ধর্ম এবং নৈতিকতার মধ্যকার বিভিন্ন অসঙ্গতি নিয়ে লেখা শুরু করেছিলাম। লেখা শুরু করতে না করতেই এক ধার্মিক ভদ্রলোক সেখানে হুঙ্কার ছেড়ে তেড়ে আসলেন এই বলে
এদের মতো ব্যক্তিবর্গ যুগ যুগ ধরে এসেছে এবং ভূত হয়ে চলে গেছে। এদের সম্পর্কে কোরআনে উল্লেখ রয়েছে যে, তারা অন্ধ ও বর্বরা এদের হৃদয়ে সীলমোহর এঁটে দেওয়া আছে তারা কিছুই দেখতে পায় না এবং শুনতে পায় না। শুধু প্রাণীর মতো হাম্বা হাম্বা রব তোলে।
কোরআনে যদি সত্যিই এমনটি বলা থাকে (এবং কোরআনে সত্যিই অবিশ্বাসীদের অন্ধ/বর্বর, এবং এদের হৃদয়ে যে সীলমোহর এঁটে দেওয়া আছে তা বলা আছে; দেখুন সুরা ২:৭, ৪:১৫৫, ৭:১০০, ৭:১০১, ৯:৯৩, ১৬:১০৮, ৩০:৫৯, ৪৫:২৩ ইত্যাদি) বলতেই হয় মহান সৃষ্টিকর্তার রুচিবোধ সত্যিই প্রশংসনীয়। কেবল ধর্ম মানি না বলেই ভদ্রলোক আমাকে ‘অন্ধ’ ও ‘বর্বর’ বলেছেন, আর প্রমাণ স্বরূপ ‘সাক্ষী গোপাল’ মেনেছেন তার চির আরাধ্য ওই ধর্মগ্রন্থকেই। শুধু যে কোরআনেই অধার্মিকদের সম্বন্ধে এধরনের বিষোদগার করা হয়েছে তা ভাবলে ভুল হবে। শঙ্করাচার্য প্রমুখ দার্শনিকদের প্রাচীনকালের নাস্তিক্যবাদী চার্বাক দর্শনকে ‘লোকায়াত’ বা ইতর লোকের দর্শন হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করার প্রবণতাটির কথা এক্ষেত্রে বিবেচনা করা যেতেই পারে। এমন কি চার্বাক দর্শনের উৎপত্তি সম্বন্ধেও বলা হয় যে, মহাভারতের এক কুচরিত্র রাক্ষস চার্বাকের নাম থেকেই নাকি চার্বাক দর্শনের উৎপত্তি হয়েছে। মহাভারতে আছে, চার্বাক ছিল দুর্যোধনের বন্ধু এক দুরাত্মা রাক্ষস। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে জয়ের পর চার্বাক ব্রাহ্মণের ছদ্মবেশ ধারণ করে যুধিষ্ঠিরকে জ্ঞাতিঘাতী হিসেবে ধিক্কার জানিয়ে আত্মঘাতী হতে প্ররোচিত করেছিল। কিন্তু উপস্থিত ব্রাহ্মণেরা তাদের অতীন্দ্রিয় ক্ষমতায় চার্বাকের চালাকি ধরে ফেলে যুধিষ্ঠিরকে রক্ষা করেন। বোঝাই যায়, প্রাচীন ভাববাদীরা এই নাস্তিক্যবাদী দর্শনটির প্রতি সাধারণ মানুষের ঘৃণা সৃষ্টির উদ্দেশ্যেই এমন ঘৃণ্য চরিত্রের রাক্ষসের সাথে দর্শনটিকে জুড়ে দিতে সচেষ্ট হয়েছিলেন। আরেকটি উদাহরণ দেখি।
মহাভারতের শান্তিপর্ব। এক ধনী বণিক রথে যাওয়ার সময় এক ব্রাহ্মণকে ধাক্কা মেরে দিলো। ক্ষুব্ধ ব্রাহ্মণ অপমানের জ্বালা ভুলতে আত্মহত্যা করার কথা চিন্তা করলো। দেবরাজ ইন্দ্র ব্রাহ্মণের আত্মহত্যার মধ্যে সর্বনাশের সঙ্কেত দেখতে পেয়ে শিয়াল সেজে হাজির হলেন। ব্রাহ্মণকে তার পশু জীবনের নানা দুঃখ-দুর্দশার কথা বলে মানবজীবনের জয়গান গাইলেন। জানালেন অনেক জন্মের পুণ্যের ফল সম্বল করে এই মানব জন্ম পাওয়া। এমন মহার্ঘতম এই মানবজীবন আর তায় আবার ব্রাহ্মণ! এমন জীবন পাওয়ার পরও কি কেউ আত্মহত্যা করে? কাজেই অভিমানে আত্মহত্যা করা মোটেই বুদ্ধিমানের কাজ হবে না। শিয়াল বলল, সে নিজেও আগের জন্মে ব্রাহ্মণ হয়ে জন্মেছিল। কিন্তু সেই জন্মে সে চুড়ান্ত মূর্থের মতো এক মহাপাতকের কাজ করেছিল বলেই আজ এই শ্যিাল জন্ম। চুড়ান্ত মূর্থের মতো কাজটি কী? এ বারেই কিন্তু বেরিয়ে এলো নীতি কথা–
অহমাংস পণ্ডিতকো হৈতুকো দেবনিন্দকঃ
আম্বীক্ষিকীং তর্কবিদ্যঅনুরক্তো নিরার্থিকাম
হেতুবাদাপ্রবদিতা বক্তা মুংসৎসু হেতুমৎ।
আক্রোষ্টা চ অভিবক্তা চ ব্রাহ্মবাক্যেষু চ দ্বিজা।।
নাস্তিকঃ সর্বশী চ মূর্খ পণ্ডিতমানিকঃ
ভাষ্য ইয়ং ফলনিবৃত্তিঃ শৃগালত্বং মম দ্বিজ (শান্তিপর্ব ১৪০/৪৭-৪৯)
(অর্থাৎ, আমি ছিলাম এক বেদ সমালোচক পণ্ডিত। নিরর্থক তর্কবিদ্যায় ছিলাম অনুরক্ত। বিচার সভায় ছিলাম তর্কবিদ্যার প্রবক্তা। যুক্তিবলে দ্বিজদের ব্রহ্মবিদ্যার বিরুদ্ধে আক্রোশ মেটাতাম। ছিলাম জিজ্ঞাসু মনের নাস্তিক, অর্থাৎ কিনা পণ্ডিত্যাভিমানী মূর্খ। হে ব্রাহ্মণ, তারই ফলস্বরূপ আমার এই শিয়ালজন্ম)।
বোঝাই যায়, বৈদিক যুগেও যুক্তিবাদীদের সংশয, অযাচিত প্রশ্ন আর অনর্থক তর্ক বিতর্ক একটা ফ্যাক্টর’ হয়ে উঠেছিল। পণ্ডিত্যাভিমানী মূর্থ’- এধরনের লেবেল এঁটে দিযে বেদ-সমালোচকদের প্রতিহত করার প্রচেষ্টা তারই ইঙ্গিত বহন করে। আজকেও কি এ দৃষ্টিভঙ্গির খুব একটা পরিবর্তন হয়েছে? যে ভদ্রলোকটি আমাকে ধর্মগ্রন্থের সমালোচনা করার জন্য ‘অন্ধ’ বা ‘বর্বর’ হিসেবে চিত্রিত করছেন, সে ধরনের লোকজনের কিন্তু আজো সমাজে অভাব নেই, নাস্তিক শুনলেই তারা খ্যাঁক করে ওঠেন- “ও তুমি নাস্তিক! তবে তো তুমি যা ইচ্ছা তাই করতে পারো! তোমার তো চরিত্র বলে কিছু নেই। এরা আসলে নাস্তিকদের মানুষ বলেই মনে করেন না, ভালো-মানুষ ভাবা তো অনেক পরের কথা। কিন্তু, নাস্তিক মানেই কি অনৈতিক, চরিত্রহীন, লম্পট গোছের কিছু? এমনিভাবে ভাবার মোটেই কোনো কারণ নেই। নাস্তিকরা আসলে নাকের সামনে থেকে ঈশ্বর নামক মূলাটি সরিয়ে বাস্তবসম্মতভাবে ‘মরালিটি বা নৈতিকতাকে দেখবার পক্ষপাতী। ঈশ্বরের ভয়ে নয়, একটি সুন্দর এবং সুস্থ সমাজ গড়ে তুলবার প্রযোজনেই মানুষের চুরি, লাম্পট্য, খুন, ধর্ষণ। বিসর্জন দিয়ে সামাজিক মূল্যবোধগুলো গড়ে তোলা দরকার। নয়ত সমাজের ভিত্তিমূলই যে একসময় ধ্বসে পড়বে! কাজেই অধার্মিকদের চোখে ‘নৈতিকতা’ বেহেস্তে যাওয়ার কোনো পাসপোর্ট নয়, বরং নিতান্তই সামাজিক আবশ্যকতা। ধর্মান্ধরা যেহেতু সামাজিক-মূল্যবোধের এই বিষয়গুলো একেবারেই বুঝতে চান না, তাই তাদের মধ্যে যুদ্ধ, দাঙ্গা, জিহাদ, মারামারি লেগেই আছে। ১৯৭১ সালের কথাই ধরা যাক। সারা বাংলা হতবিহ্বল হয়ে দেখেছে কিছু ধর্মান্ধ মানুষ ধর্ম রক্ষা করতে গিয়ে কী করে পশুর স্তরে নেমে যেতে পারে।
এক ভদ্রলোককে চিনতাম। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক। সাতে-পাঁচে নেই; সাদা চোখে দেখলে নিতান্ত ভালোমানুষ বলেই মনে হবে। কিন্তু ভুক্তভোগীরা জানেন যে একাত্তরে ভদ্রলোক এহেন দুষ্কর্ম নেই যে করেন নি। সেসময় এমন কি তিনি ফতোয়া দিয়েছিলেন এই বলে যে, খান-সেনারা যদি কোনো বাঙালি মেয়েকে ধর্ষণ করে তবে সেটি অন্যায় বলে বিবেচিত হবে না, বঙ্গনারীরা পাক-বাহিনীর জন্য ‘মালে গনিমত’, কারণ তারা ইসলামের জন্য লড়ছে। এমন নয় যে ভদ্রলোক অশিক্ষিত ছিলেন, অথবা ছিলেন বুদ্ধিহীন। বরং সৎ এবং হৃদয়বান হিসেবেই একটা সময় তার খ্যাতি ছিল; কিন্তু এই ‘সজ্জন ব্যক্তিও স্রেফ ধর্মের প্রতি ভালোবাসায় অন্ধ হয়ে নেমে গেলেন পশুর স্তরে। উনি ভেবেছিলেন পাকিস্তান ভেঙ্গে গেলে ইসলাম হবে বিপন্ন। তাই ধর্ম বাঁচাতে যা যা করা দরকার সবই করেছেন। এমন কি খান সেনাদের সাথে পাল্লা দিয়ে তার বিরুদ্ধে ধর্ষণের অভিযোগও আছে। ব্যাপারটি অনেকের কাছে অবিশ্বাস্য মনে হলেও অতিমাত্রায় ধর্মপ্রবণদের জন্য এধরনের কাজ খুবই স্বাভাবিক। অনেক সময়ই মানবিকতার চেয়ে তাদের কাছে ধর্মবোধটাই বড় হয়ে দাঁড়ায়। এই ভদ্রলোকের কথা ভাবলেই নোবেল বিজয়ী পদার্থবিদ স্টিভেন ওযাইনবার্গের বিখ্যাত উক্তিটি মনে পড়ে যায়[৯৫]–
‘ধর্ম মানবতার জন্য এক নির্মম পরিহাস। ধর্ম মানুক বা নাই মানুক, সবসময়ই এমন অবস্থা থাকবে যে ভালো মানুষেরা ভালো কাজ করছে, আর খারাপ মানুষেরা খারাপ কাজ করছে। কিন্তু ভালো মানুষকে দিয়ে খারাপ কাজ করানোর ক্ষেত্রে ধর্মের জুড়ি নেই।‘
কেবল একাত্তরে নয়, ২০০২ সালে গুজরাটে ঘটে যাওয়া মর্মান্তিক দাঙ্গা, কিংবা তারও আগে অযোদ্ধায় বাবরি মসজিদ ভেঙ্গে শিবসেনাদের তাণ্ডব নৃত্য ধর্মের এই ভয়াবহ রূপটিকেই স্মরণ করিয়ে দেয়। অপরপক্ষে নাস্তিকদের যেহেতু এই অতিমানবিক সত্তা-কেন্দ্রিক নৈতিকতায় কোনো বিশ্বাস নেই, একজন নিষ্ঠাবান নাস্তিক সত্যিকার অর্থে গড়ে উঠতে পারেন একজন যথার্থ প্রথা-বিরোধী মানুষ হিসেবে। সুমন তুরহান নামে এক লেখক মাসিক দেশ পত্রিকার ৪ নভেম্বর ২০০২ সংখ্যায় ‘নাস্তিকতার সংজ্ঞা’ শীর্ষক প্রবন্ধে লিখেছিলেন[৯৬]–‘নাস্তিকদের অবিশ্বাস তাই শুধু অতিমানবিক সত্তায় নয়, তারচেয়ে অনেক গভীরে, তিনি অবিশ্বাস করেন প্রথাগত সভ্যতার প্রায় সমস্ত অপবিশ্বাসে। সবকিছুই তারা যুক্তি দিয়ে বিচার করে দেখতে চান। এর মধ্যে কিছুটা হলেও যে সত্যতা নেই তা নয়। তবে ভালোমানুষ হোন, আর নাই হোন এটা কিন্তু ঠিক যে নাস্তিক বা অধার্মিকদের মধ্যে থেকে কখনোই আল-কায়েদা, তালিবান, হরকত-উল-জিহাদ, রাজাকার, আলবদর বা শিবসেনাদের মতো সাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠানের সাংগঠনিকরূপ দেখা যায় না। যতদিন ধর্ম থাকবে, ঈশ্বরে বিশ্বাস থাকবে ধর্মের সাম্প্রদায়িক এই সাংগঠনিক রূপটিও কিন্তু বজায় থাকবে পুরোমাত্রায়। কাজেই যতদিন মানুষের আনুগত্য ঈশ্বর এবং মানুষের মধ্যে বিভক্ত। হয়ে থাকবে ততদিন তা মানুষকে স্বাধীনভাবে আর বিজ্ঞানসম্মতভাবে নৈতিকতা ও মূল্যবোধ অর্জনে বাধা দেবেই। বেহেস্তের লোভে বা ঈশ্বরকে তুষ্ট করার জন্য নয়, মানুষকে ভালোবেসে মানুষের জন্য কাজ করার প্রচেষ্টা যদি আন্তরিক হয়, তবেই গড়ে উঠবে সার্বজনীন মানবতাবাদ। সম্প্রতি এর প্রচেষ্টা শুরুও হয়েছে। ঈশ্বরকেন্দ্রিক মিথ্যার বেসাতি মন থেকে সরিয়ে শুধু মানুষের জন্য মানুষের কাজ করার বাসনা নিয়ে সারা পৃথিবী জুড়ে নতুন শতকের আধুনিক মতবাদ হিসেবে এসেছে হিউম্যানিজম। এমন কি আমাদের পার্শ্ববর্তী দেশ ভারতে মানবতাবাদী সমিতি এবং যুক্তিবাদী সমিতি অফিস আদালতের ফর্মে বা বিয়ের রেজিস্ট্রেশনে ‘হিন্দু’, ‘মুসলিম’ এই শব্দগুলোর পাশাপাশি ধর্মের জায়গায় ‘মনুষ্যত্ব’ শব্দটি ব্যবহারের আইনি অধিকার আদায় করেছে[৯৭]। এ প্রসঙ্গে ভারতীয় যুক্তিবাদী প্রবীর ঘোষের একটি চমৎকার উক্তি তার ‘অলৌকিক নয়, লৌকিক গ্রন্থ থেকে হুবহু তুলে দিচ্ছি[৯৮]–
‘আগুনের ধর্ম যেমন দহন, ছুরির ধর্ম যেমন তীক্ষ্ণতা তেমনি মানুষের ধর্ম হওয়া উচিত মনুষ্যত্বের বিকাশ সাধন। আর সে হিসেবে নামাজ না পড়েও বা শনি শীতলার পূজা না করেও আমরা যুক্তিবাদী নাস্তিকেরাই প্রকৃত ধার্মিক, কারণ আমরা মনুষ্যত্বের চরম বিকাশ চাই।
ধর্মগ্রন্থগুলো কি সত্যিই নৈতিকতার ধারক এবং বাহক?
ইদানীং এক নতুন ধরনের প্রগতিবাদী (নাকি সুবিধাবাদী আন্দোলন শুরু হয়েছে, যার মূলমন্ত্র হলো ধর্ম নয় কেবল মৌলবাদকে আঘাত করো। মুক্তমনা যুক্তিবাদীদের অনেকেই দেখছি বুঝে হোক, না বুঝে হোক এ প্রচারণায় গা ভাসিয়ে দিযে রাজনৈতিক নেতাদের মতোই ইদানীং সোচ্চারে বলছেন: “শরীরের শেষ রক্তবিন্দু দিয়ে হলেও মৌলবাদ রুখব’, যেন মৌলবাদ ব্যাপারটি হঠাৎ করেই আকাশ থেকে আবির্ভূত হয়েছে মহীরুহ আকারে কোনো শিকড়-বাকড় ছাড়াই। যারা ধর্মকে শাশ্বত চিরন্তন আর জনকল্যাণমূলক বলে মনে করেন আর যত দোষ চাপাতে চান কেবল মওদুদী, গোলাম আজম, আদভানী কিংবা ‘মৌলবাদ’ নামক নন্দঘোষটির ঘাড়ে, তাদের প্রথমে খোদ মৌলবাদ’ শব্দটিকেই বিশ্লেষণ করে দেখতে বলি। মৌল’ শব্দের অর্থ মূল থেকে আগত, বা “মূল সম্বন্ধীয়’ আর ‘বাদ’ শব্দের অর্থ যে ‘মত’, ‘তত্ব’ বা ‘থিওরি’, তা তো আমরা জানিই। তা হলে মৌলবাদ শব্দের প্রকৃত অর্থ কী দাঁড়ালো? দাঁড়ালো- মূল থেকে আগত তত্ব। কোন্ মূল থেকে আগত তত্ব? শেষ পর্যন্ত ওই ধর্মগ্রন্থের গোঁড়া মূলনীতিগুলো হতে আগত তত্ব। কাজেই বিচার বিশ্লেষণ করতে গিয়ে কিন্তু থলের বিড়াল ঠিকই বেরিয়ে পড়ছে যে, ধর্মশাস্ত্রের মূলনীতিগুলোকে চরম সত্য বলে যারা মনে করেন, তারাই শেষ পর্যন্ত মৌলবাদী হন। মৌলবাদ শব্দের ইংরেজি প্রতিশব্দ হলো ‘Fundamentalism’। এর সংজ্ঞা দিতে গিয়ে অক্সফোর্ড ডিকশনারিতে বলা হয়েছে- “Strict maintenance of traditional scriptural beliefs’; চেম্বার্স ডিকশনারি শব্দটি সম্পর্কে বলছে ‘Belief in literal truth in Bible, against evolution etc.’। কাজেই ধর্মকে বাদ দিয়ে মৌলবাদ রুখবার চেষ্টা অনেকটা বিষবৃক্ষের গোঁড়ায় পানি ঢেলে তাকে বাঁচিয়ে রেখে আগায় কাঁচি চালানোর প্রচেষ্টা, নিছক ভণ্ডামি। প্রসঙ্গত তসলিমা নাসরিন একবার একটি ইংরেজি সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন[৯৯]–
‘আমি সাধারণভাবে মৌলবাদীদের আর সেইসাথে ধর্মের- দুয়েরই সমালোচনা করেছিলাম। আমি আসলে ইসলামের সাথে ইসলামি মৌলবাদের কোনো তফাৎ দেখি না। আমি মনে করি ধর্মই হচ্ছে মূল উৎস, যেটি থেকে মৌলবাদ নামক বিষাক্ত ডালপালাগুলো সময় সময় বিস্তার লাভ করে। যদি আমরা ধর্মকে অক্ষত রেখে দেই, কেবল মৌলবাদ নামক একটি ডালকে হেঁটে ফেলতে সচেষ্ট হই, দেখা যাবে কিছু দিন পর মৌলবাদের আরেকটা শাখা অচিরেই বেড়ে উঠেছে। আমি খুব পরিষ্কারভাবেই এটি বলছি কারণ, কিছু উদারপন্থী লোকজন আছেন যারা। এধরনের প্রশ্নে ইসলামকে ডিফেন্ড করেন আর সমস্ত সমস্যার জন্য কেবল মৌলবাদীদের ঘাড়ে দোষ চাপিয়ে দিয়ে ক্ষান্ত হন। কিন্তু ইসলাম নিজেই তো নারী-নির্যাতনকারী। ইসলাম নিজেই তো গণতন্ত্র সমর্থন করে না আর সমস্ত মানবিক অধিকার হরণ করে।‘
আমার এক পরিচিতজন আছেন- সেকুলার এবং প্রগতিশীলতার দাবিদার। কিন্তু তসলিমার এই সাক্ষাৎকার পড়ে তার যেন পিত্তি জ্বলে গেল! তসলিমা ‘শ্যালো’, তসলিমা ‘নির্বোধ’, তসলিমা ‘ইডিয়ট’, কী নন তিনি! বুঝলাম, তসলিমার বড় অপরাধ তিনি ধর্ম আর মৌলবাদকে এক করে ফেলেছেন। কিন্তু তসলিমা ভুল বলছেন না ঠিক বলছেন সেটি বিশ্লেষণ করতে হলে নির্মোহ সংশয়বাদী দৃষ্টিকোণ থেকে ধর্মগ্রন্থগুলোর দিকে তাকানো দরকার। আসুন প্রিয় পাঠক, আমরা যুক্তিবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে বিশ্লেষণ করে দেখি ধর্মগ্রন্থগুলোর সাথে মৌলবাদের সত্যিই কোনো প্রত্যক্ষ যোগাযোগ আছে কিনা, এবং ধর্মগ্রন্থগুলো আদপেই ‘নৈতিকতার ভাণ্ডার হিসেবে পরিচিত হবার যোগ্যতা রাখে কিনা!
ধর্মগ্রন্থগুলো আসলে কী বলছে?
পৃথিবীতে প্রচলিত ধর্মমতগুলো সৃষ্টি হয়েছে বড় জোর বিগত ২-৪ হাজার বছরের মধ্যে। হিন্দু, ইসলাম কিংবা খ্রিস্ট ধর্ম কোনোটাই সে অর্থে চিরন্তন বা সনাতন নয়। কাজেই ‘সনাতন ধর্ম’ নিছকই একটি ভ্রান্ত বিশ্বাস। তবে সনাতন না হলেও ধর্ম সৃষ্টির প্রক্রিয়া শুরু কিন্তু হয়েছিল বহু হাজার বছর আগে। বিরূপ প্রকৃতির নানা দুর্যোগ- দাবানল, প্লাবন, বজ্রপাত প্রভৃতির ব্যাখ্যা খুঁজতে অসহায় হয়ে আর ওগুলোর হাত থেকে মুক্তি খুঁজতে মানুষ সৃষ্টি করেছিল নানা দেবদেবীর; মৃত্যুকে সঠিকভাবে ব্যাখ্যা না করতে পেরে সৃষ্টি করেছিল অদৃশ্য আত্মারা যারা সমাজ বিজ্ঞান নিয়ে সামান্য পড়াশোনা করেছেন তারাই এগুলো জানেন। আর এখন পর্যন্ত জানা তথ্যের ভিত্তিতে বলা যায়, মানুষের মধ্যে তথাকথিত ‘ধর্মবিশ্বাসের সৃষ্টি হয়েছিল নিয়াণ্ডার্থাল মানুষের আমলে- যারা পৃথিবীতে রাজত্ব করেছে এখন থেকে প্রায় আড়াই লক্ষ বছর আগে। নিয়ান্ডার্থাল মানুষের আগে পিথেকানথ্রোপাস আর সিনানথ্রোপাসদের মধ্যে ধর্মাচরণের কোনো নিদর্শন পাওয়া যায় নি। তবে নিয়ান্ডার্থাল মানুষের বিশ্বাসগুলো ছিল একেবারেই আদিম- আজকের দিনের প্রচলিত ধর্মমতগুলোর তুলনায় একেবারেই আলাদা। এখন থেকে ৪০-১৮ হাজার বছর আগে উচ্চতর পুরা-প্রস্তর যুগে এসে আত্মা, পরমাত্মা, ধর্মীয় আচার আর জাদুবিদ্যা সংক্রান্ত ব্যাপার-স্যাপারগুলো সুসংহত হয়। আজকের দিনের ধর্মবিশ্বাসগুলোর মধ্যে বৈদিক ধর্মের (হিন্দু ধর্মের পূর্বসূরি) উদ্ভব হয়েছিল আজ থেকে মাত্র ৩৫০০ বছর আগে, ইসলাম ধর্ম এসেছে ১৪০০ বছর আগে, খ্রিস্টধর্ম ২০০০ বছর আগে, ইত্যাদি। একটা সময় সামাজিক প্রয়োজনে যে ধর্মীয় রীতিনীতি নিয়ম কানুন তৈরি হয়েছিল, আজ তার অনেকগুলোই কালের পরিক্রমায় স্থবির, পশ্চাৎপদ, নিবর্তনমূলক এবং অমানবিক বলে প্রতীয়মান হয়েছে। ইতিহাস পরিক্রমায় দেখা যায় ফোনিকান, হিব্রু, ক্যানানাইট, মায়া, ইনকা, অ্যাজটেক, ওলমেক্স, গ্রিক, রোমান কার্যাগিনিয়ান, টিউটন, সেল্ট, ভুইড, গল, থাই, জাপানি, মাউরি, তাহিতিয়ান, হাওয়াই অধিবাসী- সবাই নিজ নিজ ধর্ম অনুযায়ী দেদারসে শিশু, নারী, পুরুষ বলি দিয়েছে তাদের অদৃশ্য দেব-দেবীদের তুষ্ট করতে। এই বইয়ের বহু জায়গাতেই এ নিয়ে আলোচনা আছে। তবে এই অধ্যায়ে আমরা কেবল প্রচলিত এবং গুরুত্বপূর্ণ ধর্মমতগুলোর ঐশী ধর্মগ্রন্থগুলোতে চোখ রাখব; আমরা নির্মোহভাবে বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করব, ধর্মগ্রন্থগুলো আসলে কী বলছে।
যারা কোরআন আগাগোড়া পড়েছেন তারা সকলেই জানেন, পবিত্র কোরআনের বেশ অনেকটা জুড়েই রয়েছে উত্তেজক নির্দেশাবলী। যেমন[১০০]__
কোরআন আহ্বান জানাচ্ছে যেখানেই অবিশ্বাসীদের পাওয়া যাক তাদের হত্যা করতে (২:১৯১, ৯:৫), তাদের সাথে সংঘাতে লিপ্ত হতে, কঠোর ব্যবহার করতে (৯:১২৩), আর যুদ্ধ করে যেতে (৮:৬৫)। বিধর্মীদের অপদস্থ করতে আর তাদের উপর জিজিয়া কর আরোপ করতে (৯:২৯)। অন্য সকল ধর্মের অনুসারীদের কাছ থেকে ধর্মীয় স্বাধীনতার নির্যাসটুকু কেড়ে নিয়ে সোচ্চারে ঘোষণা করছে যে ইসলামই হচ্ছে একমাত্র মনোনীত ধর্ম (৩:৪৫)। এটি অবিশ্বাসীদের দোজখে নির্বাসিত করে (৫:১০), এবং ‘অপবিত্র’ বলে সম্বোধন করে (৯:২৮); মুসলিমদের ততক্ষণ পর্যন্ত যুদ্ধ চালিয়ে যেতে আদেশ করে যতক্ষণ পর্যন্ত না অন্য সকল ধর্মকে সরিযে ইসলামি রাজত্ব কাযেম হয় (২:১৯৩)। কোরআন বলছে যে শুধু ইসলামে অবিশ্বাসের কারণেই একটি মানুষ দোজখের আগুনে পুড়বে আর তাকে সেখানে পান করতে হবে দুর্গন্ধময় পুঁজ (১৪:১৭)। অবিশ্বাসীদের হত্যা করতে অথবা তাদের হাত-পা কেটে ফেলতে প্ররোচিত করছে, দেশ থেকে অপমান করে নির্বাসিত করতে বলছে- ‘তাদের জন্য পরকালে অপেক্ষা করছে ভয়ানক শাস্তি’ (৫:৩৪)। আরও বলছে, “যারা অবিশ্বাস করে তাদের জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে আগুনের পোশাক, তাদের মাথার উপর ফুটন্ত পানি ঢেলে দেওয়া হবে যাতে ওদের চামড়া আর পেটে যা আছে তা গলে যায়, আর ওদের পেটানোর জন্য থাকবে লোহার মুগুর’ (২২:১৯)। কোরআন ইহুদি এবং নাসারাদের সাথে বন্ধুত্বটুকু করতে পর্যন্ত নিষেধ করছে (৫:৫১), এমন কি নিজের পিতা বা ভাই যদি অবিশ্বাসী হয় তাদের সাথে সম্পর্ক না রাখতে উদ্বুদ্ধ করছে (৯:২৩, ৩:২৪)। আল্লা-রসুলে যাদের বিশ্বাস নেই, তাদের জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ড (৪৯:১৩)। ইসলামে অবিশ্বাস করে কেউ মারা গেলে কঠোরভাবে উচ্চারিত হবে- ‘ধরো ওকে, গলায় বেড়ি পড়াও এবং নিক্ষেপ করো জাহান্নামে আর তাকে। শৃঙ্খলিত করো সত্তর হাত দীর্ঘ এক শৃঙ্খলে’ (৬৯:৩০-৩৩)। আল্লাহর নামে যুদ্ধ করতে সবাইকে উৎসাহিত করা হয়েছে এই বলে- ‘এটা আমাদের জন্য ভালোই, এমন কি যদি আমাদের অপছন্দ হয় তবুও’ (২:২১৬), তারপর- ‘কাফেরদের গর্দানে আঘাত করো’ আর তারপর তাদের উপর রক্তগঙ্গা বইয়ে দেবার নির্দেশের পর রয়েছে অবশিষ্টদের ভালোভাবে বেঁধে ফেলতে (৪৭:৪)। আল্লাহতালা এই বলে প্রতিজ্ঞা করেছেন- ‘কাফেরদের হৃদয়ে আমি গভীর ভীতির সঞ্চার করব’ এবং বিশ্বাসীদের আদেশ করেছেন কাফেরদের কাঁধে আঘাত করতে আর হাতের সমস্ত আঙ্গুলের ডগা ভেঙ্গে দিতে (৪:১২)।
আল্লাহ জিহাদকে মুমিনদের জন্য আবশ্যক’ (mandatory) করেছেন আর সতর্ক করেছেন এই বলে-”তোমরা যদি সামনে না এগিয়ে আসো (জিহাদের জন্য) তবে তোমাদের জন্য অপেক্ষা করছে মর্মন্তুদ শাস্তি’(৯:৩৯)। আল্লাহ তার পেয়ারা নবীকে বলছেন, “হে নবী, অবিশ্বাসীদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করো আর কঠোর হও- কেননা, জাহান্নামের মতো নিকৃষ্ট আবাস স্থলই হলো তাদের পরিণাম’ (৯:৭৩)।
এই হচ্ছে কোরআন (হাদিস এবং অন্যান্য গ্রন্থগুলোর কথা না হয় বাদই থাকুক আপাতত)। অনেকেই দেখেছি নিজস্ব বিশ্বাসে আপ্লুত হয়ে কোরআনকে নির্দ্বিধায় ‘The book of guidance’ বলে মেনে নেন, আর ইসলামকে মনে করেন ‘শান্তির ধর্ম। যারা এমনটি ভাবেন, তারা কি কখনো ভেবে দেখেছেন যে উপরের আয়াতগুলো কেউ যদি। নির্দ্বিধায় বিশ্বাস করে আর সমাজে তার বাস্তব প্রয়োগ চায় তবে তারা কী ধরনের শান্তি এ পৃথিবীতে বয়ে আনবে? জিহাদিদের কল্যাণে আজকের বিশ্বে ইসলামি সন্ত্রাসবাদ’ (Islamic Terrorism) একটি প্রতিষ্ঠিত শব্দ। প্রতিদিন কাগজের পাতা খুললেই দেখা যায় এই জিহাদি জোশে উদ্বুদ্ধ কিছু লোক বোমা মারছে মানুষজন, বাড়ি-ঘর, কারখানা, রাস্তাঘাট, যানবাহন, সিনেমা হল, সাংস্কৃতিক অঙ্গন বা সমুদ্র-সৈকতে। হাজার খানেক জিহাদি সংগঠন যেমন- আকায়দা, ইসলামিক জিহাদ, হামাস, হরকত-উল-জিহাদ, হরকত-উল-মুজাহিদিন, জেইস-মুহম্মদ, জিহাদ-এ-মুহম্মদ, তাহ-রিখ-এ-নিফাজ-সারিত-এ-মুহম্মদ, আল-হিকমা, আল-বদর-মুজাহিদিন, জামাতে ইসলামিয়া, হিজাব-এ-ইসলামিয়া, আনসারুল্লা বাংলা টিম আজ সারা পৃথিবী জুড়ে কাযেম করছে এক ভীতির পরিবেশ[১০১]।
বাংলাদেশ সরকার হিযবুত তাহরীর সহ কিছু দলকে নিষিদ্ধ করেছে জঙ্গিবাদের অভিযোগে গ্রেফতার করেছে আনসারুল্লা বাংলা টিমের প্রধান মুফতি জসীম উদ্দিনসহ ৩১ জনকে। ব্লগার রাজীব হত্যা মামলায় মুফতি জসীম উদ্দিনকে গ্রেপ্তার দেখানো হয়। এর আগে বিএনপি জামায়াত জোট সরকারের আমলে জমিয়াতুল মুজাহিদিন বাংলাদেশ (জেএমবি), হরকাতুল জিহাদ আল ইসলামি বাংলাদেশ (হুজি) নিষিদ্ধ হয়; শাহাদাত ই আল হিকমা ও জাগ্রত মুসলিম জনতা বাংলাদেশ (জেএমজেবি) নিষিদ্ধ হয় চারদলীয় জোট সরকারের আমলে। বাংলাদেশে হরকাতুল জিহাদ প্রথম আলোচনায় আসে ১৯৯৬ সালে। ওই বছর ১৯ ফেব্রুয়ারি কক্সবাজার জেলার উখিয়া থানার পাইনখালী গ্রামসংলগ্ন লুন্ডাখালীর জঙ্গলে সেনাবাহিনী ও পুলিশ যৌথ অভিযান চালিয়ে সশস্ত্র প্রশিক্ষণের সময় ঐ সংগঠনের ৪১ জঙ্গি সদস্যকে অস্ত্র-গোলাবারুদসহ গ্রেফতার করে। ওই ৪১ জনের মধ্যে একজন বিদেশি নাগরিক ছাড়া বাকিরা ছিল দেশের বিভিন্ন জেলা থেকে আসা মাদ্রাসার ছাত্র ও শিক্ষক। এরপর ১৯৯৯ সালের ১৮ জানুয়ারি ঢাকায় কবি শামসুর রাহমানের বাড়িতে তার উপর হামলাকালে ঘটনাস্থল এবং পরে বিভিন্ন স্থান থেকে আটক ১০ জঙ্গিও নিজেদের হরকাতুল জিহাদের সদস্য পরিচয় দ্যে। এরপর যশোরে উদীচীর অনুষ্ঠানে, ২০০০ সালের ২৩ জুলাই গোপালগঞ্জের কোটালীপাড়ায় তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার জনসভার অদূরে বোমা পুঁতে রাখার ঘটনায়, এরপর ২০০১ সালের ১৪ এপ্রিল রমনার বটমূলে নববর্ষের অনুষ্ঠানে, ২১ আগস্ট গ্রেনেড হামলা এবং ২০০৫ সালের ১৭ আগস্ট সিরিজ বোমা হামলাসহ সারা দেশে বেশ কিছু বোমা, গ্রেনেড হামলা চালিয়ে হরকাতুল জিহাদ আবার আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে আসে।
১৯৯৮ সালে জন্ম নেয়া জেএমবি ২০০২ সাল থেকে নাশকতা শুরু করলেও ব্যাপক আলোচনায় আসে ২০০৫ সালের ১৭ আগস্ট দেশব্যাপী একযোগে বোমা হামলা চালিযে। পাঠকদের অনেকেরই হয়তো সেদিনকার ভয়াবহতার কথা মনে আছে। সেদিন সারা বাংলাদেশে একনাগাড়ে ৬৩টি জেলায় বোমার মহড়া চালিয়েছিল। মহড়ার প্রকোপ এমনই ব্যাপক ছিল যে অনেকেই ১৭ই আগস্ট দিনটিকে সেসময় বাংলাদেশের ৯-১১’ বলে অভিহিত করেছিলেন। জঙ্গিবাদের সাথে বিশুদ্ধ ইসলামের সম্পর্ক কতটুকু তা বোঝা হয়ে গেছে বোমা মহড়ার স্থানগুলোতে পাওয়া তাদের ছাপানো লিফলেটগুলো থেকেই। সারা লিফলেট জুড়ে কোরআন হাদিস থেকে নানা উদ্ধৃতি আর কাফের নাফরমানদের বিরুদ্ধে জিহাদের ডাক। সেসময় ফরহাদ মজহার আর বদরুদ্দিন উমরেরা পালের হাওয়া অন্য দিকে ঘোরানোর চেষ্টা করলেও, বিশুদ্ধ ইসলামের সাথে জঙ্গিবাদের যে একটা সম্পর্ক রয়েছে, তা আর চাপা থাকে নি[১০২]। ধর্মভিত্তিক ৫টি জঙ্গি সংগঠনের কার্যক্রম নিষিদ্ধ। হলেও ইতোমধ্যে গোপনে আরো ৭০টি জঙ্গি সংগঠন এদের সাথে যুক্ত হয়েছে। এরা একযোগে গোপনে দেশব্যাপী বড় ধরনের নাশকতা ঘটানোর জন্য তৎপর হয়ে উঠেছে। এদের মূল টার্গেট হচ্ছে যুদ্ধাপরাধীদের বিচার বানচাল করা[১০৩]।
সচেতন শান্তিকামী ধার্মিক মানুষদের আজ আত্মাপলব্ধির সময় এসেছে, সময় এসেছে সংশয়বাদী দৃষ্টিকোণ থেকে প্রশ্ন করার কেন এই জঙ্গি দলগুলো এত ইসলামিক? কেন তারা সন্ত্রাসী? কারা ধীরে ধীরে গড়ে তুলেছে মোল্লা ওমর, বিন-লাদেন, মৌলানা মান্নান, গোলাম আজম, শাইখ আব্দুর রহমান, মুফতি হান্নান আর বাংলা ভাইদের? কে ইন্ধন যোগায় তাদের সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডে? আজ অত্যন্ত পরিষ্কারভাবে তাই বলার সময় এসেছে এই পবিত্র ধর্মগ্রন্থগুলো অনেকাংশেই ধর্মীয় সন্ত্রাসবাদের মূল উৎস। অবশ্য সেইসাথে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং পশ্চিমা দেশগুলোর সাম্রাজ্যবাদী দৃষ্টিভঙ্গি এবং মধ্যপ্রাচ্যের প্রতি দীর্ঘদিনের বিদ্বেষমূলক পররাষ্ট্রনীতির কথাও আমাদের ভুলে গেলে চলবে না[১০৪]। জনবিধ্বংসী যুদ্ধাস্ত্র না পাওয়া কিংবা সাদ্দামের সাথে আল-কায়েদার কোনো সম্পর্ক না খুঁজে পাওয়া কিংবা জৈব-যুদ্ধাস্ত্র না পাওয়া সত্বেও নির্লজ্জভাবে ইরাকের উপর যে আগ্রাসন চালিয়েছে তা শুধু যে আমেরিকার চিরচেনা সাম্রাজ্যবাদী চেহারাটাকেই স্পষ্ট করে তুলেছে তা নয়, ইসলামি বিশ্ব এই আগ্রাসনকে যেকোনো কারণেই হোক ‘ইসলামের উপর আঘাত’ হিসেবে নিয়েছে। সেজন্য রাজনৈতিক বিশ্লেষণে দেখা যায়, সেসমস্ত দেশেই ইসলামি আত্মঘাতী বোমা হামলার মাত্রাটা বেশি যে দেশের সরকার ইরাক যুদ্ধে বুশ-ব্লেয়ারকে নগ্ন ভাবে সমর্থন করেছে। প্যালেস্টাইনিদের বঞ্চিত করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রসহ অন্যান্য পশ্চিমা। দেশগুলো যেভাবে দীর্ঘদিন ধরে ইসরায়েলকে নগ্নভাবে সমর্থন করেছে তাও মুসলিম সমাজকে সংঘাতের পথে ঠেলে দিয়েছে। এই রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়া আর প্রতিহিংসার ব্যাপারগুলো ভুলে গেলে কোনো আলোচনাই কখনো সম্পূর্ণ হতে পারে না। আরেকটি ব্যাপার উল্লেখ করাও বোধহয় এক্ষেত্রে অপ্রাসঙ্গিক হবে না। রাষ্ট্রযন্ত্র কীভাবে ধর্ম ও মৌলবাদকে লালন করে, পালন করে আর সময় বিশেষে উস্কে দেয় তার একটি বাস্তব প্রমাণ হচ্ছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। বিজ্ঞানীরা স্টেম সেল নিয়ে গবেষণা করবে কি করবে না, কৃত্রিমভাবে সংযুক্ত জীবন রক্ষাকারী যন্ত্র তুলে ফেলা হবে কি হবে না, স্কুলে বিবর্তনবাদ পড়ানো হবে কিনা, আর হলে কীভাবেইবা পড়াতে হবে, সবকিছুই সূক্ষভাবে নিয়ন্ত্রণ করছে সরকার। বিজ্ঞানীদের গবেষণা আর কাজকর্ম নৈতিক না অনৈতিক- এ নিয়েও উপযাজক হয়ে জ্ঞানগর্ভ মত দিতে এগিয়ে আসছে সরকারি পৃষ্ঠপোষকতায় পরিচালিত অর্ধশিক্ষিত পাদ্রি আর যাজকেরা। যুদ্ধের আগে নবী-রাসুলদের মতোই ‘ঈশ্বরের কণ্ঠস্বর’ শুনতে পেয়েছে সে দেশের প্রেসিডেন্ট; মিডিয়া, বৃহৎ পত্রিকা গোষ্ঠী আর প্রকাশক নির্ধারণ করে দিচ্ছে কোন্ খবরে আমরা বিশ্বাস করব, আর কোন খবর চেপে যাওয়া হবে। আসলে ‘মুক্ত বিশ্বের কথা মুখে বলে এভাবেই নাগরিক রুচি, চাহিদা, চেতনা আর পুরো জীবনধারাকেই নিয়ন্ত্রণ করতে চাইছে ধর্মান্ধ শাসককুল আর ধনকুবের গোষ্ঠী; সে অন্য এক ইতিহাস।
তবে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ সমস্যা হলেও আমরা মনে করি না সেটা ইসলামি সন্ত্রাসবাদের কারণ ইসলামি সন্ত্রাসবাদের উৎস মূলত ইসলামেই নিহিত। মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের কারণে কোরআনে যেখানেই অবিশ্বাসীদের পাওয়া যাক তাদের হত্যা করার আয়াত, ‘তাদের সাথে সংঘাতে লিপ্ত হবার’ আয়াত, বিধর্মীদের উপর ‘জিজিয়া কর আরোপ করার’ আয়াত, ‘গর্দানে আঘাত করার’ আয়াত পয়দা হয়নি। ধর্মগ্রন্থগুলোতে নারীদের অবরুদ্ধ রাখার, শস্যক্ষেত্রের সাথে তুলনা করার, কিংবা যুদ্ধবন্দিনীদের সাথে সহবাসের আয়াত, অথবা ব্যভিচারী নারীদের পাথর ছুঁড়ে হত্যার নির্দেশ মার্কিনরা করে যায়নি। ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় মহানবী মুহাম্মদ নিজে ৬২৪ খ্রিস্টাব্দে বনি কুনুকা, ৬২৫ খ্রিস্টাব্দে বনি নাদির আর ৬২৭ খ্রিস্টাব্দে বনি কুরাইজার ইহুদি ট্রাইবকে আক্রমণ করে তাদের হত্যা করেন। বনি কুনুকার ইহুদিদের সাতশ জনকে এক সকালের মধ্যে হত্যা করতে সচেষ্ট হন (কিন্তু ‘ভণ্ড’ বলে কথিত আব্দুল্লাহ ইবনে ওবাইযের হস্তক্ষেপে সেটা বাস্তবায়িত হয়নি)[১০৫], আর বনি কুরাইজার প্রায় আটশ থেকে নয়শ লোককে আব্দুল্লাহর বাধা উপেক্ষা করে শেষ পর্যন্ত হত্যা করেই ফেলেন, এমন কি তারা আত্মসমর্পণ করার পরও[১০৬]। হত্যার ভয়াবহতা এতই বেশি ছিল যে, ক্যারেন আর্মস্ট্রং-এর মতো লেখিকা, যিনি মুসলিম সমাজের পছন্দের তালিকায় শীর্ষস্থানীয় হিসবে গণ্য হন, তিনি পর্যন্ত এধরনের কর্মকাণ্ডকে নাৎসি বর্বরতার সাথে তুলনা করেছেন[১০৭]। বহু বিশ্লেষকই অতীতে দেখিয়েছেন যে, বিন লাদেন, বাংলা ভাই, মুফতি জসিম কিংবা মোহাম্মদ আতাসহ শীর্ষ সন্ত্রাসীরা মূলত ইসলামকে নিয়মনিষ্ঠভাবে অনুসরণ করেছেন। এ নিয়ে বিস্তৃতভাবে জানতে চাইলে পাঠকেরা মুক্তমনায় প্রকাশিত আকাশ মালিকের লেখা ‘যে সত্য বলা হয় নি’ ই-বইটি পড়ে নিতে পারেন[১০৮]। কিন্তু তারপরেও অনেকেই আবার আছেন যারা ইতিহাস এবং বাস্তবতা ভুলে কেবল আমেরিকাকেই সব সময় ইসলামি সন্ত্রাসবাদের উৎস বলে মনে করেন। যেমন, নোয়াম চমস্কি যদিও আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদ নিয়ে বহু বিশ্লেষণমূলক লেখা লিখেছেন, এবং বাংলাদেশসহ বহু মুসলিম প্রধান দেশগুলোতে তার বিশ্লেষণ খুবই জনপ্রিয়, তিনিও মনে করেন, ‘আমেরিকা নিজেই এক সন্ত্রাসবাদী দেশ, সে কারণেই ৯-১১ এর মতো আক্রমণ আমেরিকার ঘাড়ে এসে পড়েছে’[১০৯]। সিএনএন- এর নিউজহোস্ট এবং নিউজ উইক ইন্টারন্যাশনালের এডিটর ফরিদ জাকারিয়া তার ২০০৭ সালে প্রকাশিত ‘ভবিষ্যতের স্বাধীনতা’ নামক বইয়ে বলেছেন, “যদি মুসলিম সন্ত্রাসবাদের পেছনে কেবল একটি মাত্র কারণ পাওয়া যায়, তা হবে আরব বিশ্বে আমেরিকান পলিসির ব্যর্থতা’[১১০]। মুক্তচিন্তক স্যাম হ্যারিস জবাব দিয়েছেন এই বলে, ‘হতে পারে। কিন্তু মুসলিম সন্ত্রাসবাদের উত্থান যদি সমস্যা হয়ে থাকে, তবে সমস্যার মূল কারণ হলো, ফান্ডামেন্টালস অফ ইসলাম[১১১]।
ধর্ম, মৌলবাদ এবং সন্ত্রাসবাদ নিয়ে আলোচনার একটা বড় সমস্যা হলো অযাচিত ‘স্টেরিওটাইপিং’ এর ভ্য। এধরনের আলোচনা শুরু হলেই আমরা দেখেছি বিশ্বাসীদের অনেকেই ক্ষিপ্ত হয়ে বলতে থাকেন- শুধু গুটি কযেক সন্ত্রাসীদের কারণে সামগ্রিকভাবে ইসলামকে বা মুসলিমদের দায়ী করা কি ঠিক হচ্ছে? একজন বিন লাদেন বা একজন মুফতি হান্নান কি ইসলামের প্রতিনিধিত্ব করে নাকি? না, সত্যিই করে না। কাজেই আমিও বলি যে, পৃথিবীর সমস্ত মুসলিম জনগোষ্ঠীকে কখনোই সন্ত্রাসী বলা উচিত নয়, যারা এধরনের ‘স্টেরিওটাইপিং করতে চান তারা ভুল করেন। এটি এক ধরনের Racism। কেউবা বলেন এটি এক ধরনের রোগ- ‘ইসলামোফোবিয়া’! রোগই বলুন আর পশ্চিমা জাত্যাভিমানই বলুন (যাকে প্রয়াত এডোয়ার্ড সাইদ অভিহিত করেন ‘ওরিয়েন্টালিজম’ নামে), ৯-১১ এরপর পশ্চিমা বিশ্বে বসবাসরত মুসলিমরা এধরনের শারীরিক ও মানসিক নির্যাতনের স্বীকার হয়েছে বহু ক্ষেত্রেই এ তো অস্বীকার করবার জো নেই। মুসলিম মানেই যে ‘সন্ত্রাসী’ নয় এটি বোঝার জন্য তো কোনো দর্শন কপচানোর দরকার নেই, আমার-আপনার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাই তো যথেষ্ট হবার কথা। আমার নিজেরই অনেক মুসলিম বন্ধু-বান্ধব রয়েছে। তাদের কেউই তো সন্ত্রাসী নন। কেউই বিন লাদেন নন, কেউই নন মুফতি হান্নান। তারা আমার বিপদে আপদে খোঁজ-খবর নেন, বাসায় এসে গল্প-গুজব করেন, খাওয়া-দাওয়া করেন, এমন কি নামাজের সময় হলে এই কাফিরের বাসায় পশ্চিম দিক কোনটা জানতে চেযে নামাজও পড়েন। এরা নিপাট ভালো মানুষ। তারা কোরআনের কোন আয়াতে ভায়োলেন্সের কথা আছে তা সম্বন্ধে মোটেও ওয়াকিবহাল নন, সেটা নিয়ে আগ্রহীও নন- তারা আসলে ‘স্পিরিচুয়াল ইসলামের’ চর্চা করেন। বিপদটা কখনোই এদের নিয়ে নয়। এরা সবাই শান্তি, ভালোবাসা আর সহিষ্ণুতায় বিশ্বাস করেন। কিন্তু এই মূল্যবোধগুলো তারা যতটা না ইসলাম থেকে পেয়েছেন, তার চেয়ে অনেক বেশি ছোটবেলা থেকেই সামাজিক শিক্ষা হিসেবে গ্রহণ করেছেন। কারণ কোনোদিন কোরআনের বা ইসলামের চর্চা না করেও তো বহু মানুষ এই গুণাবলী বর্জিত নয়, এমন হাজারো উদাহরণ হাজির করা যায়। কিন্তু এই ‘স্পিরিচুয়াল ইসলামের’চর্চাকারী দলের বাইরেও একটা অংশ রয়েছে যারা রীতিমতো আক্ষরিকভাবে কোরআনের চর্চা করেন, চোখ-কান বন্ধ করে কোরআনের সকল আদেশ-নির্দেশ মেনে চলেন আর কোরআনের আলোকে দেশ ও পৃথিবী গড়তে চান। বিপদটা এদের নিয়েই। কারণ কেউ যদি সামাজিক শিক্ষার বদলে কোরআনের সকল আদেশ-নির্দেশ চোখ-কান বন্ধ করে মেনে নেন তাহলে কী হবে? সুরা আল-ইমরানের নিচের আয়াতটায় চোখ বোলানো যাক[১১২]–
‘মুমিনগণ যেন অন্য মুমিনকে ছেড়ে কোনো অমুসলিম/কাফেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ
করে। যারা এরূপ করবে আল্লাহর সাথে তাদের কোনো সম্পর্ক থাকবে না। (৩:২৮)।
যারা কোরআনের মধ্যে কথনো ভায়োলেন্সের টিকিটিও খুঁজে পান না, বরং পবিত্র কোরআনের আলোকে জীবন সাজাতে চান, তারা নিজেরাই কি তাদের কোনো হিন্দু, খ্রিস্টান বা অধার্মিক প্রতিবেশীদের প্রতি কোরআনে বর্ণিত উপরের নির্দেশ অনুযায়ী ব্যবহার করেন? তারা কি সত্যিই শুধুমাত্র অমুসলিম বলেই কারো বন্ধুত্ব প্রত্যাখ্যান করেন? যদি তা না হয়, তবে বলতেই হয় যে তারা আসলে কোরআনের নির্দেশ অনুযায়ী চলছেন না। কিন্তু কোরআন তো আল্লাহর কিতাব’। কেউ যদি ভাসা ভাসা উদ্দেশ্যমূলকভাবে কোরআনের চর্চা না করে কোরআনের সকল নির্দেশ আক্ষরিকভাবেই মেনে চলার সিদ্ধান্ত নেন আর অবশেষে সাম্প্রদায়িক ‘তালিবান’ হিসেবে বেড়ে ওঠেন, তবে দোষটা কার হবে?
সুরা আল বাকারা থেকে আরেকটি আয়াত দেখিl[১১৩]
‘তোমাদের উপর যুদ্ধ ফরজ করা হয়েছে, অথচ তা তোমাদের কাছে অপছন্দনীয়। পক্ষান্তরে তোমাদের কাছে হয়তো কোনো একটা বিষয় পছন্দসই নয়, অথচ তা তোমাদের জন্য কল্যাণকর’ (২:২১৬)।
অথবা সুরা আন নিসা থেকে উদ্ধৃত করা যাক[১১৪]–
আল্লাহর জন্য যুদ্ধ করতে থাকুন, আপনি নিজের সত্তা ব্যতীত অন্য কোনো বিষযের জিম্মাদার নন! আর আপনি অন্য মুসলমানদেরকেও উৎসাহিত করতে থাকুন। শীঘ্রই আল্লাহ কাফেরদের শক্তি-সামর্থ্য খর্ব করে দেবেন। আর আল্লাহ শক্তি-সামর্থ্যের দিক দিয়ে অত্যন্ত কঠোর এবং কঠিন শাস্তিদাতা (৪:৪৪)।
কোরআনের বর্ণিত নির্দেশ মতো জিহাদি জোশে উদ্বুদ্ধ হয়ে তালিবানদের সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিযে ইহুদি-নাসারাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবার জন্য আফগানিস্তান চলে গিয়েছিলেন অনেকেই; কারণ ইহুদি-নাসারাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করাকে তারা আল্লাহর নির্দেশ বলেই মেনে নিয়েছিলেন। তাদের যে খুব একটা দোষ দেওয়া যায় তাও নয়। ২০০৫ সালের ১৪ই অক্টোবর দৈনিক প্রথম আলোর রিপোর্টে প্রকাশিত হয়েছে নিষিদ্ধ ঘোষিত হরকাতুল জিহাদের তত্ত্বাবধানে আশির দশকে বাংলাদেশ থেকে প্রায় তিন হাজার মাদ্রাসার ছাত্র শিক্ষক জিহাদি জোশে উদ্বুদ্ধ হয়ে সোভিয়েত বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে আফগানিস্তানে চলে গিয়েছিল। কোরআনের কিছু শিক্ষাই যে শেষ পর্যন্ত মাদ্রাসা পড়া ছাত্রদের মধ্যে ‘কাফিরদের বিরুদ্ধে অযথা হিংসা-বিদ্বেষ ছড়ানোতে বহুলাংশে দায়ী, এটি অস্বীকার করার চেষ্টা স্রেফ আত্মপ্রবঞ্চনা ছাড়া আর কিছু নয়। এ স্পর্শকাতর বিষয়টি আলোচনা করতে গেলে সবসময়ই ঘুরে ফিরে ৯-১১ এর ঘটনাটি সামনে চলে আসে। ৯-১১ এর ঘটনায় সারা পৃথিবী স্তম্ভিত হয়ে দেখেছিল কী করে কিছু ধর্মোন্মাদ জিহাদি সৈনিক উড়োজাহাজকে অস্ত্র বানিয়ে হাজার হাজার নিরপরাধ লোকের প্রাণহানি ঘটাতে পারে। যারা ইসলামের মধ্যে প্রতিনিয়ত শান্তি খোঁজেন, তারা বলবেন, এগুলো কতিপয় পথভ্রষ্ট দুষ্কৃতকারীদের কাজ যার সাথে প্রকৃত ইসলামের সাথে কোনোই সম্পর্ক নাই। কিন্তু সমস্যা হচ্ছে এই ‘কতিপয় পথভ্রষ্ট দুষ্কৃতকারীরা তো আর নিজেদের দুষ্কৃতকারী ভাবে নি। বরং ভেবেছে তারাই সাচ্চা মুসলিম, যারা কিনা আল্লাহর দেওয়া অর্পিত দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করছে। ৯-১১ ঘটার অনেক আগেই- ১১ই জানুয়ারি ১৯৯৯ এর নিউজ উইকের একটি সংখ্যায় ওসামা বিন লাদেনের একটা সাক্ষাতকার ছাপা হয়েছিল। সেই সাক্ষাতকারে লাদেন সাহেব পরিষ্কারভাবে ব্যাখ্যা করেছিলেন কেন তিনি সকল আমেরিকানদের মেরে ফেলাকে ‘জায়েজ’ মনে করেন। পাঠকদের উদ্দেশ্য কিছু অংশ তুলে দেওয়া হলো[১১৫]–
QUESTION: Why have you asked Muslims to target civilian Americans all over the world? Islam prohibits its followers from killing civilians in war?
BIN LADEN: If the Israelis are killing small children in Palestine and the Americans are killing the innocent people in Iraq, and if the majority of the American people support their dissolute president, this means the American people are fighting us and we have the right to target them.
QUESTION: All Americans?
BIN LADEN Muslim scholars have issued a fatwa [a religious order] against any American who pays taxes to his government. He is our target, because he is helping the American war machine against the Muslim nation.
হিন্দু ধর্মকে ইসলাম থেকে কোনো অর্থেই ভালো বলবার জো নেই। যে জাতিভেদ প্রথার বিষবাষ্প প্রায় তিন হাজার বছর ধরে কুড়ে কুড়ে ভারতকে খাচ্ছে তার প্রধান রূপকার স্বয়ং ঈশ্বর। মনুসংহিতা থেকে আমরা পাই- মানুষের সমৃদ্ধি কামনায় পরমেশ্বর নিজের মুখ থেকে ব্রাহ্মণ, বাহু থকে ক্ষত্রিয়, উরু থেকে বৈশ্য, আর পা থেকে শূদ্র সৃষ্টি করেছিলেন (১:৩১)। বিশ্বাসীরা জোর গলায় বলেন, ঈশ্বরের চোখে নাকি সবাই সমান! অথচ, ব্রাহ্মণদের মাথা থেকে আর শূদ্রদের পা থেকে তৈরি করার পেছনে ঈশ্বরের উদ্দেশ্যটি কিন্তু বড়ই মহান! শূদ্র আর দলিত নিম্ন বর্ণের হিন্দুদের প্রতি তাই ‘ঈশ্বরের মাথা থেকে সৃষ্ট’ উঁচু জাতের ব্রাহ্মণদের দুর্ব্যবহারের কথা সর্বজনবিদিত। সমস্ত বড়লোকের বাসায় এখনও দাস হিসেবে নিম্নবর্ণের হিন্দুদের নিয়োগ দেয়া হয়। মনু বলেছেন- দাসত্বের কাজ নির্বাহ করার জন্যই বিধাতা শূদ্রদের সৃষ্টি করেছিলেন (৪:৪১৩)। এই সমস্ত নিম্নবর্ণের হিন্দুরা বাসার সমস্ত কাজ সম্পন্ন করে চলে যাওয়ার পর গঙ্গা-জল ছিটিয়ে গৃহকে ‘পবিত্র করা হতো (ক্ষেত্র বিশেষে এখনও হয়)। আর হবে নাই বা কেন! তারা আবার মানুষ নাকি? তারা তো অচ্ছুৎ! শ্রী এম.সি.রাজার কথায়, “আপনি বাড়িতে কুকুর বিড়ালের চাষ করতে পারেন, গো-মূত্র পান করতে পারেন, এমন কি পাপ দূর করার জন্য সারা গায়ে গোবর লেপতে পারেন, কিন্তু নিম্নবর্ণের হিন্দুদের ছায়াটি পর্যন্ত আপনি মারাতে পারবেন না! এই হচ্ছে হিন্দু ধর্মের নৈতিকতা! এমন কি হিন্দু ধর্মের দৃষ্টিতে শূদ্রদের উপার্জিত ধন সম্পত্তি তাদের ভোগেরও অধিকার নেই। সব উপার্জিত ধন দাস মালিকেরাই গ্রহণ করবে- এই ছিল মনুর বিধান- ‘ন হি তস্যাস্তি কিঞ্চিত স্বং ভর্তৃহার্যধনো হি সঃ (৮:৪১৬)। শূদ্ররা ছিল বঞ্চণার করুণতম নিদর্শন; তাদের না ছিল নাগরিক অধিকার, না ছিল ধর্মীয় বা অর্থনৈতিক অধিকার। শূদ্রদের যাতে অন্য তিন বর্ণ থেকে আলাদা করে চেনা যায় এবং শূদ্ররা যেন প্রতিটি মুহূর্তে মনে রাখে যে তিন বর্ণের মানুষের ক্রীতদাস হয়ে সেবা করবার জন্যই তাদের জন্ম। তিন বর্ণের মানুষদের থেকে শূদ্ররা যে ভিন্নতর জীব তা জানানোর জন্য প্রতি মাসে মাথার সব চুল কামিয়ে ফেলবার নির্দেশ দিয়েছেন মনু (৫:১৪০)। একজন শূদ্রকে বেদ পাঠ তো দূরের কথা, শ্রবণেরও অধিকার দেওয়া হয় নি। একজন শূদ্রকে তার উঁচু জাতে বিয়ে করবার অনুমতি পর্যন্ত। দেওয়া হয় নি। একজন শূদ্র যদি ব্রাহ্মণের জন্য সংরক্ষিত আসনে বসে পড়ে, তবে তার বুকে গরম লোহার দন্ডের ছ্যাঁকা দেবার অথবা পশ্চাৎদেশ কর্তন করে নেবার বিধান রযেছে (৮: ২৮১)[১১৬]।
মনুর এসব বর্ণবাদী নীতির বাস্তব রূপায়ণ আমরা দেখতে পাই রামায়ণ ও মহাভারতে। বিশেষত ধর্মশাস্ত্রীয় অনুশাসন যে শ্রেণী বৈষম্যের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহৃত হতো এবং শূদ্রদের দমন-নিপীড়নের উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হতো, তার সবচেয়ে বড় উদাহরণ রামায়ণের শম্বুকবধ কাহিনি। তপস্যা করার অপরাধে’ রামচন্দ্র খড়গ দিযে শম্বুক নামক এক শূদ্র তাপসের শিরচ্ছেদ করেন তার তথাকথিত রামরাজ্যে[১১৭]।
প্রায় একই ধরনের ঘটনা আমরা দেখি মহাভারতে যখন নিষাদরাজ হিরণ্যধনুর পুত্র একলব্য দ্রোণাচার্যের কাছে অস্ত্রবিদ্যা শিখতে এলে তাকে নীচ জাতি বলে প্রত্যাখ্যান করেন দ্রোণ। শুধু তাই নয়, পরবর্তীতে স্বশিক্ষায় শিক্ষিত একলব্যের শর নিক্ষেপের দক্ষতা নষ্ট করে ধনুর্বিদ্যায় দ্রোণের প্রিয় ছাত্র অর্জুনের শ্রেষ্ঠত্ব অক্ষুণ্ণ রক্ষার অভিপ্রায়ে ‘গুরু দক্ষিণা হিসেবে একলব্যের বুড়ো আঙ্গুল কেটে নেন তিনি। এধরনের অনেক উপকরণ ছড়িয়ে রয়েছে প্রাচীন মহাকাব্যগুলোতে।[১১৮]
আসলে এইসব প্রাতিষ্ঠানিক ধর্ম আদিম মানুষের সাম্যের সমাজকাঠামোর ভিত উপড়ে ফেলে প্রতিষ্ঠা করেছিল অসাম্য, শ্রেণীবিভক্ত সমাজের ধর্মই তৈরি করেছিল হুজুর-মুজুর শ্রেণীর কৃত্রিম বিভাজনের, কিংবা হয়তো বলা যায় শোষক শ্রেণীই শ্রেণীবিভক্ত সমাজের ফায়দা পুরোপুরি লুটবার জন্য প্রথম থেকেই কাজে লাগিয়েছিল ধর্মকে; যেভাবেই দেখি না কেন এর ফলে প্রতিষ্ঠা হয়েছিল সামাজিক আর অর্থনৈতিক শোষণের। এই শোষণ প্রক্রিয়া অব্যাহত রাখবার জন্যই ব্রাহ্মণেরা প্রচার করেছিল- ধর্মগ্রন্থগুলো স্বয়ং ঈশ্বরের মুখ নিঃসৃত। মানুষে মানুষে বিভেদ নাকি ঈশ্বর-নির্দেশিত! ঈশ্বরকে সাক্ষী মেনে রাজনৈতিকভাবে ধর্মকে প্রতিষ্ঠিত সুদূরপ্রসারী প্রয়াস লক্ষ্য করা যায় উপমহাদেশের রাজনীতির গতি-প্রকৃতি পর্যবেক্ষণ করলো।
ইসলামি জিহাদি সৈনিকদের মতোই ভারতে বিভেদের হাতিয়ার ‘সনাতন ধর্ম রক্ষায় আজ সচেষ্ট হয়েছে বিজেপি, রাষ্ট্রীয় স্বয়ং সেবক সংঘ, বিশ্বহিন্দু পরিষদ, শিব-সেনা, বজরং দলের মতো প্রতিক্রিয়াশীল দলগুলো। কয়েক দশক আগেও ভারতে নবহিন্দুত্বের তেমন কোনো সংগঠিত রূপ ছিল না[১১৯]। তবে অশিক্ষা, কুশিক্ষা আর ধর্মান্ধতার কারণে ভারতের আপামর জনসাধারণের কাছে সন্ন্যাসী, গেরুয়া, জটা, দণ্ড, রুদ্রাক্ষ, কমল এসব দীর্ঘকাল ধরে একটা বিমূঢ় সম্রম ভোগ করে এসেছে। ধর্মের প্রতি সাধারণ মানুষের মোহের কথা ধুরন্ধর রাজনীতিবিদরা জানে। এই ধর্মীয় ভাবালুতাকে উস্কে দিতেই বোধহয় ১৯৯৮-৯০ সালে সরকারি পৃষ্ঠপোষকতায় দূরদর্শনে ধর্মীয় অবয়বে প্রচারিত হলো রামায়ণ আর মহাভারত। সরকারি প্রচার মাধ্যমে এভাবে অন্ধবিশ্বাসকে উৎসাহ দেবার ফলে ভারতে মৌলবাদী এবং সাম্প্রদায়িক রাজনীতির দুয়ার উন্মোচিত হলো, রোপণ করা হলো এক বিষ-বৃক্ষের চারা। দূরদর্শনের পর্দায় প্রথমবার রামায়ণ চলাকালে কল্পিত রাম জন্মভূমি নিয়ে মৌলবাদী আন্দোলনের জোয়ার এবং পরবর্তীকালে ১৯৯২ সালে বাবরী মসজিদ ধ্বংসের মাধ্যমে প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিগুলোর উত্থান সেই প্রক্রিয়ারই অংশ। জয়ন্তানুজ বন্দ্যোপাধ্যায় এ প্রসঙ্গে তার ‘মহাকাব্য ও মৌলবাদ’ বইয়ে বলেন[১২০]–
‘দুর্ভাগ্যবশতঃ ভারতবর্ষে রামায়ণ ও মহাভারতকে প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির মহাকাব্যিক প্রতিফলন হিসেবে অথবা ভারতীয় তথা বিশ্বসাহিত্যের অমূল্য ধ্রুপদী সম্পদ হিসেবে গণ্য না করে মৌলবাদী এবং সাম্প্রদায়িক রাজনীতির উপাদান হিসেবে ব্যবহার করার প্রবণতাই বেশি লক্ষ্য করা যাচ্ছে। এখানেই আমাদের গভীর লজ্জা। প্রথমে ১৯৮৮-৯০ সালে এবং আরও কয়েকবার সরকারি দূরদর্শনে রামায়ণ ও মহাভারত যে অবয়ব ও প্রকাশভঙ্গিমায় সম্প্রচারিত হয়েছে, তা এই মৌলবাদী রাজনীতিতে ইন্ধন জুগিয়েছে বলেই মনে হয়। দূরদর্শনে সম্প্রচারিত রামায়ণের কাহিনি প্রধানত তুলসী দাস রচিত রামচরিত মানস গ্রন্থকে ভিত্তি করেই রচিত হয়েছে, বাল্মীকি রামায়ণকে ভিত্তি করে নয়। তুলসী রামায়ণের কাহিনি মধ্যযুগীয় ভক্তি আন্দোলনের ফলশ্রুতি এবং বৈষ্ণব ভক্তি সাহিত্যের অন্তর্গত। আদি বাল্মীকি রামায়ণে বালকাণ্ড ও উত্তরকাণ্ড ছিল না। আর পরবর্তী কালে সংযোজিত এই দুই কাণ্ড এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য প্রক্ষিপ্ত কথা বাদ দিলে আদি বাল্মীকি রামায়ণে রামের অবতারত্বের বিশেষ চিহ্ন পাওয়া যায় না। মহাকাব্য হিসেবেও রামায়ণের সাহিত্যগুণ বৃদ্ধি পায়। কিন্তু তুলসী রামায়ণে বিষ্ণুকে শ্রেষ্ঠ দেবতা রামকে বিষ্ণুর অবতার হিসেবে প্রতিষ্ঠা করাই ছিল প্রধান লক্ষ্য। যা এমন কি বালকাণ্ড ও উত্তরকাণ্ডসহ পল্লবিত বাল্মীকি রামায়ণেরও প্রধান বিষয়বস্তু নয়। দূরদর্শনে এভাবে রামায়ণকে মহাকাব্য হিসেবে উপস্থিত না করে বিকৃতরূপে অবতারকাহিনি ও ধর্মগ্রন্থরূপেই জনসাধারণের সামনে তুলে ধরা হয়েছে। সরকারি প্রচারমাধ্যমে এভাবে অন্ধবিশ্বাসকে উৎসাহ দেওয়ার ফলে মৌলবাদী ও সাম্প্রদায়িক রাজনীতি সঞ্জীবিত হয়েছে, এ ধারণা যুক্তিসঙ্গত। দূরদর্শনের পর্দায় প্রথমবার রামায়ণ চলাকালে রাম জন্মভূমি নিয়ে মৌলবাদী আন্দোলনের জোয়ার এবং পরবর্তীকালে তার ব্যাপক রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়াই এর অকাট্য প্রমাণ।
২০০২ সালে গুজরাটে ঘটে যাওয়া স্মরণকালের সবচাইতে ভয়াবহ দাঙ্গা আমরা দেখেছি ধর্মের মায়াজালে পড়ে সাধারণ মানুষ কী ভয়ংকর হয়ে উঠতে পারে আর নিষ্ঠুর আচরণ করতে পারে- গুজরাটের সাম্প্রতিক দাঙ্গা তার প্রমাণ। তারপরেও কিন্তু ধর্মের সমালোচনা করলে মৌলবাদীদের সাথে সাথে অনেক প্রগতিপন্থীরাও একাট্টা হয়ে বুক চিতিযে রুথে দাঁড়ান!
ইহুদি এবং খ্রিস্টানদের পবিত্রগ্রন্থের দিকে তাকালে দেখা যায়, পুরো বাইবেলটিতেই ঈশ্বরের নামে খুন, রাহাজানি, ধর্ষণকে বৈধতা দেওয়া হয়েছে। কিছু উদাহরণ তো দেওয়া যেতেই পারে। যুদ্ধজয়ের পর অগণিত যুদ্ধবন্দিকে কক্সা করার পর মুসা নির্দেশ দিয়েছিলেন ঈশ্বরের আদেশ হিসেবে সমস্ত বন্দি পুরুষকে মেরে ফেলতে[১২১]–
এখন তোমরা এইসব ছেলেদের এবং যারা কুমারী নয় এমন সব স্ত্রী লোকদের মেরে ফেলো; কিন্তু যারা কুমারী তাদের তোমরা নিজেদের জন্য বাঁচিয়ে রাখো (গণনা পুস্তক, ৩১:১৭-১৮)।
একটি হিসেবে দেখা যায়, মুসার নির্দেশে প্রায় ১০০,০০০ জন তরুণ এবং প্রায় ৬৮,০০০ অসহায় নারীকে হত্যা করা হয়েছিল[১২২]। এছাড়াও নিষ্ঠুর, আক্রমণাত্মক এবং অরাজক বিভিন্ন আয়াতসমূহের বিবরণ পাওয়া যায় যিশাইয় (২১:৯), ১ বংশাবলী (২০:৩), গণনা পুস্তক (২৫:৩-৪), বিচারকর্তৃগন (৪:৭), গণনা পুস্তক (১৬:৩২-৩৫), দ্বিতীয় বিবরণ (১২:২৯-৩০), ২ বংশাবলী (১৪:৯,১৪:১২), দ্বিতীয় বিবরণ (১১:৪-৫), ১ শমূযেল (৬:১৯), ডটারনোমি (১৩:৫-৬, ১৩:৮-৯, ১৩:১৫), ১ শমূযেল (১৫:২ ৩), ২ শমূযেল (১২:৩১), যিশাইয় (১৩:১৫-১৬), আদিপুস্তক (৯:৫-৬) প্রভৃতি নানা জায়গায়।
বিশ্বাসী খ্রিস্টানরা সাধারণত বাইবেলে বর্ণিত এই ধরনের নিষ্ঠুরতা এবং অরাজকতাকে প্রত্যাখ্যান করে বলার চেষ্টা করেন, এগুলো সব বাইবেলের পুরাতন নিয়মের (ইহুদিদের ধর্মগ্রন্থ) অধীন, যিশুখ্রিস্টের আগমনের সাথে সাথেই আগের সমস্ত অরাজকতা নির্মূল হয়ে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে। এটি সত্য নয়। বাইবেলের নতুন নিয়মে যিশু খুব পরিষ্কার করেই বলেছেন যে তিনি পূর্বতন ধর্মপ্রবর্তকদের নিয়মানুযায়ীই চালিত হবেন।[১২৩]
এ কথা মনে করো না, আমি মোশির আইন-কানুন আর নবীদের লেখা বাতিল করতে এসেছি। আমি সেগুলো বাতিল করতে আসি নি বরং পূর্ণ করতে এসেছি (মথি, ৫: ১৭)।
খ্রিস্ট ধর্মের অনুসারীরা যেভাবে যিশুকে শান্তি এবং প্রেমের প্রতীক হিসেবে বর্ণনা করে থাকেন, সত্যিকারের যিশু ঠিক কতটুকু প্রেমময় এ নিয়ে সন্দেহ থেকেই যায়। যিশু খুব স্পষ্ট করেই বলেছেন যে–
‘আমি পৃথিবীতে শান্তি দিতে এসেছি এই কথা মনে করো না। আমি শান্তি দিতে আসি নাই, এসেছি তলোয়ারের আইন প্রতিষ্ঠা করতে। আমি এসেছি মানুষের বিরুদ্ধে মানুষকে দাঁড় করাতে; ছেলেকে বাবার বিরুদ্ধে, মেয়েকে মায়ের বিরুদ্ধে, বৌকে শাশুড়ির বিরুদ্ধে দাঁড় করাতে এসেছি’ (মথি, ১০: ৩৪-৩৫)।
ব্যভিচার করার জন্য শুধু ব্যভিচারিণী নন, তার শিশুসন্তানদের হত্যা করতেও কার্পণ্য বোধ করেন না যিশু[১২৪]–
“সেইজন্য আমি তাকে বিছানায় ফেলে রাখব, আর যারা তার সঙ্গে ব্যভিচার করে তারা যদি ব্যভিচার থেকে মন না ফেরায় তবে তাদের ভীষণ কষ্টের মধ্যে ফেলব। তার ছেলেমেয়েদেরও আমি মেরে ফেলব’ (প্রকাশিত বাক্য, ২: ২২-২৩)।
ধর্মের সমালোচনা কেন?
মানবতাবাদীরা আর যুক্তিবাদীরা কেন ধর্মগ্রন্থগুলোর সমালোচনা করেন? সমালোচনা করেন কারণ তা সমালোচনার যোগ্য, তাই। কোনোকিছুই তো আসলে সমালোচনার ঊর্ধ্বে নয়- তা সে অর্থনীতি বা পদার্থবিজ্ঞানের নতুন কোনো তত্বই হোক, বা মহান আল্লাহর বাণীই হোক। আসলে পুরো ধর্মবিশ্বাসই তো দাঁড়িয়ে আছে এক জলজ্যান্ত মিথ্যার উপর ভর করে। ধর্ম মানেই আজ কিছু অবৈজ্ঞানিক চিন্তা-চেতনা, কুসংস্কার আর রীতি-নীতির সমাহার, যেগুলো কালের পরিক্রমায় উপযোগিতা হারিযেছে। ধর্মের সমালোচনার আর একটি বড় কারণ হলো, ধর্মগ্রন্থগুলোর মধ্যে বিরাজমান নিষ্ঠুরতা। ধর্মগ্রন্থগুলো তো আর গীতাঞ্জলি বা সঞ্চিতার মতো নির্দোষ কাব্যসমগ্র নয় যে অবসর সময়ে শুয়ে শুয়ে কাব্য চর্চা। করলাম আর তারপর আলমারীর তাকে তুলে রেখে দিলাম! ধর্মগ্রন্থগুলোতে যা লেখা আছে তা ঈশ্বরের বাণী হিসেবে পালন করা হয় আর উৎসাহের সাথে সমাজে তার প্রয়োগ ঘটান হয়। হিন্দু ধর্মগ্রন্থগুলোতে বর্ণিত সতীদাহর মাহাত্ম্যকে প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে শুধুমাত্র ১৮১৫ সাল থেকে ১৮২৬ সালের মধ্যে সতীদাহের স্বীকার হয়েছে ৪১৩৫ জন নারী। এই তো সেদিনও- ১৯৮৭ সালে রূপ কানোয়ার নামে একটি মেয়েকে রাজস্থানে পুড়িয়ে মারা হলো ‘সতী মাতা কী জয়’ ধ্বনি দিযে। সারা গ্রামের মানুষ তাকিয়ে তাকিয়ে দেখল কেউ টু শব্দটি করলো না। আর করবেই বা কেন? ধর্ম নাশ হয়ে যাবে না? মহাভারতের কথা শুনলে যেমন পুণ্য হয়, সতী পোড়ানো দেখলেও নাকি তেমনি। আমি আমার পূর্ববর্তী ‘অবিশ্বাসের দর্শন’ বইটাতে সতীদাহের পরিসংখ্যান হাজির করেছিলাম। এক ‘মডারেট’ হিন্দু বইটার রিভিউ করতে গিয়ে একটা ব্লগ সাইটে লিখে দিলেন— পুরো ব্যাপারটাই নাকি সাংস্কৃতিক, ধর্মগ্রন্থে নাকি সতীদাহের কোন অস্তিত্ব নেই। আসলে এই ‘মডারেট’ হিন্দুরা নিজের ধর্মগ্রন্থটাও ঠিকমত পড়ে দেখেন না। অনেক হিন্দুই জানেন না। তাদের ধর্মগ্রন্থে “স্বামী মারা গেলে বিধবাকে স্বামীর চিতায় আগুনে পুড়ে মরে সতী। হওয়ার সুস্পষ্ট নির্দেশ রয়েছে। যেমন, ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলের ১৮নং সূক্তের ৭ নং ঋক (১০/১৪/৭) দ্রষ্টব্য :
इमा नारीरविधवाः सुपत्नीराजनेन सर्पिषा संविशन्तु।
भनअवो.अनमीयाः सूज़ा आ रोहन्तु जनयॉयोनिम
শ্লোকটির ইংরেজি হচ্ছে : Let these women, whose husbands are worthy and are living, enter the house with ghee (applied) as collyrium (to their eyes). Let these wives first step into the pyre, tearless without any affliction and well adorned.’)
অথর্ববেদে রয়েছে : “আমরা মৃতের বধূ হবার জন্য জীবিত নারীকে নীত হতে দেখেছি।” (১৪/৩/১,৩)। পরাশর সংহিতায় পাই, “মানুষের শরীরে সাড়ে তিন কোটি লোম থাকে, যে নারী মৃত্যুতেও তার স্বামীকে অনুগমন করে, সে স্বামীর সঙ্গে ৩৩ কোটি বৎসরই স্বর্গবাস করে।” (৪:২৮)। দক্ষ সংহিতার ৪:১৮-১৯নং শ্লোকে বলা হয়েছে, “যে সতী নারী স্বামীর মৃত্যুর পর অগ্নিতে প্রবেশ করে সে স্বর্গে পূজা পায়। এই দক্ষ সংহিতার পরবর্তী শ্লোকে (৫:১৬০) বলা হয়েছে, “যে নারী স্বামীর চিতায় আত্মােৎসর্গ করে সে তার পিতৃকুল, স্বামীকুল উভয়কেই পবিত্র করে”
হিন্দু ধর্মের সতীদাহ আসলে ধর্মগ্রন্থ থেকেই উৎসারিত ছিল, তা এখন যতই অস্বীকার করার চেষ্টা হোক না কেন। ধর্ম যে কীরকম নেশায় বুঁদ করে রাখে মানুষকে, তার জলজ্যান্ত প্রমাণ এই সতীদাহ। এজন্যই বোধহয় প্যাসকেল বলেছেন- “Men never do evil so completely and cheerfully as when they do it from religious conviction.’ খুবই সত্যি কথা। চিন্তা করুন ব্যাপারটা- জীবন্ত নারী-মাংস জ্বলছে, ছটফট করছে, অনেক সময় বেঁধে রাখতে কষ্ট হচ্ছে, মাঝে মাঝে পালাতে চেষ্টা করছে- আফিম জাতীয় জিনিস গিলিয়ে দিয়ে লাঠি দিয়ে খুঁচিযে আবার চিতায় তুলে দেওয়া হচ্ছে- কী চমৎকার মানবিকতা[১২৫]! প্রায় প্রতিদিনই পত্র-পত্রিকায় পড়ছি যে, ইসলামি বিশ্বে শরিয়ার শিকার হয়ে প্রাণ হারাচ্ছে অসহায় সাফিয়া, আমিনারা। তবুও নেশায় বুঁদ হয়ে ধর্ম আর ধর্মগ্রন্থের মধ্যে শান্তি’, ‘প্রগতি’ আর ‘সহিষ্ণুতা’ খুঁজে চলেছেন মডারেট ধর্মবাদীরা।[১২৬]
তবে এ কথা অনস্বীকার্য যে প্রতিটি ধর্মগ্রন্থেই বেশ কিছু ভালো ভালো কথা আছে (এগুলো নিয়ে আমার কিংবা কারোই আপত্তি করার কিছু নেই); এগুলো নিয়েই ধার্মিকেরা গর্ববোধ করেন আর এ কথাগুলোকেই নৈতিকতার চাবিকাঠি বলে মনে করেন তারা। কিন্তু একটু সংশয়বাদী দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলেই বোঝা যাবে- ভালোবাসা প্রেম এবং সহিষ্ণুতার বিভিন্ন উদাহরণ যে ধর্মগ্রন্থ এবং তার প্রচারকদের সাথে লেবেল হিসেবে লাগিয়ে দেওয়া হয়, সেগুলো কোনোটাই ধর্ম বা ধর্মগ্রন্থের জন্য মৌলিক নয়। যেমন, যিশুখ্রিস্টের অনেক আগেই লেভিটিকাস (১৯:১৮) বলে গেছেন, নিজেকে যেমন ভালোবাস, তেমনি ভালোবাসবে তোমার প্রতিবেশীদের বাইবেল এবং কোরআনে যে সহনশীলতার কথা বলা আছে, সেগুলোর অনেক আগেই (খ্রিস্টের জন্মের পাঁচশ বছর আগে) কনফুসিয়াস এইরকম ভাবে বলেছিলেন- “অন্যের প্রতি সেরকম ব্যবহার করো না, যা তুমি নিজে পেতে চাও না। আইসোক্রেটস খ্রিস্টের জন্মের ৩৭৫ বছর আগে বলে গিয়েছিলেন, “অন্যের যে কাজে তুমি রাগান্বিত বোধ করো, তেমন কিছু তুমি অন্যদের প্রতি করো না। এমন কি শত্রুদের ভালোবাসতে বলার কথা তাওইজমে রয়েছে, কিংবা বুদ্ধের বাণীতে, সেও কিন্তু যিশু বা মুহম্মদের অনেক আগেই[১২৭]।
কাজেই নৈতিকতার যে উপকরণগুলোকে ধর্মানুসারীরা তাদের স্ব স্ব ধর্মের ‘পৈত্রিক সম্পত্তি’ বলে ভাবছেন, সেগুলো কোনোটাই কিন্তু আসলে ধর্ম থেকে উদ্ভূত হয় নি, বরং বিকশিত হয়েছে সমাজবিবর্তনের অবশ্যম্ভাবী ফল হিসেবে। সমাজব্যবস্থা টিকিয়ে রাখার স্বার্থেই সৃষ্টির প্রারম্ভ থেকে মানুষ কিছু কিছু বৈশিষ্ট্যকে ‘নৈতিক গুণাবলী’ হিসেবে গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছে; কারণ ওভাবে গ্রহণ না করলে সমাজব্যবস্থা অচিরেই ধ্বসে পড়তো। বিখ্যাত নৃতাত্ত্বিক সলোমন অ্যাশ বলেন–
‘আমরা এমন কোনো সমাজের কথা জানি না, যেখানে সাহসিকতাকে হেয় করা হয়, আর ভীরুতাকে সম্মানিত করা হয়; কিংবা উদারতাকে পাপ হিসেবে দেখা হয় আর অকৃতজ্ঞতাকে দেখা হয় গুণ হিসেবে।‘
এমন ধরনের সমাজের কথা আমরা জানি না কারণ এমন সমাজ টিকে থাকতে পারে না। খুব সাদা চোখে দেখলেও, একটি সমাজে চুরি করা যে অন্যায়, এটি বোঝার জন্য কোনো স্বর্গীয় ওহি নাজিল হবার দরকার পড়ে না। কারণ যে সমাজে চুরি করাকে না। ঠেকিযে মহিমান্বিত করা হবে, সে সমাজের অস্তিত্ব লোপ পাবে অচিরেই। ঠিক একইভাবে আমরা বুঝি, সত্যি কথা বলার বদলে যদি মিথ্যা বলাকে উৎসাহিত করা হয়, তবে মানুষে মানুষে যোগাযোগ রক্ষা করাই দুরূহ হয়ে পড়বে। এ ব্যাপারগুলো উপলব্ধির জন্য কোনো ধর্মশিক্ষা লাগে না। আবার এমনও দেখা গেছে যে, শতাব্দীপ্রাচীন কোনো চলমান ব্যবস্থার পরিবর্তন মানুষ নিজে থেকেই করেছে পরিবর্তিত মূল্যবোধের কষ্টিপাথরে মানবতাকে যাচাই করে, এবং অনেকক্ষেত্রেই ধর্ম কী বলছে না বলছে তার তোয়াক্কা না করেই। দাসত্বপ্রথার উচ্ছেদ এমনি একটি ঘটনা। বলা বাহুল্য, কোনো ধর্মগ্রন্থেই দাসত্ব উচ্ছেদের আহ্বান জানানো হয় নি। বাইবেলের নতুন কিংবা পুরাতন নিয়ম, কিংবা কোরআন, অথবা বেদ, উপনিষদ, মনুসংহিতা- কোথাওই দাস প্রথাকে নির্মূল করার কথা বলা হয় নি, বরং সংরক্ষিত করার কথাই বলা হয়েছে প্রকারান্তরে। কিন্তু মানুষ সামাজিক প্রযোজনেই একটা সময় দাসত্ব উচ্ছেদ করেছে, যেমনিভাবে হিন্দু সমাজ করেছে সতীদাহ নির্মল বা খ্রিস্ট সমাজ করেছে ডাইনি পোড়ানো বন্ধ। সতীত্ব সম্পর্কে প্রাচীন ধারণা, কিংবা সমকামিতা বা গর্ভপাতের অধিকার সংক্রান্ত দৃষ্টিভঙ্গিরও ব্যাপক পরিবর্তন ঘটেছে সারা পৃথিবী জুড়ে এ কয় দশকে। এ পরিবর্তিত দৃষ্টিভঙ্গির অনেকগুলোই ধর্ম কর্তৃক অনুমোদিত নয়।
বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি: লেট দ্য ডেটা ডিসাইড
আজ আধুনিক রাষ্ট্রগুলোর দিকে তাকালে বোঝা যায় যে, আল্লাহর গোনাহর দোহাই দিয়ে মানুষজনকে সৎ পথে পরিচালিত করার ব্যাপারটি কী নিদারুণভাবে ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে। আল্লাহ বা ঈশ্বরের গোনাহর ভয় দেখিযেই যদি মানুষজনকে পাপ থেকে বিরত রাখা যেত, তা হলে রাষ্ট্রে পুলিশ-দারোগা, আইন-কানুন, কোর্ট-কাঁচারি কোনো কিছুরই প্রয়োজন হতো না। এক ইন্টারনেট ফোরামে একটা সময় রাষ্ট্রের উৎপত্তি এবং ধর্মের নৈতিকতা বিষয়ে লিখতে শুরু করেছিলাম; সাথে সাথেই এক ধার্মিক ভদ্রলোক উত্তেজিত হয়ে বলতে শুরু করলেন- ‘অভিজিৎ রায়ের মতো নাস্তিক লোকজন রাষ্ট্রে আছেন বলেই পুলিশ দারোগার প্রয়োজন’। এধরনের উক্তিকে স্রেফ একজনমাত্র অজ্ঞ ধার্মিকের আস্ফালন বলে মনে করলে কিন্তু ভুল হবে। এধরনের ধ্যান ধারণা অনেকেই মনে মনে পোষণ করেন, তাদের বেশ বড় অংশই আবার সুশিক্ষিত। আমেরিকার রক্ষণশীল লেখিকা অ্যান কোল্টার তার ‘গডলেস’ বইয়ে মন্তব্য করেছেন, ‘সমাজ ঈশ্বরের নির্দেশিত পথে না চললে দাসত্ব, গণহত্যা, পশুবৃত্তিতে নিমজ্জিত হয়ে যাবে’[১২৮]। একই কথা উচ্চারণ করেছেন ডিসকভারি ইন্সটিউটের পুরোধা ব্যক্তিত্ব এবং ইন্টেলিজেন্ট ডিজাইনের অন্যতম প্রবক্তা ফিলিপ জনসনও একটু ভিন্ন ভাবে। তার মতে, যেহেতু অবিশ্বাসীরা ডারউইনের মতানুসারে মনে করে মানুষ বানর থেকে উদ্ভূত হয়েছে, সেহেতু তারা যেকোনো ধরনের ‘নাফরমানি’ করতে পারে- সমকামিতা, গর্ভপাত, পর্নোগ্রাফি, তালাক, গণহত্যা সবকিছু। এমন একটা ভাব, ডারউইন আসার আগ পর্যন্ত সারা পৃথিবী যেন এগুলো থেকে একেবারেই মুক্ত ছিল! ফক্স টিভির ‘ও’রাইলি ফ্যাক্টরের জনপ্রিয় উপস্থাপক বিল ও’রাইলি তার একটি বইয়ে লিখেছেন, ঈশ্বরের আইনের বিরুদ্ধে গেলে পুরো সমাজ নৈরাজ্য এবং অরাজকতায় পতিত হবে, আর আইন-লঙ্ঘনকারীরা সমাজকে জঙ্গল বানিয়ে ফেলবে’[১২৯]।
একজন বিজ্ঞানমনস্ক ব্যক্তি হিসেবে অ্যান কোল্টার, বিল ওরাইলি কিংবা ফিলিপ জনসনের এধরনের আবেগপ্রবণ আপ্তবাক্যাবলীতে আমাদের বিশ্বাস করার কোনো কারণ নেই, বরং আমাদের আস্থা থাকবে বৈজ্ঞানিক সমীক্ষা হতে প্রাপ্ত ফলাফলে; বিজ্ঞানীরা যেটিকে বলেন, ‘Let the data decide’। আমরা ফিলিপ জনসনের সমর্থনে এমন কোনো উপাত্ত বা ডেটা খুঁজে পাই নি যা থেকে প্রমাণিত হয় যে, অবিশ্বাসীরা বিশ্বাসীদের চাইতে বেশি অপরাধপ্রবণ; বরং কিছু পরিসংখ্যান একেবারেই উল্টো সিদ্ধান্ত হাজির করেছে। আমেরিকায় বিভিন্ন গবেষণায় দেখা গিয়েছে নাস্তিকদের চাইতে পুনরুজ্জীবিত খ্রিস্টানদের মধ্যে বিবাহবিচ্ছেদের হার বেশি; এও দেখা গিয়েছে, যেসব পরিবারের পরিবেশ ধর্মীয়গতভাবে অতিমাত্রায় রক্ষণশীল সেসমস্ত পরিবারেই বরং শিশুদের উপর পরিবারের অন্য কোনো সদস্যদের দ্বারা বেশি যৌন নিপীড়ন হয়[১৩০]। ১৯৩৪ সালে আব্রাহাম ফ্রান্সব্লাউ তার গবেষণাপত্রে দেখিয়েছেন ধার্মিকতা এবং সতোর মধ্যে বরং বৈরী সম্পর্কই বিদ্যমান। ১৯৫০ সালে মুর রসের গবেষণা থেকে বেরিয়ে এসেছে যে, ধার্মিকদের তুলনায় নাস্তিক এবং অজ্ঞেয়বাদীরাই বরং সমাজ এবং মানুষের প্রতি সংবেদনশীল থাকেন, তাদের উন্নয়নের জন্য ত্যাগ স্বীকার করেন। ভারতীয় বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী সমিতি ১৯৮৮ সালে ভারতের জেলখানায় দাগী আসামীদের মধ্যে একটি জরিপ চালিয়েছিল। জরিপের যে ফলাফল পাওয়া গিয়েছিল, তা ছিল অবাক করার মতো দেখা গিয়েছে, আসামীদের শতকরা ১০০ জনই ঈশ্বর এবং কোনো না কোনো প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মে বিশ্বাসী’[১৩১]। আমেরিকায়ও এরকম একটি জরিপ চালানো হয়েছিল ৫ ই মার্চ, ১৯৯৭ তারিখে। সে জরিপে দেখা গেছে যে আমেরিকার জনসাধারণের মধ্যে একটা উল্লেখযোগ্য অংশ (৮-১০৪) ধর্মহীন হওয়া সত্বেও তাদের মধ্যে অপরাধপ্রবণতা কম (মাত্র ০.২১৪), সে তুলনায় ধার্মিকদের মধ্যে শতকরা হিসেবে অপরাধপ্রবণতা অনেক বেশি[১৩২]। আমার ধারণা আজ বাংলাদেশে জরিপ চালালেও ভারতের মতোই ফলাফল পাওয়া যাবে। ঈশ্বরে বিশ্বাস, পরকালে বিশ্বাস, বেহেস্তের লোভ বা দোজখের ভয় কোনোটাই কিন্তু অপরাধীদের অপরাধ থেকে নিবৃত্ত রাখতে পারে নি। আল্লাহর গোনাহ কিংবা ঈশ্বরের ভযেই যদি মানুষ পাপ থেকে, দুর্নীতি থেকে মুক্ত হতে পারত, তবে তো বাংলাদেশ এতদিনে বেহেস্তে পরিণত হতো। কিন্তু বাংলাদেশের দিকে তাকালে আমরা আজ কী দেখছি? বাংলাদেশে শতকরা ৯৯ জন লোকই আল্লা-খোদা আর পরকালে বিশ্বাসী হওয়া সত্বেও দুর্নীতিতে এই দেশ প্রায়ই থাকে পৃথিবীর শীর্ষে। ধর্মে বিশ্বাস কিন্তু দেশবাসীকে দুর্নীতিমুক্ত রাখতে পারে নি। পারবেও না। যে দেশে সর্বোচ্চ পদ থেকে বইতে শুরু করে দুর্নীতির স্রোত, যে দেশে ধর্ষকেরা রাজনৈতিক ছত্রছায়ায় থাকে এবং বুক চিতিয়ে ঘুরে বেড়ায়, নেতা হবার সুযোগ পায়, সে দেশের মানুষ নামাজ পড়েও দুর্নীতি চালিয়ে যাবে; তারা রোজাও রাখবে, আবার ঘুষও খাবে। তাই হচ্ছে। এই তো ধর্মপ্রাণ, আল্লাহ-খোদায় বিশ্বাসী বাংলাদেশের সামাজিক অবস্থা। অপরদিকে ঈশ্বরবিহীন দেশগুলোর দিকে তাকানো যাক। আমাকে পেশাগত কারণে একটা সময় দীর্ঘদিন সিঙ্গাপুরে থাকতে হয়েছিল। সেখানে থাকাকালীন সময়গুলোতে লক্ষ্য করেছিলাম যে, দেশটিতে অধিকাংশ লোকই প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মপরিচয় থেকে মুক্ত। ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির অনেক চীনা ছাত্র-ছাত্রীকেই তিনি দেখেছেন ধর্মপরিচয় জিজ্ঞাসা করলে তারা বলিষ্ঠ কণ্ঠে বলে- “ফ্রি থিঙ্কার’। অথচ ধর্ম নয়, শুধু আইনের শাসন আর সামাজিক মূল্যবোধগুলোর চর্চা করে সিঙ্গাপুর আজ পৃথিবীর সবচেযে কম দুর্নীতিগ্রস্ত দেশগুলোর একটি। অধিকাংশ সিঙ্গাপুরবাসীরা আল্লাহ-খোদার নামও করেন না, নরকের ভয় অথবা বেহেস্তের লোভও তাদের নেই। কোন জাদুবলে তারা তাহলে দুর্নীতি থেকে মুক্ত থাকছে?
এটি আমার ব্যক্তিগত উপলব্ধি ভাবলে ভুল হবে। সাম্প্রতিককালে বহু আন্তর্জাতিক গবেষকই এই পর্যবেক্ষণের সাথে একমত পোষণ করেন। যেমন, গবেষক ফিল জুকারম্যান ২০০৫ থেকে ২০০৬ সাল পর্যন্ত পূর্ব ইউরোপীয় দেশগুলোতে সমীক্ষা চালিয়েছেন। সেসব দেশগুলোতে ঈশ্বরে বিশ্বাস এখন একেবারেই নগণ্য। যেমন, সুইডেনে জনসংখ্যার প্রায় ৪৫ ভাগ এবং ডেনমার্কে প্রায় ৮০ ভাগ লোক এখন ঈশ্বরে বিশ্বাস করে না’[১৩৩]। অথচ সেসমস্ত ‘ঈশ্বরে অনাস্থা পোষণকারী দেশগুলোই আজ পৃথিবীতে সবচেয়ে কম দুর্নীতিগ্রস্থ এবং সবচেয়ে কম সহিংস দেশ হিসেবে চিহ্নিত। ফিল জুকারম্যান তার অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে সম্প্রতি একটি বই লিখেছেন, “ঈশ্বরবিহীন সমাজ’ শিরোনামে[১৩৪]। তিনি সেই বইয়ে নিজের অভিজ্ঞতা থেকে লিখেছেন যে, ডেনমার্কের দ্বিতীয় বৃহত্তম শহর আরহাসে থাকাকালীন সময়গুলোতে কোনো পুলিশের গাড়ি দেখেন নি বললেই চলে। প্রায় ৩১ দিন পার করে তিনি প্রথম একটি পুলিশের গাড়ি দেখেন রাস্তায়। পুরো ২০০৪ সালে মাত্র একজন লোক হত্যার খবর প্রকাশিত হয়। এ থেকে বোঝা যায় এ সমস্ত দেশগুলোতে মারামারি হানাহানি কতো কম। শুধু তাই নয়, সাম্প্রতিক একটি সমীক্ষা থেকে দেখা গেছে ডেনমার্ক পৃথিবীর সবচেয়ে সুখী দেশ[১৩৫]।
আরেকটা সাম্প্রতিক উদাহরণ দেই। ২০১৩ সালের ডিসেম্বর মাসের ০৩ তারিখ একটি সংবাদ প্রকাশিত হয়েছিল বাংলাদেশের শীর্ষস্থানীয় দৈনিক পত্রিকাগুলোতে, যা হয়তো অনেকেরই চোখ এড়িয়ে গেছে। খবরের শিরোনাম— ‘অপরাধী কম, তাই বন্ধ হয়ে যাচ্ছে কারাগার’। না, দেশটা বাংলাদেশ নয়, সুইডেন। বিষয় হল– সুইডেনের কারাগারগুলো নাকি সব ক্রমশ বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। বিগত সময়গুলোতে কারাবন্দির সংখ্যা নাটকীয়ভাবে কমে যাওয়ার ফলেই এই সিদ্ধান্ত নিতে হচ্ছে রাষ্ট্রকে। সুইডেন পৃথিবীর অন্যতম শীর্ষস্থানীয় নাস্তিক-প্রধান দেশ (আমরা বইয়ের শেষ অধ্যায়ে এ নিয়ে আরো আলোচনা করব)। কিন্তু এই মুহূর্তে প্রশ্ন হচ্ছে, রাষ্ট্র ধর্মহীন হলেই সেখানে অপরাধপ্রবণতা হু হু করে বাড়বে বলে যারা মনে করেন, তারা সুইডেনে অপরাধপ্রবনতার ক্রমশ নিম্নহারকে কিভাবে ব্যাখ্যা করবেন?

উপরের পরিসংখ্যানগুলো দেওয়ার উদ্দেশ্য এটা প্রমাণ করা নয় যে, মানুষ নাস্তিক হলেই ভালো হবে। কিংবা আস্তিক হলেই খারাপ হবে, বরং এটাই বোঝানো যে, ধর্ম কোনোভাবেই নৈতিকতার ‘মনোপলি ব্যবসা’ দাবি করতে পারে না। আসলে কোনো বিশেষ ধর্মের আনুগত্যের উপর কিন্তু মানুষের নৈতিক চরিত্র-গঠন নির্ভর করে না, নির্ভর করে একটি দেশের আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপট আর সমাজ-সাংস্কৃতিক পরিবেশের উপর। আসলে আধুনিক যুগের জীবন যাত্রার প্রেক্ষাপটে এ কথা বলা যায়, প্রাচীনকালের ধর্মগ্রন্থগুলোর আলোকে নৈতিকতাকে বিশ্লেষণ করলে আর চলবে না, বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ থেকে অনুসন্ধান এবং বিচার-বিশ্লেষণ করতে হবে।
প্রখ্যাত মনোবিদ, বিজ্ঞানের দার্শনিক এবং স্কেপটিক ম্যাগাজিনের প্রতিষ্ঠাতা ড. মাইকেল শারমার মানব সমাজে মূল্যবোধ এবং নৈতিকতার অভিব্যক্তি নিয়ে আলাদা করে ভেবেছেন এবং এ নিয়ে লিখেছেন। তিনি তার ‘দ্য সায়েন্স অফ গুড এন্ড এভিল’ গ্রন্থে ব্যাখ্যা করেছেন সমাজ বিকাশের প্রয়োজনেই মানুষ কিছু নীতিকে প্রথম থেকে ‘গোল্ডেন রুল’ হিসেবে গ্রহণ করেছিল[১৩৬]–
Do unto others, as you would have them do unto you.
(অন্যদের প্রতি সেরকম ব্যবহারই করো যা তুমি তাদের থেকে পেতে চাও) কারণ এই নীতির অনুশীলন ছাড়া কোনো সমাজ ব্যবস্থা টিকে থাকবে না। মাইকেল শারমার তার গবেষণায় দেখিয়েছেন যে, মানব বিবর্তনের ধারাতেই পারস্পরিক প্রতিযোগিতার পাশাপাশি আবার নৈতিকতা, মূল্যবোধ, সহনশীলতা, উদারতা, স্বার্থত্যাগ, সহানুভূতি, সমবেদনা প্রভৃতি গুণাবলীর চর্চা হয়েছে। সভ্যতার প্রতিনিয়ত সংঘাত ও সংঘর্ষেই গড়ে উঠেছে মানবীয় প্রোভিশনাল এথিক্স’, যা মানুষকে প্রকৃতিতে টিকে থাকতে সহায়তা করেছে।
বিবর্তন ও নৈতিকতার উদ্ভব
একটা সময়ে ধর্মবাদীরা একচেটিয়াভাবে নৈতিকতার উৎসের জন্য ধর্ম এবং ঈশ্বরকে সাক্ষীগোপাল হিসেবে উপস্থাপন করতেন। তারা বহুঁকাল ধরেই নৈতিকতার পুরো ব্যাপারটাকে ঐশ্বরিক প্রলেপ লাগিয়ে উপস্থাপন করার চেষ্টা করেছেন এবং দাবি করেছেন (এবং এখনো অনেকে করেন) যে, জৈববৈজ্ঞানিকভাবে নৈতিকতা এবং মূল্যবোধের উদ্ভবের মতো ব্যাপারগুলো ব্যাখ্যা করা যাবে না। এগুলোর কোনো জৈবিক ব্যাখ্যা নেই। এগুলোর ব্যাখ্যা একমাত্র ঈশ্বর। কিন্তু তাদের প্রচেষ্টা বৈজ্ঞানিক মাপকাঠিতে উত্তীর্ণ হয় নি মোটেই, বরং বিজ্ঞানীরা বিবর্তন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে কীভাবে পরার্থতা কিংবা সহযোগিতার মতো ব্যাপারগুলো প্রাণীজগতে উদ্ভূত হয়েছে তার বিজ্ঞানভিত্তিক ব্যাখ্যা দিতে সমর্থ হয়েছেন। এমন কি ডারউইন নিজেও তার সময়ে জিনেটিক্সের কোনো জ্ঞান ছাড়াই কেবল জীবজগৎ পর্যবেক্ষণ করে সহযোগিতা এবং পরার্থতার বিবর্তনীয় উপযোগিতা অনুধাবন করতে পেরেছিলেন। আধুনিক বিজ্ঞানী, দার্শনিক এবং চিন্তাবিদেরা বহুভাবে দেখিয়েছেন যে এই ডারউইনীয় পদ্ধতিতে প্রাকৃতিকভাবেই পরার্থপরায়নতা, সহযোগিতা, নৈতিকতা আর মূল্যবোধের মতো অভিব্যক্তিগুলো জীবজগতে উদ্ভূত হতে পারে, যা বিবর্তনের পথ ধরে মানব সমাজে এসে আরো বিবর্ধিত আর বিকশিত হয়েছে। সাম্প্রতিক সময়গুলোতে জীববিজ্ঞান, সাংস্কৃতিক এবং বিবর্তনীয় উৎসের সন্ধান করে বহু বৈজ্ঞানিক গ্রন্থ এবং গবেষণাপত্র প্রকাশিত হয়েছে[১৩৭]।
একটু খেয়াল করলেই দেখা যাবে যে, নৈতিকতার ব্যাপারটি যে শুধু মানব সমাজেরই একচেটিয়া তা নয়, ছোট স্কেলে তথাকথিত অনেক ‘ইতর প্রাণী জগতের মধ্যেও কিন্তু এটি দেখা যায়। ভ্যাম্পায়ার বাদুড়েরা নিজেদের মধ্যে খাদ্য ভাগাভাগি করে, বানর এবং গরিলারা তাদের দলের কোনো সদস্য মানসিকভাবে বিপর্যস্ত থাকলে তাকে সহায়তা করার জন্য প্রাণান্তকর চেষ্টা করে, এমন কি ‘দশে মিলে কাজ করে তার জন্য খাবার পর্যন্ত নিয়ে আসে। ডলফিনেরা অসুস্থ অপর সহযাত্রীকে ধাক্কা দিয়ে সৈকতের দিকে নিয়ে যায়, যার ফলে অসুস্থ ডলফিনটির পর্যাপ্ত আলো বাতাস পেতে সুবিধা হয়, তিমি মাছেরা তাদের দলের অপর কোনো আহত তিমি মাছকে দ্রুত সারিয়ে তুলতে চেষ্টা করে। হাতিরা তাদের পরিবারের অসুস্থ বা আহত সদস্যকে বাঁচানোর জন্য সর্বোচ্চ ত্যাগ স্বীকার করে। এধরনের দৃষ্টান্ত বিরল নয়।
বিবর্তন তত্ব আমাদের খুব ভালোভাবেই দেখিয়েছে জিনগত স্তরে স্বার্থপরতা কিংবা প্রতিযোগিতা কাজ করলেও, জিনের এই স্বার্থপরতা থেকেই পরার্থতার মতো অভিব্যক্তির উদ্ভব ঘটতে পারে। এ ব্যাপারটি শিক্ষায়তনে গবেষণার মাধ্যমে প্রথমবারের মতো তুলে ধরেন বিজ্ঞানী উইলিয়াম হ্যামিলটন। পরবর্তীতে ধারণাটিকে জনপ্রিয় করে তোলেন স্বনামখ্যাত বিজ্ঞানী রিচার্ড ডকিন্স তার ‘সেলফিশ জিন’ বইয়ের মাধ্যমে[১৩৮]। এই বইয়ের মাধ্যমেই আসলে জীববিজ্ঞানীরা সমাজ এবং জীবনকে ভিন্নভাবে দেখা শুরু করলেন। পরার্থতা, আত্মত্যাগ, দলগত নির্বাচনের মতো যে বিষয়গুলো আগে বিজ্ঞানীরা পরিষ্কার করে ব্যাখ্যা করতে পারতেন না, সেগুলো আরো বলিষ্ঠভাবে জীববিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যাখ্যা করতে পারলেন। শুধু মানুষ নয় অন্য যেকোনো প্রাণীর মধ্যেই সন্তানদের প্রতি অপত্য স্নেহ প্রদর্শন কিংবা সন্তানদের রক্ষা করার জন্য মা বাবারা সর্বোচ্চ ত্যাগ স্বীকার করে। অর্থাৎ, নিজের দেহকে বিনষ্ট করে হলেও পরবর্তী জিনকে রক্ষা করে চলে। পরবর্তী জিন’ রক্ষা না পেলে নিজের দেহ যত সুষম, সুন্দর, শক্তিশালী আর মনোহর কিংবা নাদুস নুদুস হোক না কেন, বিবর্তনের দিক থেকে কোনো অভিযোজিত মূল্য নেই। সেজন্যই নেকড়ে যখন আক্রমণ করে, গোত্রের ছোট বাচ্চাদের রক্ষা করার জন্য বুনো মোষেরা বাচ্চাদের চারিদিকে ঘিরে শিং উঁচিযে নেকড়ের সামনে দাঁড়িয়ে থাকে, নিজেদের জীবনকে বিপন্ন করে হলেও। এভাবেই জীব বিবর্তনের পথ ধরে তার জিন-বিস্তারে কিংবা ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে রক্ষায় উদ্যোগী হয়, টিকে থাকার প্রয়োজনেই। আসলে যার সাথে সে বেশি জিন বিনিময় করবে, যত ঘনিষ্ঠতা বাড়াবে, তত বাড়বে নিজের জিন বিস্তারের সম্ভাবনা, সেজন্যই, সন্তানের প্রতি, পরিবারের প্রতি, নিকটাত্মীযের প্রতি এবং গোত্রের প্রতি এক ধরনের জৈবিক টান উপলব্ধি করে, এবং তাদেরকে রক্ষার চেষ্টা করে। বিজ্ঞানীরা আরো দেখেছেন, স্বার্থপর জিন যেমন আত্মত্যাগ কিংবা পরার্থতা তৈরি করে, ঠিক তেমনি আবার প্রতিযোগিতামূলক জীবন সংগ্রাম থেকেই জীবজগতে তৈরি হয় বিভিন্ন ধরনের পারস্পরিক সহযোগিতা, মিথোজীবিতা কিংবা সহ-বিবর্তন টিকে থাকার প্রয়োজনেই কিন্তু এগুলো ঘটে। শিকারী মাছদের থেকে বাঁচার জন্য ক্লাউন মাছদের সাথে এনিমোনের সহবিবর্তন, হামিং বার্ডের সাথে অর্নিথোপখিলাস ফুলের সহবিবর্তন, এংরাকোয়িড অর্কিডের সাথে আফ্রিকান মথের সহবিবর্তন এগুলোর প্রত্যক্ষ উদাহরণ প্রকৃতিতেই আছে।
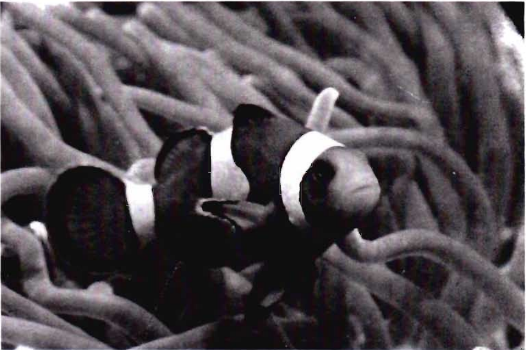
কোনো শিকারী পাখি যখন কোনো ছোট পাখিকে লক্ষ্য করে আক্রমণ করে, তখন অনেক সময় দেখা যায় যে, গোত্রের অন্য পাখি চিৎকার করে ডেকে উঠে তাকে সতর্ক করে দেয়। এর ফলে সেই শিকারী পাখি আর তার আদি লক্ষ্যকে তাড়া না করে ওই চিৎকার করা পাখিটিকে আক্রমণ শুরু করে। এই ধরনের পরার্থতা এবং আত্মত্যাগ কিন্তু প্রকৃতিতে খুব স্বাভাবিকভাবেই দেখা যায়। এই ব্যাপারগুলো বিবর্তনের কারণেই উদ্ভূত হয়েছে। মুক্তমনায় সম্প্রতি ‘বিবর্তন ও নৈতিকতার উদ্ভব’ শিরোনামে দুই পর্বের একটি লেখা লিখেছিলাম (লেখাটি ২০১১ সালে শুদ্ধস্বর থেকে প্রকাশিত ‘ভালবাসা কারে কয়?” বইয়ে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে)[১৩৯]। সেই প্রবন্ধটিতে বাংলায় প্রথমবারের মতো মেনার্ড স্মিথসহ অন্যান্য বিজ্ঞানীদের গাণিতিক মডেলের উল্লেখ করে দেখানো হয়েছে যে, শুধু প্রতিযোগিতা কিংবা। বিবাদ করে জিনপুলকে সর্বোচ্চ দক্ষতায় বাঁচিয়ে রাখা যায় না, সাথে আনতে হয় সহযোগিতা এবং পরার্থতার কৌশলও। কাজেই ঈশ্বর কিংবা কোনো বিশেষ ধর্মীয় বিশ্বাস নয়, এই মুহূর্তে নৈতিকতা এবং মূল্যবোধের উদ্ভবকে সফলভাবে ব্যাখ্যা করতে পারছে বিবর্তন তত্ব। নৈতিকতার জন্য ধর্মের কি আর কোনো প্রয়োজন আছে?
একটা সময় হয়তো ধর্মীয় নৈতিক বিধানগুলোর একটা ইতিবাচক ভূমিকা ছিল সমাজের উপর। নানা ধরনের ধর্মীয় বিধানই ছিল সে সময়কার আইন, ওগুলোই ছিল সুনীতিবোধ গড়ে তোলার ভিত্তিভূমি। কিন্তু সভ্যতার অগ্রগামীতার সাথে সাথে ধর্মীয় প্রযোজনিয়তা ফুরিয়ে যাচ্ছে, অনেক আগেই ফুরিযেছে ধর্মপ্রবর্তকদের ভূমিকাও। আজ আধুনিক মননের অধিকারী মানুষের কাছে প্রাচীন উপাসনা ধর্মগুলো একেবারেই অপাংক্তেয় হয়ে উঠেছে। কেউই আজ বিশ্বাস করে না তন্ত্র-মন্ত্রে অসুখ সারে, কিংবা ‘আল্লাহ মেঘ দে পানি দে’ বলে ডাকলেই বৃষ্টি ঝরে। সমাজে শৃঙ্খলা বজায় রাখতেও আজ ধর্মগুরু, নবী কিংবা পয়গম্বরদের ‘মহান মিথ্যার চেযে ধর্মনিরপেক্ষ বিজ্ঞানমনস্ক সমাজ, আইনের শাসন আর সাংস্কৃতিক অগ্রগতি অনেক বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখছে। ধর্মকেন্দ্রিক নৈতিকতার বিষয়গুলো অগ্রণী চিন্তার মানুষদের কাছে গুরুত্বহীন, তাদের মতো ধর্মমুক্ত মানুষেরাই হয়তো আগামীর পরিবর্তিত বিশ্বে নির্ধারণ করবে নৈতিকতা ও মূল্যবোধের এক নতুন সংজ্ঞা। শেষ করি রুদ্র মুহম্মদ শহীদুল্লাহর ‘আফিম তবুও ভালো, ধর্ম সে তো হেমলক বিষ’ কবিতাটি থেকে কিছু চরণ উদ্ধৃত করে—
একদার অন্ধকারে ধর্ম এনে দিয়েছিল আলো,
আজ তার কংকালের হাড় আর পচা মাংসগুলো
ফেরি করে ফেরে কিছু স্বার্থান্বেষী ফাউল মানুষ
সৃষ্টির অজানা অংশ পূর্ণ করে গালগল্প দিয়ে।
আফিম তবুও ভালো, ধর্ম সে তো হেমলক বিষ।
ধর্মান্ধের ধর্ম নেই, আছে লোভ, ঘৃণ্য চতুরতা,
মানুষের পৃথিবীকে শত খণ্ডে বিভক্ত করেছে
তারা টিকিয়ে রেখেছে শ্রেণিভেদ ঈশ্বরের নামে।
ঈশ্বরের নামে তারা অনাচার করেছে জায়েজ।
ইহকাল ভুলে যারা পরকালে মত্ত হয়ে আছে
চলে যাক সব পরপারে বেহেস্তে তাদের
আমরা থাকবো এই পৃথিবীর মাটি জলে নীলে,
দ্বন্দ্বময় সভ্যতার গতিশীল স্রোতের ধারায়
আগামীর স্বপ্নে মুগ্ধ বুনে যাবো সমতার বীজ।
“বিশ্বাসের ভাইরাস” বই সম্পর্কিত আপনার মন্তব্যঃ