মূল্যবোধঃ কে কোন সৃষ্টির যন্ত্রণা?
‘মূল্যবোধ’ শব্দটি ‘মূল্য’ এবং ‘বোধ’ শব্দ দুটির সমষ্টি। ‘মূল্য’ বলতে আমরা সাধারণভাবে বুঝি কোনও কিছুর সঙ্গে মুদ্রার বিনিময় হার। কিন্তু আমরা যদি বলি— “পথের পাঁচালী বিদেশ থেকে সম্মান আনার আগে আমরা সত্যজিৎ রায়ের প্রতিভার সঠিক মূল্যায়ন করতে ব্যর্থ হুয়েছিলাম”, এই বাক্যটির ক্ষেত্রে ‘মূল্য’ শব্দটি ‘মুদ্রা বিনিময় হার’ হিসেবে প্রয়োগ করা হয়নি। এখানে ‘মূল্যায়ন’ শব্দটি ‘যোগ্যতা নিরূপণ’ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।
‘বোধ’ শব্দের অর্থ ‘জ্ঞান’, ‘বুদ্ধি’, ‘চৈতন্য’, ‘বোঝা’ অর্থাৎ কোনও ঘটনা মস্তিষ্ক-স্নায়ুকোষে যে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে-তাই হল সে সম্পর্কে আমাদের বোধ।
‘মূল্যবোধ’ শব্দটির একটা গ্রহণযোগ্য অর্থ আমরা পেলাম—‘যোগ্যতা বোঝা’ বা ‘যোগ্যতা নিরূপণ’-এর ক্ষমতা এবং প্রবণতা। Value-র বাংলা অর্থ ‘যোগ্যতা’। ‘Sense of Value-র বাংলা হিসেবেই আমরা ‘মূল্যবোধ’ শব্দটির ব্যবহার করি, ‘Price’-এর বাংলা অর্থ হিসেবে নয়। এই ‘মূল্যবোধ’ শব্দটির সাহায্যে আমরা কোনও কিছুর ভালো-মন্দ, উচিত-অনুচিত ইত্যাদির যোগ্যতা পরিমাপ করি।
এই ‘বোধ’ বা ‘যোগ্যতা’ বোঝার ক্ষমতা সবার সমান নয়। তথাকথিত অলৌকিক রহস্য-ভেদের ক্ষেত্রে আমার যা বোধশক্তি তা একজন জারোয়ার চেয়ে যতগুণ বেশি, তার চেয়েও বোধহয় বেশিগুণ বেশি আমার ফুটবল বোধশক্তির তুলনায় পেলে বা মারাদোনার ফুটবল বোধশক্তি ।
‘মূল্যবোধ’ আপেক্ষিক। মূল্যের যে পরিমাপ আপনি করছেন, অর্থাৎ ‘যোগ্যতা নিরূপণ’ করছেন, তা অন্যের কাছে খারাপ মনে হতে পারে, আবার ভালোও মনে হতে পারে। আপনার কাছে যা আদর্শ, অন্যের কাছে তা অনাদর্শও হতে পারে।
সময় ও সমাজ অনুসারে মূল্যবোধ পাল্টায়। আবার একই
দেশের মানুষদের অগ্রসর অংশেরা যে মূল্যবোধে
বিশ্বাস করে, সেই মূল্যবোধ পিছিয়ে
থাকা মানুষদের চোখে অবক্ষয়
মনে হতেই পারে।
এক সময় সমাজের এক বৃহৎ অংশ মনে করত, স্বামীর সঙ্গে সহমরণে যাওয়াটাই নারী জীবনের চরম মূল্যবোধ। এক সময় নারী-শিক্ষা, বিধবা-বিবাহ ইত্যাদি অনগ্রসর রক্ষণশীলদের চোখে সমাজের অবক্ষয় বলেই ঘোষিত হয়েছে। রামমোহন রায় সতীদাহ-প্রথা রোধে আন্দোলন করেছিলেন, বিদ্যাসাগর নারী-শিক্ষা ও বিধবা বিবাহের পক্ষে আন্দোলন করেছিলেন। রামমোহন রায় ও বিদ্যাসাগরের এই আন্দোলন অনেকের চোখেই খারাপ ঠেকেছে। তাদের মনে হয়েছে এই আন্দোলন সমাজের অবক্ষয় ঘটাবে। আবার রামমোহন, বিদ্যাসাগরের চিন্তায় প্রভাবিত মানুষদের চোখে এই আন্দোলন মোটেই অবক্ষয় ছিল না, ছিল শ্রেয় মূল্যবোধ যা সমাজ পোষণ করছে না। ‘মূল্যবোধ’ আপেক্ষিক বলেই বিধবা বিবাহ, নারী শিক্ষা কারও চোখে ভালো, কারও চোখে খারাপ বলে মনে হয়েছে।
‘মূল্যবোধ’ বিষয়টিকে এবার আমরা মনস্তত্ত্ব ও সমাজতত্ত্বের দিক থেকে ভাবার চেষ্টা করি আসুন। মনস্তত্ত্ব ব্যক্তি ভাবনাকে ব্যাখ্যা করে, সমাজতত্ত্ব ব্যাখ্যা করে যৌথ ভাবনাকে, গোষ্ঠীবদ্ধ ভাবনাকে। আপাতভাবে মনে হতে পারে ব্যক্তির সমষ্টিকে নিয়েই যখন সমাজ, তখন অনেক ব্যক্তি-ভাবনার ব্যাখ্যা থেকেই তো সমষ্টির ভাবনার হদিশ মেলা উচিত ৷ অথবা গোষ্ঠীর ভাবনা ধরে আমরা পৌঁছতে পারি ব্যক্তি ভাবনায়। আসলে বাস্তব ক্ষেত্রে ব্যাপারটা তেমন অতি সরলীকৃত নয় যে, সবসময় ব্যক্তি ভাবনা থেকে গোষ্ঠী ভাবনায় অথবা গোষ্ঠী ভাবনা থেকে ব্যক্তি ভাবনায় পৌঁছে যাওয়া যায় সহজ-সরল নিয়মের সহায়তায়। অফিস টাইমের ট্রেনের একটি লেডিজ কামরায় যদি সমীক্ষা চালান, দেখতে পাবেন এঁদের প্রায় প্রত্যেকের মধ্যেই রয়েছে সুকুমারবৃত্তি, সুন্দরের প্রতি ভালোবাসা, নাচ, গান, সাহিত্য, নাটক, সিনেমার প্রতি টনটনে টান। এঁরাও ব্যক্তি জীবনে কারও না কারও স্নেহময়ী জননী, ভগ্নী, কারও প্রেমময়ী প্রেমিকা, কারও স্ত্রী, কারও বা কন্যা। ব্যক্তি ভাবনার এমন মহিলাদেরই সমষ্টিগত অন্য এক চেহারার পরিচয় পেয়েছি মাঝে-মধ্যে। কখনও কখনও খবর কাগজের খবর হয়েছে—লেডিজ কম্পার্টমেন্টে হঠাৎ উঠে পড়া কোনও পুরুষকে মহিলাগোষ্ঠীর তীব্র অপমান ও শারীরিক লাঞ্ছনা থেকে বাঁচতে লাফিয়ে পড়ে মৃত্যু বরণ করতে হয়েছে। তাই কমপার্টমেন্টে একটি পুরুষকে একা পেতেই সম্মিলিত মহিলাদের যে নিষ্ঠুরতা প্রকট হয়েছে, তার হদিশ পেতে ব্যক্তি ভাবনা ছেড়ে যৌথ ভাবনাকে ব্যাখ্যা করতে হবে। ইট দিয়ে বাড়ি তৈরি হলেও বাড়ি যেমন শুধুমাত্র ইটের পর ইট সাজানোর ব্যাপার নয়, তেমনই ব্যক্তি নিয়ে সমাজ হলেও সমাজ শুধু ব্যক্তির সমষ্টি নয়। বাড়তি কিছু। তাই শুধুমাত্র মনস্তত্ত্বের সাহায্যে সমাজ জীবনের ভাবনা বা সমাজ জীবনের ধারাকে ধরা নাও যেতে পারে।
অনেক সময় এমনও হয়েছে, ব্যক্তিগত মূল্যবোধ শেষ অবধি
সামাজিক মূল্যবোধে রূপান্তরিত হয়েছে। এ ক্ষেত্রে ব্যক্তি
তার চিন্তাভাবনার দ্বারা বহুকে প্রভাবিত করেছে
বহু থেকে বহুতরতে ছড়িয়ে পড়েছে সেই চিন্তার
রেশ। এই ভাবনা থেকে বহুতে ছড়িয়ে পড়ার
মধ্যে, গোষ্ঠীবদ্ধ ভাবনাতে রূপ পাওয়ার
মধ্যে যে প্রক্রিয়া, পদ্ধতি বা তত্ত্ব
রয়েছে— সেও সমাজতত্ত্ব।
‘মূল্যবোধ’ বিষয়টি মনস্তত্ত্বের দিক থেকে একটু ভাবনার চেষ্টা করা যাক। ব্যক্তি মানুষের মূল্যবোধ বা নীতিবোধের প্রকাশ ও বিকাশ তার সামাজিক পরিবেশের উপর অতিমাত্রায় নির্ভরশীল। পরিবেশগতভাবে কিছু মানুষের মনে হতেই পারে-ঈশ্বরে অবিশ্বাস নীতিহীনতারই পরিচয়, মূল্যবোধের অবক্ষয়েরই পরিচয়। আবার এই সামাজিক পরিবেশের প্রভাবেই কেউ কেউ মনে করতে পারেন-যুক্তিহীন ঈশ্বর-বিশ্বাস, অদৃষ্ট-বিশ্বাস নীতিহীন অন্ধ কুসংস্কার বই কিছুই নয়। বিপরীত মানসিকতার এই দুই শ্রেণির মানুষই কিন্ত পরিবেশগত ভাবেই প্রভাবিত হয়েছেন। এই প্রভাব ফেলার ক্ষেত্রে সক্রিয় ভূমিকা নিতে পারে আত্মীয়, বন্ধু, পরিচিত মানুষ, শিক্ষক, প্রচার মাধ্যম, সাহিত্য, নাটক, চলচিত্র, দূরদর্শন, আলোচনা সভা, বই-পত্তর, পত্র-পত্রিকা ইত্যাদি অনেক কিছুই, যা এরই কোনও একটি, যা মনকে বিপুলভাবে নাড়া দিয়েছে।
এমন বক্তব্য পেশ করার পর কেউ প্রশ্ন করে বসতে পারেন, আমাদের মানসিক জিন বৈশিষ্ট্য যদি পুরোপুরি জিন বা বংশগতি প্রভাবিত না হয়ে পরিবেশ দ্বারাই বেশি প্রভাবিত হয়, অর্থাৎ আমাদের মানসিক বৃত্তির উপর বংশগতির চেয়ে পরিবেশই যদি বেশি প্রভাবশালী হয় তবে অনুকূল পরিবেশের মধ্যে রেখে পশুদের মধ্যেও তো মানবিক-গুণ বা মানবিক-বৈশিষ্ট্যের বিকাশ ঘটানো সম্ভব-এমন তত্ত্বকেও মেনে নিতে হয়।
দু-কথায় উত্তরটা এই—মানবশিশু প্রজাতিসুলভ জিনের প্রভাবে মানবধর্ম বিকশিত হওয়ার পরিপূর্ণ সম্ভাবনা ( potentialities) নিয়ে অবশ্যই জন্মায় ৷ কিন্তু সম্ভাবনাকে বাস্তব রূপ দেয় মা-বাবা, ভাই-বোন, আত্মীয়-বন্ধু, শিক্ষক, অধ্যাপক, সহপাঠী, খেলার সঙ্গী, পরিচিত ও আশপাশের মানুষরা অর্থাৎ সামাজিক পরিবেশ। আমরা যে দু’পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়াই, হাঁটি, পানীয় পশুর মতন জিব দিয়ে চেটে গ্রহণ না করে পান করি, কথা বলে মনের ভাব প্রকাশ করি- এ সবের কোনওটাই জন্মগত নয়। এইসব অতি সাধারণ মানব-ধর্মগুলোও আমরা শিখেছি, অনুশীলন দ্বারা অর্জন করেছি। শিখিয়েছে আমাদের আশেপাশের মানুষগুলো, অর্থাৎ আমাদের সামাজিক পরিবেশ। এই মানবশিশুই কোনও কারণে মানুষের পরিবর্তে পশু সমাজের পরিবেশে বেড়ে উঠতে থাকলে তার আচরণে, হাঁটা-চলায়, খাদ্যাভ্যাসে, পানীয় গ্রহণের কায়দায়, ভাব বিনিময়ের পদ্ধতিতে পশু সমাজের প্রভাবই প্রতিফলিত হবে। কিন্তু একটি বনমানুষ বা শিম্পাঞ্জিকে শিশুকাল থেকে আমাদের সামাজিক পরিবেশে মানুষ করলেও এবং আমাদের পরিবারের শিশুর মতো তাকেও লেখাপড়া শেখাবার সর্বাত্মক চেষ্টা চালালেও তাকে আমাদের সমাজের স্বাভাবিক শিশুদের বিদ্যে, বুদ্ধি, মেধার অধিকারী করতে পারব না; কারণ এই বনমানুষ বা শিম্পাঞ্জির ভিতর বংশগতির ধারায় বংশানুক্রমিক মানবিক গুণ না থাকায় তা অনুকূল পরিবেশ পেলেও বিকশিত হওয়া কোনওভাবেই সম্ভব নয়। অর্থাৎ মানব গুণ বিকাশে জিন ও পরিবেশ দু’য়েরই প্রভাব বিদ্যমান।
আবার একই পরিবেশের মধ্যে বেড়ে ওঠা বিভিন্ন ব্যক্তির মধ্যে বৈচিত্র্য ও বিভিন্নতার পরিচয়ও আমরা পাই বইকি। কেন এমনটা হয়? এই প্রসঙ্গে মনস্তত্ত্ব নিয়ে আসবে বিভিন্ন ব্যক্তি মানুষের বিভিন্ন প্রবণতার কথা। যমজ হওয়ার সুবাদে একই ধরনের গাত্র-বর্ণ, একই ধরণের দেহ-গঠন এবং একই ধরনের মুখাকৃতি হওয়া সত্ত্বেও প্রত্যেক ব্যক্তিমানুষ স্বতন্ত্র-‘ইন্ডিভিজুয়াল’, প্রত্যেক মানুষের মস্তিষ্ক স্নায়ুকোষের গতিময়তা, উত্তেজনা-নিস্তেজনা, আবেগপ্রবণতা বা সংবেদনশীলতা ইত্যাদি ধর্মগুলো ভিন্নতর। তাই একই সামাজিক পরিবেশের সঙ্গে বেড়ে ওঠার দরুন সাধারণভাবে ও সামগ্রিকভাবে সেই পরিবেশ দ্বারা প্রভাবিত হলেও সেই প্রভাবেরও নানা তারতম্য ঘটে, রকমফের ঘটে এমনকী, ভিন্নতর, নতুন চিন্তা-ভাবনার উন্মেষও দেখা যায়। অনেকসময়ই দেখা যায় সমাজতত্ত্ব ও মনস্তত্ত্ব উভয় উভয়েরই সঙ্গে একটা বিরোধের ভাব পোষণ করে থাকে। সমাজতত্ত্ব যেন একটা ধরণা উপর থেকে চাপিয়ে দিচ্ছে। ব্যক্তির উপর বহুর চিন্তা বা শাসকশ্রেণির চিন্তা চাপানোর মধ্যে অনেক সময় দেখা দেয় বিরোধ
যে সমাজে শোষণ আছে, সে সমাজে শোষিত থাকবেই, থাকবে শোষক । শোষকরা তাদের প্রতিনিধিদের দ্বারাই চালিয়ে থাকে শাসন। নির্বাচননির্ভর গণতন্ত্রে বাক্সে জেতার মতো ভোট ফেলতে ‘বুথ জ্যাম’, ‘রিগিং’, মস্তান বাহিনী, প্রচার, এজেন্ট নিয়োগ ইত্যাদি প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়েই এগোতে হয়- যা বিপুল ব্যায়সাধ্য, এবং যে ব্যয়ভারের পুরোটাই জোগায় শোষকশ্রেণি । তার ফলশ্রুতিতে
শ্রেণিবিভক্ত সমাজে শাসকশ্রেণি শোষকশ্রেণির স্বার্থরক্ষার
প্রয়োজনে বহু নীতিবোধ বা মূল্যবোধ সমাজের উপর
চাপিয়ে দেয়। এই নীতিবোধ বা মূল্যবোধ ব্যাপক
প্রচারের ফলে ব্যাপক মগজ ধোলাইয়ের
ফলে বহুর কাছেই গ্রহণযোগ্যতা
অর্জন করে।
বিজ্ঞানভিত্তিক চিন্তা, সমাজ সচেতনতা, রাজনৈতিক বিশ্বাস থেকে অথবা নৃতত্ত্ব, ইতিহাস, সমাজবিজ্ঞান ও বিজ্ঞান পড়ার ফলে, কিংবা সঞ্চিত অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে পরিচালিত হওয়ার ফলে আমরা যদি এই সিদ্ধান্তে পৌঁছোই-একঃ দেশপ্রেম মানে দেশের মাটির প্রতি প্রেম নয়, দেশের সংখ্যাগুরু মানুষের প্রতি প্রেম। দুইঃ সমাজসেবার মাধ্যমে শোষণ মুক্তি ঘটেছে, এমন দৃষ্টান্ত আজ পর্যন্ত কোনও ঐতিহাসিকের জ্ঞান ভাণ্ডারে নেই। হাজারটা রামকৃষ্ণ মিশন, হাজারটা ভারতসেবাশ্রম সংঘ, হাজার মাদার টেরিজার সাধ্য নেই ভারতের শোষিত-জনতার শোষণমুক্তি ঘটানোর। তিনঃ ঈশ্বর, ভূত, কর্মফল, অদৃষ্ট এবং অলৌকিকত্বের বাস্তব কোনও অস্তিত্ব নেই। শোষক ও শাসকশ্রেণি শোষণকে কায়েম রাখতেই শোষিতদের মধ্যে এই ভ্রান্ত চিন্তাগুলোর প্রসারকামী। চারঃ দাম্পত্যজীবন গড়ে তোলার প্রথম শর্ত হওয়া উচিত বন্ধুত্ব, যৌন স্বত্বাধিকার নয়-ইত্যাদি আরও বহুতর মূল্যবোধ সম্পর্কিত ধারণায়, তবে এই পরিবর্তনটা হবে অবশ্যই কাম্য। পূর্বতন পুরুষদের কাছে, সংখ্যাগুরু মানুষদের কাছে, পশ্চাদবর্তী মানুষদের কাছে, মগজ ধোলাইয়ের শিকার মানুষদের কাছে আমাদের অগ্রবর্তী চিন্তার ফসল হিসাবে গড়ে ওঠা মূল্যবোধকে ‘মূল্যবোধের অবক্ষয়’ মনে হওয়াটাই স্বাভাবিক। এক্ষেত্রে যুক্তিবাদী, প্রগতিবাদী, সুস্থ চেতনার মুক্তিকামী মানুষদের কাছে এই যুগোচিত পরিবর্তিত চিন্তা মূল্যবোধের উত্তরণ। এই মূল্যবোধের প্রতিষ্ঠার অর্থ অবৈজ্ঞানিক মূল্যবোধের ক্ষয়। মূল্যবোধের পরিবর্তন মানেই ‘অবক্ষয়’ অবশ্যই নয়। শাসকশ্রেণির চাপিয়ে দেওয়া নীতির ব্যক্তিগতভাবে প্রতিবাদ করার অধিকার আপনার, আমার সবারই সব সময়ই থেকে যাবে। এই প্ৰতিবাদকেই আপনি, আমি সক্রিয় চেষ্টার ফলে যৌথ চেহারা দিতে পারি। কাজেই সমাজের সঙ্গে ব্যক্তিগত মূল্যবোধের সম্পর্ক একটা সচল সম্পর্ক। এমন হতেই পারে—আপনার, আমার ব্যক্তিগত মূল্যবোধ শেষ পর্যন্ত জন সমর্থন পেয়ে সামাজিক মূল্যবোধ হয়ে উঠতেই পারে। সমাজের সঙ্গে ব্যক্তিগত মূল্যবোধের সম্পর্ক একই সঙ্গে বিরোধ এবং সংগতির।
পৃথিবীতে সর্বকালে বিপ্লবীদের সংগ্রাম চেতনা মুক্তির সংগ্রাম, মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম, শোষণ মুক্তির সংগ্রাম। মানব প্রগতির পক্ষে প্রয়োজনীয় মূল্যবোধ ধ্বংস করার ক্ষেত্রে সেই শক্তিগুলোই প্রধান, যে সমস্ত শক্তি সমাজের উপর নিজ স্বার্থসংশ্লিষ্ট মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠা করতে সক্রিয়-অর্থাৎ শোষক ও শাসকশ্রেণি। আমাদের শাসকশ্রেণি যে দুর্নীতির পরিমণ্ডল ও রাজনৈতিক অভ্যাস গড়ে তুলেছে তা অবশ্যই মূল্যবোধে অবক্ষয়কারী। এই রাজনৈতিক অভ্যাসের সঙ্গে রাজনৈতিক দর্শনকে আমরা যদি গুলিয়ে ফেলে বিচারে বসি, তাহলে ভুল হবে। গান্ধিবাদী দর্শন, মার্কসবাদী দর্শন ও জাতীয়তাবাদী দর্শন—সকল দর্শনেই অনেক ভালো ভালো কথা আছে অতএব গান্ধিবাদী কংগ্রেস, মার্কসবাদী বামপন্থী অথবা জাতীয়তাবাদী ভারতীয় জনতা পার্টি সকলেই ভালো রাজনৈতিক দর্শনযুক্ত দল এবং ভালো দল—এমনটা ভাবলে বেজায় ভুল করা হবে।
রাজনৈতিক দলগুলোর দর্শনের সঙ্গে আচরণের মধ্যে যে
অসংগতি তাই হল দুর্নীতি ও রাজনৈতিক
অভ্যাস-যা মূল্যবোধকে ধ্বংস করার
পক্ষে পারমাণবিক বোমা।
নিপীড়িত মানুষের দর্শন হিসেবে মার্কসবাদী দর্শন এক সময় এ দেশের কিছু অঞ্চলের মানুষদের যথেষ্ট আস্থা অর্জন করেছিল। এই আস্থা অর্জনের পিছনে ছিল দলীয় নেতা ও কর্মীদের অনাড়ম্বর জীবনযাত্রা, ত্যাগস্বীকারের ইচ্ছে, রাজনৈতিক দর্শন ও আচরণের মধ্যে সংগতি। তারপর সংসদীয় গণতন্ত্রের লাগাম নিজেদের হাতে নিতে মার্কসবাদী দলকেও সেই রাজনৈতিক অভ্যাসের কাছে আত্মসমর্পণ করতে হচ্ছে যে অভ্যাসের সঙ্গে মিশে রয়েছে চরম দুর্নীতি। ভারতবর্ষে নির্বাচন-কেন্দ্রিক রাজনীতির ক্ষেত্রে নিরন্তর চলেছে বিশাল টাকার খেলা, নীতিকে শিকেয় তুলে যে কোনও উপায়ে ভোট পাওয়ার চেষ্টা এবং ভোট পাওয়ার আগে ও ভোট পাওয়ার পরের আচরণের মধ্যে চরম অসংগতি। কিছু রাজ্যে ক্ষমতার গদিতে বসা মার্কসবাদী দলও ক্ষমতার গদিতে থাকার তীব্র আগ্রহে মার্কসীয় দর্শনকে শিকেয় তুলে রেখে চালু রাজনৈতিক অভ্যাসের সঙ্গে সড়োগড়ো হতে সচেষ্ট থাকে। তারই ফলশ্রুতিতে আজ আত্মত্যাগী, আদর্শবাদী কমরেডদের পরিবর্তে প্রমোটার মার্কসবাদী, জমি-বাড়ির দালাল মার্কবাদী, বাজারের তোলা আদায়কারী মার্কসবাদী, চোরা কারবারি মার্কসবাদী, মস্তান মার্কসবাদী, ধর্ষক মার্কসবাদী ইত্যাদি ক্ষমতার শাঁসে-জলে পুষ্ট মার্কসবাদীতে দল ছেয়েছে। বহু ‘বিপ্লবী’ আজ হুজুরদের নির্ভরযোগ্য প্রতিনিধিতে রূপান্তরিত হয়েছেন।
শোষিত মানুষদের দুঃখ ও শোষণ থেকে মুক্তিলাভের আকুতি থেকে মানুষ মহৎ আদর্শের অনুসন্ধান চালিয়েছে। নিরন্তর সংগ্রাম ও বহু রক্তের বিনিময়ে কখনও কোনও আদর্শবাদ ছিনিয়ে এনেছে নিজেদের মুক্তি, জয়, দখল করেছে রাষ্ট্রক্ষমতা। ইতিহাস থেকে আমরা বারবার শিক্ষা নিয়েছি-রাষ্ট্রক্ষমতা দখলের কিছুকাল বাদে সেই মহৎ আদর্শের প্রচারক নেতারা আদর্শ বোধের অন্তর্গত ত্যাগের বোধকে নির্বাসনে পাঠিয়ে ভোগসর্বস্বতায় নিজেদের ডুবিয়ে রাখতে দুর্নীতিকে নিজেদের বেঁচে থাকার শ্বাসপ্রশ্বাস করে নিয়েছে। সুন্দর কথা ও অসুন্দর আচরণের অসংগতি প্রতিটি ক্ষেত্রেই মানুষের চোখে ধরা পড়েছে। নেতৃত্বের প্রতি মানুষের মোহভঙ্গ হয়েছে, বিশ্বাসভঙ্গ হয়েছে।
কিন্তু সংগ্রামী মুক্তিকামী মানুষ আবারও নতুন আশায় বুক
বেঁধেছে, নতুন করে বাঁচতে চেয়েছে, সংগ্রামের মধ্য
দিয়ে নিজেদের জয়কে ছিনিয়ে আনতে চেয়েছে।
ফলে নতুন মূল্যবোধের মধ্য দিয়েই
অঙ্কুরোদগম ঘটেছে বিপ্লবের।
ইতিহাসে নবযুগ আসবেই—এই প্রত্যয় নিয়ে আসুন, প্রতিটি সমাজ-সচেতন মানুষ মানবিকতার বিকাশকামী, মুক্তিকামী নতুন নতুন মূল্যবোধ গড়ে তুলতে সচেষ্ট হই।
প্রেম ও বিবাহঃ বন্ধন মেনো না, ভাঙো অচলায়তন
২৭ আগস্ট ১৯৯২ ‘আজকাল’ পত্রিকায় একটি খবর প্রকাশিত হয়েছিল-কমিউনিস্ট পার্টি অব ইন্ডিয়া (মার্কসিস্ট) -এর এক নেতাকে প্রেম করার অপরাধে অভিযুক্ত হতে হয়েছে এবং দলের সদস্যপদ ত্যাগ করতে হয়েছে। এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের সমিতির সদস্য পাচু রায়ের একটি চিঠি আজকালে প্রকাশিত হয় ৩০ আগস্ট। আলোচনার শুরুতেই চিঠিটি তুলে দেওয়ার লোভ সংবরণ করতে পারলাম না।
যতই কমিউনিস্ট পার্টি করি, যতই মার্কসবাদের কথা বলি, যতই ‘লেনিনবাদ লেনিনবাদ’ বলে চেঁচাই, সংস্কার আমাদের চেতনার আণবিক স্তরে বদ্ধমূল। বৃদ্ধ-বিপত্নীক সি পি এম নেতাটি ভুল বা অন্যায় কী করলেন বুঝতে পারলাম না। তাঁর প্রেমিকা বিগত দশ বছর স্বামীর সঙ্গে সম্পর্করহিত। তাহলে এখানে পরস্পরের বন্ধু হয়ে বসবাস করতে অসুবিধা কোথায়। সাংবিধানিক অসুবিধা?
বিবাহ বিচ্ছেদ হয়নি বলে? নাকি বুড়ো বয়সে আবার, প্রেম-ভালবাসা কী ? ওসব তো যৌবনের ব্যাপার, শারীরিক সক্ষমতার ব্যাপার সি পি এম-এর হাওড়া-নেতৃত্ব কি এই লাইনে ভাবছেন? আসলে সংবিধানের প্রতি, বুর্জোয়া প্রতিষ্ঠানগুলির প্রতি, সামন্ততান্ত্রিক ধ্যানধারণার প্রতি এক দূরপনেয় আনুগত্য আমাদের মজ্জার আণবিক স্তরে প্রোথিত। মুখে কংগ্রেসের বিরুদ্ধে, বি জে পি-র বিরুদ্ধে ভোট বাক্সটাকে সামনে রেখে আসর গরম করা যায়, মালিকদের ক্ষেত্রে বিশেষ বিশেষ সময়ে ট্রেড ইউনিয়ন করা যায়, ২২ এপ্রিল সাড়ম্বরে লেনিনের জন্মদিন পালন করা যায়, ৫ মে কার্ল মার্কসের জন্মদিনে মালা-ফালা দেওয়া যায়। কিন্তু মাটির কাছের সমস্যাগুলি যখন আসে তখন মাথার ভিতর বুর্জোয়া জমিদারতন্ত্রের পোকাগুলি নড়েচড়ে বসে। তারাই তখন প্রাধান্য পায়। বিবাহ নামক প্রতিষ্ঠানটির গণ্ডদেশে সজোরে চপেটাঘাতও করেছিলেন ভ্লাদিমির ইলিচ লেনিন। স্ক্রুপস্কায়াকে কোনদিন সেই অর্থে বিয়ে করেননি। কার্ল মার্কস প্রচণ্ড ভালবাসতেন জেনি মার্কসকে, তৎসত্ত্বেও তাঁদের পরিচারিকার প্রেমে পড়েছিলেন কার্ল মার্কস । একটি পুত্র সন্তানের জন্ম হয়েছিল তাঁদের মিলিত প্রয়াসে। মাও সে তুং প্রথম স্ত্রী বেঁচে থাকতেই পার্টির একজন সহকর্মীকে বিয়ে করেছিলেন, পার্টির পলিটব্যুরোর সামনে। একদিন বিবাহপ্রথা এবং বিবাহ নামক প্রতিষ্ঠানের জন্ম হয়েছিল পরিবারতন্ত্রকে বাঁচিয়ে রাখতে। পরিবারতন্ত্র গর্বিত হয়েছিল শ্রেণিশোষণকে বজায় রাখতে। যদি কোনওদিন সাম্যবাদ আসে তবে শ্রেণিশোষণ যেমন বিলুপ্ত হবে, তেমনি লুপ্ত হবে পরিবারের প্রচলিত কাঠামো, লোপ পাবে বিবাহ নামক বহুলালিত প্রতিষ্ঠানটি।
সাধারণ মানুষ এতসব বুঝবেন না। হয়ত, তাঁরা বাঁচতে চাইবেন পুরনো ব্যবস্থাকে আঁকড়ে। কিন্তু যাঁরা নিজেদের মার্কসবাদী বলে সাইনবোর্ডে প্রচার করছেন তাঁদের ক্ষেত্রেও কি বুর্জোয়া অনুশাসন এত তীব্রভাবে প্রযোজ্য? যারা কি এঙ্গেলস পড়েননি? নাকি ভোটের ডামাডোলে সে-সব ভুলে গেছেন বেমালুম। দলত্যাগী শচীন্দ্রনাথের প্রতি আমার আন্তরিক অভিনন্দন রইল এই কারণে যে, পার্টির চেয়ার অটুট রাখতে মার্কসবাদগ্রাহ্য সুন্দর সম্পর্ককে তিনি অসম্মান করেননি।
এই চিঠি প্রকাশিত হওয়ার পর আমাকে অনেকেই প্রশ্ন করেছেন, আপনি কি এই চিঠির বক্তব্যের সঙ্গে একমত? উত্তরটা স্বভাবতই হয়েছে— হ্যাঁ। অমনি এমন প্রশ্নও অনেকে করেছেন, কার্ল মার্কস-এর স্ত্রী অথবা মাও সে তুং-এর স্ত্রী যদি অন্য কোনও পুরুষের সঙ্গে বন্ধুত্বের সূত্রে সহবাস করতেন,
তাহলে কি মার্কস বা মাও সে তুং বাস্তবিকই স্বাভাবিকভাবে মেনে নিতে পারতেন? প্রতিটি ক্ষেত্রেই উত্তর দিয়েছিলাম। যেহেতু দুই ইতিহাসপ্রসিদ্ধ পুরুষের স্ত্রীরা এমন ঘটনা ঘটাননি এবং চরিত্রগুলির কেউই আজ জীবিত নন, তাই ভবিষ্যতে এমন ধরনের ঘটনা ঘটার সম্ভাবনাও শূন্য। অতএব মার্কস ও মাও কী করতে পারতেন এমন সম্ভাব্য উত্তরগুলির মধ্যে যে কোনওটিই ঠিক বা বেঠিক হতেই পারত। মার্কস ও মাও ঠিক কী করতেন, দু’জনের মধ্যে একই ধরনের প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হত কি না –এ সবের সঠিক উত্তর দেওয়া যখন একেবারেই অসম্ভব, তখন এ বিষয়ে আমিই বা কী উত্তর দেব?
পুরুষ ও নারীর ‘স্বামী-স্ত্রী’ জাতীয় কোনও স্থায়ী সম্পর্কের ক্ষেত্রে বন্ধুত্বই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। প্রতিষ্ঠানিক বিবাহের ক্ষেত্রে এই বন্ধুত্বটাই সবচেয়ে গুরুত্বহীন বলে বিবেচিত হয়ে থাকে। পত্রিকা খুলে ‘পাত্রী চাই” -এর বিজ্ঞাপনের দিকে নজর দিলেই দেখতে পাবেন এ দেশের ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, সি এ, আই এ এস, আই পি এস, বি সি এস, ব্যাঙ্ক অফিসার ইত্যাদি পদের হীরের টুকরো ছেলেরা উর্বশী, মেনকা, রম্ভার খোঁজ করছেন। আর ‘পাত্র চাই’ বিজ্ঞাপনের দিকে যদি চোখ বোলান তাহলে দেখতে পাবেন সুন্দরী আর শিক্ষিতা মেয়েরা হীরের টুকরো ছেলে খুঁজছেন। এক্ষেত্রে সাধারণত হীরের টুকরো ছেলেরা তাঁর সম্ভাব্য স্ত্রীকে গাড়ি, ফ্ল্যাট, ফ্রিজ, ভি সি আর ইত্যাদির মতোই আভিজাত্যের প্রতীক অর্থাৎ স্ট্যাটাস সিম্বল একটি বস্তু সামগ্রী হিসেবেই দেখেন। উর্বশী, মেনকা, রম্ভা অথবা সরস্বতীর দলও সাধারণত একইভাবে তাঁদের সম্ভাব্য স্বামীটিকে আর পাঁচটা স্ট্যাটাস নির্ধারক বস্তুসামগ্রী হিসেবেই বিবেচনা করেন। নারীরা যতই নারী স্বাধীনতা ও পুরুষের সমান অধিকার দাবি করুন না কেন, বেকার ছেলে বিয়ে করতে তো কখনোওই বিজ্ঞাপন দেন না? তবে বেকার মেয়েরা কী করে প্রত্যাশা করেন রাজপুত্তুররা তাঁদের বিয়ে করবেন? আসলে
মেয়েদের চেতনার অণুতে অণুতে সংস্কারের মজ্জায় মজ্জায় ঢুকে
গেছে স্বামীকে আভিজাত্যের নিদর্শন একটি বস্তু হিসেবে
পরিমাপ করা, স্বামীকে নিজের চেয়ে অনেক বড়
মাপের হিসেবে চাওয়া, নিজের ওপর স্বামীর
স্বত্বাধিকার মেনে নেওয়া। এই চাওয়ার
মধ্যে কোনও রকম ভাবেই একটি
নতুন পুরুষের সঙ্গে আপন
বন্ধু হিসেবে সম্পর্ক
স্থাপনের আন্তরিক
প্রচেষ্টা দেখতে
পাই না।
এই প্রসঙ্গে মনে পড়ে যাচ্ছে একটি ঘটনার কথা। ভারতের সর্বকালের শ্রেষ্ঠ ফুটবল খেলোয়াড়দের অন্যতম এক চরিত্র এই ঘটনার নায়ক। নায়কের প্রেমে পড়লেন এক অতি সাধারণ দেখতে এম এ পাশ ব্যাঙ্ক কেরানি। নায়কের সঙ্গে মাঠে, পার্টিতে সর্বত্র তাঁকে বিচরণ করতে দেখা গেল। এক সময় বয়সের সঙ্গে সঙ্গে প্রাকৃতিক নিয়মেই নায়ককে তাঁর স্থান ছেড়ে দিতে হল নতুন প্রতিভার কাছে। খেলাহীন নায়ক গ্ল্যামারের জগৎ থেকে ঝপ করে বিদায় নিতেই নায়িকাও বিদায় নেওয়ার জন্য ছট্ফট্ করতে লাগলেন বন্দি পাখির মতোই। নায়কের অনুরোধে আমি নায়িকার সঙ্গে কথা বলতে বসেছিলাম। নায়িকা দেখলাম বেশ কয়েক বছর পর হঠাৎ আবিষ্কার করে ফেলেছেন— নায়কের শিক্ষাগত যোগ্যতা স্কুল ফাইনাল, নায়ক শিডিউলকাস্ট, নায়ক চাকরি জীবনে মামুলি ব্যাঙ্ক কেরানি, নায়ক ভালো ইংরেজি বলতে পারেন না, ইত্যাদি ইত্যাদি। আজ যেগুলো নায়কের বিশাল ‘ডিসকোয়ালিফিকেশন’ বলে মনে হচ্ছে, তার কোনোটাই কয়েক বছর আগেও নায়িকার অজানা ছিল না—আমি জানি। কিন্তু এতদিন পর আজ নায়িকার মাথায় এ প্রশ্ন বড় হয়ে দেখা দিল কেন— এমন মানুষটিকে বিয়ে করলে বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-স্বজনের সামনে মাথা হেঁট হয়ে যাবে, এমন মানুষকে আর যাই হোক জীবনের নায়ক করা যায় না।
গ্ল্যামারের জগৎ থেকে প্রেমিকের বিদায় ঘোষিত হতেই প্রেমিকা তাঁর হৃদয় থেকে নির্বাসন দিয়েছিলেন, ‘স্বামী’ নামক বস্তুটিকে স্ট্যাটাস সিম্বল হতে হবে এই ধারণা থেকেই। এটা কোনও ‘বিচ্ছিন্ন’ ঘটনা বা ‘ব্যতিক্রম’ ঘটনা নয়। এটাই আমাদের সমাজের নারী-পুরুষ উভয়ের ক্ষেত্রেই স্বাভাবিক চিত্র, এটাই আমাদের সমাজ জীবনের মানসিকতার ছবি।
নারীরা যেমন সাধারণভাবে তাঁর চেয়ে কম ব্যক্তিত্বসম্পন্ন, গুণসম্পন্ন পুরুষকে জীবনসঙ্গী করতে একেবারেই নারাজ, তেমনই সমব্যক্তিত্বসম্পন্ন, সমপর্যায়ের অথবা উচ্চতর পর্যায়ের নারীকে দাম্পত্যজীবনে বন্ধু করে নিতে পুরুষরা একেবারেই গররাজি। ব্যতিক্রম নারী ও পুরুষ নিশ্চয়ই আছে, কিন্তু তাঁদের সংখ্যা এতই কম যে, শতকরা হিসেবের মধ্যে আসে না।
দাম্পত্য জীবন গড়ে তোলার প্রথম শর্ত যখন হওয়া উচিত বন্ধুত্ব, তখন প্রথম শর্ত বিষয়কে দূরে সরিয়ে রেখে এ-সমাজ যদি অন্য কোনও পরিমাপকে অধিকতর গুরুত্ব দেয়, তবে তাকে যুক্তিনিষ্ঠ সমাজ সচেতন মানুষরা মেনে নেবে কেন?
কেন এমন একটা অসুস্থ মানসিকতার দ্বারা পরিচালিত হয়ে গড়ে উঠেছে নারী-পুরুষ দাম্পত্য সম্পর্ক? এর জন্য অবশ্যই দায়ী সামাজিক পরিবেশ— যেখানে আমরা অহরহ দেখতে পাচ্ছি পাত্র-পাত্রী নির্বাচনের ক্ষেত্রে অদ্ভুত এক পরিমাপ পদ্ধতি, যেখানে আমরা নারীর আদর্শ বলতে সতীত্ব এবং পরিপূর্ণতা বলতে মাতৃত্বকে চিহ্নিত করি, যেখানে আমরা স্বামী-স্ত্রীর মানসিক দূরত্ব শত-যোজন হলেও হিমালয়ের চেয়ে ভারী সেই সম্পর্ককে বয়ে বেড়ানোর মধ্যেই সুনীতিকে খুঁজে পাই, যে পরিবেশ শৈশব থেকে আমাদের কানে মন্ত্র জপেছে, ছেলেরা সোনার মতো, কোনও কলঙ্কেই যা মলিন হয় না, আর নারী জীবনে কলঙ্ক স্পর্শ করলে তা কখনওই মোছে না। এমনি হাজারো জানা-বোঝা-শোনা আমাদের চিন্তাকে আমাদের সংস্কারকে বিপুলভাবে প্রভাবিত করেছে। নারী-পুরুষের যুগল সম্পর্ক বিষয়ে এমন যুক্তিহীন চিন্তার উপর ভিত্তি করেই গড়ে উঠেছে আমাদের মূল্যবোধ, আমাদের নীতিবোধ ।
সমাজে যে শৃঙ্খলা আনতে প্রাতিষ্ঠানিক বিবাহের সূচনা,
সেই বিবাহই আজ হয়ে দাঁড়িয়েছে নারীদের
শৃঙ্খলিত করার এক প্রক্রিয়া।
নারী প্রাক্বিবাহিত জীবনে পিতার, বিবাহিত যৌবনে স্বামীর এবং বার্ধক্যে পুত্রের অধীনতা অবনত মস্তকে আজও মেনে চলেছে। পুরুষ-শাসিত এই সমাজ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে ‘কোটিতে গুটিক’ নারী বিদ্রোহিণী হয়েছেন, শৃঙ্খল মুক্তির জন্য সোচ্চার হয়েছেন, কিন্তু সংখ্যাগরিষ্ঠেরা দীর্ঘকালীন মগজ ধোলাইয়ের শিকার হয়ে পুরুষের অধীনতা মেনে নেওয়ার মধ্যেই সুখ খুঁজে পেয়েছেন। বার্ট্রান্ড রাসেল একবার তীব্র বিদ্রূপ মেশানো রসিকতায় মন্তব্য করেছিলেন-পিতৃতান্ত্রিক সমাজে নারীদের স্বাধীনতা না থাকলেও পুরুষদের ছিল। তারা সুখী ছিল। জনসংখ্যার অর্ধেক সুখী থাকা কম কথা নয়। পরাধীন নারী সমাজের কিয়দংশও অসুখী ছিল না।
এইসব প্রাতিষ্ঠানিক বিয়েতে যেহেতু পাত্র-পাত্রীরা নিজেদের মধ্যে মতাদর্শগত মিলের মধ্য দিয়ে বন্ধুত্ব গড়ে তোলার চেয়ে বস্তু সামগ্রী হিসেবে উভয়কে বিবেচনা করতে বেশি আগ্রহী থাকেন, তাই এই ধরনের বিয়ের মধ্য দিয়ে শুধুমাত্র যৌন স্বত্বাধিকারই প্রতিষ্ঠিত হয়। মতাদর্শগতভাবে মিলহীন, প্রেমহীন, গভীর বন্ধুত্বহীন এমন দেহ-মিলনকে ‘সুবিধাবাদী লাম্পট্য’ ছাড়া আর কিছু বলে অভিহিত করা যায় কি? এই ধরনের বিয়ে থেকে সাধারণত গভীর ও সুন্দর বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে না, গড়ে ওঠে ‘রুম মেট’ জাতীয় এক ধরনের পরিচিতের সম্পর্ক যা, এক সঙ্গে থাকা, খাওয়া ও ঘুমোনোর মধ্যেই সীমাবদ্ধ। এই সম্পর্ক যেহেতু মতাদর্শগত মিল ছাড়াই গড়ে ওঠে, তাই স্বামী-রত্নটির জীবনে আর্থিক বিপর্যয় ঘটলে এবং তার দরুন পারিবারিক স্ট্যাটাসের বিশাল রকম পতন ঘটলে স্বামীগর্বে ও স্বামী প্রেমে মাতোয়ারা স্ত্রীর প্রেমও চটকে যায়—প্রায় সব ক্ষেত্রেই এমনটা হয়। এরপরও প্রায় ক্ষেত্রেই স্বামী-স্ত্রীর প্রাতিষ্ঠানিক সম্পর্ক অবশ্যই টিকে থাকে— কিন্তু তা ভালোবাসাহীন, বন্ধুত্বহীন ভাবেই। আর্থিক বিপর্যয়ে প্রেম বিপর্যস্ত হবে— এমন পরিণতি ঘটার সম্ভাবনা কিন্তু মতাদর্শগত মিল থেকে গড়ে ওঠা সম্পর্কের ক্ষেত্রে শূন্য। মতাদর্শগত মিলন থেকে গড়ে ওঠা সম্পর্ক অর্থনৈতিক বিপর্যয়ে ভাঙে না, ভাঙে মতাদর্শের সংঘাতে।
স্ত্রীর উপর স্বামীর এমন স্বত্বাধিকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার কারণ যেমন অনেক ক্ষেত্রেই স্বামীর ওপর স্ত্রীর অর্থনৈতিক নির্ভরশীলতা, তেমনি অনেক সময় সামাজিক পরিবেশগত কারণে অনেক নারী ধরেই নেন স্বামী পুত্র-কন্যার সেবায় জীবন উৎসর্গ করার মধ্যেই নারী জীবনের সার্থকতা। আপনি যখন মা হিসেবে ছেলের জামা-প্যান্ট ধোয়া, ইস্ত্রি করা, স্কুলের টিফিন তৈরি করে গুছিয়ে দেওয়া, জুতোর পালিশ ঠিক রাখা ইত্যাদি কাজগুলো করেন স্নেহময় জননীর মহান কর্তব্য হিসেবে, তখন একেবারের জন্যেও কি ভাবছেন আপনার এমনতর কাজ-কর্মের ফলে যৌবনে পৌঁছে আপনার ছেলে প্রত্যাশা করবে তার স্ত্রীও এমনি করে গৃহকর্ম ও শিশুপালনের কাজগুলো একা হাতেই . সামলাক। সে তখন নিশ্চয়ই স্ত্রীকে গৃহকর্ম, শিশুপালন ইত্যাদি বিষয়ে পরিপূর্ণ সহযোগিতা করতে এগিয়ে আসবে না। আপনার মেয়ে যৌবনে পৌঁছে আপনার প্রভাবে এটাই ধরে নেবে এসর কাজ করার একক দায়িত্ব একজন আদর্শ স্ত্রী। ও মা হিসেবে তারই। এখনও আমাদের সমাজে সাধারণভাবে প্রচলিত স্ত্রী চাকুরিরতা হলেও তার উপরই বর্তায় গৃহকর্ম ও শিশুপালনের ঝক্কি। এমন এক অবস্থা সৃষ্টির জন্য দায়ভাগ পুরুষশাসিত সমাজ ব্যবস্থায় যেমন পুরুষদের ওপর বর্তায়, তেমনই কিছুটা দায়ভাগ অবশ্যই নারীদের যাঁরা এই ধারাকে স্থায়ী রাখার মানসিকতা সন্তানদের মধ্যে তৈরি করে চলেছেন।
আমার এসব কথা অনেকের কাছেই নিন্দিত হবে জানি। এই ধরনের কথা বলার দরুন ইতিমধ্যেই কিছু কিছু কথা শুনতে হয়েছে। যেমন, “এমনতর মতের বিকাশ সমাজে স্বেচ্ছাচারিতাই বৃদ্ধি করবে। নারীমুক্তির নামে, স্ত্রী-পুরুষের সমানাধিকার অর্জনের নামে পশ্চিম দুনিয়ার নারীরা ষাটের দশকে যে অন্তর্বাস পোড়ানোর আন্দোলনে নেমে ছিলেন তার পিছনে যৌক্তিকতা রয়েছে বলে কি আপনি রায় দেবেন?” আমার এক পরিচিতা এ প্রশ্নও রেখেছিলেন, “আপনি যে সব যুক্তি মুখে দেন, কাজের বেলায় সে সব যুক্তিকে কি মেনে নিতে পারেন? আপনার স্ত্রী যদি অন্য কোনও পুরুষের সঙ্গে যৌন সম্পর্ক গড়ে তোলেন, আপনি কি পারবেন সেই সম্পর্ককে মেনে নিতে?” আর এক পরিচিতা একথাও বলেছিলেন, “আমি আপনার যুক্তিতেই বিশ্বাস করি। মনে করি, আমি স্বামীর কেনা দাসী নই। যার সঙ্গে ইচ্ছে যৌন সম্পর্ক গড়ে তুলব। জীবনকে উপভোগ করব। আমার এমন জীবন যাপন পদ্ধতিকে আপনি ঘৃণা করেন—আমি বুঝি। যদি ঘৃণাই করেন তো মুখে নারীমুক্তির কথা বলেন কেন? এ কি ভণ্ডামি নয়?”
খোলামনে এইসব নিন্দার যৌক্তিকতা নিয়ে চুলচেরা বিশ্লেষণে বসলে মন্দ হয় না। প্রতিবাদীরা আসলে ‘মুক্তি’, ‘স্বাধীনতা’ ইত্যাদি শব্দগুলোর প্রকৃত অর্থই ধরতে পারেননি। মূল্যবোধহীন, দর্শনহীন কোনও আন্দোলনই প্রকৃত অর্থে মানব প্রগতি, মুক্তি বা স্বাধীনতা আনতে পারে না। পৃথিবীতে সর্বকালে প্ৰগতিবাদী, মুক্তিকামী, স্বাধীনতাকামী, বিপ্লবীদের সংগ্রাম মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম । মূল্যবোধহীন, দর্শনহীন অনাদর্শ প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম প্রকৃত মুক্তিকামী ও স্বাধীনতাকামীদের চিন্তাকে ঘুলিয়ে দিতে পারে মাত্র—কিন্তু কোনও অর্থেই মূল্যবোধহীন আন্দোলন ‘মানব-মুক্তির’ বা ‘শ্রেণি মুক্তি’র সমার্থক শব্দ হয়ে উঠতে পারে না। যা হয়ে উঠতে পারে তা হল উচ্ছৃঙ্খলতা, মূল্যবোধের অবক্ষয় ।
নারী স্বাধীনতা বা নারী মুক্তির নামে ষাটের দশকে অন্তর্বাস পোড়ানোর যে আন্দোলন সূচিত হয়েছিল, তারই পরিণতি কানাডায় সম্প্রতি অনুষ্ঠিত হয়েছে নারীদের অভিনব বিক্ষোভ। সে দেশের আইনে পুরুষরা অনাবৃত বক্ষে প্রকাশ্য স্থানে চলাফেরা করতে পারে, নারীরা পারে না। নারীরা বক্ষ উন্মুক্ত রেখে ঘুরে বেড়ালে অশালীন আচরণের দায়ে পড়তে হয়। এই বৈষম্যের প্রতিবাদে কিছু নারী মিছিল করে পথে নেমেছিলেন বক্ষ অনাবৃত রেখেই। অর্থাৎ আইন অমান্য
পাশ্চাত্য নারীমুক্তির আন্দোলনে দেখতে পাই দর্শনের পরিবর্তে ইস্যু ভিত্তিক ধাঁচ। কখনও ওরা নারীমুক্তির দাবি ঘোষণা করেছে অন্তর্বাস পুড়িয়ে, কখনও বা প্রকাশ্যে বক্ষ উন্মুক্ত ও নগ্ন হয়ে ঘোরাঘুরি করার অধিকার প্রতিষ্ঠার মধ্যে নারীর মুক্তিকে আবিষ্কার করেছে। কখনও বা নারীকেই নারীর জীবন সঙ্গিনী হিসেবে বেছে নেওয়ার অধিকার প্রতিষ্ঠার মধ্যে স্বাধীনতার পূর্ণতা খুঁজে পেয়েছে। এই নারীমুক্তির নেত্রীরা যেসব দাবি আদায়ের মধ্য দিয়ে নারীমুক্তি আন্দোলন আনবেন বলে মনে করছেন, সেই দাবিগুলো প্রতিষ্ঠিত হলেও বাস্তবে এর দ্বারা নারী সমাজের মুক্তি কখনওই প্রতিষ্ঠিত হবে না, হতে পারে না। অনাবৃত বক্ষ বা শরীর নিয়ে ঘোরা যদি নারীমুক্তি ও নারী প্রগতির চূড়ান্ত নিদর্শন হিসেবে গণ্য হয়, তবে বলতেই হয় ভারতীয় নারীরা মুক্ত নারী—কারণ ভারতবর্ষের অধিকাংশ মানুষের লজ্জা নিবারণের জন্য প্রয়োজন মেটাবার মতো কাপড় কেনার সামর্থ্যই যেখানে নেই, সেখানে সংখ্যাগুরু নারীরা যে ব্লাউজ এবং তারও তলায় অন্তর্বাস পরবে না, এটাই স্বাভাবিক। তাদের এই অন্তর্বাস পরিধান না করা নারী প্রগতি এবং নারীমুক্তিরই সাক্ষ্য বহনকারী ভাবলে তা হবে অযৌক্তিক। ‘মুক্তি’, ‘প্রগতি’, ‘স্বাধীনতা’ শব্দগুলোর সঙ্গে ‘মূল্যবোধ’ ও ‘দর্শন’-এর সম্পর্ক জড়িয়ে রয়েছে। আর তাই মূল্যবোধহীন, দর্শনহীন, তথাকথিত নারীবাদী আন্দোলনকে উচ্ছৃঙ্খলতা ছাড়া আর কিছু নামে চিহ্নিত করা যায় না।
একই ভাবে কিছু পুরুষ যদি তাদের অধমাঙ্গ অনাবৃত রেখে প্রকাশ্যে চলাফেরা করার মধ্যে এবং নারীর মতো প্রসাধন করার মধ্যে তাদের মুক্তি ও স্বাধীনতা চরম পূর্ণতাকে অর্জন করল ভেবে উদ্বেল হয়ে ওঠে, তবে সেই পুরুষদের মানসিক সুস্থতা নিয়ে সন্দেহ জাগাটাই স্বাভাবিক। এই পুরুষদের বিকৃতকাম ও উচ্ছৃঙ্খল বলে চিহ্নিত করাটা মোটেই অযৌক্তিক বলে বিবেচিত হবে না— একই যুক্তিতে।
মূল্যবোধহীন, দর্শনহীন কোনও আন্দোলনই কখনও
কোনও শ্রেণিরই মুক্তি আনতে পারেনি, পারবেও না।
দাম্পত্য জীবনের আদর্শ সম্পর্ক গড়ে ওঠার প্রাথমিক শর্তই হল বন্ধুত্ব, বিশ্বাস, শ্রদ্ধা ও মতাদর্শগত মিল। যে দম্পতির জীবনে এইসব প্রাথমিক শর্তগুলো অনুপস্থিত সেখানে সম্পর্কের বোঝা টানা অর্থহীন, নীতিহীন এবং সুস্থ মানসিকতার পরিপন্থী। এ ক্ষেত্রে স্ত্রী বা স্বামীর জীবনে বন্ধু হিসেবে কোনও পুরুষ বা নারী যদি বসন্তের হাওয়া নিয়ে আসেন, তাকে স্বাগত জানানো মানসিকতার দিক থেকে একান্তই কাম্য। উভয়ের বন্ধুত্ব শ্রদ্ধা ও ভালোবাসার উত্তাপে বিকশিত হয়ে যদি শারীরিক মধুর সম্পর্ক স্থাপন করে, তাকে তো শ্রদ্ধা জানাবই, স্বাগত জানাবই। তার পরিবর্তে শ্রদ্ধাহীন, বন্ধুত্বহীন নারী পুরুষের সম্পর্ককে স্বাগত জানানো কি আদৌ সুযুক্তির পরিচয় হত? বন্ধুত্ব, বিশ্বাস ও শ্রদ্ধার মধ্য দিয়ে নারী পুরুষের মধ্যে যখন সুস্থ শারীরিক সম্পর্ক গড়ে ওঠে তখন তার চেয়ে সুন্দর তার চেয়ে শ্রেয় সম্পর্ক আর কিছু হয় না। যে সম্পর্ক মন্ত্রের জোরে শৃঙ্খলিত নয়, অন্তরের জোরে যুক্ত তাই শ্রেয়। আমার এই কথাগুলো যেহেতু আন্তরিক, তাই স্ত্রীর ক্ষেত্রে মত পরিবর্তনের কোনও প্রশ্নই আসে না।
আবার যেখানে নারী-পুরুষ শুধুমাত্র যৌন-উত্তেজনার আগুন পোহাতে নতুন নতুন অ্যাডভেঞ্চারে মেতে ওঠে, সেখানে এইসব মূল্যবোধহীন, ভোগসর্বস্ব, বিকৃতকামী নারী-পুরুষদের সুস্থ-সমাজ ও সুস্থ সংস্কৃতির শত্রু ছাড়া আর কিছুই মনে করার অবকাশ থাকে না। বন্ধুত্বহীন, মতাদর্শহীন, শ্রদ্ধাহীন কামতাড়িত নারী পুরুষদের যৌনাচার, যৌন-উচ্ছৃঙ্খলতা আরও বহু জনের মধ্যে ভোগসর্বস্ব সংস্কৃতির বীজ বপন করবেই, সমাজকে পচন ধরাবেই—এই পরিবেশগত প্রভাবের সত্যকে মাথায় রেখে প্রতিটি সুস্থ সমাজ-সচেতন মানুষের ঘৃণা নেমে আসা উচিত ওদের উপর ৷ শৃঙ্খলিত নারী-পুরুষদের মুক্তির জন্য নতুন মূল্যবোধ গড়ে তোলার প্রয়োজনে, নতুন সস্কৃতি গড়ে তোলার প্রয়োজনে নারী-পুরুষের দাম্পত্য সম্পর্ককে, যৌন সম্পর্ককে যুক্তির নিরিখে বিচার করতে হবে। এবং তার প্রয়োগ করতে হবে নিজেদের জীবনে। ফলে নারী-পুরুষের নতুন সম্পর্ক গড়ে উঠবে স্বত্বাধিকারের ভিত্তিতে নয়, বন্ধুত্বের ভিত্তিতে। নিজের জীবনে এই প্রয়োগের জন্য চাই নিষ্ঠা ও সাহস—তেজে উদ্দীপ্ত সাহস।
এ-জাতীয় চিন্তাধারা স্বেচ্ছাচারিতা বৃদ্ধিতে কতটা সহায়ক হবে, এই অভিযোগ বাস্তবিকই কতটা গ্রহণযোগ্য একটু দেখা যাক।
হিন্দুদের বহুগামী বিয়েতে অবশ্যই বহু নারীর উপর একটি পুরুষের যৌন স্বত্বাধিকার প্রতিষ্ঠিত, স্পষ্টতই যা স্বেচ্ছাচার। ইংরেজদের প্রভাবে এ যুগের হিন্দুরা একগামী বিয়ে করলেও নারীদের অর্থনৈতিক স্বাধীনতা না থাকার দরুন আজও এই বিয়ের মধ্য দিয়েও একটি পুরুষ একটি নারীর ওপর যৌন স্বত্বাধিকারই প্রতিষ্ঠিত করে, যা স্পষ্টতই স্বেচ্ছাচারিতা। যে ক্ষেত্রে নারী অর্থনৈতিকভাবে স্বনির্ভর সে ক্ষেত্রেও একগামী বিয়ে যৌন স্বত্বাধিকারের ওপরেই প্রতিষ্ঠিত—একজনের উপরে আর একজনের স্বত্বাধিকার। প্রেমহীন যৌন স্বত্বাধিকার সুবিধাবাদী লাম্পট্য ছাড়া কিছুই নয়, স্বেচ্ছাচারিতা ছাড়া কিছুই নয়।
মুসলমান সমাজে যেখানে বহুগামী বিয়ে প্রচলিত সেখানে বহু নারীর উপর এক পুরুষের যৌন স্বত্বাধিকার সন্দেহাতীতভাবে মর্মান্তিক স্বেচ্ছাচারিতা ! আদালতে স্বামীর বিরুদ্ধে জোর করে সহবাসের অর্থাৎ ধর্ষণের অভিযোগ এনেছেন, এমনটা বিলেতে ঘটলেও আমাদের দেশে দুর্লভ। নারীর ইচ্ছা-অনিচ্ছাকে সামান্যতম দাম না দিয়ে স্বামীরা তো অহরহই সহবাস করছেন, স্বত্বাধিকার প্রয়োগের মাধ্যমে মোদ্দা কথায় ধর্ষণই করছেন—এ কি স্বেচ্ছাচারিতার নিদর্শন নয়? না কি, বিয়ে করার সুবাদে, যৌন স্বত্বাধিকার লাভ করার ফলে স্ত্রীকে যখন-তখন ধর্ষণ করা যায়?
এই ধরনের স্বত্বাধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য বিয়ে কখনওই কাম্য হতে পারে না, এই স্বত্বাধিকার প্রতিষ্ঠা ব্যক্তিত্ব, আত্মমর্যাদা ও স্বতন্ত্র সত্তা খর্বকারী এবং সমাজের অগ্রগমন ব্যাহতকারী।
সহধর্মিণী, প্রেমিকা, সহযোদ্ধার চেয়েও নারীর বড়
পরিচয় হয়ে ওঠা উচিত সে আত্মমর্যাদাসম্পন্ন,
স্বাধীন, স্বতন্ত্র সত্তা-
এর মধ্যে কোথাও প্রেম ও দাম্পত্যের রক্ষণশীলতা নেই, ব্যক্তিত্বকে বেঁধে রাখার ফাঁদ পাতা নেই ।
ষাটের দশকের শেষ ও সত্তরের দশকের গোড়ায় রাজনীতি সচেতন বহু প্রেমিক-প্রেমিকা প্রাতিষ্ঠানিক বিবাহ পদ্ধতিকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করে নতুনভাবে তাঁদের দাম্পত্যজীবন শুরু করেছিলেন। নিজের নিজের পার্টি কমিটির কাছে তাঁরা জানাতেন বিয়ে করার সিদ্ধান্তের কথা। পার্টি কমিটির অনুমোদন পাওয়ার পর বিবাহ সভা ডাকা হত। এ সভায় শালগ্রাম শিলা সাক্ষ্য থাকত না, থাকত না কোনও ধর্মীয় মন্ত্র উচ্চারণ। হত না কোনও মালাবদল, শুভদৃষ্টি। নবদম্পতি পাঠ করতেন মাও সে তুং-এর কিছু উদ্ধৃতি। উপস্থিত সকলে গান ধরতেন—বিপ্লবী গণসংগীত। আনন্দের অঙ্গ হিসেবে খাওয়া-দাওয়াও হত। এইসব দাম্পত্যবন্ধনগুলো যে শেষ পর্যন্ত অটুট ছিল, এমন নয় । অনেক স্বামী-স্ত্রী এবং প্রেমিক-প্রেমিকা মতাদর্শগত পার্থক্য গড়ে উঠতেই শ্রদ্ধাহীন, বন্ধুত্বহীন, দাম্পত্যজীবন, প্রেমের সম্পর্ক ছিন্ন করে পরস্পরের থেকে দূরে সরে গেছে।
রাজনীতি সচেতন, আদর্শ সচেতন, মূল্যবোধ সচেতন, আত্মমর্যাদা, সচেতন, স্বাধীন মানসিকতাসম্পন্ন দম্পতিদের বিচ্ছেদ তুলনামূলকভাবে অসচেতন ও স্বল্প-সচেতন দম্পতিদের চেয়ে অনেক বেশি ঘটে। দু’জনেই যখন আদর্শ-সচেতন মূল্যবোধ-সচেতন, আত্মমর্যাদা সম্পন্ন, রাজনীতি ও সমাজনীতি সম্পর্কে সচেতন তখন আদর্শগত দ্বন্দ্ব দেখা দিতেই পারে— সেটা একপক্ষের আদর্শচ্যুতির জন্যেও যেমন হতে পারে, তেমনই আদর্শগত মতপার্থক্য থেকেও হতে পারে। এই দ্বন্দ্ব নিয়ে ‘প্রেমিক-প্রেমিকা’ অথবা ‘স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক অটুট রাখা অবাঞ্ছিত মনে হওয়াটা অস্বাভাবিক কী?
আমি যে পাড়ায় থাকি, সে পাড়ায় মধ্যবয়স্ক ও বয়স্কদের একটি তাসের আড্ডা আছে। সন্ধায় আড্ডায় প্রায় প্রত্যেকেই আসেন, তাস খেলেন, রাতে বাড়ি ফিরে যান। বদলি, স্থায়ী অসুস্থতা ও মৃত্যু ছাড়া আড্ডার কোনও সদস্য বিদায় নেননি আমার দেখা পনেরোটি বছরের মধ্যে। এই একই চিত্রের পুনরাবৃত্তি দেখতে পাবেন অন্যান্য পাড়ার তাস বা দাবার অড্ডার ক্ষেত্রে কিন্তু আমাদের যুক্তিবাদী সমিতির সভ্যদের ক্ষেত্রে এমন অবস্থা আমরা গত সাত বছরে আদৌ দেখিনি। যখনই কোনও সদস্য লোভ বা ভয়ের দ্বারা চালিত হয়ে সমিতির আদর্শ থেকে বিচ্যুত হয়েছেন, আমাদের সমিতির অন্যান্য সভ্য-সভ্যাদের সঙ্গে তাঁর তীব্র দ্বন্দ্ব দেখা দিয়েছে। পরিণতিতে বিচ্যুতকে অন্য সভ্যদের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করতে হয়েছে। আজ আমার প্রতি যে গভীর বিশ্বাস ও ভালোবাসা সমিতির সভ্য-সভ্যাদের আছে, আমি বিচ্যুত হলে সেই বিশ্বাস ও ভালোবাসায় ভাঙন ধরতে বাধ্য। তারও পরে সভ্য-সভ্যাদের সঙ্গে আমার অতীত সম্পর্ক অটুট থাকা যেমন অসম্ভব, তেমনই নীতিহীন। তাসের আড্ডার সভ্য এবং আমাদের সমিতির সভ্যদের মধ্যে আদর্শগত সচেতনার পার্থক্যের দরুনই দ্বন্দ্ব দেখা না দেওয়ার এবং দেখা দেওয়ার পার্থক্য আমরা লক্ষ করি। তাস, দাবার আড্ডায় কোনও মতাদর্শগত সংগ্রাম নেই বলেই দ্বন্দ্বেরও সম্ভাবনা নেই। আর আমাদের সমিতির ক্ষেত্রে তীব্রভাবে মতাদর্শগত সংগ্ৰাম আছে বলেই দ্বন্দ্বও তীব্রতর হয়ে ওঠে। এই একই ব্যাপার ঘটে প্রেমিক-প্ৰেমিকা ও স্বামী-স্ত্রীর ক্ষেত্রে।
আদর্শ সচেতন নর-নারীদের সম্পর্কের ক্ষেত্রে দ্বন্দ্ব দেখা দেবার
সম্ভাবনা যেমন অচেতনদের তুলনায় বেশি, তেমনই আদর্শগত
মত-পার্থক্যের পর তাঁরা জোর করে একটা দাম্পত্য-
সম্পর্ক বজায় রাখবেন—এটাও প্রত্যাশিত
নয়, শ্রদ্ধা আকর্ষণ করার মতো নয়।
পাশাপাশি সাধারণ গৃহবধূ নানা ঝড়-ঝাপটা এবং অত্যাচার সহ্য করেও দাম্পত্য সম্পর্ক অটুট রাখতে সচেষ্ট থাকেন, স্বামীর প্রতি অর্থনৈতিক নির্ভরশীলতা এবং আদর্শগত সচেতনতার অভাবের দরুন।
স্ত্রী ও পুরুষের মধ্যে নানা ধরনের বন্ধুত্ব গড়ে উঠতে পারে। অনেক সময় মতাদর্শগত মিল থেকে, উভয়ের প্রতি উভয়ের শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস থেকে গড়ে উঠতে পারে মধুর বন্ধুত্বের সম্পর্ক— যেখানে দেহ-মিলন বন্ধুত্বকে আরও সমৃদ্ধতর, দৃঢ়বদ্ধ করতেই পারে। এ মিলন স্বত্বাধিকার দ্বারা প্রতিষ্ঠিত নয়, নারী ও পুরুষের পারস্পরিক শ্রদ্ধা, বিশ্বাস, ও বন্ধুত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত । এমন মিলনই তো সংস্কারমুক্ত মানসিকতার লক্ষণ, সুস্থতার লক্ষণ।
প্রাতিষ্ঠানিক বিয়ের মধ্য দিয়ে যেহেতু যৌন স্বত্বাধিকার প্রতিষ্ঠিত এবং এই প্রচলিত সংস্কার আমদের অস্থি মজ্জায় মিশে গেছে, তাই আমরা মেনে নিই—বিয়ে করার সঙ্গে সঙ্গে একটি নারী ও একটি পুরুষের যথাক্রমে অন্য পুরুষ ও অন্য নারীকে ভালোবাসার অধিকার বাজেয়াপ্ত হয়ে যায়। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে সম্পর্ক গভীর বন্ধুত্ব বর্জিত হয়ে প্রধানত যৌন স্বত্বাধিকার দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হলেও জীবনের প্রায় বাকি অর্ধেকটা সময় সেই ভালোবাসাহীন দাম্পত্য সম্পর্ককেই বোঝার মতো বয়ে বেড়ানোটাই আমাদের সমাজের ‘ট্র্যাজিক ট্র্যাডিশন’ হয়ে দাঁড়িয়েছে—জীবনের এই শ্রেষ্ঠ অর্ধেকটা সময়ে ভালোবাসার মতো মানুষের সংস্পর্শে এলেও, মতাদর্শগতভাবে গভীর বন্ধুত্ব গড়ে ওঠার সম্ভাবনা থাকলেও সেই সমস্ত সুন্দর ইচ্ছেগুলোকে দিয়ে চিতা সাজিয়ে ‘দাম্পত্য পবিত্রতা’ রক্ষা করার মধ্যে খুঁজে পাওয়া যায় সংস্কারাচ্ছন্ন অনগ্রসর মানসিকতারই পরিচয়। নারী-পুরুষের প্রেম-সুন্দর সম্পর্ক গড়ে তোলার ক্ষেত্রে ভূমিকা নেয় মানসিক মিল, মতাদর্শের মিল; শাঁখা, সিঁদুর বা মন্ত্রোচ্চারণ নয়। গতানুগতিক যুগল সম্পর্কের ছক ভেঙেই আমাদের খোঁজ করতে হবে নির্ভুল আত্মপরিচয়ের, স্বয়ংসম্পূর্ণ স্বাধীন অস্তিত্ব প্রতিষ্ঠার।
পুরুষশাসিত আমাদের এই সমাজে পুরুষেরা তাদের স্বার্থে যে নীতিবোধ ও মূল্যবোধ চাপিয়ে দিয়েছে, তাতে আদর্শ নারীর গুণ হিসেবে ঘোষিত হয়ে আসছে পতি-সেবা, সন্তান-পালন, পতির পরিবারের সেবা ইত্যাদি । পতি-দেবতার শত লাঞ্ছনা ও অত্যাচার সহ্য করে টিকে থাকা নারীকে সমাজ চিহ্নিত করেছে মহান পতিব্রতা রমণী হিসেবে। পতির চিতায় জীবন্ত দগ্ধ হওয়া নারীকে পূজ্যপদ দেওয়া হয়েছে সতী হিসেবে। যদি বলি এ-সবই পুরুষ দ্বারা নারী শোষণের অপচেষ্টা বই কিছুই নয়, তবে অন্যায় বলা হবে কি? তবে এ-ক্ষেত্রে নারীরা সাধারণভাবে কিছুটা ‘দাস-নারী’র মতোই অবস্থান মেনে নিয়ে চলেন। এ-ক্ষেত্রে আমি ‘শোষণ’ শব্দটিকে ব্যবহার করলেও এই শব্দটির প্রতি পাঠক-পাঠিকাদের একটু সতর্ক নজর রাখতে অনুরোধ করছি। না হলে একটু গোলমাল বাধার সম্ভাবনা রয়ে যাচ্ছে। কারণ সামাজিক শোষণ বলতে আমরা সাধারণত যা বুঝি এ বইতেও সেই অর্থে শব্দটি একাধিকবার ব্যবহৃত হয়েছে ইতিমধ্যে,–অর্থাৎ যার সঙ্গে উৎপাদন ব্যবস্থার সরাসরি যোগাযোগ আছে, এ ‘শোষণ’ কিন্তু তা নয়, বরং এ-ভাবে বলা যেতে পারে, একটা নির্দিষ্ট সামাজিক কাঠামোকে টিকিয়ে রাখার স্বার্থেই সমাজের মাথারা নারী-পুরুষদের বর্তমান অবস্থানকে ধরে রাখতে নারী-পুরুষ সম্পর্কের এই মূল্যবোধকে চাপিয়ে দিয়েছে। সমাজের মাথারা যেহেতু পুরুষ তাই প্রচলিত মূল্যবোধের ক্ষেত্রে পুরুষরা সাধারণভাবে কিছুটা সুবিধাজনক জায়গায় আছে । ‘পুরুষদের দ্বারা নারী শোষণ’ বলতে এই অবস্থানগত সুবিধার ফলকেই বোঝাতে চাইছি। এটা মাথায় না রাখলে ‘শোষণ’ শব্দের যথেচ্ছ ব্যবহারে কেবল বিভ্রান্তিই বাড়বে। সে-ক্ষেত্রের ব্যাপারটা অনেকটাই ফেমিনিস্টদের অর্থাৎ তথাকথিত নারীমুক্তির সমর্থকদের অনর্থক হট্টগোলের মতোই শোনাবে।
এ-সব বলার অর্থ এই নয়, আমি পুরুষদের সুবিধাজনক অবস্থার সমর্থক বা ব্যাপারটাকে মেনে নেওয়ার পক্ষপাতী। এমনকী এও বলি না—আমূল অর্থনৈতিক সংস্কার হওয়ার আগে পর্যন্ত এ ব্যাপারে চুপচাপ থাকতে হবে। সন্দেহ নেই, এ-সবই মানবিকতার প্রতি চূড়ান্ত অপমান। এবং আমি সমস্যার মূলকে স্পষ্টভাবে চিনে নিতে চাইছি। ‘মাতৃত্বে নারীত্বের চরম সার্থকতা’— এমন লাগাতার প্রচার চালিয়ে নারীকে শুধু সন্তান উৎপাদনকারী এবং যৌন উত্তেজনা-ভোগকারী যন্ত্র হিসেবে কাজে লাগাতে চেয়েছে পুরুষশাসিত এই সমাজ। সমাজ আরোপিত এই নীতিবোধ ও মূল্যবোধ কখনওই যুক্তিসংগত বলে মেনে নেওয়া যায় না। নারীর উপর পুরুষের শাসন ও স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার বিরুদ্ধে কিছু নারী-পুরুষ যে প্রতিবাদ ও চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিয়েছেন, তাকে কারো
কারো দৃষ্টিতে মূল্যবোধের অবক্ষয় বলে মনে হতেই পারে। সব দেশেই সমাজের অগ্রসর অংশরা যে মূল্যবোধে বিশ্বাস করেন, সেই মূল্যবোধকে অনেক সময়ই অনগ্রসরদের পুরোনো দৃষ্টিতে অবক্ষয় মনে হয়। আমরা ইতিহাস থেকে শিক্ষা নিয়েছি—অগ্রবর্তী অংশের মূল্যবোধ দ্বারা প্রভাবিত হয়ে সমাজের মূল্যবোধও পাল্টায়। পরিবর্তনের হাওয়া লাগুক নারী-পুরুষদের প্রণয় সম্পর্ক, দাম্পত্য সম্পর্ক গড়ে ওঠার ক্ষেত্রে। যুগল নারী-পুরুষের মধুর সম্পর্ক গড়ে উঠুক গভীর বন্ধুত্বের মধ্য দিয়ে। ভেঙে যাক যৌন স্বত্বাধিকারের উপর গড়ে ওঠা, বস্তু সামগ্রী বিবেচনায় গড়ে ওঠা, মূল্যবোধহীন শারীরিক সম্পর্কের ওপর গড়ে ওঠা যুগল সম্পর্ক। নতুন সমাজ গড়ার স্বপ্নকে সার্থক করার প্রয়োজনেই গড়ে ওঠা যুগল সম্পর্ক। নতুন সমাজ গড়ার স্বপ্নকে সার্থক করার প্রয়োজনেই গড়ে উঠুক যুক্তির দ্বারা প্রতিষ্ঠিত নারী-পুরুষের সুন্দর সম্পর্ক নিয়ে নতুন মননশীল মূল্যবোধ।
প্রসঙ্গ জনসেবাঃ ভালোবাসার মধ্যে নিবিড় অন্ধকার
গত কয়েক বছরে যুক্তিবাদী আন্দোলন সাধারণ মানুষের ব্যাপক থেকে ব্যাপকতর অংশে দ্রুত ছড়িয়ে পড়তে শুরু করেছে। সাধারণ মানুষকে কুযুক্তির গারদ ভেঙে স্বচ্ছ চিন্তার জগতে নিয়ে আসতে যুক্তিবাদী আন্দোলনের আগুন ছড়িয়ে দেওয়ার কাজে এগিয়ে এসেছে বহু বিজ্ঞান ক্লাব, স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা, নাট্যগোষ্ঠী, লিটল ম্যাগাজিন প্রমুখ গণসংগঠন। কাজ-কর্মে এরা অনেকেই খুবই আসন্তরিক। কুসংস্কার মুক্তির কাজের সঙ্গে সঙ্গে এদের অনেকেই আরও নানা ধরনের সমাজ কল্যাণমূলক, সমাজসংস্কারমূলক কাজের সঙ্গে যুক্ত। সাক্ষরতা অভিযান, রক্তদান, চক্ষুদান, মরণোত্তর দেহদান, কৃষিজমি পরীক্ষা, হাসপাতালে সাপেকাটা রোগীর চিকিৎসার সুব্যবস্থার দাবি তোলা, জল বাঁচাও, বৃক্ষরোপণে, বিনামূল্যে চিকিৎসাকেন্দ্র, ফ্রি কোচিং সেন্টার, ফ্রি রিডিংরুম এমনি আরও বহুতর সেবামূলক কাজের মধ্য দিয়ে অনেক মানুষের ভালোবাসা ও শুভেচ্ছাও এইসব সংস্থার পাথেয় হয়েছে। ফলে এরা সার্থক গণসংগঠন হয়ে উঠেছে।
জনকল্যাণমূলক কাজের মধ্য দিয়ে জনচিত্ত জয় করার পদ্ধতিটি আরও সফলভাবে কাজে লাগিয়েছেন বিভিন্ন ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান। মাদার টেরিজা, রামকৃষ্ণ মিশন, ভারত সেবাশ্রম সংঘ, মোআমার-অল-আলক-আল-ইসলামি প্রমুখ বহু ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান নানা ধরনের জনকল্যাণমূলক কাজের সঙ্গে নিজেদের জড়িত রেখেছে। হাসপাতাল, অনাথ আশ্রম, বন্যায় বা সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় ক্ষতিগ্রস্তদের সেবা, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ধর্মশালা এমনি নানা ধরনের জনকল্যাণমূলক কাজকর্মের প্রলেপে সাধারণের মন জয় করে তাদের আবেগ সিক্ত, কৃতার্থ হৃদয়ে রহস্যবাদ, দুর্জেয়বাদ, ধর্মীয় কুসংস্কার, অদৃষ্টবাদ, কর্মফল ও রকমারি ভাববাদী চিন্তাও ঢুকিয়ে দিচ্ছে। আবেগ সিক্ত, ঋণী, কৃতার্থ মগজ তাৎক্ষণিক লাভ-ক্ষতির অঙ্ক কষে এদের নিপীড়িত মানুষদের বন্ধু হিসেবেই ধরে নিচ্ছে। নিপীড়িত, শোষিত মানুষগুলো এইসব প্রতিষ্ঠানকর্মীদের সেবার সঙ্গে সঙ্গে গ্রহণ করছেন এইসব ভালো-লাগা মানুষগুলোর চিন্তাও।
ভাববাদী শিবিরের এই ধরনের মগজ ধোলাই কৌশল থেকে শিক্ষা নিয়ে যুক্তিবাদী আন্দোলনের কর্মীদেরও প্রয়োজনে জনচিত্ত জয়ের জন্য নানা জনকল্যাণমূলক কাজের সঙ্গে জড়িত হতে হবে পাল্টা মগজ ধোলাই করতে। যাঁরা যুক্তিবাদী আন্দোলনকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার মধ্যেই সাধারণ মানুষের চেতনা মুক্তি এবং সেই পথ ধরে সার্বিক শোষণ মুক্তির স্বপ্ন দেখছেন তাদের কিন্তু একটা বিষয়ে সচেতন থাকতে হবে—উপলক্ষ যেন লক্ষ্যকে ছাড়িয়ে না যায়। কুসংস্কার মুক্তির লক্ষ্যে পৌঁছতে জনকল্যাণমূলক কাজকর্ম যে শুধুমাত্র উপলক্ষ্যই হতে পারে, এই বিষয়ে অতি সচেতনতার প্রয়োজন । স্পষ্টতই মনে রাখতে হবে পরম সত্যটি-
সেবায় আর যাই করা যাক, সমাজব্যবস্থা পাল্টানো যায় না,
শোষণমুক্তি ঘটতে পারে না। শোষণমুক্তি ঘটতে
পারে শুধুমাত্র সাধারণ মানুষের
সমাজসচেতনতা বোধ থেকে।
সাধারণ মানুষের বৃহত্তর অংশ যেদিন বুঝতে শিখবে তাদের বঞ্চনার কারণ অদৃষ্ট নির্ধারিত নয়, পূর্বজন্মের কর্মফল নয়, ঈশ্বরজাতীয় কোনও কিছুর অভিশাপ নয়, বঞ্চনার কারণ শোষকশ্রেণি, সে-দিন তাদের নিজেদের স্বার্থেই, বাঁচার তাগিদেই বঞ্চনামুক্তির জন্য পাথর না পরে, পুজো না দিয়ে আঘাত হানবে শোষকশ্রেণির দুর্গে।
কিন্তু এই আঘাত হানার প্রসঙ্গ তখনই আসবে যখন শোষিতশ্রেণির ঘুম ভাঙবে, তারা বঞ্চনার কারণগুলো বুঝতে পারবে। গরিবদের ক্ষোভকে ভুলিয়ে রাখার জন্যই ধনীর অর্থে চলছে ‘দরিদ্র নারায়ণ সেবা’। দরিদ্র- নারায়ণের সেবা যাদের চিরন্তন লক্ষ্য, তাদের সেবা বিলোবার জন্য দরিদ্র-নারায়ণের সরবরাহও যে চিরন্তন হওয়া প্রয়োজন— এই সত্যটুকু আমাদের ভুললে চলবে না। এই সেবামূলক তাৎক্ষণিক লাভ গরিবদের হলেও ভবিষ্যতের জন্য পড়ে রইল অনন্ত বঞ্চনাময় জীবন।
জনসেবামূলক কাজের সঙ্গে শোষণমুক্তির সংগ্রামের সম্পর্কটা বুঝতে হবে। বুঝতে হবে, যুক্তিবাদী আন্দোলনের, শোষণমুক্তির সংগ্রামের সম্পর্কটা। যাঁরা বুঝতে চাইবেন না, বুঝতে পারবেন না, তাঁরা যুক্তিবাদী আন্দোলনকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারবেন না। কিছুতেই পারা সম্ভব নয়। এইভাবে যুক্তিবাদী আন্দোলনকে সাধারণ মানুষের ব্যাপক থেকে ব্যাপকতর অংশে নিশ্চয়ই ছড়িয়ে যেতে দেবে না রাষ্ট্রশক্তি। কারণ রাষ্ট্রশক্তি সাধারণ মানুষের চেতনাকে ততদূর পর্যন্তই এগিয়ে নিয়ে যেতে দেবে, যতদূর পর্যন্ত এগোলে তাদের কোনও বিপদের সম্ভাবনা নেই। যখনই বিপদের গন্ধ পাবে, তখনই নানাভাবে প্রতিরোধ করার চেষ্টা করবে। কখনও সংস্থাকে আর্থিক সাহায্যে মুড়িয়ে দিয়ে লেজুড় করতে চাইবে, কখনও সংস্থা দখল করতে চাইবে নিজের পেটোয়া দালালদের নিয়ে। কখনও ব্যক্তিগতভাবে নেতাদের পাইয়ে-দেওয়ার রাজনৈতিক চালেই কিনে নিয়ে সংস্থাকে পকেটে পুরতে চাইবে, কখনও সংস্থাকে জনসাধারণ থেকে বিচ্ছিন্ন করতে লাগাতারভাবে প্রচেষ্টা চালিয়ে যাবে। কখনও সংস্থার সুনাম জনমানসে মলিন করতে সংস্থা-প্রধানের চরিত্রহননের চেষ্টা করা হবে, কখনও বা সংস্থাগুলোকে উৎসাহিত করা হবে সমাজসংস্কারমূলক, জনসেবামূলক কাজকর্মের সঙ্গে জড়িত হওয়ার জন্য। শেষ পদ্ধতিটি আপাত নিরীহ হলেও মগজ ধোলাইয়ের জন্য শাসকশ্রেণির পক্ষে খুবই কার্যকর অস্ত্র। সেবামূলক বা সমাজসংস্কারমূলক কাজকর্ম যেমন বৃক্ষরোপণ, পরিবেশ দূষণ, রক্তদান, মরণোত্তর দেহদান, চক্ষুদান, সাক্ষরতা অভিযান ইত্যাদির পক্ষে দীর্ঘমেয়াদি ব্যাপক প্রচার চালান। যে সব ব্যক্তি ও সংস্থা এ-সব কাজে এগিয়ে আসে বার বার তাদের মুখ ভেসে ওঠে দূরদর্শনে, গলা ভেসে ওঠে বেতারে। এগিয়ে আনা হয় আরও সব প্রচারমাধ্যমকে !
মন্ত্রীরা বার বার হাজির হতে থাকেন এইসব সংস্থার অনুষ্ঠানগুলোতে । মন্ত্রীর সাহচর্য, বেতার দূরদর্শনে প্রচার, সব মিলিয়ে একটা ক্রেজ। একটু একটু করে আরো বেশি বেশি সংস্থা সবাজসেবা, সমাজসংস্কারের কাজে এগিয়ে আসতে থাকেন। অনেকেই আরও বেশি বেশি করে অনুভব করতে থাকেন এই ধরনের কাজকর্মে এগিয়ে আসার প্রয়োজনীয়তা।
এই কথাটাও স্পষ্ট করে বলি—সমাজসেবা নিশ্চয়ই ভালো, কিন্তু সমাজসেবার মধ্য দিয়ে ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলো যেভাবে সাধারণ মানুষের চিন্তায় চেতনায় রহস্যবাদ, অদৃষ্টবাদ, কর্মফল, জন্মান্তরবাদ, ধর্মীয় কুসংস্কার ইত্যাদি ঢুকিয়ে দিচ্ছে, তাকে রুখতে আমরাও কি পারছি, সমাজসেবার মধ্য দিয়ে সাধারণ মানুষের চেতনায় স্বচ্ছতা আনতে? যদি পারি, তবে আমাদের সার্থকতা, নতুবা আমরা সমাজসেবার আবর্তে শাসক ও শোষকশ্রেণির সুতোর টানে পুতুলনাচই নেচে যাব।
পরিবেশ আন্দোলনঃ মানুষ থাক বা না থাক বাঁচাও সোঁদরবনের বাঘ
একটি মিথ্যেকে বার বার সাজিয়ে গুছিয়ে প্রচার করতে করতে এমন একটা অবস্থার সৃষ্টি করা যায়, যার ফলে মিথ্যেটাই মানুষের বিশ্বাসে সত্যি হিসেবে জ্বল জ্বল করে। এই সত্যটাকেই মাথায় রেখে তাবৎ রাজনীতিকরা পরিবেশ দূষণ নিয়ে প্রচারে নেমেছেন। কত টাকা উড়ছে সেমিনারে, ওয়ার্কশপে, গাছ বিলি করতে, গাছ পুঁততে, কত লক্ষ মিটার দুর্মূল্য ফিল্ম, কত টন নিউজপ্রিন্ট খরচ হয়েছে তার হিসেব রাখা ভার। কিন্তু প্রতিনিয়ত প্রচারে ফল পাওয়া গেছে দারুণ। এখন পরিবেশ বলতে তামাম দেশবাসীর মাথায় শুধু ভেসে ওঠে প্রাকৃতিক পরিবেশের ছবি। কিন্তু পরিবেশ বলতে কি শুধুই প্রাকৃতিক পরিবেশ? মানুষের ওপর শুধুই কি প্রাকৃতিক পরিবেশই প্রভাব ফেলে?
যারা পরিবেশ বলতে শুধুই প্রাকৃতিক পরিবেশের কথা সাধারণ মানুষের মাথায় ঢোকাতে চাইছে, তারা ভালোমতোই জানে ‘আর্থ-সামাজিক’ ও ‘সমাজ-সাংস্কৃতিক’ নামের দুটি বিশাল প্রভাবশালী পরিবেশের কথা, মানবজীবনে যাদের প্রভাব বহু ক্ষেত্রেই প্রাকৃতিক পরিবেশের চেয়ে অনেক বেশি শক্তিশালী। সমাজ-সাংস্কৃতিক পরিবেশের বিপুল প্রভাবের সাম্প্রতিকতম উদাহরণ রাশিয়া সমেত পূর্ব ইউরোপের দেশগুলো থেকে মার্কসবাদের বিদায়। ওইসব মার্কসবাদী দেশে দীর্ঘ দিন ধরে নানা ভাবে পাচার করা হয়েছে মার্কিন-সংস্কৃতি, উত্তেজক মার্কিন সংস্কৃতি, ভোগসর্বস্ব মার্কিন সংস্কৃতি। মার্কসবাদী দেশগুলোর সমাজ-সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে ভেসে আসা উদ্দাম মার্কিন সংস্কৃতি মানুষগুলোকে মানসিকভাবে নেশাগ্রস্ত করেছে, ক্ষুধার্ত করেছে। আর তাইতেই একের পর এক ধস নেমেছে।
‘সুসংস্কৃতি’ মানুষকে এগিয়ে নিয়ে যেতে সাহায্য করে। ‘সুসংস্কৃতি’ প্রগতির ধারক। মানবতাবাদী জীবনবোধের উপাদানই হল সুসংস্কৃতি। যে ‘সংস্কৃতি’ এইসব ধারার বিপরীতগামী তা ‘অপসংস্কৃতি’। ভারতবর্ষের সাহিত্যে, চলচ্চিত্রে, দূরদর্শনে, যাত্রায়, নাটকে সর্বত্র এক অসংস্কৃতির ঢল নেমেছে। কারণ এইসব সৃষ্টির পিছনে মানুষকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার কোনও প্ৰয়াস নেই। বরং রয়েছে ভোগসর্বস্ববাদ, অবাধ যৌনতা, হত্যা-হানাহানি-ধর্ষণ, দুজ্ঞেয়বাদ, অদৃষ্টবাদ, ঠাকুর দেবতার রমরমা, ধর্মীয় সংস্কার সৃষ্টি ইত্যাদির মধ্য দিয়ে মানুষকে ব্যক্তিকেন্দ্রিক করে তুলে বৃহত্তর শোষিত জনসমষ্টিকে পিছিয়ে রাখার প্রয়াস।
কোনও কোনও সমাজ সচেতন গোষ্ঠী কোনও কোনও জায়গায় শোষিত মানুষদের যখন বোঝাচ্ছে তাদরে বঞ্চনার কারণগুলো আকাশের গ্রহ-নক্ষত্ৰ বা স্বর্গের দেবতা নয়, বঞ্চনার কারণ এই সমাজব্যবস্থা, যখন এই অপসাংস্কৃতিক পরিবেশের প্রভাব মুক্ত করতে সুস্থ সাংস্কৃতিক পরিবেশ গড়ে তুলতে চাইছে তখন বাংলাভাষার জনপ্রিয়তম সাহিত্য পত্রিকায় দুই ঔপন্যাসিকের কলম ঝলসে উঠল ওইসব সমাজ-সচেতন যুক্তিবাদী গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে। কলমচিরা জ্যোতিষশাস্ত্রের পক্ষে, অলৌকিক ক্ষমতাবানদের পক্ষে সোচ্চার হলেন ।
যাঁরা সমাজ-সাংস্কৃতিক পরিবেশকে ধর্তব্যের মধ্যে আনতেই
নারাজ, তাঁরা কী বলবেন? দেশ জুড়ে এই যে ধর্ম নিয়ে
উন্মাদনা, হানাহানি এ-সব কোন্ পরিবেশের ফল?
ধর্ম নিয়ে এমন উন্মত্ততা তো একদিন গাছের পাকা ফলটির মতো টুপ করে এসে পড়েনি। সাম্প্রদায়িক দল বলে আজ যাদের গাল পাড়ছে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল, সেই সাম্প্রদায়িক দলটি তো হঠাৎ করে উজ্জীবিত হয়ে ওঠেনি। ভারতবর্ষের মাটিতে ধর্মের চাষ, ধর্মের ফসল উৎপাদন ও ধর্মব্যবসা দীর্ঘদিন ধরেই চলছিল। সাম্প্রতিক কয়েক বছরে বারোয়ারি দুর্গাপুজো, কালীপুজো, জগদ্ধাত্রীপুজোর রমরমা বেড়েছে। অনেক মার্কসবাদীই দলের নির্দেশে পুজো কমিটিতে ঢুকে জনসাধারণের মধ্যে কাজ করতে নেমে পড়েছেন। এই নতুন শক্তির আগমনে পুজোর বাজেট বেড়েছে চড়চড় করে । ফুটপাত আর সরকারি জমির দখল নিয়ে রাজনৈতিক মদতপুষ্ট মস্তানেরা শনি-শীতলার দোকান খুলেছে। রাজনীতিকরা পুজো উদ্বোধন, জ্যোতিষ – মহাসম্মেলন উদ্বোধনে হাজির থেকে পোঁতা বিষবৃক্ষের বীজে সার ঢেলেছেন, জলসিঞ্চন করেছেন। বাবা ‘তারকনাথ’, ‘সন্তোষী মা’ ছবির কৃপায় পাড়ায় পাড়ায় যুবক-যুবতীদের উদাত্ত অংশগ্রহণে মাইক, আলো, দেবদারুপাতা ও বাঁক-শোভিত চত্বরের সংখ্যা বেড়েছে। বাঁক কাঁধে শ্লীল-অশ্লীল স্লোগান দিতে দিতে যুবক-যুবতীরা ছুটে চলে তারকেশ্বরে। ‘জয় সন্তোষী মা’ ছবির কৃপায় মা সন্তোষীর জাঁক-জমক বাড়ে। দূরদর্শনে ‘রামায়ণ’ ‘মহাভারত’ দেশবাসীকে ভাবাবেগ ও ভক্তিরসের তীব্র নেশায় বুঁদ করে রাখে। ‘সতী মন্দির’ রাজস্থানের ব্যাপার, পশ্চিমবাংলার মাটিতে বসবাসকারী রাজস্থানী ভোটারের সংখ্যা এতই নগণ্য যে তারা নির্বাচনকে প্রভাবিত করতে পারবে না। এই অঙ্ক মাথায় রেখে ভোটারদের কাছে প্রগতিশীল ইমেজ তৈরি করতে তাবড় রাজনীতিকরা ঘোষণা করেন, মৃতকে নিয়ে স্মৃতি-সৌধ হতে পারে, কিন্তু মৃতকে পুজো? এ তো কুসংস্কার। এই কুসংস্কারের আবর্জনা আমরা পশ্চিমবাংলায় জমতে দেব না। এই রাজনীতিকরাই আবার রামকৃষ্ণ, রামঠাকুর, অনুকূলচন্দ্র, লোকনাথের পুজো নিয়ে নীরব থেকে ধর্মশিকারিদের পরোক্ষ মদত দিয়েছেন। এইসব মৃত ধর্মীয়নেতাদের ভক্ত-সংখ্যা বিশাল এবং তাদের ভোটাধিকার আছে বলেই কি এইসব রাজনীতিকদের প্রগতিশীল বুলির ফানুস চুপসে যায় ?
‘আত্মা অবিনশ্বর’ এই যুক্তিহীন বিশ্বাস যতদিন মানুষের মনে থাকবে ততদিন সতী-মন্দির সহ নানা মৃত বাবাজি মাতাজিদের মন্দিরও থাকবে তাঁদের আশীর্বাদ লাভের আশায়। বিভিন্ন ধর্ম-বিশ্বাসে বলা হয়েছে ‘আত্মা’ মানে ‘চিন্তা’, ‘চেতনা’, ‘চৈতন্য’ বা ‘মন’। শারীরবিজ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে আমরা এও জেনেছি ‘চিন্তা’, ‘চৈতন্য’, ‘চেতনা’ বা ‘মন’ হল মস্তিষ্ক স্নায়ুকোষের কাজকর্মের ফল। মানুষ মারা গেলে তার মস্তিষ্ক স্নায়ুকোষগুলোও মারা যায়। তারপর এক সময় মস্তিষ্ক স্নায়ুকোষগুলোর অস্তিত্বই বিলীন হয়ে যায় সমাধির মাটির তলায়, আগুনে পুড়ে, পচে অথবা কোনও প্রাণীর পাকযন্ত্রে হজম হয়ে। মস্তিষ্ক স্নায়ুকোষগুলোর অস্তিত্বই যখন থাকে না তখন সেই অস্তিত্বহীন স্নায়ুকোষের কাজকর্মের ফল হিসেবে ‘চিন্তা’, ‘চেতনা’, ‘চৈতন্য’ বা ‘মন’-এর অস্তিত্বও যে আর থাকতে পারে না, এই সাধারণ যুক্তির কথাটুকু বুদ্ধিজীবী রাজনীতিকদের অজানা থাকার কথা নয়। ধরে নিলাম শিক্ষার সুযোগ না পাওয়া, অশিক্ষিত সমাজবিরোধী মাফিয়া নেতা এবং কুসংস্কারাচ্ছন্ন কিছু শক্তিমান রাজনীতিক আছেন যাঁরা শক্তিপ্রয়োগের বিষয় যতটা বোঝেন, ‘চিন্তা’, ‘চেতনা’, ‘মন’ ইত্যাদির কথা ততটাই বোঝেন না। কিন্তু এর বাইরে যে সংখ্যাগুরু বুদ্ধিমান, শিক্ষিত ধুরন্ধর রাজনীতিবিদরা রয়েছেন তাঁদেরকেও মাথা-মোটা ভাবলে ভুলই করা হবে। সবগুলো মাথা-মোটার পেছনে অর্থ ব্যয় করে তাদের নির্বাচনে জিতিয়ে আনলেই বা লাভ কী? ওইসব মোটা-মোটারা দেশের দরিদ্র শোষিত মানুষদের মগজ ধোলাই করে বঞ্চনার থেকে উঠে আসার সম্ভাবনাময় প্রতিবাদের কণ্ঠকে রোধ করতে পারবে? পারবে না। তাহলে তো রাতারাতি শোষকশ্রেণির গণেশ উল্টোবে। ধুরন্ধর এইসব ধনীর দালাল রাজনীতিকরা ‘চিন্তা’, ‘চেতনা’, ‘মন’, ‘আত্মা’, ‘অদৃষ্টবাদ’ কর্মফল ইত্যাদি খুব ভালোমতই বোঝেন। বোঝেন বলেই জানেন, দরিদ্র মানুষগুলোর চেতনা কতদূর পর্যন্ত এগোতে দেওয়া নিরাপদ। ওইসব রাজনীতিক ও তাদের দলের বুদ্ধিজীবীরা ভালোমতোই জানেন ‘আত্মা অবিনশ্বর’ এই ভ্রান্ত চিন্তা মানুষের মাথায় বদ্ধমূল করতে পারলে সেই সূত্র ধরেই গরিবদের মাথায় ঢোকানো যায়, ‘এই জন্মে এই যে এত কষ্ট পাচ্ছি, এসব গত জন্মের কোনও পাপের ফল, এজন্মে দেব-দ্বিজে ভক্তি রেখে, রাজপদে (বর্তমানে রাজনীতিকদের পায়ে) ভক্তি রেখে, কোনও হিংসার আশ্রয় না নিয়ে ঈশ্বরের দেওয়া এই জীবনের দুঃখগুলোকে মেনে নিয়ে সুশীল হয়ে চললে আগামী জন্মে ভাল ফল পাব।’
শিল্পপতিদের মালিকানাধীন বিশাল বিশাল ঝাঁ-চক্চক্ কাগজগুলোতে বিশাল বিশাল মাইনের বিশাল বিশাল লেখক পোষা হচ্ছে। পত্রিকার মালিক নিত্য রুটিনমাফিক পত্রিকার বিভাগীয় সম্পাদকদের সঙ্গে মিটিং করছেন, বুঝিয়ে দিচ্ছেন পেপার পলিসি। আর সেই পেপার পলিসিকে মাথায় রেখেই কলম চালাচ্ছেন, কলম চালাতে হচ্ছে মাইনে করা তা-বড় লেখকদের।
পেপার পলিসি কী? পত্রিকার মালিকগোষ্ঠীর স্বার্থরক্ষার কৌশলই, পত্রিকার কৌশল। পত্রিকার মালিকের স্বার্থ কখনও ব্যক্তিগত, যেখানে আর এক পত্রিকাগোষ্ঠীর তিনি প্রতিদ্বন্দ্বী। আবার কখনও শ্রেণিগত, যেখানে সামগ্রিকভাবেই ধনিকশ্রেণির স্বার্থ মিলেমিশে আছে। পত্রিকার মালিক এই দুই ধরনের স্বার্থেই তাঁর মাইনে করা লেখকদের কাজে লাগিয়ে পাঠক- পাঠিকাদের মগজ ধোলাই করে।
এ-যুগের সাংস্কৃতিক পরিবেশ এমনি হাজারো উপায়ে হাজারো ফন্দিতে মুঠোবন্দি করে রেখেছে হুজুরের দল, হুজুর-মজুর সম্পর্ককে বজায় রাখতেই । দেশের সমাজ-সাংস্কৃতিক পরিবেশের এই বিশাল দূষণ নিয়ে, পচন নিয়ে নীরব কেন সেইসব রাজনৈতিক দল যারা গরিবি হটাতে চায়, যারা শ্রমিক শ্রেণির সংগ্রামের হাতিয়ার? যারা দেশপ্রেমী জাতীয়তাবাদী? ওদের নীরবতার একটাই অর্থ—ওরা চায় এই সমাজ-সাংস্কৃতিক পরিবেশ বজায় রাখতে, তাই তো পরিবেশ বলতে শুধুমাত্র ‘প্রাকৃতিক পরিবেশে’র কথা আমাদের মাথায় ঢোকাতে দীর্ঘস্থায়ী লাগাতার প্রচার চালিয়েই যাচ্ছে।
যুদ্ধ নয়, শান্তি চাইঃ যুদ্ধ ছাড়া শান্তি নেই
কয়েক কিলোমিটার দীর্ঘ বর্ণাঢ্য ‘যুদ্ধ নয়, শান্তি চাই’ মিছিলের ঢল কল্লোলিনী কলকাতাকে একানব্বুইয়েও কল্লোলিত করেছে, একটু বেশি মাত্রায়ই করেছে। সত্যি কথা বলতে কি, মাত্রা ছাড়াই করেছে। রাস্তার এ-মুড়ো থেকে ও মুড়ো চওড়া মিছিলের মাথা যখন পার্কসার্কাস ময়দান অতিক্রম করছে, তখন লেজ রয়েছে একগাদা পাক মেরে যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে। মুড়োয় রাজনৈতিক, চলচ্চিত্র, ক্রীড়া, সাহিত্য ও বিজ্ঞান জগতের স্টার-মেগাস্টারদের ভিড়। মাথায় মাথায় শান্তির সাদা টুপি। ট্যাবলোয় শান্তির বিশাল পায়রা, মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের বেয়নেটের সামনে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ মুষ্ঠিবদ্ধ হাত, যুদ্ধের বিপক্ষে শান্তির পক্ষে বলিষ্ঠ হরফের স্লোগান। আগাম প্রচারের ব্যাপকতায় রাস্তার দু-ধারে স্টার-মেগাস্টার দর্শনার্থীদের লাগামছাড়া ভিড়। এক সময় বয়ানে-বাঁধা বক্তব্যে আকাশে-বাতাশে আগুন ছড়ান পেশাদার গরিব-দরদী, সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী, যুদ্ধ-বিরোধী সুবক্তারা। প্রেস ও দূরদর্শনের আলোর ঝলকানিতে ঝলমল করতে করতে গলার ওঠা-নামায় নানা নাটকীয় মুহূর্ত তৈরি করে দেশবাসীদের সতর্ক করে দেন সাম্রাজ্যবাদীদের বিশ্বব্যাপী যুদ্ধ চক্রান্তর বিরুদ্ধে।
সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী ‘যুদ্ধ নয়, শান্তি চাই’ মার্কা-সভা-মিছিল বিভিন্ন সাংস্কৃতিক সংস্থা, বিজ্ঞান আন্দোলনকারী সংস্থা প্রথাগতভাবে প্রতিবছরই করছেন। নামতা পড়ার মতো আউড়ে যাচ্ছেন যুদ্ধের বিপক্ষে, শান্তির পক্ষে গরম গরম নানা কথা। সভা-মিছিলে অংশগ্রহণকারীদের অনেকেই দু-কান ভরে শুনছেন ধনবাদী-রাষ্ট্রশক্তি ও অস্ত্রব্যবসায়ীদের আপন প্রয়োজনে কীভাবে নির্ধনী মানুষগুলোর উপর চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে যুদ্ধ। কী সুনিপুণ চক্রান্তের মধ্য দিয়ে শান্তিকে পাঠানো হচ্ছে নির্বাসনে। সাম্রাজ্যবাদীদের কালো হাত ভেঙে দেবার, পুড়িয়ে দেবার শপথ বাক্যগুলো দু-কান দিয়ে ঢোকে বটে—কিন্তু মস্তিষ্ক কোষকে প্রভাবিত করতে পারে না, ভাসা-ভাসা থেকে যায়।
কারা সাম্রাজ্যবাদী? কারা সম্প্রসারণশীল? কাদেরকে চিহ্নিত করব ধনবাদী-রাষ্ট্রশক্তি হিসেবে? যুদ্ধবাজ দেশ হিসেবে কাদের গায়ে মারব সিলমোহর? প্রতিরক্ষা ও যুদ্ধ খাতে যারা ব্যয়ের বহর বাড়িয়ে যায় তাদের বিরুদ্ধে কতখানি সোচ্চার হব? প্রশ্নগুলো শুনে যতটা নিরীহ মনে হয়, “যুদ্ধ নয়, শান্তি চাই’ আন্দোলনের নেতাদের মস্তিষ্ক ঘুরে উত্তরগুলো যখন মুখ দিয়ে বেরিয়ে আসে তখন আর সেগুলো মোটেই সহজ-সরল থাকে না, এ যেন মাথায় পেরেক ঢোকানোর পর স্ক্রু হয়ে বেরিয়ে আসা। ‘জনপ্রিয়তা’, ‘ভোটার-তোষণ’ ইত্যাদি বিষয়গুলো নিজের জীবনের গণনার মধ্যে আনলেই অনেক মাপ-ঝোক করে কথা বলতে হয়, সাদা সত্যি কথা বলার বিলাসিতা শোভা পায় না। ফলে আমাদের শান্তিকামী, পায়রা ওড়ানো নেতারা কোনও দিনই সত্যের খাতিরেও উচ্চারণ করতে পারেননি যুদ্ধের চক্রান্ত ও আয়োজন মার্কিন হামলাবাজরাই শুধু করছে না। রাশিয়াও সমান উৎসাহেই যুদ্ধের সরঞ্জাম উৎপাদনে ব্যস্ত ছিল তাসের ঘরের মতো ভেঙে পড়ার আগে পর্যন্ত । ওদের অস্ত্রও পৃথিবী জুড়ে বহু দেশেই বিক্রি হত।
আমাদের দেশের সরকারও যে যুদ্ধ সরঞ্জাম উৎপাদন ব্যবস্থা
দিন দিন বাড়িয়েই চলেছে, প্রতিরক্ষা তথা জাতীয়
নিরাপত্তা খাতে আমাদের দেশের ব্যয় সম্মিলিত
জাতিপুঞ্জের একশো ষাটটি দেশের মধ্যে
পঞ্চম-এই কথাগুলো ‘যুদ্ধ নয়,
শান্তি চাই’ দিবসে কোনও
শান্তি-দরদি বক্তা কি
উচ্চারণ করেছেন?
আমাদের দেশে পারমাণবিক বোমা বানানো চলবে না— এমন সোচ্চার দাবি করতে কি সৎসাহস দেখাবে কোনও ভোট-নির্ভর রাজনৈতিক দল? যুদ্ধ বিরোধী সভায়-মিছিলে নেতৃত্ব দানকারী রাজনৈতিক দলগুলো ভাসা-ভাসা গোলা-গোলা কথা বলে উত্তেজনার আগুন পোহানোর মধ্যে নিজেদের দায়বদ্ধতা সীমাবদ্ধ রাখতে চায়, তাই অকপট উচ্চারণে তারা এত দ্বিধাগ্রস্ত।
বাংলাদেশ-শ্রীলঙ্কা মালদ্বীপে ভারত সেনা পাঠিয়ে দৈনিক যে কোটি-কোটি টাকা ব্যয় করেছে, ফি বছর আট দশ হাজার কোটি টাকার যুদ্ধাস্ত্র কিনছে বিদেশ থেকে, হাজার হাজার কোটি টাকার যুদ্ধ সরঞ্জাম তৈরি করে চলেছে প্রতিরক্ষা কারখানাগুলোয়, এর পরিবর্তে আমরা কি পারতাম না বন্ধ কারখানাগুলোর তালা খুলতে? নতুন নতুন শিল্পোদ্যোগ গড়ে তুলতে? কোটি কোটি বেকারদের জন্য কর্মসংস্থান করতে? কয়েক লক্ষ গ্রামে স্কুল খুলতে, পানীয় জল সরবরাহের উদ্যোগ নিতে?
দেশের অর্থনৈতিক তীব্র সংকট যখন বাঘের থাবা হয়ে হামলা চালায় কোটি কোটি অবর্ণনীয় দারিদ্রগ্রস্ত মানুষকে লক্ষ করে তখন অসহায় সরকার তাদের সরকারি তহবিলের শোচনীয় তলানির কথা জানিয়ে দেশের স্বার্থে আরও কৃচ্ছ্রসাধনের বাণী শোনায়। হে শান্তির মহান দূতরা-আপনারা কি তবে মনে করেন গরিবদের পিছনে টাকা খরচ করার চেয়ে বাংলাদেশ- শ্রীলঙ্কা-মালদ্বীপে সেনা পাঠিয়ে ‘দাদাগিরি’ করার প্রয়োজন অনেক বেশি? বিদেশ থেকে বাহারি কামান, আধুনিক বিমান, রাজকীয় জাহাজ ও ছিমছাম ট্যাঙ্ক ও ত্রাস সৃষ্টিকারী ক্ষেপণাস্ত্র কেনা অনেক জরুরি? অনেক শ্রেয়তর রকেট ও পারমাণবিক অস্ত্ৰ নিৰ্মাণ ?
আমাদের পড়শি দেশ পাকিস্তান মার্কিন দেশ থেকে অস্ত্র কিনলে শান্তি সচেতন রাজনৈতিক দল ও সংস্থাগুলো যতটা সরব হয়, তার ভগ্নাংশ প্রতিবাদও কি প্রকাশ করি আমাদের সরকার যখন প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা জোরদারের নামে প্রতিবছর বহু সহস্র কোটি টাকার বিদেশি অস্ত্র ঘরে তোলে? আমাদের দেশের আধা-সামন্ততান্ত্রিক, আধা-পুঁজিবাদী, আধা ঔপনিবেশিক, আধা সম্প্রসারণশীল সরকার বিনা বাধায় প্রতিরক্ষার নামে জনসাধারণের ট্যাক্সের হাজার হাজার কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মাণ করেই চলেছে যুদ্ধাস্ত্র, রকেট, পারমাণবিক অস্ত্র। বিদেশ থেকে আমদানি করেই চলেছে অত্যাধুনিক মারণাস্ত্র, জাতীয় নিরাপত্তার নিছক অজুহাত খুঁজে তখকে সুদৃঢ় করতে আধা-সামরিক বাহিনীর আয়তন বৃদ্ধি করে চলেছে— এ বিষয়ে বিরোধী রাজনৈতিক প্রতিটি দলই আশ্চর্য রকম নীরব, নীরব সাংস্কৃতিক আন্দোলনের নেতৃত্বে থাকা সংস্থা ও ব্যক্তিরা। এরপর যখন এরাই যুদ্ধের বিপক্ষে শান্তির পক্ষে সরব হন, তখন এই স্ববিরোধিতাই কি এই সরবতাকে ‘ন্যাকামি’র পর্যায়ে নামিয়ে আনে না? জনগণকে সত্যি বলার ক্ষমতা যখন থাকে না, তখন ন্যাকা ন্যাকা, গোলা- গোলা, ভাসা-ভাসা কথা ছাড়া আর কিই বা বলার থাকতে পারে শান্তির ধান্দাবাজ দূতদের ?
স্পষ্ট উচ্চারণে সত্য কথাগুলো বলতে এত জড়তা কেন? কেন এমন মুখে কুলুপ দিয়ে থাকা? যদি রাষ্ট্রশক্তি দেশদ্রোহীর অপবাদ রটায়—এই ভয়ে ? দলে ভারী হওয়ার লোভে, বিচ্ছিন্ন হওয়ার ভয়ে সত্যকে সচেতনভাবে এগিয়ে চলার মধ্যে আদর্শ কোথায় ?
কোনও অবস্থাতেই আদর্শের কোনও বিকল্প নেই–
একথা যেমন সত্য, তেমনই সত্য-স্থূলতা
সব সময় স্বাস্থ্যের লক্ষণ নয়।
তবে বোবা হয়ে থাকার পিছনে আরও একটি সম্ভাবনার সচেতনদের ভুলে থাকার কোনও অবকাশ নেই। রাষ্ট্রক্ষমতায় গেলে এই বিপ্লবী-বক্তারা একই ছাঁচে-ঢালা পদ্ধতিতেই শাসন চালাবে, ঠিক করাই আছে, তাই জনচেতনাকে গুলিয়ে দিতেই যুদ্ধ-শান্তি নিয়ে আবেগ সর্বস্ব, যুক্তিহীন গোলা-গোলা কথার ফুলঝুরিতে আগুন দেওয়া। পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠী দেশটাকে কীভাবে সাম্রাজ্যবাদীদের চক্রান্তের ঘাঁটি করে তুলতে সাহায্য করছে—এই নিয়ে আমরা যখন উষ্মা প্রকাশ করি তখন আমাদের নিরপেক্ষতাহীন দৃষ্টিতে ধরা পড়ে না প্রকৃত চিত্র -পাকিস্তানের শাসকশ্রেণির সঙ্গে আমাদের দেশের শাসকশ্রেণির এবং আমাদের দেশের শাসন ক্ষমতা দখলকারী সংসদের বিরোধী শক্তিগুলোর চরিত্রগত ও আচরণগত মিল বড়ই বেশি।
শান্তিকামী মানুষের উপর যুদ্ধ চাপিয়ে দিচ্ছে যুদ্ধবাজ শাসকশ্রেণি ও তাদের দোসর শাসক শ্রেণি। শোষিত শ্রেণির চাওয়া, না চাওয়ার উপর আজ যুদ্ধ নির্ভরশীল নয়। বঞ্চিত মানুষরা শান্তি আনতে চাইলে মুখের কথায় তা আসবে না, অশান্তি সৃষ্টিকারীদের নির্মূল করেই শান্তি আনতে হবে। অশান্তি নির্মূল করতে লড়াই করতেই হবে। সে লড়াই অবশ্যই শোষকের সঙ্গে শোষিতের— দীর্ঘস্থায়ী শান্তির স্বার্থেই এই লড়াই একান্ত কাম্য। এমন একটা যুদ্ধ ছাড়া শান্তি নেই ।
দেশপ্রেমঃ কানামাছি ভোঁ ভোঁ
সিনেমায়, যাত্রায়, নাটকে, গল্পে-উপন্যাসে যখনই দেশপ্রেমের প্রসঙ্গ এসেছে, সাধারণ মানুষের মগজ ধোলাই করতে বারবার বোঝানো হয়েছে, দেশ মানে, ‘ধরতি’, ‘দেশের মাটি’, ‘দেশের নদী-পাহাড়’। দেশের মাটিকে এক খাবলা তুলে নিয়ে শপথ নিচ্ছে দেশপ্রেমিকরা এবং তার জন্য প্রাণ পর্যন্ত দিয়ে দিচ্ছে।
বারবার প্রচারে যে কথাটা আমাদের মাথায় ঢোকানো হয়েছে এবং হচ্ছে, তা তো বাস্তব সত্য নয়। ‘দেশপ্রেম’ মানে কখনওই দেশের মাটিকে ভালোবাসা হতে পারে না ।
দেশপ্রেম মানে ‘দেশবাসীর প্রতি প্রেম’। কিন্তু তামাম দেশবাসীকে
তো এক সঙ্গে প্রেম বিলোনো যায় না। হুজুরের দলকে
প্রেম বিলোলে মজুরের দলকে অপ্রেম বিলোতে
হয়। আর মজুরের দলকে প্রেম বিলোনো
মানেই হুজুরের দলকে অপ্রেম।
রবীন্দ্রনাথ তাঁর ‘আত্মপরিচয়’ গ্রন্থে লিখেছিলেন, ‘দেশ মানুষের সৃষ্টি। দেশ মৃন্ময় নয়, সে চিন্ময়। মানুষ যদি প্রকাশমান হয় তবে দেশ প্রকাশিত । সুজলা সুফলা মলয়জশীতলা ভূমির কথা যতই উচ্চকণ্ঠে রটান ততই জবাবদিহির দায় বাড়বে, প্রশ্ন উঠপে প্রাকৃতিক দেশ তো উপাদান মাত্র, তা নিয়ে মানবিক সম্পদ কতটা গড়ে তোলা হল। মানুষের হাতে দেশের জল যদি যায় শুকিয়ে, ফল যদি যায় মরে, মলয়জ যদি বিষিয়ে ওঠে মারীবীজে, শস্যের জমি যদি হয় বন্ধ্যা, তবে কাব্য কথায় দেশের লজ্জা চাপা পড়বে না। দেশ মাটিতে তৈরি নয়, দেশ মানুষে তৈরি।’
এক শতাব্দী আগে রবীন্দ্রনাথ যে পরম সত্যটি অনুভব করেছিলেন, উপলব্ধি করেছিলেন, সেই উপলব্ধি ও অনুভবে এখনও যদি বুদ্ধিজীবীরা পৌঁছতে না পেরে থাকেন, তবে এইসব তথাকথিত বুদ্ধিজীবীদের হয় নির্বোধ অথবা অতি বুদ্ধিজীবী অর্থাৎ ‘ধান্দাবাজ’ বলতে হয়।
আজ ‘দেশপ্রেম’ বলতে দেশের মাটিকে দেশের ভূখণ্ডের চৌহদ্দিকে চিহ্নিত করাটাই প্রচলিত সংস্কার হয়ে দাঁড়িয়েছে। ‘৯২-এ একটি বৃহৎ মার্কসবাদী দলের ছাত্র সংগঠনের রাজ্য সম্মেলনে তোরণে তোরণে সোচ্চারে ঘোষিত হয়েছে, “এ দেশে তোমার আমার, এ দেশ রক্ষা করার দায়িত্ব আমাদের।” দেশের মানুষ ছেড়ে দেশের চৌহদ্দির প্রতি প্রেম জাগিয়ে তোলার এমনতর চেষ্টায় প্রায় প্রতিটি রাজনৈতিক দল ও তাদের শাখা-প্রশাখাগুলো লাগাতার মগজ-ধোলাই করেই চলেছে। তাই দেশপ্রেমের প্রকৃত অর্থ অনুধাবন করে যখন কোনও মানবগোষ্ঠী হুজুরের শোষণের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায়, তাদের শোষণের থাবা থেকে বেরিয়ে আসতে চায়, তখন মগজ ধোলাইয়ের কল্যাণে অমনি চারদিক থেকে নিপীড়িত মানুষগুলোই তথাকথিত বুদ্ধিজীবীদের সুরে সুর মিলিয়ে ‘গেল গেল’ রব তুলে ছুটে আসে। এবং যা নয় তাই বলে গাল পাড়তে থাকে। এরপর ওইসব আন্দোলনকারীদের ‘দেশদ্রোহী’ আখ্যা দিতে পারলে কাজ অর্ধেক হাসিল।
একটি বারের জন্য গভীরভাবে ভাবুন তো, বাস্তবিকই ‘দেশদ্রোহী’ কে? কে চিহ্নিত করবে দেশদ্রোহীদের ও দেশপ্রেমিকদের? যে ফসল ফলায় তাকে সমাজ ফসলের অধিকার দেয়নি। যে কলে-কারখানায়-খনিতে উৎপাদন করে তাকে সমাজ দেয়নি উৎপাদিত দ্রব্যের অধিকার। ওদের অধিকার বঞ্চিত করেই কিছু মানুষ তাদের জীবনযাত্রাকে সমৃদ্ধ করেছে।
দক্ষিণ-বিহার, যে অঞ্চল ঘিরে স্বতন্ত্র ঝাড়খণ্ড রাজ্য গড়ে উঠেছে। সেই দক্ষিণ বিহারের প্রাকৃতিক সম্পদ শোষণ করে উত্তর-বিহারের মহাজন জোতদাররা আজ ধনী। পশ্চিমবঙ্গের বাঁকুড়া-পুরুলিয়া, মেদিনীপুরের একাদশ ও ওড়িশার আদিবাসী অধ্যুষিত অঞ্চলের প্রাকৃতিক সম্পদ লুটে সমৃদ্ধ হয়েছে শহরাঞ্চলের মহাজনেরা। মিজোরাম-নাগাল্যান্ডের সম্পদ আহরণ করে সমৃদ্ধ হয়েছে সমতলের কিছু মানুষ সমতলের জনপথ। এই শোষণ এই বঞ্চনা অবিরল ধারায় বয়েই চলেছে বছরের পর বছর। কেউ এই শোষিত বঞ্চিত মানুষদের হয়ে প্রশ্ন তোলেনি কেন এদের শোষণ করে সমৃদ্ধ হবে কিছু ব্যবসায়ী মহাজন ও তাদের সাথী রাজনীতিকরা। এই বঞ্চনা ও শোষণ যখন বঞ্চিত মানুষদের সমাজ জীবনের মূলস্রোত থেকে বিচ্ছিন্ন হতে প্ররোচিত করেছে, ক্ষুব্ধতার ঝড় তুলতে উদ্বেল করেছে, তখন ব্যবসায়ী, মহাজন ও তাদের রাজনীতি পেশার সঙ্গীরা শঙ্কিত হয়েছে। ওদের চিহ্নিত করতে চেয়েছে বিচ্ছিন্নতাবাদী হিসেবে, দেশের শত্রু হিসেবে। দেশের সর্বত্রই প্রায় একই নিয়মে দেশদ্রোহী–বিচ্ছিন্নতাবাদীদের চিহ্নিত করা হচ্ছে।
প্রশ্নটা এই— কারা চিহ্নিত করছে? না, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক। সেই মন্ত্ৰক ঠিক করবে কারা দেশদ্রোহী। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক চলবে কার তর্জনী হেলনে? না, প্রধানমন্ত্রী ও তাঁর গোমস্তা স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীর তর্জনী হেলনে। দেশের মানুষের যথার্থ স্বার্থ রক্ষার জন্য যে আন্দোলন, যে সংগ্রাম, তার সঙ্গে যুক্ত মানুষদের ‘দেশদ্রোহী’ ঘোষণা করাটাই তো দেশের মানুষের স্বার্থের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা। মানুষের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতাই তো দেশদ্রোহিতা। ব্যক্তি স্বার্থে বা গোষ্ঠীস্বার্থে যারা বলি চড়িয়েছে বিভিন্ন অঞ্চলের হতদরিদ্র মানুষগুলোর স্বার্থকে। সেই শাসকগোষ্ঠী আর তার চামচা-হাতারাই তো প্রকৃত দেশদ্রোহী। দেশপ্রেমিক মানুষ তো তারাই, যারা বঞ্চিত মানুষদের অধিকার রক্ষার জন্য কাঁধে কাঁধ দিয়ে সংগ্রামে নেমেছে।
সত্য সেলুকাস কী বিচিত্র এই দেশ! এখানে ‘ভারতরত্ন’-এর
মুকুট চড়ে সেইসব রাজনীতিকদের মাথায় যারা দেশের
বঞ্চিত মানুষদের মিথ্যে আশার বাণীতে ভুলিয়ে
রেখে শোষণ প্রক্রিয়াকে কায়েম রাখতে
সচেষ্ট রেখেছে নিজেদের ‘তন্-মন’।
যারা বিবেচনা শক্তিকে পকেটে পুরে রেখে সরকারের সুরে সুর মিলিয়ে সোচ্চার হয়, “জল উঁচু-জল উঁচু, জল নিচু-জল নিচু” বলে, তারাই সরকার চিহ্নিত দেশপ্রেমিক।
১৯৯২-এর আগস্ট মাস ধরে দেশপ্রেমের বাড়তি বান ডাকাল ভারতের বড়-মেজ-সেজ-ছোট নানা মাপের রাজনৈতিক দলগুলো। আকাশবাণীর ধ্বনিতে আর দূরদর্শনের পর্দা জুড়ে শুধু দেশপ্রেমের অনুষ্ঠানের সারিবদ্ধ প্রদর্শনী। একটি মার্কসবাদী দলের যুব সংগঠন এক লাখ গানের ক্যাসেট বাজারে ছেড়ে দেশপ্রেমের ঝটতি বন্যায় বাড়তি জল সরবরাহ করল। সম্মিলিত প্রচারের স্রোতে ভাসিয়ে নিয়ে যেতে চাইল একটি বিশ্বাসের শিশুকে—মানুষকে ভালোবাসাই দেশপ্রেম, মানুষের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতাই দেশদ্রোহিতা। ওরা মৌলবাদ রোখার কথা বলল, বলল না মৌলবাদের ধারক-বাহক-পালক প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মের বিরুদ্ধে একটিও কথা। কেন এমন তালগোল পাকানো অস্বচ্ছ-চিন্তাকে সাধারণের মাথায় ঢোকাতে এত বিপুল আয়োজন? কে সেই বিশ্বাসের শিশু?
এই বিশ্বাসের শিশুটির জন্ম হয়েছিল ‘৯২-এর জানুয়ারির কলিকাতা পুস্তক মেলায় ‘অলৌকিক নয়, লৌকিক’ বইটির তৃতীয় খণ্ড প্রকাশ মুহূর্তে। এই খণ্ডটি প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে যে অভাবনীয় জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল এবং বিশাল সংখ্যক জনগণকে বিপুলভাবে প্রভাবিত করেছিল, তাতে রাষ্ট্রশক্তি ও বিভিন্ন জন-প্রতারক রাজনৈতিক দল অনুভব করেছিল সর্বনাশের ঝড় আসন্ন। দেশপ্রেম-বিচ্ছিন্নতাবাদ- ধর্মনিরপেক্ষতা-বিজ্ঞানজাঠা ইত্যাদি নিয়ে যে ব্যাখ্যা হাজির করা হয়েছিল উল্লিখিত বইটিতে, সেসব ব্যাখ্যা যে কী বিশালভাবে জনগণকে প্রভাবিত করেছিল তারই এক অকাট্য প্রমাণ রাষ্ট্রশক্তি পেয়েছিল—তাদের বড় সাধের বিজ্ঞান জাঠার চক্রান্ত সম্পূর্ণভাবে ছিন্ন-ভিন্ন হয়ে ধসে যাওয়ায়। এই বইটিতে ‘দেশপ্রেম’ -এর প্রকৃত সংজ্ঞা প্রকাশিত হয়ে মানুষকে দারুণভাবে আন্দোলিত করল। গ্রামে-গঞ্জে-হাটে-মাঠে সর্বত্র আমাদের সমিতির শাখা সংগঠনগুলোও সহযোগী সংস্থাগুলো ‘অলৌকিক নয়, লৌকিক’ শিরোনামের অনুষ্ঠানে জনগণের মাথায় ঢুকিয়ে দিতে লাগল যুক্তির আলোকে দেশপ্রেমের ব্যাখ্যা। এই অভাবনীয় অবস্থাকে সামাল দিতে রাষ্ট্রশক্তি ও ধনকুবেরদের দিকে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেওয়া রাজনৈতিক দলগুলো পালটা মগজ ধোলাই করে জনগণের মাথায় ঢোকাতে চাইল— দেশপ্রেম মানে দেশের ভূখণ্ডের প্রতি প্রেম; দেশের নদী, মাটি, সমুদ্র, পর্বতের প্রতি প্রেম।
কিন্তু একটু আগে যে কথা বলছিলাম, দেশ তো মাটি-নদী-পৰ্বত নয়, মানুষকে বাদ দিয়ে তো আর যাই হোক, দেশ হয় না, তাই গ্রামে-শহরে সাংস্কৃতিক আন্দোলনে নেতৃত্ব দেওয়া বহু নতুন কণ্ঠ তাদের লাগাতার প্রচারে প্রতিষ্ঠা করেই চলেছে ‘দেশপ্রেম’-‘বিচ্ছিন্নতাবাদ’ – ‘ধর্মনিরপেক্ষতা’ ইত্যাদির যুক্তিগ্রাহ্য ব্যাখ্যা।
আমাদের সমাজে প্রকৃত দেশপ্রেমের কোনও ঐতিহ্য নেই। আর সেই ঐতিহ্য যাতে গড়ে উঠতে না পারে সেজন্য তথাকথিত দেশপ্রেমীরা সদা-সতর্ক, সদা তৎপর। এ দেশের ঐতিহ্যে দেশপ্রমিক বলে চিত্রিত রানাপ্রতাপ, শিবাজি থেকে শুরু করে ঝান্সির রানি, বারো ভূঁইয়ার মতো ভিড় করে আসা বহু চরিত্র। এঁদের ব্যক্তিস্বার্থের দ্বন্দ্বকেই বিকৃতভাবে আমাদের সামনে বারবার হাজির করা হয়েছে ও হচ্ছে দেশপ্রেমের নিদর্শন হিসেবে। ধনিকশ্রেণির অর্থপুষ্ট, ধনিকশ্রেণির স্বার্থরক্ষাকারী রাজনীতিকদেরই ‘ভারতরত্ন’ বলে ভুষিত করার ঐতিহ্যই আমরা বহন করে চলেছি। হুজুরের প্রতি প্রেমময় এইসব ভারতরত্নরা যদি দেশপ্রেমিক হন, তাহলে দেশদ্রোহী কারা? এই ঐতিহ্য অনুসারী আমরা তাই নিপীড়িতদের স্বার্থরক্ষাকারীকেই ‘দেশদ্রোহী’ বলে চিহ্নিত করেই চলেছি।
ঐতিহাসিক, পাঠ্যপুস্তক রচয়িতা, নাট্যকার, কবি, গল্পকার, ঔপন্যাসিক, প্রবন্ধকার, বিদ্যালয়ের পাঠ্যপুস্তক, পত্র-পত্রিকা, আকাশবাণী, দূরদর্শন লাগাতার প্রচারে ‘জাতীয়-মনীষী’, ‘জাতীয় মহাপুরুষ’ হিসেবে যাঁদের চিত্রিত করেছেন, তাঁদের প্রতি ভক্তির প্লাবনে অনেক সময়ই যুক্তিচ্যুত হয়েছি। এই মনীষীদের যে সীমাবদ্ধতা আছে, ভ্রান্তি আছে এসব ভুলে গিয়ে ‘অভ্রান্ত’ হিসেবে ধরে নিয়েছি, ‘মিথ’ হিসেবে গড়ে তুলেছি। আমরা এইসব ‘জাতীয় নেতাদের’ ‘জাতীয় মুক্তির প্রতীক’, ‘প্রাতঃস্মরণীয়’, ‘অনুকরণযোগ্য’, ‘জাতীয় প্রগতির প্রতীক’ ইত্যাদি বিশেষণে বিশেষিত করি। সাংস্কৃতিক আন্দোলনের স্বার্থেই এইসব জাতীয় মনীষীদের সঠিক মূল্যায়ন একান্তই প্রয়োজন। ভ্ৰান্ত মূল্যায়নকে বজায় রেখে সাংস্কৃতিক আন্দোলন গড়তে গেলে ওইসব মনীষীদের ভ্রান্তিকেই সাংস্কৃতিক আন্দোলন ধ্বংসের অস্ত্র হিসেবে প্রয়োগ করবে শোষকশ্রেণি ও রাষ্ট্রশক্তি। এইসব মনীষীদের চরিত্রের মাঝে-মাঝেই যে স্ববিরোধিতা, দ্বিচারিতা প্রকট হয়ে উঠেছিল, প্রকৃত মূল্যায়নের স্বার্থেই সে বিষয়ে স্পষ্ট আলোচনায় আসা একান্তই প্রয়োজনীয়, নতুবা এইসব মনীষীদের ছবি ঘিরে জ্যোতি নামক কুয়াশা সৃষ্টি হলে প্রগতির গতি হবে রুদ্ধ।
এও তো ঐতিহাসিক সত্য-যে রামমোহন ফরাসি বিপ্লবের জয়ের খবরে উল্লসিত হয়ে ভাঙা পা নিয়েও ছুটে গিয়েছিলেন ফরাসি জাহাজে ফরাসি পতাকাকে অভিনন্দন জানাতে; স্পেনের গণতান্ত্রিক বিপ্লবের বিজয় সংবাদে আনন্দের প্রাবল্যে ভোজসভার আয়োজন করেছিলেন কলকাতার টাউন হলে; ইতালীর বিপ্লব ব্যর্থ হওয়ার সংবাদে শয্যা নিয়েছিলেন; সেই “স্বাধীনতার পূজারি’, ‘জাতীয়তাবাদের জনক’ হিসেবে পূজিত রামমোহন ব্রিটিশ পার্লামেন্টের সামনে দাঁড়িয়ে নির্দ্বিধায় বলতে পেরেছিলেন, “ইংরেজ জাতির অভিজাত সম্প্রদায় ভারতে উপনিবেশ বিস্তার করলে তার ফল ভারতীয়দের কাছে বিশেষ মঙ্গলময় হবে।” শোষক ও উৎপীড়ক নীলকর সাহেবদের পক্ষ নিয়ে নিলজ্জের মতো বলতে পেরেছিলেন, “নীলকর সাহেবরা এ-দেশে অকল্যাণের চেয়ে কল্যাণই করেছে বেশি।” নীলকর সাহেবদের অত্যাচার ও শোষণের বিরুদ্ধে যে রক্তক্ষয়ী কৃষক সংগ্রাম গড়ে উঠেছিল সেই সংগ্ৰাম রামমোহনের চোখে ছিল, ‘সংস্কারবদ্ধ মনের অদূরদর্শী আন্দোলন।’ সংবাদপত্রের স্বাধীনতার ক্ষেত্রে রামমোহনের বিশাল অবদানের কথা সুবিশাল প্রচারের কল্যাণে অনেকেরই অজানা হয়। কিন্তু ক’জনের জানা আছে, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা চাওয়ার ক্ষেত্রে রামমোহনের ঘৃণ্য চক্রান্তের কথা? রামমোহনের কথায়, ‘প্রজাবর্গের অভাব-অভিযোগ সংবাদপত্রের রামমোহনের বিশাল অবদানের কথা সুবিশাল প্রচারের কল্যাণে অনেকেরই অজানা নয়। কিন্তু ক’জনের জানা আছে, সাংবাদপত্রের স্বাধীনতা চাওয়ার ক্ষেত্রে মাধ্যমে প্রকাশিত হতে না পারলে অথবা তার প্রতিকার না হলে বিপ্লব ঘটে যেতে পারে, কিন্তু সংবাদপত্রের স্বাধীনতা সেই বিপদ নিবারণ করতে পারে । হিন্দু-ধর্মের কুসংস্কারের বিরুদ্ধে রামমোহন সোচ্চার ছিলেন বলে যে চরিত্রটি চিত্রিত হয়ে আসছে তাও তো ঠিক নয়। এ-বিষয়েও তাঁর সীমাবদ্ধতা ছিল । জাত-পাতের বিরুদ্ধে তিনি সংগ্রামী পুরুষ বলে যে সীমাহীন প্রচার অবিরল ধারায় চলে আসছে, সেও তো গল্পের গরুকে গাছে তোলারই নামান্তর মাত্র ।
রামমোহন হিন্দুধর্মের কুসংস্কার ও কু-আচারের বিরুদ্ধে সোচ্চার হলেও নিজে কিন্তু জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত পৈতেটি পরিত্যাগ করতে পারেননি। বাবার মৃত্যুর পর শ্রাদ্ধ করেছিলেন। বিলেতে নিয়ে গিয়েছিলেন ব্রাহ্মণ রাঁধুনি । তাঁরই প্রতিষ্ঠিত ব্রাহ্মসভার একটি ঘরে ব্রাহ্মণরা বেদ ও উপনিষদ পাঠ করতেন। ওই ঘরে অব্রাহ্মণদের প্রবেশাধিকার ছিল নিষিদ্ধ ।
যে বিদ্যাসাগর বিধবা-বিবাহ প্রচলন ও বাল্য-বিবাহ রোধের আন্দোলনে ঋজুতার প্রমাণ দিয়েছিলেন, বেদান্ত-সাংখ্য ইত্যাদি দর্শনকে ভ্রান্ত বলে ঘোষণা করেছিলেন, তিনিই আবার শিক্ষা উচ্চবিত্ত ও মধ্যবিত্তদের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখার পরামর্শ দিয়েছিলেন। কিছু কিছু ক্ষেত্রে সমাজ সংস্কারকের ভূমিকা গ্রহণ করলেও জাতিভেদের বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে তোলার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেননি। শিক্ষিকাদের প্রশিক্ষণের জন্য বিদ্যালয় স্থাপনের বিরোধিতা করেছিলেন। মঞ্চে কোনও নারীকে অভিনেত্রীর ভূমিকায় সহ্য করতে পারতেন না। সিপাহি বিদ্রোহ দমনকারী ব্রিটিশ সেনাবাহিনীর থাকার জন্য তাঁর পরিচালনাধীন সংস্কৃত কলেজকে ছেড়ে দিয়ে বৃটিশ শাসকদের প্রতি পূর্ণ সহযোগিতা করেছিলেন। এরপরও বিদ্যাসাগরকে সীমাবদ্ধতার ঊর্ধ্বে এক ‘জাতীয়-নেতা’, ‘দেশ-প্রেমিক’ বলা যায় কি?
বাংলা গদ্যসাহিত্যে বঙ্কিমচন্দ্রের অসামান্য অবদান অনস্বীকার্য। কিন্তু ভক্তিরসের অতি-প্লাবনে ভারতবর্ষের স্বাধীনতার পরম-মন্ত্র ‘বন্দে মাতরম’ ধ্বনির স্রষ্টা হিসেবে হাজির করা হলেও বঙ্কিমচন্দ্র তো মোটেই ব্রিটিশ সরকার বিরোধী ছিলেন না। তিনিই বরং ব্রিটিশ সরকারকে ‘ভারতের পরমোপকারী’ বলে সোচ্চার ঘোষণা রেখেছিলেন। এই বঙ্কিমচন্দ্রই মীর মশাররফ হোসেনের ‘জমিদার দর্পণ’ নাটক প্রচার বন্ধ রাখতে বলেছিলেন এই কারণে যে, কৃষক বিদ্রোহের এই নাটক অভিনীত হতে থাকলে ইংরেজ বিরোধিতার ‘জ্বলন্ত অগ্নিতে ঘৃতাহুতি দেওয়া হবে।’ দীনবন্ধু মিত্রর ‘নীলদর্পণ’ নাটকের তীব্র বিরোধিতা করে বলেছিলেন, “সমাজ সংস্কারাভিপ্রায়ে নাটক প্রণীত হইলে নাটকে নাটকত্ব থাকে না।” বঙ্কিমচন্দ্রই ভারতমাতাকে চিত্রিত করেছিলেন হিন্দুদেবীর রূপ কল্পনায় যা মেনে নেওয়া মুসলমানদের কাছে ধর্মীয় কারণে ছিল অসম্ভব। তিনিই এভাবে ভারতবর্ষে দ্বিজাতিতত্ত্বের বিষবৃক্ষকে পালন ও পুষ্ট করতে সাহায্যকারীর ভূমিকা গ্রহণ করেননি কি?
দীনবন্ধু মিত্র চরম সাহসিকতার পরিচয় দিয়ে ‘নীলদর্পণ’ রচনা করলেও এই নাটকের ভূমিকাতেই ব্রিটিশ সম্রাজ্ঞী মহারানি ভিক্টোরিয়ার জয়গান গেয়ে এবং ব্রিটিশ পার্লামেন্টের প্রশস্তি গেয়ে রাজভক্তির যে পরিচয় দিয়েছিলেন, তাকেও তো অস্বীকার করার উপায় নেই ।
স্বামী বিবেকানন্দকে যতই যুক্তিবাদী ও প্রগ্রতিবাদী বলে প্রচার করা হোক না কেন তার বিজ্ঞান বিরোধী, যুক্তি বিরোধী, স্ববিরোধী চরিত্র তাতে বিন্দুমাত্র বদলায় না। বিবেকানন্দ রচনাবলি শুধুমাত্র তাকে সাজিয়ে না রেখে তাতে চোখ বোলালেই এমন অজস্র উদাহরণ সাধারণ দৃষ্টিতেও ধরা পড়বে। তিনি যেমন জাত-পাতের বিভেদের সমর্থক ছিলেন তেমনই সমর্থক ছিলেন সতীদাহ প্রথার । স্বামীজির কথা মতো সতীরা মৃত্যুর পর ‘অমরলোকে প্রস্থান করেছেন। বিধবা বিবাহের ঘোর বিরোধী স্বামী বিবেকানন্দের কথায়, “আমি এখনো এমন কোনো জাতি দেখিনি, যার উন্নতি বা শুভাশুভ বিধবাদের পতিসংখ্যার উপর নির্ভর করে।” ভালোবাসার মধ্য দিয়ে পতি বা পত্নী নির্বাচনের ফলে “পাশবপ্রবৃত্তির পরিতৃপ্তির চেষ্টা সমাজে অবাধ বিস্তার লাভ করে, এর ফল নিশ্চয় অশুভ হবে— দুষ্ট প্রকৃতি, অসুর ভাবের সন্তান জন্মাবে” বলে বিবেকানন্দ মত প্রকাশ করেছেন। প্রচারে প্রাজ্ঞ স্বামীজির শিক্ষা বিষয়ে বক্তব্য কী? তাঁর কথায়, “যত কম পড়বে তত মঙ্গল। গীতা ও বেদান্তের উপর যেসব ভাল গ্রন্থ আছে সেগুলি পড়। কেবল এইগুলি হলেই চলবে।” স্বামীজির উপদেশকে মানব সমাজ মহাদর্শ হিসেবে নিজ জীবনে গ্রহণ করলে শিল্প-সাহিত্য-বিজ্ঞান ইত্যাদি বিষয়ের অগ্রগতি হত স্তব্ধ। জিজ্ঞাসু মন সৃষ্টির বদলে জ্ঞানের অনড়তায় আবদ্ধ থাকাকেই যিনি জীবনে পরম কাম্য জ্ঞান করেন, থাকে যাঁরা রেনেসাস যুগের পুরোধা বলে চিহ্নিত করেন, তাঁদের বিবেচনা-শক্তি বিষয়েও সন্দেহ দেখা দেয়, জ্ঞানস্পৃহাকে দ্বিধাহীন ভাষায় নিন্দা করে স্বামীজি বলেছেন, এ “অত্যন্ত চিত্তবিক্ষেপ ও ভ্রম সৃষ্টি করে”। আরও বলেছেন, “গ্রন্থ দ্বারা জগতে ভাল অপেক্ষা মন্দ অধিক হইয়াছে।” জাতিভেদ প্রথাকে সমর্থন জানিয়ে স্বামীজি বলেছেন, “জাতিভেদ আছে বলেই ত্রিশ কোটি মানুষ এখনো খাবার জন্য এক টুকরো রুটি পাচ্ছে।” আদর্শ জীবনচর্যার পথ নির্দেশ দিয়ে স্বামীজি জানিয়েছেন, “ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় ‘দেব’ ও ‘দেবী’ লিখিবে, বৈশ্য ও শূদ্রেরা ‘দাস’ ও ‘দাসী’।”
ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে সংঘর্ষের প্রতিটি সম্ভাবনাকে সযত্নে এড়িয়ে গিয়েছিলেন পরাধীন দেশের এই চিন্তা-নায়কটি। লুণ্ঠনকারী ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধাচারণ চিন্তাকে স্থান না দেওয়ার কারণ সম্ভবত দেশীয় রাজাদের উপর স্বামীজির অতি-নির্ভরতা। রাজারা ও জমিদার শ্রেণি ব্রিটিশ সরকারের অনুগত হওয়ার দরুন স্বামীজির পক্ষে ব্রিটিশ শক্তির বিরোধিতা স্বার্থবিরোধী হয়ে পড়েছিল। তাই তিনি তৎকালীন রাজনৈতিক আন্দোলনকে স্রেফ ‘বাঁদরামি’ বলে নিন্দা করেছিলেন।
স্বামী বিবেকানন্দের চোখে হিন্দুত্ব ও ভারতীয়ত্ব ছিল সমার্থক। বহু-ধর্মাবলম্বীদের দেশে কোনও একটি বিশেষ ধর্ম যে আদৌ জাতীয়তাবাদের ভিত্তি হতে পারে না, এই সত্যকে অস্বীকার করে তিনি বেদান্তকে হাতিয়ার করে হিন্দু-জাতীয়তাবাদের সৃষ্টি করেছিলেন।
এমন সব চিন্তাধারার নায়ককে যদি ‘প্রগতি বিরোধী’ না বলে ‘প্ৰগতিবাদী’ বলা হয়, তাহলে ‘প্রগতি’ শব্দের অর্থই পালটে যায় না কি?
একটি পরাধীন দেশে অধীন প্রভুর বিরোধিতা করাটাই কোনও ব্যক্তি বা আন্দোলনের পক্ষে প্রগতিশীলতা-বিচারের মূল পরিমাপক হওয়া উচিত। যাঁরা ভারতবর্ষের অথাকথিত রেনেসাঁস যুগের পুরোধাদের প্রতি সমর্থন জানিয়ে বলেন, “উনবিংশ শতাব্দীতে ভারতবর্ষে ব্রিটিশ শাসনকে সমর্থন জানানোই ছিল প্রগতিশীলতার লক্ষণ, কারণ ব্রিটিশ শাসনই ভারতীয় অনড় সমাজজীবনে গতি এনেছিল”, তাদের যুক্তিকে মেনে নিলে বলতেই হয় সবচেয়ে বড় প্রগতিশীল হিসেবে পূজিত হওয়া উচিত বিশ্বাসঘাতক মিরজাফরের। কারণ তিনিই এদেশে ব্রিটিশ-শাসন প্রতিষ্ঠায় সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। একই সঙ্গে আমাদের সমর্থন জানাতে হয় সেইসব উপনিবেশিক শক্তিকে যারা গত কয়েক শতক ধরে তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোকে নিজেদের থাবার তলায় রেখে শোষণ চালিয়ে গিয়েছে ও যাচ্ছে। কারণ, একই ভাবে ঔপনিবেশিক শক্তির অধীন দেশগুলোর সমাজ জীবনে কিছু গতি যুক্ত হয়েছিল সাম্রাজ্যবাদীদের অনুপ্রবেশে।
বাস্তবিকই কি আমরা উন্মাদের মতো আচরণ করে সমর্থন জানান ঔপনিবেশিক ও সাম্রাজ্যবাদী শক্তির দ্বারা তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোতে নগ্ন লুণ্ঠন চালিয়ে যাওয়াকে? এ সমর্থন যদি যুক্তিহীন বলে ত্যাজ্য হয়, তবে তথাকথিত রেনেসাঁস যুগের তথাকথিত মনীষীদের প্রতি সমর্থন ও ভক্তিকেও বর্জন করতেই হয় ৷ সঠিক মূল্যায়ন ও নিরপেক্ষতার নিরিখে ‘দেশপ্রেমিক’ও ‘দেশদ্রোহী’দের চিহ্নিত করতে না পারলে, হুজুরদের ও সাম্রাজ্যবাদীদের দালালদের এবং বিরোধী সংগ্রামী চরিত্রদের চিনতে না পারলে সাংস্কৃতিক বিপ্লব এবং সর্বাত্মক বিপ্লবের স্বপ্নে ধ্বংসের সম্ভাবনার বীজ থেকেই যাবে। আজ মুখোশ টেনে নামাবার সময় এসেছে। মুখোশের আড়ালের মুখগুলোকে চিনে নেওয়ার সময় এসেছে। আজ যারা মুখোশ তৈরির শিল্পীর ভূমিকায় রয়েছে— তাদেরও চিনে নেওয়ার সময় এসেছে। সাংস্কৃতিক বিপ্লবের যে কল্লোল ধ্বনি শোনা যাচ্ছে তাতে গতি সঞ্চারিত করতে আবেগের পরিবর্তে যুক্তির নিরিখে আন্দোলনের ও ব্যক্তির চরিত্রের বিচার অপরিহার্য হয়ে পড়েছে।
গণতন্ত্রঃ একটি মোরগের কাহিনি
আমাদের দেশ বৃহত্তম ‘গণতান্ত্রিক’ দেশ। এ দেশে প্রতিটি মানুষের সমান অধিকার। সংবিধান সেই অধিকার রক্ষায় সদা সতর্ক। এখানে লৌহযবনিকার অন্তরালে মানুষের কণ্ঠ রুদ্ধ করা হয় না। দেশের মানুষ খাঁচার পাখি নয়, বনের পাখির মতোই মুক্ত। এদেশে সর্বোচ্চ পদাধিকারী রাষ্ট্রপতির আর ওড়িশার কালাহান্ডির মানুষগুলো একই অধিকার ভোগ করে, চুলচেরা সমান অধিকার ।
এই ধরনের প্রতিটি কথাকে বর্বর রসিকতা বলেই মনে হয় যখন দেখি, কালাহান্ডির মানুষগুলো দিনের পর দিন ক্ষুধার আগুনে জ্বলতে জ্বলতে প্রতিবাদহীনভাবে মৃত্যুকে মেনে নিল, আর তারই সঙ্গে মৃত্যু ঘটল একটি গণতান্ত্রিক দেশের মানুষদের বেঁচে থাকার অধিকারের। এ-সব আপনজন হারা বহু মানুষের হৃদয়কে দুমড়ে-মুচড়ে রক্তাক্ত করে। এই রক্তাক্ত হৃদয়গুলোই দাউ দাউ করে জ্বলে ওঠে, যখন দেখে শোষকশ্রেণির কৃপায় দিতে বসা কতকগুলো রাজনীতিক ওই একই সময় রাষ্ট্রপতির গণতান্ত্রিক অধিকারসম্মতভাবে দেওয়া ছত্রিশ কোর্সের ভোজসভায় কবজি ডুবিয়ে খাওয়ার গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা করতে করতে ভারতবর্ষকে ‘সুমহান গণতন্ত্রের দেশ’, ‘সর্ব বৃহৎ গণতান্ত্রিক দেশ’ ইত্যাদি বলে কদর্য বর্বর রসিকতা করছে।
প্রতিটি গণতান্ত্রিক অধিকারই বিড়লা, আম্বানিদের সঙ্গে সঙ্গে
দেওয়া হয়েছে রাস্তার ভিখারিটিকে পর্যন্ত। পার্থক্য শুধু
রাষ্ট্রশক্তির অকরুণ সহযোগিতায় বিড়লা, আম্বানিদের
অধিকারের হাত দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হয়েছে।
ওদের নিয়ে ব্যস্ত থাকতে গিয়ে ভিখারির
অধিকার রক্ষা করার ব্যবস্থা করতেই
শুধু ভুলে গেছে রাষ্ট্রশক্তি—এই যা।
১৬ সেপ্টেম্বর ‘৯১ আনন্দবাজার পত্রিকার প্রথম পৃষ্ঠায় প্রকাশিত একটা খবরের দিকে আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। খবরটাকে ছোট্ট করে নিলে দাঁড়ায় এই—পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুলিশের এক বড়কর্তার বাগান আছে ঝাড়গ্রামের জিতুশোল মৌজায়। সেই বাগান থেকে তিনটি আমগাছের চারা চুরি যাওয়ায় রাজ্য পুলিশবাহিনী তাণ্ডব চালিয়েছে ওই অঞ্চলে। পুলিশের নৃশংস অত্যাচারে জিতুশোল মৌজার তিনশো গ্রামবাসী জঙ্গলে পালিয়ে গিয়েছেন। একটিও বয়স্ক পুরুষ নেই গ্রামে। তবু গ্রামবাসীদের ওপর চলেছে পুলিশের ভীতিপ্রদর্শন । অনেকেই থানা-লকআপে আটক রেখে দিনের পর দিন পেটানো হচ্ছে। আর পুলিশের বড়কর্তার বাগান পাহারা দিতে রাজ্যের জনগণের টাকায় পালিত পুলিশ একটি স্থায়ী চৌকি বসিয়েছে।
একবার উত্তেজিত মাথাকে ঠান্ডা করে ভাবুন তো –একটি গরিব লোকের বাগান থেকে তিনটে আমগাছের চারা চুরি গেলে থানায় রিপোর্ট লেখাতে গেলে পুলিশ তার সঙ্গে কী ব্যবহার করবে? আমচারা চোর ধরে দেওয়ার বেয়াদপি আবদার শুনে থানার মেজবাবু হয় বেজায় রসিকতা ভেবে অট্টহাসিতে ফেটে পড়বেন, নতুবা বেয়াদপটাকে এক দাবড়ানিতে থানা-ছুট করতে বাধ্য করবেন।
কিন্তু রাজ্য-পুলিশের বড়কর্তার বাগান থেকে মাত্র তিনটি আমচারা চুরি যেতেই গণতান্ত্রিক দেশের নাগরিকদের গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষায় অতন্দ্র-প্রহরী পুলিশবাহিনী পাগলা-কুকুরের মতোই ঝাঁপিয়ে পড়ল জিতুশোলের মানুষগুলোর ওপর। পুলিশি অত্যাচারে তিনশো মানুষ জঙ্গলের রাজত্ব থেকে বাঁচতে জঙ্গলে আশ্রয় নিল। ধরে নিলাম, ওই গ্রামবাসীদের মধ্যেই রয়েছে এক, দুই বা তিনজন আমরা চার চোর। ধরে নিলাম, পুলিশ তাদের ধরেও ফেলল। ফেলুক, খুব ভালো কথা। তারপর পুলিশের কর্তব্য চোরটিকে বা চোরদের বিচার বিভাগের হাতে তুলে দেওয়া। অপরাধ প্রমাণে শাস্তি যা দেওয়ার তা দেবেন বিচার বিভাগ। ওই বিচারাধীন চোর বা চোরদের পেটাই করার কোনও অধিকার আমাদের দেশের গণতন্ত্রে তো পুলিশদের হাতে তুলে দেওয়া হয়নি।
জিতুশোল মৌজার এক দুই বা তিনজন সম্ভাব্য অপরাধীর ওপর পুলিশি অত্যাচার নেমে আসেনি, পুলিশবাহিনী বর্বর গুন্ডামি চালিয়েছিল তামাম গ্রামবাসীদের ওপর। গ্রামবাসীদের একটিই অপরাধ বড় কর্তার বাগান এলাকায় তাদের বাস।
আইন ভাঙা অপরাধ। আইনের রক্ষকদের আইন ভাঙা আরও বড় অপরাধ। পুলিশের ইউনিফর্ম পরা ওইসব বর্বর গুন্ডাদের বিরুদ্ধে আইন আদৌ কঠিন হতে পারবে? তা যদি না পারে তবে অত্যাচারিত মানুষগুলো, যুক্তিবাদী মানুষগুলো, অনপুংসক মানুষগুলো কী করে বিশ্বাস করবে—আমাদের দেশের গণতন্ত্রে রাজ্য-পুলিশের বড়কর্তার ও একজন দরিদ্র গ্রামবাসীর সমান গণতান্ত্রিক অধিকার ?
পুলিশের সামান্য বড়কর্তার সঙ্গে সাধারণ অধিকারের পার্থক্য যদি এমন আশমান-জমিন হয়, তবে মন্ত্রী-টন্ত্রীদের সঙ্গে এবং মন্ত্রী বানাবার মালিক অর্থকুবেরদের সঙ্গে গরিব মানুষগুলোর গণতান্ত্রিক অধিকারের পার্থক্য যে সীমাহীন হবে, এই তো প্রকৃত সত্য।
এ-দেশে অনেক বিত্তবানেরাই, অনেক জোতদারেরাই নিজস্ব গণতন্ত্রের হাতকে আরও বেশি দীর্ঘ করতে বাহিনী পোষে। এইসব বাহিনী বা সেনাবাহিনীর নামও নানা বিচিত্র ধরণে— ভূমিসেনা, লোরিকসেনা, ব্রাহ্মর্ষিসেনা, এমনি আরও কত নামেই রয়েছে এইসব সংগঠিত হিংস্র সেনাবাহিনী। সেইসব বাহিনীর হাতে নিত্যই নিপীড়িত, খেটে খাওয়া মানুষদের গণতান্ত্রিক অধিকার লুণ্ঠিত হচ্ছে। সামান্য ইচ্ছায় এরা গ্রামকে গ্রাম পুড়িয়ে ছারখার করে দেয়, লুটে নেয় মহিলাদের লজ্জা। আর নির্লজ্জের মতো সরকার দেখেও অন্ধ হয়ে থাকে। এই উগ্রপন্থী নরখাদকদের কঠোর হাতে দমন করতে কখনোই তো এগিয়ে আসে না সরকার? কোন্ গণতান্ত্রিক অধিকারে এই সব সেনাবাীহিনী পুষে চলেছে হুজুরের দল? নিপীড়িত মানুষদের দাবিকে দাবিয়ে রাখতে ওদের সেনাবাহিনী পোষা যদি গণতন্ত্র-সম্মত হয়, উগ্রপন্থা না হয়, তবে অত্যাচারিত মানুষদের অধিকার রক্ষার জন্য সেনা গঠন অগণতান্ত্রিক ও উগ্রপন্থা হিসেবে বিবেচিত হতে পারে না।
আমাদের দেশের গণতন্ত্র-বীরভোগ্যার গণতন্ত্র। যার যত বেশি ক্ষমতা, যত বেশি অর্থ, যত বেশি শক্তি, তার তত বেশি বেশি গণতন্ত্র। শোষকদের অর্থে গদিতে আসীন হয়ে শোষক ও শোষিতদের সমান গণতান্ত্রিক অধিকার বিলানো যায় না। শাসক ও শোষকরা শুধু এই অধিকারের সীমা ভঙ্গই করে পরম অবহেলে; আর শোষিতদের অধিকার বার বার লাঞ্ছিত হয়, লুণ্ঠিত হয়—এ অতি নির্মম সত্য । আপনার দৈনন্দিন অভিজ্ঞতার সঙ্গে মিলিয়ে দেখুন; তাহলেই দিনের আলোর মতন পরিষ্কার হয়ে যাবে ‘গণতন্ত্র’ আছে দেশের সংবিধানে ও বইয়ের পাতায়, গরিবদের জীবনে নয়।
যে দেশের মানুষের দু’বেলা পেট ভরে খাওয়ার অধিকার নেই,
বেঁচে থাকার অধিকার নেই, চিকিৎসার সুযোগ-সুবিধে গ্রহণের
অধিকার নেই, শিক্ষালাভের সুযোগ-সুবিধে গ্রহণের অধিকার
নেই সেখানে বিড়লা, আম্বানি, রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী আর
গরিব মানুষগুলোর সমান গণতান্ত্রিক অধিকারের
কথা যারা বলে, তারা শয়তানেরই
দোসর—এটুকু নির্দ্বিধায়
বলা যায়।
গণতন্ত্র মানে কি শুধুই ভোট দেওয়ার অধিকার? সেটাই বা কজনের আছে? ছাপ্পা ভোট, বুথ দখল, চতুর রিগিং সেই অধিকারে তো অনেক দিনই থাবা বসিয়েছে।
তারপরও যদি ভোট দেওয়ার অধিকারের প্রসঙ্গ টেনে কেউ বলেন এই দেশের মানুষই কখনও ইন্দিরাকে তুলেছেন কখনও নামিয়েছেন, কখনও রাজীবকে সিংহাসনে বসিয়েছেন, কখনও বা ছুঁড়ে ফেলেছেন, কখনও এনেছেন ভি.পি-কে, কখনও বা পি.ভি-কে; তাঁদের আবারও মনে করিয়ে দেব পরম সত্যটি, অভিজ্ঞতার সঙ্গে মিলিয়ে নিতে বলব কথাটি – মন্ত্রী যায়, মন্ত্রী আসে এদের বহু অমিলের মধ্যে একটাই শুধু মিল—এঁরা প্রত্যেকেই শোষকশ্রেণির কৃপাধন্য, পরম সেবক। এরা শোষকদের শোষণ বজায় রাখার ব্যবস্থা করে দেওয়ার বিনিময়ে আখের গোছান।
আর একটি ঘটনার দিকে আপনাদের দৃষ্টি একটু ফিরিয়ে নিয়ে যাচ্ছি। ১৪ আগস্ট ‘৯১ আনন্দবাজারে তিনটি সংবাদ প্রকাশিত হয়েছিল, যাদের শুরু একই রকম হলেও পরিণতি ভিন্নতর। সংবাদ এক : সৌদি আরবের এক বৃদ্ধ এক নাবালিকাকে বিয়ে করার অভিযোগে গ্রেপ্তার হয়েছে। আদালত ওই বিচারাধীন আসামিকে পনেরো দিন পুলিশ হাজতে রাখার নির্দেশ দিয়েছে। সংবাদ দুই : ওড়িশার জনতা দলের বিধায়ক তথাগত শতপথী একটি নাবালিকাকে ফুঁসলিয়ে ভুবনেশ্বর থেকে পুরী নিয়ে যান এবং নাবালিকা অপহরণের অভিযোগে পুলিশ তথাগতকে গ্রেপ্তার করে। ওড়িশার বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী জনতা দলের শ্রীবিজু পট্টনায়কের হস্তক্ষেপে তাঁর দলের বিধায়ক তথাগতর উপর থেকে সমস্ত অভিযোগ তুলে নেওয়া হয়। তথাগত অবশ্য গর্বের সঙ্গে স্বীকার করেছেন ‘এমন মেয়ে ফুঁসলানো’ তাঁর জীবনে ‘এই প্রথম নয়।’ সংবাদ তিন : ত্রিপুরার মন্ত্রী জহর সাহা স্ত্রী থাকা সত্ত্বেও অবিবাহিত মহিলার সঙ্গে অসামাজিক কাজে লিপ্ত থাকার সময় মহিলাটির পাড়ার লোকেদের হাতে ধরা পড়েন। জহর সাহাকে মন্ত্রিসভা থেকে বরখাস্ত করালেন ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী সুধীররঞ্জন মজুমদার। জহর ঘোষণা করলেন, তাঁকে মন্ত্রিসভার ফিরিয়ে না নিলে মুখ্যমন্ত্রীসহ অন্যান্য মন্ত্রীদের দুর্নীতি সম্পর্কিত প্রামাণ্য দলিল তুলে দেবেন সংবাদপত্রের হাতে। শঙ্কিত ও জহর ভয়ে কম্পিত মুখ্যমন্ত্রী ওই দিনের সংবাদে জহর সাহাকে ‘ধোয়া তুলসী পাতা’ বলে ঘোষণা করে ইঙ্গিত দিয়েছেন জহরকে মন্ত্রিসভায় ফিরিয়ে নেবেন ।
আরবের শেখ, তথাগত শতপথী ও জহর সাহার খবর পড়ে যদি ভারতের কোনও ভবিষ্যৎ নাগরিক তার শিক্ষককে প্রশ্ন করে বসে— ভারতবর্ষ কেমন গণতন্ত্রের দেশ, দুর্নীতিপরায়ণ লম্পটরা রাজনীতিক হওয়ার সুবাদে আইনকে লাথি কষিয়ে ফুটবল খেলে আর খুঁটির অভাবে তার চেয়ে লঘু অপরাধে জেলেপচে শেখ? কী জবাব দেবেন শিক্ষক? সত্যি কথাটুকু বলতে গেলে যে দরাজ বুকের পাটা প্রয়োজন তা এই চাটুকার ধান্দাবাজ ও ক্লীবে ছেয়ে ফেলা দেশে কতজনের আছে? শিক্ষকরা আজ যদি সত্যির থেকে মুখ ঘুরিয়ে থাকে, ছাত্ররা যারা দেশের ভবিষ্যৎ তারা কী শিখবে?
জানি-দুর্নীতি যেখানে অসীম, দলবাজি যেখানে চূড়ান্ত, অন্যায়ের সঙ্গে আপস যেখানে বেঁচে থাকার শর্ত—সে দেশে সত্যি বলাটা, সত্যি শেখানোটা চূড়ান্ত অপরাধ, ‘উগ্রপন্থী ‘দেশদ্রোহী’ বলে দেগে দেওয়ার পক্ষে যথেষ্ট। তবু ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কথা ভেবে শিক্ষার মহান দায়িত্ব মাথায় তুলে নেওয়া মানুষদেরই তুলে নিতে হবে মানুষ গড়ার দায়িত্ব, নতুন প্রজন্মের মানুষ গড়ার দায়িত্ব ।
মানবাধিকারঃ এসো মুক্ত কর
কলকাতার বড়বাজারে কোনও দুই উদ্ধত লরিচালক ভেবে নিয়েছিল গাড়ির কাগজ-পত্তর ও ড্রাইভিং লাইসেন্স ঠিক থাকলে এবং বে-আইনি মালপত্তর না বয়ে আইন মেনে গাড়ি চালালেই বুঝি সব ঠিক-ঠাক। পুলিশরা তাদের চা খাওয়ার জন্য মাত্তর কয়েকটি হাজার টাকা চাইতেই লরির সামান্য ড্রাইভার সামান্য কথাই বলেছিল— বে-আইনি কিছু তো করিনি! আইন ভাঙলে কেস্ দিন।
বেয়াদপের মতো এমন কথা বলায়, এমন মানুষের অধিকার বুক ঠুকে দাবি করায়, পুলিশরা ওদের থানায় নিয়ে গিয়ে বুটের লাথিতে বুক ভেঙে দিয়েছিল।
লরির ড্রাইভারদের জানা উচিত ছিল তার আজব দেশের আজব আইন-কানুন। এখানে বাস (সরকারি বাস বাদ), মিনিবাস, লরি প্রত্যেকের চাকা ঘোরাবার অধিকার কিনতে হয় পুলিশের সঙ্গে রফা করে। কোনও মানুষের অধিকার নেই পুলিশ ও রাজনৈতিক মস্তানদের সঙ্গে রফা না করে ফুটপাত দখল করে আনাজ বেচে কি কামিজ বেচে নিজের বেঁচে থাকার খোরাক তুলবে। এখানে কোনও মানুষ মানবাধিকারের ধুয়ো তুলে পারবে না, রাজনীতির দাদাদের হাতে কিছু তুলে না দিয়ে শেষ সম্বল ভিটে-মাটিটুকুও বিক্রি করতে। ভাড়াটে তুলবেন, ভাড়াটে বসাবেন—সর্বত্র আপনার মানবাধিকারকে ছেঁটে ছোট করতে হবে পাড়ার রাজনীতিকদের সঙ্গে আপস করতে গিয়ে। আপনি আপনার মানুষের অধিকারে কাজ পাবেন না ইনকামট্যাক্স, সেলসট্যাক্স, মোটর ভেহিকলস্ কোর্ট এমনি হাজারো প্রতিষ্ঠানে। মানবাধিকারকে ছেঁটে ফেলে কিঞ্চিত মুদ্রা হাজির করলে তবেই কাজ মেলে, মেলে ব্যাঙ্ক ঋণ, পাস হয় বিল, পাওয়া যায় টেন্ডার, পাস হয় দূরর্শনের কাহিনি, কলেজের অ্যাডমিশন, কি নয় ?
মানুষ আজ আপস করতে করতে পাপোশ হয়ে পড়ায় তার অধিকারটুকুও দাবি করতে ভুলেছে। আর তাই আমাদেরই অর্থে আমাদের সেবার নামে পালিত সাংসদ, বিধায়ক, পুলিশ প্রত্যেকেই সাধারণভাবে দুর্বিনীত, হাতে মাথা কাটে। কখনও কোনও ন্যায্য দাবি আদায় আপনাকে সাহায্য করলে ভাবটা এমন দেখায়, যেন দয়া করছে, তার ঘর থেকে সাহায্য তুলে দিচ্ছে। ওদের প্রায় সকলেরই ভাবটা এমন, যেন জনগণের সেবক ওরা নয়, দণ্ডমুণ্ডের কর্তা। বিভিন্ন দেশের সংবিধানেই সে দেশের মানুষদের কিছু অধিকার দেওয়া হয়েছে। রাষ্ট্রশক্তি বা সরকার এই যে অধিকারগুলো দেশের মানুষদের দিয়েছে, এগুলো ওরা ভিক্ষা দেয়নি, কোনও অধিকারই সংগ্রাম ছাড়া আসেনি। যে সব অধিকার সংগ্রামের মধ্য দিয়ে আদায় করা গেছে তার বাইরেও বহু অধিকারই অধরা রয়ে গেছে, যেগুলো পাওয়ার জন্য মানুষ লড়াই চালিয়েই যাচ্ছে। মানবিকতার বিকাশের জন্য মানুষের যে যে অধিকার একান্তই প্রয়োজন, তা আজও দেয়নি আমাদের দেশ ভারত-এর রাষ্ট্রশক্তি বা সরকার। আজও এ-দেশের মানুষের অধিকার নেই মাথা গোঁজার ছোট্ট ঠাঁইটুকু পাওয়ার। দু-মুঠো ভাত—দু’টো রুটি—একটু ত্যানা জোটাবার জন্য চাকরির অধিকারও আমাদের সংবিধানে নেই। অধিকার নেই সাংসদরা বা বিধায়করা জন-বিরোধী কাজে জড়িত থাকলে বা অঞ্চলের দিকে বিন্দুমাত্র দিপাত না করলেও তাকে ফিরিয়ে আনার। আমরা আজ যে মানুষের অধিকারগুলো রাষ্ট্রের কাছ থেকে পেয়েছি তা স্পষ্টতই খর্বিত অধিকার।
কিন্তু এই আদায়করা খর্বিত অধিকারের কতটুকু আপনি ভোগ করতে পারেন? শুরুতে অতি সংক্ষিপ্ত যে কটি উদাহরণ টেনেছি তারই সূত্র ধরে আপনি কাঁটায় কাঁটায় বিচারে নামুন, দেখবেন আপনার অধিকার প্রতিটি দিন কী বিপুলভাবে লঙ্ঘিত হচ্ছে এবং আমার সংক্ষিপ্ত ফদটা আপনার অভিজ্ঞতার সঙ্গে যুক্ত হয়ে দীর্ঘতর হচ্ছে। এরপরও একটা কথা থেকে যায়, আপনার স্বাধীনতার অধিকার ভোগ করতে তখনই পারবেন এবং ভোগ না করতে পারলে সেই বিষয়ে অন্তত প্রতিবাদ জানাতে পারবেন, যখন জানবেন কী কী অধিকার আপনার আছে।
তারই সঙ্গে এও ঠিক, আপনার-আমার যে অধিকারের জন্য
সরকার বিপন্ন বোধ করবে, সেই অধিকারই কেড়ে
নেবে যে কোনও অজুহাতে।
ভারতীয় সংবিধানের প্রচলিত আইন অনুসারে অভিযুক্তের (অভিযুক্তকে কখনোই আসামি বলা যায় না) অপরাধ প্রমাণের দায়িত্ব অভিযোগকারীর। কেউ যদি হত্যাকারী, বেআইনি অস্ত্র বহনকারী অন্তর্ঘাতমূলক কাজ-কর্মের সঙ্গে যুক্ত বলে প্রমাণিত হয়, তবে তাদের বিরুদ্ধে নানা ধরনের শাস্তির বিধান আমাদের সংবিধানে আছে। কিন্তু এটা কি আপনি মেনে নেবেন আজ পুলিশ আপনাকে যদি হত্যার অপরাধে ধরে বলে, “আপনি হত্যা করেছেন ‘ক’ বাবুকে, সাক্ষী আছেন কয়েকজন, এবং আপনিই প্রমাণ করুন আপনি আপনার পাশের পাড়ার ক’বাবুকে হত্যা করেন নি?”
আপনি হয় তো বললেন, “আমি খুনের সময় ক’বাবুর পাড়াতেই যাইনি।” অমনি দেখলেন আপনাকে বলা হল, “আপনার বিরুদ্ধে তিনজন সাক্ষী আছে। তার একজন জানিয়েছে আপনার একটা বে-আইনি অমুক রিভলবার আছে। ক’বাবুকে ওই জাতীয় রিভলবার থেকেই হত্যা করা হয়েছে। ওই রিভলবার পুলিশের হাতে তুলে দিলে পুলিশ পরীক্ষা করে দেখতে পাবে ঠিক ওই রিভলবার থেকেই গুলি চালানো হয়েছে কি না?”
আপনি বললেন, “অমন কোনও বেআইনি রিভলবার তো আমার নেই?” পুলিশ বলল, “আপনি প্রমাণ করুন আপনার ওই রিভলবার নেই।” এছাড়াও পুলিশ জানাল, “আপনি যে গুলি চালিয়েছেন, তার দু’জন প্রত্যক্ষদর্শী রয়েছে। তারা সাক্ষ্যও দিয়েছে।”
আপনি বললেন, “এ তো উদ্ভট মিথ্যে। তখন আমি আমার বাড়িতেই ছিলাম, সাক্ষী আমার স্ত্রী ও ছেলে।”
পুলিশ বলল, “এমন কেসে স্ত্রী ও ছেলের সাক্ষ্যর কোনও দামই নেই।” আপনি বললেন, “আমার বিরুদ্ধে সাক্ষী কারা?”
পুলিশ জানাল, “নাম, পরিচয় জানানো যাবে না।”
বললেন, “ঠিক আছে, তাই সই। ওদের মুখ ঢেকে নিয়ে আসুন, অথবা আমার চোখ দিন বেঁধে। আমি ওদের জেরায় জেরায় জেরবার করে বুঝিয়ে দেব মিথ্যে সাক্ষী দেওয়ার মজাটা। ”
পুলিশ বলল, “না, সাক্ষীদের জেরা করতে দেব না।”
হতাশ আপনি অন্ধকার দেখলেন, চেঁচালেন, “এভাবে তোমরা আমার বেঁচে থাকার অধিকার কেড়ে নিতে পারো না।”
আপনার কথা বিচারক ও পুলিশ ছাড়া কেউই শুনল না, জানল না, কারণ আপনার বিচার হচ্ছে গোপনে, এখানে আর কারও প্রবেশ নিষেধ।
আপনি আপনার নির্দোষিতা কোনওভাবেই প্রমাণ করতে পারছেন না, তাই আপনার শাস্তি হয়ে গেল। আপনি ফাঁসিতে চড়লেন ।
এই সমস্ত শুনে আপনি হয় তো চেঁচাবেন, “এমনটা আমাদের দেশে হয় না, ওসব অসভ্য দেশে হয়। ডিক্টেটররা নিজেদের গদিকে মসৃণ রাখতে রাষ্ট্রদ্রোহিতার অপরাধে যাদের ধরে তাদের আইনের নামে হত্যা করতেই এমন প্রহসন করে।”
তখন আমি বলব, আপনার ধারণাকে বিশাল অট্টহাসিতে খানখান্ করে দিয়েছে আমাদের দেশেরই শাসককুল। ‘সন্ত্রাসবাদী’ সিলমোহর দেগে দিয়ে আপনাকে ধরলে আপনাকেই প্রমাণ করতে হবে আপনি বোম মারেননি, অস্ত্র পাচার করেননি বা খুন করেননি ইত্যাদি। আপনার বিরুদ্ধে যারা সাক্ষ্য দিয়েছে তাদের নাম পরিচয় জানতে পারবেন না, তাদের জেরা করতেও না। আর ‘সন্ত্রাসবাদী’ ছাপ পড়লে Terrorist and Disruptive Activities (Pre- vention) Act (TADA) অনুসারে ন্যূনতম সাজা ১০ বছর জেল। আইনের প্রচলিত নিয়ম থাকা সত্ত্বেও এমন অদ্ভুত, বীভৎস, মানবাধিকার লঙ্ঘনকারী আইন আজও ভারতে চালু আছে।
এক সময় এমন মানবিকতা বিরোধী আইনের প্রতিবাদ করেছিল পশ্চিমবঙ্গের যুক্তফ্রন্ট সরকারের গণ-প্রতিনিধিরা। কিন্তু এই কালা আইনকেই এই পশ্চিমবঙ্গ সরকারই প্রয়োগ করল গোর্খাল্যান্ড আন্দোলন ঠেকাতে। বামফ্রন্ট সরকার বিপন্ন বোধ করলে মানবিক অধিকারেও থাবা বসাবে। প্রগতিশীলতার মুখোশ ছিঁড়ে প্রকাশিত করল সেই সত্য— রাজা আসে, রাজা যায়, ক্ষমতা হাত পাল্টায়; ওরা সিংহাসনে পাছা রেখেই হাঁক পাড়ে— হালুম; হাড়-হাভাতে তেমনই আছে, চোখ মেলতেই মালুম।
আমাদের, সাধারণ মানুষদের বিশ্বাসের অণুতে পরমাণুতে মিশে রয়েছে, ‘পুলিশে ছুঁলে আঠারো ঘা’। পুলিশ অভিযুক্তকে থানায় নিয়ে গিয়ে পৌঁছিয়ে বাবার নাম না ভুলিয়ে ছেড়েছে, এমন অভিজ্ঞতা আমাদের দেশের শহর-গাঁয়ের মানুষদের হয়নি। গোটা দেশেরই একটি রাজ্য পশ্চিমবাংলাকে প্রতীক হিসেবে ধরে নিয়েই গত কয়েকটা বছরের ইতিহাসের দিকে একটু চোখ বোলাই আসুন। পশ্চিমবাংলায় শুধুমাত্র বামফ্রন্ট সরকারের আমলে এই বইটি লেখা পর্যন্ত অর্থাৎ ১৯৯২-এর নভেম্বর পর্যন্ত পুলিশ কাসট্যাডিতে (custody)) বা হেফাজতে অভিযুক্ত মারা গেছেন ১৩৬ জন। custody কথার অভিধানগত অর্থ ‘নিরাপদ তত্ত্বাবধান’, ‘নিরাপদ রক্ষণ’। সন্তান যেমন পিতা-মাতার নিরাপদ তত্ত্বাবধানে বা হেফাজতেই বড় হয় পরম নিশ্চিন্তে, তদন্ত চলাকালীন তেমন নিশ্চিন্তেই পুলিশ হেফাজতে অভিযুক্তের থাকাটা আইনমাফিক স্বাভাবিক। সেই আইনকে ভঙ্গ করে পুলিশ যে বর্বরোচিত নির্যাতন অভিযুক্তদের ওপর চালায়, তা অভিজ্ঞতাহীন মানুষদের পক্ষে কল্পনা করা একেবারেই অসম্ভব। অথচ ১৬৩ নম্বর ফৌজদারি দণ্ডবিধি মতো পুলিশ কখনওই কোনও অভিযুক্তকে মারধর তো করতে পারেই না, এমনকী, হুমকি বা ভয় পর্যন্ত দেখাতে পারে না। এই আইনটি-সহ প্রতিটি আইনের রক্ষক হল পুলিশ। একই সঙ্গে সংবিধান অনুসারে পুলিশ আইনের অধীন। অর্থাৎ কোনও অবস্থাতেই সে আইনকে ভঙ্গ করতে পারে না। ভঙ্গ করলে সেও অবশ্যই অপরাধী, শাস্তি-যোগ্য অপরাধী। কিন্তু আপনার আমার অভিজ্ঞতা কী বলে? পুলিশ নিজেই আইন মানে না। প্রতিটি মুহূর্তে আইনের রক্ষকদের হাতে আইন লঙ্ঘিত হচ্ছে। লরি আর বাসের ঘুষে সন্তুষ্ট নয়। চোরাকারবারি, ভেজালদার, ডাকাত, মস্তান, ড্রাগ ব্যবসায়ী, বিল্ডিং প্রমোটার, সবার সঙ্গেই আজ থানা ও পুলিশের দেওয়া-নেওয়ার সম্পর্ক। আইন ভঙ্গকারীরা আইনের রক্ষকদের ছত্র-ছায়ায় আইন ভাঙছে। আইনের রক্ষকরা আইনের মুখে নিত্য প্রতিটি প্রহরে লাথি কষিয়ে বেআইনি কাজের সঙ্গে যুক্ত মানুষদের রক্ষকের ভূমিকা নিচ্ছে। বার-বার তাই পুলিশকে বিভিন্ন অঞ্চলের মানুষ বয়কট করেছে জঘন্য সমাজবিরোধী বিবেচনায়, চূড়ান্ত ঘৃণায়। এলাহাবাদ আদালতের বিচারপতির ভাষায় “পুলিশ মানে সবচেয়ে সংগঠিত গুন্ডাবাহিনী। ”
প্রসঙ্গতে ফিরি—পুলিশ হেফাজতে মৃত ১৩৬ জনের জন্য কতজন পুলিশকে সরকারি শাস্তি দিয়েছে? একজনকেও না। তবে কি ওইসব মৃত্যুর জন্য পুলিশ দায়ী নয়? সকল অভিযুক্তই কি তবে আত্মহত্যা করেছিলেন? একটু চোখ বোলান পৃথিবীর আরও কিছু দেশে, এই যেমন সাউথ আফ্রিকা থেকে শুরু করে ফৌজি একনায়ক শাসিত দেশগুলোতে, দেখবেন ও-সব দেশেও পুলিশ হেফাজতে প্রচুর অভিযুক্ত মারা যান। ওরা প্রত্যেকেই আত্মহত্যা করে। তাই ও-সব দেশের পুলিশদের বিরুদ্ধে হত্যার অভিযোগ আসে না। সম্ভবত আমাদের দেশ ও ও-সব দেশের মতো অভিযুক্তরা পুলিশের অতি সুন্দর নিরাপদ তত্ত্বাবধানে থেকে রোমান্টিক হয়ে ওঠেন রাতারাতি এবং ‘মরণ রে তু হুঁ মম শ্যাম সমান’ বলে ঝপাৎ করে আত্মহত্যা করে ফেলেন। এইসব দেশের পুলিশি হেফাজতে থাকলে যে আত্মহত্যার প্রবণতা বাড়ে— এই সহজ সরল সত্যকে আমাদের আপন সরকার মেনে নিয়েছেন এবং ঘোষণা করেছেন, এই রাজ্যে মানুষের অধিকার কখনওই লঙ্ঘিত হয় না, রক্ষিতই হয়। জানি না প্রতি মুহূর্তে প্রতিটি পদে-পদে মানবাধিকার লঙ্ঘিত হওয়ার পরও এ দেশের মানুষের পদদলিত সত্তা সোচ্চারে ঘোষণা করবে কি না- “রাজা তুমি মিথ্যেবাদী।”
চাটুকার, ক্লীব ও মেরুদণ্ডহীন মানুষ তৈরির জন্য যে সংস্কৃতি হুজুরের দল সমাজে চাপিয়ে দিয়েছে, তারই পরিণতিতে আজ সংখ্যাগুরু মানুষ অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদহীন, এমনকী, অনেক সময় সমস্ত কিছু জেনে-বুঝেও মেরুদণ্ডহীন চাটুকারী মানসিকতা থেকে অথবা আখের গোছাবার লোভে শাসক ও শোষকদের শত অন্যায়কেও হাত কচলে সমর্থন জানায়। এই সমাজের সংস্কৃতির ফসল এমন বুদ্ধিজীবীই তো সংখ্যাগরিষ্ঠ যাঁরা অন্যায়ের প্রতি বিপুল জনসমর্থন দেখলে প্রতিবাদ করতে ভয় পান। এমন অনেক সমাজ-প্রতিষ্ঠিত উন্নাসিক ব্যক্তি প্রতিবাদে মুখর না হওয়ার পিছনে যুক্তি খাড়া করেন—“এ দেশের আর কিছুই হবে না।” এমন কথাও সাধারণ থেকে অসাধারণ বহু মানুষের মুখ থেকেই বেরিয়ে এসেছে আমাদেরই উদ্দেশে— “আপনাদের আন্দোলন ভালো, স্বীকার করি। কিন্তু এই দুর্নীতিতে ডুবে যাওয়া, শোষণে ছিবড়ে হয়ে যাওয়া সমাজের বিরুদ্ধে কতটুকু আপনারা করতে পারবেন? দুর্নীতি, ধর্মের শোষণ, রাষ্ট্রের শোষণ, জ্যোতিষী ও বাবাজি- মাতাজিদের রমরমা কি আপনারা কমাতে পেরেছেন ? ”
এমন নৈরাশ্যপীড়িত হয়ে বসে থাকলে সমাজ যে আরও অবক্ষয়ের সংস্কৃতির পাঁকে ডুবতেই থাকবে, তা তো বক্তাদের বক্তব্যের সূত্র থেকেই বেরিয়ে আসে। ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কথা ভেবে পৃথিবীকে সুন্দর করে গড়ে তুলতে চাইলে এক নতুন সংস্কৃতির বাতাবরণ সৃষ্টির জরুরি কাজে প্রত্যেকেরই কিছু করার আছে। আর এই গড়ার জন্যেই অবক্ষয়ী সংস্কৃতিকে ভাঙার প্রয়োজন। প্রতিটি অবক্ষয়ী সংস্কৃতির বিরুদ্ধে সোচ্চার হওয়ার প্রয়োজন, আর সেই সূত্রেই প্রয়োজন, একান্তভাবেই প্রয়োজন মানবাধিকার রক্ষার জন্য সোচ্চার হওয়ার, লড়াইয়ে নামার।
পুরোনো প্রসঙ্গে একটু ফিরে তাকাই। পুলিশ হেফাজতে ১৩৬ জন অভিযুক্তকে হত্যা করা হল। আইনের রক্ষকদের হাতেই আইন ধর্ষিত হল, মানবাধিকার একটা বিশাল তামাশায় পরিণত হল, তবু রাজ্য সরকার একজনকেও শাস্তি দিল না। যেখানে শাস্তি হয়েছে, সেখানেও দেখা গেছে অত্যাচারিতের আপনজনেদের চেষ্টায় আইনের দীর্ঘ প্রক্রিয়ার পথে এই শাস্তি দিতে বাধ্য করা হয়েছে।
গত দশ বছরে পশ্চিমবাংলায়, কেবলমাত্র পুলিশ কর্তৃক ধর্ষণ ও নারীর শ্লীলতাহানির ঘটনা ঘটেছে ৪৩টি। ১৯৮৭-র জুলাইয়ে তারকেশ্বর থানার কনস্টেবল তারই সহকর্মী মহিলাকে ধর্ষণ করেছে। এদের কতজনের শাস্তি হয়েছে? শুধুমাত্র একজনের কথা জানি, ‘৯১ সালে মেদিনীপুর জেলার ভগবানপুরের কায়দা বিবিকে থানায় এনে শ্লীলতাহানির প্রমাণে থানায় বড়বাবুর একবছর সশ্রম কারাদণ্ড হয়েছে। বাকিদের?
শিক্ষিকা অর্চনা গুহকে পুলিশ লালবাজারে নিয়ে এসেছিল। উদ্দেশ্য— অর্চনাকে জেরা করে তাঁর নকশাল ভাইয়ের খোঁজ জানা। আইনের রক্ষকরা জেরা করতে পারেন, কিন্তু কোনোভাবেই পারেন না জেরা করে কথা আদায় করার নামে, কোনও মানুষকেই মারধর করতে, ভয় দেখাতে, এমনকী, লোভনীয় কোনও টোপ দিতে। ভারতীয় সংবিধানের ফৌজদারি দণ্ডবিধি অনুসারে এ-সবই বেআইনি। আইন ভাঙলে পুলিশ শাস্তিযোগ্য অপরাধ করবে। কিন্তু আমরা অভিজ্ঞতায় কী দেখলাম? বর্বরোচিত ও অশ্লীল অত্যাচারে অর্চনা পঙ্গু হয়ে গেলেন। দীর্ঘ পনেরো বছর ধরে তিনি অত্যাচারী পুলিশ অফিসার রুণু গুহ নিয়োগীর বিরুদ্ধে ফৌজদারি মামলা চালাচ্ছেন ন্যায় বিচারের আশায়, মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার আশায়। কলকাতা পুলিশের ‘রেগুলেশন’ অনুসারে এই ক্ষেত্রে অভিযুক্তকে সাসপেন্ড করার নির্দেশ থাকা সত্ত্বেও সেই নির্দেশকে অবহেলা করে রাজ্য সরকার ক্রমান্বয়ে রুণু গুহনিয়োগীর পদোন্নতিই ঘটিয়ে গেছে। এ সবই কি মানবাধিকারকে সরকার কর্তৃক লঙ্ঘনেরই প্রমাণ নয় ?
এই ‘৯২-এর শেষ অর্ধে রাজ্য সরকারের সহযোগিতায় পাঞ্জাব পুলিশ কলকাতার একবালপুর অঞ্চল থেকে দু’জনকে গ্রেপ্তার করলেন, ‘সন্ত্ৰাসবাদী ও ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপ নিবারক আইন’ (TADA) -এ। ওদের বিমানে উড়িয়ে নিয়ে যাওয়া হল পাঞ্জাবে। দুই নিরস্ত্র মানুষকে বিমান থেকে নামিয়ে পুলিশ তাদের গুলি করে হত্যা করল। এই তো এই দেশের মানুষের বেঁচে থাকার অধিকার। হত্যাকারী পুলিশদের গ্রেপ্তার করা হয়নি, হবে না। রাষ্ট্রশক্তি স্বয়ং আজ সন্ত্রাসবাদীর ভূমিকায় অবতীর্ণ, আইন ভঙ্গকারীর ভূমিকায় অবতীর্ণ, মানবাধিকার ধর্ষণকারীর ভূমিকায় অবতীর্ণ।
লেখার এই অংশটা পড়ে কেউ কেউ প্রশ্ন তুলতে পারেন—শিখ উগ্রপন্থীরা যখন নিরীহ মানুষকে হত্যা করে, তখন? সে বিষয়ে কী মতামত দেবেন ? না কি মুখ বুজে থাকবেন ?
এ-জাতীয় প্রশ্ন ওঠে, বার-বারই ওঠে। প্রশ্নকর্তারা কখনও ব্যক্তি, কখনও বুদ্ধিজীবী,কখনও রাজনীতিক, কখনও পত্র-পত্রিকা, কখনও বা রাষ্ট্রশক্তি। হুজুরের দল ও তার কৃপাধন্যেরা বারবার এমন প্রশ্ন তুলে সাধারণ মানুষদের মগজ ধোলাই করে নিজেদের বেআইনি কাজের প্রতি জনমত তৈরি করতে চায়, জন-বিক্ষোভ এড়িয়ে মানুষের অধিকারকে ছিনিয়ে নিতে চায়। যারা সরকার ঘোষিত সন্ত্রাসবাদী, তারা যখনই কোনও নিরীহ বা অ-নিরীহকে হত্যা করছে তখনই দেশের আইন ভঙ্গ করছে আইন ভঙ্গকারীর শাস্তির স্পষ্ট বিধান আইনে দেওয়াই আছে। এবং সেই আইনমাফিক শাস্তি দেওয়ার অধিকার রাষ্ট্রশক্তির আছে। রাষ্ট্রশক্তি সেই আইন মাফিক না চলে আইনকে ভঙ্গ করে যা করছে তা অবশ্যই বে-আইনি, তা অবশ্যই রাষ্ট্র-সন্ত্রাস, তা অবধারিতভাবেই মানবাধিকার লঙ্ঘন ।
১৯৭০ থেকে ৭৬-এ কংগ্রেস সরকারের আমলে জেলখানায় ৪০০ বন্দি হত্যা হয়েছিল। কলকাতার কাশীপুর বরাহনগরের এক দিন-রাতের অভিযানে হাজার মানুষ নিখোঁজ হয়েছিল। স্থানীয় মানুষ দেখেছে, ঠেলায় চাপিয়ে গাদা করে কীভাবে গঙ্গায় ঢেলে দিতে চাপানো হচ্ছে মানুষের দেহগুলোকে। ‘৭৭-এ রাজ্যে ক্ষমতায় আসার আগে মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টির নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি ছিল, আধা ফ্যাসিবাদী সন্ত্রাসের জমানা (‘৭০-’৭৭)-র নায়কদের শাস্তি দেবেন। ‘৯২-এর শেষে দাঁড়িয়ে যদি কেউ প্রশ্ন তোলেন—কতজন হত্যাকারীর শাস্তি হয়েছে? উত্তর পাওয়া যাবে না।
ক্ষমতার সিংহাসনের যে চারটি পায়া তারই একটি হল
পুলিশ। অতএব বিরোধী পক্ষে থেকে আইনভঙ্গকারী
পুলিশদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের
প্রতিশ্রুতি দেওয়া যতটা সোজা, ক্ষমতার
সিংহাসনে বসে শাস্তি দেওয়া
ততটাই কঠিন।
অতীত ইতিহাসের দিকে একটু চোখ বোলালে দেখতে পাব, ব্রিটিশ সরকারের বিনা বিচারে আটকের বিরোধিতা করেছিল কংগ্রেস। কংগ্রেস বই প্রকাশ করেছিল, ‘পুলিশরাজ আন্ডার ব্রিটিশ-ইন্ডিয়া’। ব্রিটিশ বিদায় নিতে ক্ষমতার সিংহাসনে বসে কংগ্রেস সেই ‘পুলিশ-রাজ’ -কেই বরণ করল।
মুলায়ম সিং যাদব সরকারের আমলে উত্তর প্রদেশ সরকার সরকারি সিমেন্ট কারখানা বেসরকারি হাতে তুলে দিতে চাইল। প্রতিবাদ জানাল শ্রমিকেরা। পুলিশ গুলি চালিয়ে ১৫ জন শ্রমিককে হত্যা করল। ভারতীয় জনতা পার্টি ঘোষণা করল, “কাল আমরা শাসন ক্ষমতায় এলে যারা গুলি চালিয়ে নিরীহ শ্রমিকদের হত্যা করেছে, তাদের শাস্তি দেবই।” তারপর উত্তর প্রদেশের ক্ষমতার সিংহাসনে বসল ভারতীয় জনতা পার্টি এবং সিংহাসনের একটি পায়া পুলিশসরাজকে ঠিক-ঠাক রাখতে জনগণের সামনে ঘোষিত প্রতিশ্রুতিকে ছুড়ে ফেলে দিল আঁস্তাকুড়ে।
১৯৯২-এর ২ জুন কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি শ্রীদিলীপকুমার বসু লকআপে হত্যা সংক্রান্ত জনস্বার্থ মামলায় রায় দিয়ে বলেন, পশ্চিমবঙ্গ লকআপে পিটিয়ে মারলে অথবা কেউ ধর্ষিতা হলে ক্ষতিপূরণ বাবদ তাৎক্ষণিক নিহতের পরিবারকে অথবা ধর্ষিতাকে ১ লাখ টাকা এবং লকআপে গুরুতর আহত ব্যক্তিকে ৫০ হাজার টাকা দিতে রাজ্য সরকার বাধ্য থাকবে। কিন্তু এই রায়ই বা কতটা কার্যকর হবে? ভবিষ্যতে কি রাজ্য সরকার ক্ষতিপূরণের বিনিময়ে সরকার-বিপন্নকারীর মৃত্যু কিনবে? কিনবে নারীর ইজ্জত? না কি ক্ষতিপূরণ দেওয়ার পাশাপাশি ধর্ষণকারী আইনের রক্ষকদের বিরুদ্ধে শাস্তি প্রয়োগ করা হবে?
আপনি, আপনারা স্বাধীনতার অধিকার ভোগ করতে পারেন
তখনই, রক্ষা করতে পারেন তখনই, যখন
কী কী অধিকার আছে জানবেন।
অধিকারগুলো জানা থাকলে তবেই আপনি অধিকার লঙ্ঘনের বিরুদ্ধে সোচ্চারে প্রতিবাদ করতে পারেন। ভারতের সংবিধানে স্বীকৃত কয়েকটি মৌলিক অধিকার বিষয়ে তাই নাগরিকদের সচেতনতার অতি প্রয়োজন রয়েছে। যদিও এইসব অধিকারের ক্ষেত্রে অনেক রকমের সীমাবদ্ধতা রয়েছে রয়েছে স্ব-বিরোধিতা, তবু এই সব মৌলিক অধিকার নিয়ে ছোট্ট করে একটু আলোচনা সেরে নেওয়া একান্তই প্রয়োজন। এই আলোচনাই মানবাধিকার রক্ষার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে পারে ভেবেই আলোচনার প্রয়োজন অনুভব করলাম।
ভারতীয় সংবিধানে স্বীকৃত কয়েকটি মৌলিক অধিকার
সমতার অধিকার (Right of Equality)
ভারতীয় ভূখণ্ডে প্রত্যেকেই আইনের চোখে সমান অথবা প্রত্যেককেই আইন সমানভাবে রক্ষা করবে (সংবিধানের ১৪ নম্বর ধারা)। রাষ্ট্র এই অধিকারকে অস্বীকার করবে না ।
(এখানেও কিন্তু স্ব-বিরোধিতা আছে। ১৪ নম্বর ধারায় বলা হয়েছে, ‘শ্রেণিগত’ আইন প্রণয়ন নিষিদ্ধ। অর্থাৎ বিশেষ শ্রেণির জন্য বিশেষ আইন চলবে না। কিন্তু এই ১৪ নম্বর ধারাতেই ‘যুক্তিযুক্ত শ্রেণি বিভাগ’ (Rea- sonable classification) নিষিদ্ধ করছে না।
স্বাধীনতার অধিকার (Right of Freedom )
সমস্ত নাগরিকদের (ক) মত প্রকাশের, (খ) শান্তিপূর্ণভাবে এবং নিরস্ত্র অবস্থায় সমবেত হওয়ার, (গ) সমিতি বা ইউনিয়ন গঠন করার, (ঘ) ভারতীয় ভূখণ্ডের যে কোনও স্থানে বসবাস করার এবং (ঙ) যে কোনও পেশা, ব্যবসা বা বাণিজ্য করার অধিকার রয়েছে। (সংবিধানের ১৯ নম্বর ধারা।
১৯ নম্বর ধারায়ও স্বাধীনতার অধিকারগুলোর ‘যুক্তিযুক্ত সীমাবদ্ধতা’
( Reasonable Restrictions) রয়েছে। ১৯ নম্বর ধারায় বলা হয়েছে, ‘যুক্তিযুক্ত সীমাবদ্ধতা’ আরোপ করা যাবে (ক) ভারতের সার্বভৌমত্ব, (খ) ভূখণ্ডের ঐক্য, (গ) রাষ্ট্রের নিরাপত্তা, (ঘ) জনস্বার্থ, (ঙ) তফসিলি জাতির সংরক্ষণ ইত্যাদি ক্ষেত্রে।
জীবনের নিরাপত্তা ও ব্যক্তিগত স্বাধীনতা
(Protection of Life And Personal Liberty)
কোনও ব্যক্তির জীবনও ব্যক্তিগত স্বাধীনতা হরণ করা যাবে না। কেবল মাত্র আইন অনুযায়ী প্রতিষ্ঠিত পদ্ধতিক্রমেই এর ব্যতিক্রম হতে পারে। (সংবিধানের ২১ নম্বর ধারা)।
আটকের বিরুদ্ধে রক্ষাকবচ এবং কোন কোন ক্ষেত্রে আটক রাখা যায়
(Protection Against and Detention in Certain Cases) (১) গ্রেপ্তার করার পর যত শীঘ্র সম্ভব গ্রেপ্তার হওয়া ব্যক্তিকে গ্রেপ্তারের কারণ দেখাতে হবে। কারণ না জানিয়ে কাউকে আটকে রাখা যাবে না।
(২) আটক ব্যক্তিকে আইনজীবীর সাহায্য পাওয়ার অধিকার থেকে বঞ্চিত করা যাবে না। ধৃত ব্যক্তির তার পছন্দমতো আইনজীবীর সঙ্গে পরামর্শ করার অধিকার আছে।
(৩) গ্রেপ্তার হয়েছেন বা আটক আছেন এমন ব্যক্তিকে গ্রেপ্তারের ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই নিকটবর্তী ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে হাজির করতে হবে। গ্রেপ্তারের পর, ‘ছুটির দিন আদালত বন্ধ ছিল’ এমন কোনও অজুহাত এনে এই ২৪ ঘণ্টাকে অতিক্রম করা যাবে না। এক্ষেত্রে নিকটবর্তী কোনও ম্যাজিস্ট্রেটের বাড়িতেই আটক ব্যক্তিকে হাজির করতে হবে। ম্যাজিস্ট্রেটের বিনা অনুমতিতে তাকে ২৪ ঘণ্টার বেশি আটক রাখা যাবে না। (সংবিধানের ২২ নম্বর ধারা, এছাড়াও ফৌজদারি ৫৭ ও ৭৬ নম্বর ধারা অনুসারেও)।
(কিন্তু এই অধিকারও রাষ্ট্রপতি ঘোষিত জরুরি অবস্থার সংবিধানের ৩৫১ (১) ধারা বলে বাতিল হতে পারে। জরুরি অবস্থা না থাকলে এই ২২ নম্বর ধারা অগ্রাহ্য করা যাবে না।)
সংবিধানের এই সব মৌলিক অধিকার ছাড়াও আরও কিছু অধিকার আছে যেগুলি জানা থাকলে পুলিশের বেআইনি কাজ প্রতিরোধ করা যায় অথবা বেআইনি কাজের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলা যায়।
পুলিশি হস্তক্ষেপ কোথায় অসাংবিধানিক
১। গ্রেপ্তার না করে পুলিশ কাউকে এক মিনিটের জন্যও আটক রাখতে পারে না। ‘মুক্ত-ধৃত’ বলে কিছুর অস্তিত্ব ভারতীয় আইনে নেই— ভারতের সুপ্রিম কোর্টের বহু রায়ে এই কথা স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে।
১৪৯ ধারা অনুসারে কোনও গুরুতর অপরাধ থেকে বিরত করা বা বাধাদানের প্রতিরোধের ক্ষেত্রেও পুলিশকে ওই ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করতে হবে, গ্রেপ্তার ব্যতিরেকে আটক রাখা যাবে না ।
২। গ্রেপ্তারের আগে বা গ্রেপ্তারের সঙ্গে সঙ্গে ধৃত ব্যক্তিকে পুলিশ জানাতে বাধ্য কোন্ অভিযোগে গ্রেপ্তার করা হচ্ছে।
৫০ নম্বর এবং ২২ (১) নম্বর ধারা অনুসারে সংবিধান নাগরিকদের এই অধিকার দিয়েছে। ভারতের বিভিন্ন সর্বোচ্চ আদালতের একাধিক রায় অনুসারে ধৃত ব্যক্তিকে অভিযোগ না জানানো বেআইনি।
৩। ধৃত ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসাবাদের সময় তার পছন্দমতো আইনজীবীকে উপস্থিত রাখার অধিকার ধৃতের রয়েছে। এই অধিকারের পক্ষে সুপ্রিম কোর্টের একাধিক রায় আছে।
8। কোনও মামলাসংক্রান্ত জিজ্ঞাসাবাদের জন্য কোনও থানা কোনও ব্যক্তিকে মৌখিকভাবে ডাকতে পারে না। ১৬০ নম্বর ধারার (ক) ও (খ) অনুসারে থানাকে ওই ব্যক্তির কাছে লিখিত নির্দেশ পাঠাতে হবে এবং থানায় যাতায়াতের খরচও ওই ব্যক্তিকে দিতে হবে।
১৫ বছরের কম বয়সি পুরুষ বা মহিলাকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য থানায় আনা চলবে না। তাদের বাসস্থানেই জেরা করতে হবে।
পুলিশ হাজতে অত্যাচার করতে পারে না
১। ফৌজদারির দণ্ডবিধির ১৬৩ নম্বর ধারা অনুসারে কোনও ব্যক্তিকে হুমকি দেখিয়ে, মারধরের ভয় দেখিয়ে অথবা কোন লোভনীয় টোপ দেখিয়ে বা নির্যাতন করে পুলিশের কোনও ধরনের বিবৃতি আদায় সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ । ১৬১ নম্বর ধারা অনুসারে ধৃত ব্যক্তি মিথ্যা ফৌজদারি মামলা সংক্রান্ত পুলিশের জেরার জবাব নাও দিতে পারেন।
২। ফৌজদারি দণ্ডবিধির ৫৪ নম্বর ধারা অনুসারে প্রথম সুযোগেই ধৃত ব্যক্তি পুলিশের বিরুদ্ধে লক আপে বা অন্যত্র অত্যাচার চালাবার অভিযোগ এনে বিচারকের কাছে নিজের শরীর পরীক্ষার আবেদন জানাতে পারেন।
৩। ধৃত ব্যক্তিকে মারধর করার কোনও অধিকার পুলিশের নেই । ধৃত ব্যক্তির উপর অত্যাচার চালালে ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩৩০ ও ৩৩১ নম্বর ধারা অনুসারে অত্যাচারের তারতম্য অনুসারে পুলিশের সাজা ৭ বছর থেকে ১০ বছর জেল অথবা মৃত্যুদণ্ড পর্যন্ত হতে পারে। অর্থাৎ হাজতে ধৃতের উপর একটি আঘাতের ন্যূনতম সাজাটিই হল ৭ বছরের জেল।
মহিলাদের বিরুদ্ধে পুলিশ যা আইনত করতে পারে না
১। সি আর পি সি-র ৫১(২) ধারা অনুসারে ধৃত মহিলার দেহ তল্লাশি করার কোনও অধিকার কোনও পুরুষ পুলিশেরই নেই। শুধুমাত্র মহিলা পুলিশরাই মহিলার দেহ তল্লাশি করতে পারে। এই দেহ তল্লাশি কোনওভাবেই শোভনীয়তার মাত্রা ছাড়াতে পারবে না।
২। মহিলা বন্দিকে স্বতন্ত্রভাবে মহিলা লকআপে রাখতেই হবে।
৩। ১৯৮২ সালের ফেব্রুয়ারিতে কেন্দ্রীয় সরকার বলবৎ বিজ্ঞপ্তি অনুসারে কোনও মহিলাকে সূর্যাস্ত থেকে সূর্যোদয় পর্যন্ত অর্থাৎ সন্ধ্যা থেকে পরের দিন সকাল পর্যন্ত থানায় ডাকা চলবে না, গ্রেপ্তার করা যাবে না, এমন কী বাড়িতে মহিলা থাকলে সেই বাড়ি সন্ধ্যা থেকে সকাল পর্যন্ত তল্লাশি করা চলবে না। প্রয়োজনে ওই সময় পুলিশ বাড়ি ঘিরে রেখে দিতে পারে।
পুলিশের বিরুদ্ধে ধর্ষণ সংক্রান্ত আইন
১। ১৯৮৩ সালে সংযোজিত আইনে বলা হয়েছে, হেফাজতকালীন ধর্ষণে, অর্থাৎ ধর্ষণকারী যদি পুলিশ, সরকারি কর্মচারী, সরকারি হাসপাতালের অথবা কিশোরীদের হাজতের আধিকারিক অথবা জেলখানার সিপাই হয়, তবে অভিযুক্তকেই প্রমাণ করতে হবে, সে ধর্ষণ করেনি।
২। হেফাজতকালীন ধর্ষণ, গণধর্ষণ, অন্তঃসত্ত্বা মহিলা ও বারো বছরের কম মেয়েদের ধর্ষণের জন্য ন্যূনতম দশ বছর কারাদণ্ডের বিধান আইনে দেওয়া হয়েছে।
অবশ্যই জেনে রাখুন
১। ফৌজদারি আইনের ১৬১ নম্বর ধারা অনুসারে পুলিশের কাছে আপনি কোনও বিবৃতি দিলে সেই বিবৃতিতে আপনার কোনও স্বাক্ষর অর্থাৎ সই দেওয়া বা আঙুলের টিপছাপ দেওয়ার প্রয়োজন নেই।
২। এই ধরনের বিবৃতি মামলার কোনও ক্ষেত্রেই আপনার বিরুদ্ধে ব্যবহার করা যায় না।
৩। বিচারকের কাছে আপনার স্বাক্ষর যুক্ত বিবৃতিই কেবল মামলায় ব্যবহার করা যায়।
৪। মামলায় অভিযুক্ত ব্যক্তিকে বিনামূল্যে মামলা সংক্রান্ত পুলিশ রিপোর্ট, এফ.আই.আর, ঘটনার সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিদের বিবৃতি ও সাক্ষ্যদান প্রভৃতির নকল ২০৭ ধারা মতো বিচারক দিতে বাধ্য ।
৫। ভারতীয় দণ্ডবিধির ৯৭ ও ৩৯ ধারা অনুসারে পুলিশ আপনার বাড়ির যে সব জিনিস বাজেয়াপ্ত করবে তার তালিকার নকল আপনাকে দিতে বাধ্য।
৬। আপনার বাড়িতে পুলিশ তল্লাশি চালাবার সময় আপনাকে উপস্থিত থাকতে দিতে বাধ্য। এ ছাড়াও অন্য সাক্ষ্য রেখেই পুলিশি তল্লাশি চালাতে হবে। ১৮৭ নম্বর ধারা অনুসারে এর অন্যথা করলে পুলিশ দণ্ডনীয় অপরাধ করবে।
৭। ফৌজদারি আইনের ১৫৪ নম্বর ধারা অনুসারে পুলিশ যে কোনও অভিযোগকারীর অভিযোগের ডায়েরি নিতে বাধ্য।
৮। ১৯৮০, ১৯৮৮ সালের সুপ্রিম কোর্টের রায় এবং ১৯৯০ সালের এপ্রিল মাসে ও মে মাসে যথাক্রমে বোম্বাই হাইকোর্টের ডিভিসন বেঞ্চের এবং মধ্য প্রদেশ হাইকোর্টের রায় অনুসারে কোনও অভিযুক্ত ব্যক্তিকে পুলিশ হাতকড়া লাগাতে পারে না এবং কোমরে দড়ি বেঁধে আদালতে অথবা থানায় নিয়ে যেতে পারে না। কারণ, যতক্ষণ পর্যন্ত না আদালতে প্রমাণিত হচ্ছে অভিযুক্ত ব্যক্তি অপরাধী, ততক্ষণ সে আইনের চোখে অবশ্যই নিরপরাধ ।
৯। যদি আপনাকে বেআইনিভাবে গ্রেপ্তার করা হয়ে থাকে অথবা যদি আপনাকে গ্রেপ্তারের ২৪ ঘণ্টার মধ্যে আদালতে অথবা বিচারকের কাছে হাজির করা না হয়, তবে আপনার পক্ষ থেকে কেউ হাই কোর্টে বা সুপ্রিম কোর্টে ‘হেবিয়াস করপাস’ আবেদন করতে পারেন। এই আবেদনের মধ্য দিয়ে আপনি হাই কোর্ট বা সুপ্রিম কোর্টের দৃষ্ট আকর্ষণ করতে পারেন।
মানবিক অধিকার রক্ষার স্বার্থে কিছু দাবি
১। ১৯৮০ সালে জাতীয় পুলিশ কমিশনের সুপারিশে (প্রথম অধ্যায়) স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে, লকআপে অত্যাচার বা হত্যার ঘটনা ঘটলে, পুলিশের গুলিতে দুই বা অধিক ব্যক্তির মৃত্যু হলে, অথবা ‘সাজানো সংঘর্ষে’ হত্যার ঘটনা ঘটলে বিচার বিভাগীয় তদন্ত করা উচিত, পুলিশকে দিয়ে তদন্ত নয়। এই গুরুত্বপূর্ণ সুপারিশ কার্যকর করার জন্য সরকারের উপর চাপ দিয়ে জনমত তৈরি করা উচিত।
২। পুলিশ হাজতে অত্যাচার বা হত্যার ঘটনা ঘটলে বড়বাবুকে অর্থাৎ ইনচজার্জকে অবিলম্বে সাময়িক বরখাস্ত করতে হবে এবং তাদেরই প্রমাণ করতে হবে উপর ধৃতের অত্যাচার করা হয়নি।
বিখ্যাত শীলা বারসে বনাম মহারাষ্ট্র সরকার মামলায় (১৯৮৩) সুপ্রিম কোর্ট এই একই সুপারিশ করেছেন। আইন কমিশনও এই সুপারিশ করেছেন। ১৯৮৫ সালে রামসাগর যাদব বনাম উত্তর প্রদেশ সরকার মামলায় সুপ্রিম কোর্ট ওই একই মন্তব্য করেছেন। অতএব সারা দেশে এই আইন চালু করা হোক ।
৩। কাউকে হঠাৎ যে কোনও জায়গা থেকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে যাওয়ার পর ধৃত ব্যক্তির আপনজনেরা থানায়, পুলিশের বিভিন্ন দপ্তরে ঘুরে ঘুরেও “ধৃত ব্যক্তির কোনও হদিশ পায়নি, এমন ঘটনা কম ঘটেনি। বিভিন্ন পুলিশ দপ্তর গ্রেপ্তারের কথা অস্বীকার করায় বহু জলজ্যান্ত-মানুষ হঠাৎ পৃথিবী থেকে চিরকালের মতো হারিয়ে গেছেন। এমন ঘটনাগুলোর কথা মনে রেখে কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি মাননীয় শ্রীদিলীপকুমার বসু ২ জুন ১৯৯২ এক ঐতিহাসিক রায় দিয়ে বলেন— অবিলম্বে প্রত্যেককে গ্রেপ্তারের মুহূর্তে ধৃত ব্যক্তির গ্রেপ্তারের কারণ সম্বলিত তথ্য, গ্রেপ্তারকারী পুলিশ অফিসারের নাম ঠিকানা-সহ একটি ‘কাস্টডি মেমো’ ধৃত ব্যক্তির নিকট আত্মীয়কে দিতেই হবে। রাস্তায় গ্রেপ্তার করলে এবং কোনও ভাবে ধৃতের নিকট আত্মীয়, সাধারণ আত্মীয় বা বন্ধুদের সঙ্গে পুলিশের পক্ষে দ্রুত যোগাযোগ অসম্ভব হলে যেখানে গ্রেপ্তার করা হল, সেই অঞ্চলের কোনও দোকানদারকে অন্তত ‘কাস্টডি মেমো’ দিয়ে ধৃত ব্যক্তির আত্মীয়কে ওই মেমো পৌঁছে দেবার অনুরোধ করতে হবে।
হাই কোর্টের এই রায়কে মর্যাদা দেওয়ার দায়িত্ব সরকারের। এই রায় অমান্য করা বেআইনি। সম্মিলিত দাবি তুলতে হবে, সরকারকে এই আইন মেনে চলতেই হবে।
রাষ্ট্রশক্তির দ্বারা, সরকার দ্বারা ধৃতকে নির্যাতন মানবাধিকারের একটি মৌলিক লঙ্ঘন। জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদ একে ‘মানুষের মর্যাদার বিরুদ্ধে এক জঘন্য অপরাধ’ হিসেবে তীব্র নিন্দা করেছে। এবং জাতীয় ও আন্তর্জাতিক আইনে ধৃতকে নির্যাতন নিষিদ্ধ হয়েছে।
তবু পৃথিবী জুড়ে শাসক ও শোষকরা তাদের গদি মজবুত রাখতে, নিপীড়িত মানুষের অধিকারকে প্রতিনিয়ত পদদলিত করেই চলেছে। আজ বহু দেশের তথাকথিত গণতন্ত্র আমাদের দেশের মতোই এক বিরাট প্রহসন মাত্র। এ-দেশে শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধি যে ‘ছাপ্পা-ভোট’, ‘বুথ-জ্যাম’ পরিকল্পিতভাবে ব্যাপক আকারে শুরু করেছিলেন, সেই কালচার এখন এতই ব্যাপকতা পেয়েছে যে ভোট ব্যবস্থাই একটা প্রহসনে রূপান্তরিত হয়েছে। মানুষের অধিকারকে ব্যাপকভাবে যারা খর্ব করে চলেছে তারাই সরকার অথবা এই ধরনের নির্বাচন ব্যবস্থার সুযোগ নিয়ে সরকার গঠনে পরম উৎসাহী ক্যারিয়ারিস্ট রাজনীতিক।
২৯ নভেম্বর ১৯৯২ পশ্চিমবঙ্গের বামফ্রন্ট সরকার ভুক্ত রাজনৈতিক দলগুলো আর এক ভয়াবহ মানবাধিকার লঙ্ঘনকারী রাজনীতির কালচার আমদানি করল আমাদের দেশে। দলের শক্তি প্রদর্শনের খেয়ালে মাতোয়ারা হয়ে ফ্যাসিস্ট কায়দায় যেভাবে বহু খেটে খাওয়া মানুষকে হুম্কি দেখিয়ে ব্রিগেডের জনসভায় যেতে বাধ্য করল, যেভাবে সরকারি ক্ষমতার অপব্যবহার করে সরকারি বাসগুলোকে পার্টি মিটিং-এ হাজির করল, যেভাবে দশ হাজার বাস-মিনিবাস-লরির মালিকদের বাধ্য করল বাস-মিনিবাস লরি দিতে, তাতে কলকাতার আশে-পাশে অলিখিত একটা বন্ধ দুপুর থেকেই চেপে বসল ।
এই যে কালচার শুরু করলেন পশ্চিমবঙ্গের বামফ্রন্ট নেতারা, এর পরিণতি ভয়াবহ হয়ে উঠতেই পারে। আগামী দিনে শাসক দল হিসেবে কংগ্রেস বা অন্য কেউ এলেও তারাও যে একইভাবে ফ্যাসিস্ট পেশি শক্তি এবং সরকারি ক্ষমতার চূড়ান্ত অপব্যবহার ঘটিয়ে মানুষের অধিকারকে লুণ্ঠন করে বামফ্রন্টের বিরুদ্ধে জনসমাবেশ ঘটানোর খেলায় মাতবে না, তার গ্যারান্টি কি দিতে পারবে বামফ্রন্ট সরকার বা বামফ্রন্ট দল? এই জনসমাবেশ ঘটানোর কালচার যে সরকারের গদিতে বসা অন্যান্য রাজ্যে রাজনৈতিক দলগুলোর কাছেও জনপ্রিয়তা পাবে না—এই গ্যারান্টি কি দিতে পারবে বামফ্রন্ট? মানুষের অধিকার রক্ষার আন্দোলন ভাঙতে শাসক দল যে আন্দোলন বিরোধী আন্দোলন গড়তে, আন্দোলন বিরোধী সমাবেশ গড়তে হিংস্র পেশিশক্তির সাহায্য নেবে না, মানুষের অধিকার খর্ব করবে না,–এই গ্যারান্টি কি বামফ্রন্ট দিতে পারবে?
না পারা সম্ভব নয়। যে বিষবৃক্ষের বীজ বামফ্রন্ট রোপণ করল, তা এখুনি প্রতিবাদ ও প্রতিরোধের মধ্য দিয়ে তুলে ফেলতে না পারলে ভবিষ্যতে এর বিষময় ফল আপনাকে, আমাকে সকলকেই ভোগ করতে হবে— এমনকী, বামফ্রন্টকেও। এই মানবাধিকার লঙ্ঘনকারী কালচারের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়তে এখনই বাড়তি উদ্যম নেওয়া উচিত প্রতিটি মানবাধিকার রক্ষাকারী সংগঠনগুলোর।
ভারতে মানবাধিকার ঠিকমতো রক্ষিত হচ্ছে কি না দেখতে ভারত সরকার এগিয়ে এসেছে কমিশন গড়তে। কমিশন গড়ার কাজে এগিয়ে এসেছে অনেক রাজ্য সরকার। অবাক হওয়ার মতোই ঘটনা বটে! মানুষের অধিকার যারা খর্ব করছে, কেড়ে নিচ্ছে চরম নিষ্ঠুরতার সঙ্গে, তারাই যখন কমিশন গড়ে, তখন অবাক হতেই হয়। এমন ক্ষেত্রে এই অনুমানই প্রত্যয় পায় – আসমুদ্র হিমাচল ভারতের সর্বত্র মানুষের অধিকার রক্ষিত হচ্ছে, এমন জ্বলন্ত মিথ্যেকে সত্যি বলে প্রমাণ করতেই শাসকদল কমিশন গড়তে কোমর বেঁধে নেমেছে। ভারতে মানবাধিকার রাষ্ট্র শক্তির কাছেই বার বার খর্বিত—এমন কথাগুলো বিভিন্ন দেশের প্রচার মাধ্যম মারফত বার-বার ঘুরে-ফিরে নানাভাবে উঠে আসছে। পৃথিবীর মানুষের কাছে ভারত-শাসকদের বীভৎস চেহারাটা মুখোশের আড়াল থেকে বেরিয়ে পড়তেই আবার আড়াল তৈরি করতে কমিশন গড়ার এই পরিকল্পনা।
ভারতীয়রা যে সীমিত গণতান্ত্রিক অধিকার সংবিধান অনুসারে ভোগ করার অধিকারী, তার উপর আজ এসে পড়েছে শাসক ও শোষক গোষ্ঠীর নগ্ন আক্রমণ। সুন্দর সংস্কৃতি গড়ার প্রয়োজনে মানুষের অধিকার রক্ষা ও অধিকারের সম্প্রসারণ একান্তই প্রয়োজনীয় বলে মনে করি ।
জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের মানবাধিকারের সর্বজনীন ঘোষণা অনুসারে ব্যক্তিমানুষ হিসেবে প্রত্যেকেরই রয়েছে পূর্ণ মানবিক মর্যাদা লাভের অধিকার। আর সেই হেতুই প্রতিটি মানুষের রয়েছে দৈহিক নির্যাতন থেকে অব্যাহতি লাভের অধিকার। কোনও ব্যক্তিকে রাজনীতিগত, আইনগত, বা আন্তর্জাতিক পদমর্যাদার ভিত্তিতে আলাদাভাবে না দেখে রাষ্ট্র কর্তৃক প্রত্যেক নাগরিককে সমানভাবে দেখার অধিকার ; আইনের চোখে সমানাধিকার ; স্বাধীন জীবিকা নির্বাচনের অধিকার ; ট্রেড ইউনিয়ন করার অধিকার; রাজনৈতিক দলের সদস্য হওয়ার অধিকার ; সংগঠন গঠনের অধিকার ; বিনা বিচারে বন্দি না হওয়ার অধিকার ; পক্ষপাতহীন বিচার পাওয়ার অধিকার ; স্বাধীন চিন্তা ও বিবেকের দ্বারা নিজেকে পরিচালিত করার অধিকার; স্বাধীন মত প্রকাশের অধিকার ; সামাজিক নিরাপত্তা লাভের অধিকার; শিক্ষা লাভের অধিকার; সরকারি কাজ পাওয়ার অধিকার ইত্যাদি অধিকার। জাতিসংঘের ঘোষিত মানুষের অধিকারগুলোর প্রতি আমাদের সমিতির আন্তরিক সমর্থন রয়েছে। সেই সঙ্গে আমরা মনে করি দেশের নাগরিকদের বেঁচে থাকার অধিকারকে বাস্তবায়িত করতে প্রতিটি নাগরিকের খাদ্য-বস্ত্র-গৃহ লাভের অধিকারকে স্বীকৃতি দান একান্তই প্রয়োজনীয় ।
এই সমস্ত মৌল ও অপরিহার্য মানবিক ও গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষার দায়িত্ব জনগণেরই। জনসচেতনতা গড়ে উঠলে, জনগণ তাঁদের অধিকার বিষয়ে সচেতন হলে তবেই অধিকার কোথায় কেড়ে নেওয়া হচ্ছে, তা বুঝতে আম-জনতা সক্ষম হবেন এবং প্রতিরোধ গড়ে তুলতে এগিয়ে আসবেন। জনসচেতনতাই শাসকদের কাছ থেকে নতুন নতুন অধিকার আদায়ে সোচ্চার হবে, সংগ্রামে নামবে, মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্যই নামবে। বিভিন্ন সেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান, সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান, বিজ্ঞান ক্লাব ও মানবাধিকার রক্ষা আন্দোলনে শামিল প্রতিষ্ঠান যদি মানবাধিকার বিষয়ে জনচেতনা গড়তে সচেষ্ট হন, মানবাধিকার রক্ষায় সজাগ দৃষ্টি রাখেন, মানবাধিকার লঙ্ঘনকারীর বিরুদ্ধে সোচ্চার হন, তবে নিশ্চিতভাবে অবক্ষয়ী লাঞ্ছিত মানবাধিকারের সংস্কৃতির বিরুদ্ধে সুসংস্কৃতির বিজয় ঘোষিত হবেই।
আমাদের দেশের বাস্তব পরিস্থিতির ভিতর কতকগুলি অশুভ অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক উপাদান রয়েছে। এই পরস্পর সম্পর্কিত উপাদানগুলোই মানুষের অধিকার খর্ব করার ক্ষেত্রে সক্রিয়। কিন্তু এই পরিস্থিতির কথা মাথায় রেখেও আমরা লড়াই শুরু করতে পারি সাংস্কৃতিক ক্ষেত্র থেকেই, মানুষের চেতনার ক্ষেত্র থেকেই। বর্তমানে মানুষের চেতনা ক্ষেত্রের বা সাংংস্কৃতিক ক্ষেত্রের গুরুত্ব যে কী বিশাল, তা বিশ্বের বিভিন্ন দেশের উপর ছড়ি ঘোরানো আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের দিকে তাকালেই তা বোঝা যায়। পূর্ব ইউরোপের দেশগুলোয় কী ভাবে নাক গলাবে? কী ভাবে ও সব দেশের মানুষের মগজ ধোলাই করে প্রয়োজনীয় চিন্তাগুলোকে ঢোকাবে? সাহায্য নিল তাবড় মনোবিজ্ঞানীদের। চিনের জনগণের মাথায় অন্য চিন্তা ঢোকাতে হবে— তলব করল মনোবিজ্ঞানীদেরই। গেরিলা যুদ্ধের মোকাবিলায় দেখা গেল মনোবিজ্ঞানীদের সাহায্য নিতে। তারই ফল স্বরূপ সি. আই. এ-র ম্যানুয়াল হিসাবে আবির্ভূত হতে দেখলাম ‘সাইকোলজিক্যাল অপারেশনস ইন গেরিলা ওয়ারফেয়ার’কে, যা আজ অনেক দেশেরই গেরিলা যোদ্ধাদের সংগ্রাম পরিচালনার আকরগ্রন্থ। চেতনার ক্ষেত্রের ওলট-পালট যে অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে ওলট-পালট ঘটিয়েই থাকে, সমাজের চলমান গতির উপর নজর রাখলে, ইতিহাসের দিকে নজর রাখলে তা বুঝতে একটুও অসুবিধে হয় না।
বর্তমান পৃথিবীতে গণতন্ত্র ও ব্যক্তি স্বাধীনতার সমস্যা,
মানবাধিকার রক্ষার সমস্যা আদৌ কোনও বিচ্ছিন্ন
সমস্যা নয়। যে দেশে শোষণ থাকবে সে
দেশে শোষণ বজায় রাখতেই মানবাধিকার
ও ব্যক্তি স্বাধীনতা খর্ব হবেই।
তবু আমাদের লড়াই শুরু করতে হবে সাংস্কৃতিক ক্ষেত্র থেকেই, মানুষের চেতনায় সুন্দর পৃথিবী গড়ার প্রত্যয় জাগিয়ে তোলার মধ্য দিয়েই। আর তাই আসুন প্রতিটি সমাজ সচেতন মানুষ ও সংগঠন ভারতের সীমিত গণতান্ত্রিক অধিকারের উপর নগ্ন আক্রমণের পটভূমিতে জনসাধারণের অধিকার রক্ষা ও সম্প্রসারণের উদ্দেশ্যে দ্বিধাহীন ভাবে সচেষ্ট হই, সহযোগিতার হাত প্রসারিত করি, সোচ্চার হই।
আপনি বা আপনার জানাশোনা কেউ কি
১। বিনা বিচারে জেল খাটছেন?
২। পুলিশ বা মিলিটারি দ্বারা অত্যাচারিত?
৩। পুলিশ বা সামরিক বাহিনীর হুমকির মুখে দিন কাটাচ্ছেন? ৪। পুলিশ হেফাজতে ধৃতকে হত্যা করা হয়েছে?
৫। পুলিশ হেফাজতে ধর্ষিতা হয়েছেন?
ধর্ম-বর্ণ-জাতি-ভাষা-পুরুষ-মহিলা নির্বিশেষে নীচের ঠিকানাগুলোয়
যোগাযোগ করতে পারেন—
১। ভারতীয় বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী সমিতি, কেন্দ্রীয় কার্যালয় ৭২/৮ দেবীনিবাস রোড, দমদম, কলকাতা-৭০০ ০৭৪
২। ভারতীয় বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী সমিতির যে কোনও শাখা।
৩। A.P.D.R গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা সমিতি (পশ্চিমবঙ্গ) ১৮, মদন বড়াল লেন, বউবাজার, কলকাতা – ৭০০ ০১২
৪। লিগ্যাল এইড সার্ভিসেস অ্যান্ড কাউন্সেলিং সেন্টার ৫, কিরণশংকর রায় রোড, কলকাতা – ৭০০ ০০১
৫। নারী নির্যাতন প্রতিরোধ মঞ্চ ২৯/১-এ, ওল্ড বালিগঞ্জ সেকেন্ড লেন, কলকাতা-৭০০ ০১৯
৬। পিপল্স ইউনিয়ন অব সিভিল লিবার্টিজ (P.U.C.L.) ২/১এ, আশুতোষ শীল লেন, কলকাতা-৭০০ ০০৯
৭। উইমেনস সেল ক্যালকাটা পুলিশ লালবাজার, কলকাতা-৭০০০০১ ৮। লিগ্যাল এইড কমিটি পশ্চিমবঙ্গ সরকার, সিটি সিভিল কোর্ট, দ্বিতল, কিরণশংকর রায় রোড, কলকাতা – ৭০০ ০০১
৯। এ ছাড়াও যোগাযোগ করতে পারেন সরকারি স্তরে পুলিশ সুপার অথবা জেলাশাসক, স্থানীয় মহিলা সংগঠন, সমাজসেবী সংগঠন ও সাংস্কৃতিক সংগঠনগুলোর সঙ্গে ।
জাতীয়তাবাদ ও জাতীয় সংহতিঃ গোলেমালে পীরিত কইরো না
‘জাতীয়তাবাদ’ ও ‘জাতীয়-সংহতি’ শব্দ দু’টির ব্যাপক ও বহুল অপব্যাখ্যায় সাধারণ মানুষ এতটাই প্রভাবিত যে শব্দ দু’টিই আজ শোষক ও শাসকশ্রেণির শক্তিশালী হাতিয়ার হয়ে উঠেছে। কখনও নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি পালনের ব্যর্থতা ঢাকা, কখনও তীব্র অর্থনৈতিক সংকটের অনিবার্য ফল হিসেবে বঞ্চিত, নিপীড়িত মানুষদের মধ্যে ধূমায়িত ক্ষোভে একগাদা ঠান্ডা জল ঢালতে হঠাৎ প্রতিবেশী রাষ্ট্রের জুজু দেখানো হতে থাকে। প্রতিবেশী রাষ্ট্র আমাদের সীমান্তে তৎপর হয়ে উঠেছে, আমাদের দেশে নানা নাশকতামূলক কাজ করে বেড়াচ্ছে ওদের দেশের গেরিলা সেনারা। আর দুই প্রতিবেশী দেশের শাসক ও শোষকগোষ্ঠীর একই সমস্যা হলে তো কথাই নেই, দুই সরকার গোপন সমঝোতায় নিজেদের মধ্যে যুদ্ধ বাধিয়ে দিয়ে বেতারে-দূরদর্শনে দেশপ্রেমের গানের বন্যা বইয়ে দিয়ে এমন গণউন্মাদনার সৃষ্টি করে যে, ভিখারিও একদিন উপোস করে থেকে তার একদিনের ভিক্ষে করে পাওয়া অর্থ যুদ্ধখাতে তুলে দেয়, সদ্য বিবাহিত গা থেকে খুলে দেয় গহনা। দরিদ্র মানুষগুলো আরও বেশি দারিদ্রে পাঁকে ডুবতে ডুবতে স্বপ্ন দেখে তাদের দেশের সেনারা অন্য দেশের লোকেদের কীভাবে গুলিগোলায় ছিন্নভিন্ন করে দিচ্ছে। গরিব মানুষগুলো দেশের স্বার্থে ভুলে যায় ব্যক্তিগত পাওয়া না পাওয়ার ক্ষোভ বঞ্চনার তীব্র জ্বালা।
গরিব দেশগুলো যখন একে অন্যের বিরুদ্ধে নেমে পড়ে, সীমান্ত সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ে, তখন লাভ হয় কাদের? ক্ষতিই বা কাদের? লাভ বিদেশি অস্ত্র ব্যবসায়ীদের, লাভ দেশি অস্ত্র-দালালদের, লাভ শাসক ও শোষকদের, বহু সংকটময় মুহূর্তে মানুষের দৃষ্টি অন্য দিকে ঘুরিয়ে দেওয়া যায় বলে। লোকসান পুরোটাই সাধারণ মানুষের। অনেক আন্দোলন, অনেক অবরোধ, অনেক ক্ষোভ যুদ্ধের আগুনে পুড়ে খাক হয়ে যায়। যুদ্ধের সময় যদি আন্দোলন চালাতে যান, শাসককুল আপনার সামনে পিছনে ‘পঞ্চম বাহিনী’র অর্থাৎ শত্রুদেশের গুপ্তচর বলে ছাপ মেরে দেবে। আর জাতীয়তাবাদের গণ-উন্মাদনার জোয়ারে শোষিত মানুষই সেই কথা পুরোপুরি বিশ্বাস করে নেবে, বিরোধিতা করবে আপনাদের আন্দোলনের।
‘জাতীয়তাবাদ’ শব্দটার বাস্তবিকই অর্থ কী? আসলে ‘জাতীয়তাবাদ’ শব্দের কোনও অর্থই হয় না, অর্থ হতেই পারে না। ‘জাতি’ কথার অভিধানগত অর্থ সমলক্ষণ অনুযায়ী বিভাগ। যেমন মানবজাতি, উদ্ভিদজাতি, পশুজাতি, নারীজাতি, পুরুষজাতি। আবার ধর্মের অন্তর্গত মানবসমষ্টিও জাতি। যেমন হিন্দুজাতি, মুসলমান জাতি, খ্রিস্টানজাতি। আবার সামাজিক বিভাগজাত মানবসমষ্টিও জাতি। যেমন ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, বৈদ্য, চণ্ডাল। এমনিভাবে জাতি-বিভাগ নিয়ে আলোচনা প্রায় অসীম পর্যায়ে নিয়ে যাওয়া যায়।
‘জাতীয়’ কথার অর্থ জাতি সম্বন্ধীয়। ‘বোধ’ কথার অর্থ উপলব্ধি, অনুভব। তাহলে আমরা ‘জাতীয়তাবোধ’ কথাটির অর্থ হিসেবে পেলাম ‘জাতি সম্বন্ধীয় উপলব্ধি।’ কিন্তু কোন জাতি সম্বন্ধীয় উপলব্ধি? যে কোনও জাতি সম্বন্ধীয় উপলব্ধিই হতে পারে।
শাসকশ্রেণি বা রাজনীতিকরা অথবা তাদের স্নেহধন্য কলমচীরা ‘জাতীয়তাবাদী’ বলতে ভারতের প্রতি ভালোবাসা বলে ব্যাখ্যা চাপাতে চেয়েছেন। ‘ভারতীয় জনতা পার্টি’ ও ‘বিশ্বহিন্দু পরিষদ’ ‘জাতীয়তাবাদী’ শব্দটিকে ব্যবহার করে হিন্দুজাতীয়তাবোধ জাগ্রত করতে চাইছে, হিন্দুজাতীয়তাবোধের গণউন্মাদনা সৃষ্টি করতে চাইছে। এই বিষয়ে ওরা যে বিশাল সাফল্য পেয়েছে, সাম্প্রতিক সংসদীয় নির্বাচনে ভারতীয় জনতা পার্টির সাফল্য তারই প্রমাণ। ‘আমরা বাঙালি’ আবার ‘জাতীয়তাবাদী’ শব্দটিকে প্রয়োগ করে বাঙালিদের মধ্যে সাম্প্রদায়িক সুড়সুড়ি দিয়ে বাঙালিত্ব জাগাবার চেষ্টা করছে।
শাসকশ্রেণি জাতীয়তাবাদের ধ্যানধারণা সাধারণের মাথায়
ঢুকিয়ে দিয়ে ধনীজাতীয় মানুষ ও গরিবজাতীয় মানুষদের
সহাবস্থানের কথা বোঝায়। ধনী দরিদ্র নির্বিশেষে
প্রত্যেককে দেশের জন্য, জাতির জন্য
একতাবদ্ধ হওয়ার পক্ষে
হাওয়া তোলে।
এমন ব্যাপক প্রচারে নিপীড়িত দরিদ্র মানুষগুলো তাদের শোষকদের চিনতে ভুলে যায়, তাদের শত্রু চিনতে ভুলে যায়। ভুলে যায় তাদের কারা অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক এবং সাংস্কৃতিকভাবে শোষণ করছে, গিলে খাওয়ার চেষ্টা করছে।
‘জাতীয়তাবোধ’ বলতে যদি মানবজাতি সম্বন্ধীয় উপলব্ধিকে আমরা বুঝি এবং ‘জাতীয়তাবাদ’ বলতে যদি মানবজাতি সম্বন্ধীয় মতবাদকে বুঝি তাহলেও সেই একই সমস্যা থেকেই যায়। এই জাতীয় কোনও মতবাদ দ্বারা সম্পূর্ণ মানবজাতির মঙ্গল অসম্ভব। মানবজাতির মধ্যেকার শোষকশ্রেণির মঙ্গল মানেই শোষিত শ্রেণির অমঙ্গল। আর শোষিত শ্রেণির মঙ্গল মানেই শোষকশ্রেণির অমঙ্গল। দুই শ্রেণির মঙ্গল যেহেতু একই সঙ্গে সম্ভব নয়, তাই দুই শ্রেণির সহাবস্থানে মানবজাতির মঙ্গলচিন্তাও অতি অবাস্তব। শোষিত শ্রেণির মাথার থেকে শোষিত শ্রেণির চেতনা দূর করতেই এই ধরনের জগাখিচুড়ি মতবাদ গেলানোর নিরন্তর প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছে রাষ্ট্রশক্তি ।
‘সংহতি’ শব্দের অর্থ ‘নিবিড় সংযোগ’—‘চলন্তিকা’য় এমনটাই লেখা আছে ৷ সাহিত্য সংসদ প্রকাশিত ‘বাংলা ভাষার অভিধান’-এ ‘সংহতি’র অর্থ হিসেবে আছে ‘ঘন সন্নিবেশ, নিবিড়তা’। সাহিত্য অকাদেমি প্রকাশিত ‘বঙ্গীয়, শব্দকোষ’ -এ ‘সংহতি’ বলতে বলা হয়েছে, ‘ঐকমত্য, একচিত্ততা, নিবিড়ভাব, একসঙ্গে’।
একদিকে যখন উত্তর-পশ্চিম ভারতের পাঞ্জাব জম্মু-কাশ্মীর জ্বলছে, জ্বলছে দক্ষিণ-ভারতের অন্ধ্র, পূর্ব-ভারতের গোর্খাল্যান্ড, ঝাড়খণ্ড, ত্রিপুরা, অসম, মিজোরাম, নাগাল্যান্ড, মণিপুর তখন রাষ্ট্রশক্তি ‘জাতীয় সংহতির লেবেল মেরে আর এক রকমের উত্তেজক মাদক ছাড়ল বাজারে গণ-হিস্টিরিয়া গড়ে তুলতে। ‘ব্রান্ডটিকে জনপ্রিয় করতে দূরদর্শন দারুণ দারুণ কয়েকটা অ্যাড-ফিল্ম তৈরি করল চলচ্চিত্র ও সংগীত জগতের স্টার-সুপারস্টার- মেগাস্টারদের নিয়ে। বিভিন্ন প্রচার মাধ্যম ও রাজনৈতিক দলগুলোও শুরু করল জাতীয় সংহতির বন্দনা। ‘জাতীয় সংহতি উৎসব’, ‘জাতীয় সংহতি পুরস্কার’, ‘জাতীয় সংহতি দৌড়’, এমনি নানা ধরনের জাতীয় সংহতির উপর নানা কার্যক্রম লাগাতারভাবে গ্রহণ করেই চলেছে ডান-বাম নির্বিশেষে নানা রাজনৈতিক দল। এই প্রচারগুলোর মধ্য দিয়ে তারা বারবার মানুষের মাথায় ঢোকাতে লাগল হিন্দু, মুসলমান, শিখ, খ্রিস্টান, বাঙালি, বিহারি, পাঞ্জাবি, কাশ্মীরি, অসমিয়া, নাগা, তামিল, মারাঠি ইত্যাদি নানা শ্রেণির জাতির মধ্যে শান্তি ও সহাবস্থান বজায় রাখার কথা, ক্ষুব্ধতা না রেখে ‘মিলে-জুলে’ থাকার কথা। এই প্রচারের মাধ্যমে সাধারণের মাথায় ধর্ম-ভিত্তিক, ভাষা-ভিত্তিক, প্রদেশ-ভিত্তিক শ্রেণিবিন্যাসের কথাই বলা হল। প্রেম-প্রীতি বজায় রেখে এই বিন্যাসকৃত শ্রেণি সহাবস্থানের কথা বলার মধ্য দিয়ে নিপীড়িত মানুষদের ভুলিয়ে রাখা হল আসল সত্যকে—পৃথিবীতে রয়েছে মাত্র দু’টি শ্রেণি। শোষক এবং শোষিত। এই শ্রেণি বিন্যাসের বাইরে হিন্দু, মুসলমান, শিখ, খ্রিস্টান, বাঙালি, বিহারি, পাঞ্জাবি, অসমিয়া, রাজস্থানি, তামিল, নাগা, সাঁওতাল, মণিপুরি—এসবই শেষ পর্যন্ত সমাজ সম্পর্কের ক্ষেত্রে গুরুত্বহীন। অত্যাচারিত, বঞ্চিত, শোষিত মানুষগুলোর শোষকদের সঙ্গে সংহতি অর্থাৎ শান্তি ও সহাবস্থান বজায় রেখে চলার একটিই অর্থ—শোষক ও শোষিত—এই খাদক ও খাদ্য সম্পর্কের দুই শ্রেণি বিন্যাসকেই বজায় রাখা।
গোটা পৃথিবী জুড়ে মানব-সংহতি, মানব সৌহার্দ্য, মানব-
ভ্রাতৃত্বের জন্যে একটি লড়াই অবশ্য প্রয়োজনীয়-
শোষকের বিরুদ্ধে শোষিতের লড়াই। একটি
শ্রেণির উচ্ছেদের মধ্য দিয়েই আসতে
পারে বাস্তব সংহতি – তার
আগে কখনওই নয়।
শোষক ও শোষিতের কোনও জাত হয় না, ধর্ম হয় না, ভাষা হয় না, দেশ হয় না, প্রদেশ হয় না। যে কোনও ধর্মের যে কোনও জাত-পাতের, যে কোনও ভাষাভাষী, যে কোনও দেশের শোষকদের একটিই পরিচয় হওয়া উচিত – শোষক। যে কোনও ধর্মের, যে কোনও জাত-পাতের, যে কোনও ভাষাভাষী, যে কোনও দেশের শোষিতদের একটিই পরিচয় হওয়া উচিত—শোষিত। শোষক ও শোষিতের মধ্যে সংহতির একটাই অর্থ—শোষণ ব্যবস্থার অবস্থান। এমন ‘সংহতি’ কখনওই সমাজ-সচেতন, মানবিকতার বিকাশকামী, সুস্থ সংস্কৃতির প্রসারকামীর কাছে কাম্য হতে পারে না।
বিচ্ছিন্নতাঃ যন্ত্রণার দাউদাউ আগুনে আপসের জল ঢালো নতুবা পুড়তেই থাকবে বিচ্ছিন্নতার আত্মনিগ্রহে
‘বিচ্ছিন্নতাবাদী’ শব্দটির সঙ্গে এখন আমরা বড় বেশি রকম ভাবেই পরিচিত হয়ে উঠেছি ব্যাপক ও লাগাতার প্রচারের দৌলতে। আমরা অনেকেই এই প্রচারের আবর্তে প্রভাবিত হয়ে ভাবতে শুরু করেছি ‘বিচ্ছিন্নতা’ এক ধরনের নৈরাশ্যতাড়িত অভিব্যক্তি। বিচ্ছিন্নতার এই নেতিবাচক আবেদন আমাদের চিন্তাকে প্রভাবিত করায় আমরা ‘বিচ্ছিন্নতা’র এই নেতিবাচক আবেদন শোনার সঙ্গে সঙ্গে অচেতন বা সচেতনভাবে কিছুটা বিরক্ত বা বিরূপ হয়ে উঠি। সরকার যে ‘জনগোষ্ঠী’ বা আন্দোলনকারীদের ‘বিচ্ছিন্নতাবাদী’ বলে ঘোষণা করে, তাদের সম্বন্ধেও আমরা যথেষ্ট বিরূপ ধারণা পোষণ করতে শুরু করি। আমরা ভাবতে থাকি বিচ্ছিন্নতাবাদীরা আমাদের দেশ-মাতৃকার অঙ্গহানি ঘটাতে চাইছে। এ-ভাবে বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন আরও বেশি বেশি হতে থাকলে আমাদের দেশের তো অস্তিত্বই থাকবে না। ‘দেশকে আমরা টুকরো হতে দেব না’—এই মানসিকতাই তখন আমাদের মধ্যে প্রবল হয়ে ওঠে।
‘বিচ্ছিন্নতা’ কী? সকলের থেকে স্বতন্ত্র, সকলের থেকে আলাদা, সকলের সঙ্গে না মানিয়ে নিতে পারা।
কোনও অসুস্থ সমাজ ব্যবস্থায় সুস্থ ব্যক্তিত্ববোধ
সম্পন্ন মানুষ ‘বিচ্ছিন্ন’ হতে বাধ্য।
পৃথিবীর ইতিহাসে গ্যালিলিও, প্যারাসেলসাস, ব্রুনো, বিদ্যাসাগর-এর মতো অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বের আগমনের কথা লেখা আছে, যাঁরা প্রত্যেকেই সমাজে ছিলেন একাকী। এইসব বিদ্রোহী মানুষগুলো প্রথাগত চিন্তার স্থবিরত্বকে চূর্ণ করতে গিয়ে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিলেন সেই সময়কার সমাজের বৃহত্তর মানবগোষ্ঠী থেকে। সেকালের বিচ্ছিন্ন মানুষদের সঠিক মূল্যায়ন ক্ষমতা ছিল না সেইসময়কার সংখ্যাগরিষ্ঠ মানবগোষ্ঠীর। আজ সেইসব বিচ্ছিন্ন মানুষরাই এ-যুগের মানুষদের কাছে আদর্শ ও প্রেরণার উৎস হয়ে উঠেছেন।
যে বিচ্ছিন্নতার অর্থ শোষণের অবসানমুখী সংগ্রাম, শোষণযুক্ত
সমাজ থেকে বিযুক্ত হওয়ার তীব্র আকুতি, সুস্থ সংস্কৃতি
বিকাশমুখী চেতনা, সুস্থ আত্মবিকাশের চেতনা,
সেই বিচ্ছিন্নতা অবশ্যই মনুষ্যত্বের
কাম্য, সভ্যতার কাম্য।
যে সমাজ আগাপাছতলা ডুবে আছে দুর্নীতির পঙ্কিলতায়, যে সমাজে শাসন ক্ষমতায় বসতে রাজনৈতিক দলগুলোকে ভিক্ষাপাত্র নিয়ে ঘুরতে হয় ধনকুবেরদের দোরে দোরে, যে সমাজে বৈষম্য ও শোষণ লাগাম ছাড়া, সেই সমাজ থেকে কোনও জনগোষ্ঠী যদি বেরিয়ে যেতে চায়, তবে তাদের সেই উচ্চশির স্পর্ধিত সংগ্রামকে অভিনন্দন জানানোই প্রতিটি বঞ্চিত মানুষের একমাত্র অভিব্যক্তি হওয়া উচিত। কিন্তু সেই ‘উচিত ’টাই ঘটছে না শাসকশ্রেণির সুনিপুণ মগজ ধোলাইয়ের কল্যাণে।
শক্তিমান বহু সাহিত্যিকের কলমে এমন বহু চরিত্র উঠে এসেছে যারা ‘স্যাডিস্ট’, ধর্ষকামী, বিকারগ্রস্ত, নৈরাশ্যতাড়িত, অসুস্থ, বিচ্ছিন্নতার শিকার এক মানসিক রোগী। এদের কেউ কেউ যৌন উচ্ছৃঙ্খলার পক্ষে যুক্তি হাজির করে ব্যক্তি স্বাধীনতার নামে। আর এইসব সাহিত্যিকদের সৃষ্ট ওইসব চরিত্রগুলো দু-মলাটের বাইরে দূরদর্শনের ও সিনেমার পর্দায় হাজির হয়ে আমাদের চেতনাকে প্রভাবিত করেছে। ফলে আমরা একটা ধারণা পোষণ করতে শুরু করেছি ‘বিচ্ছিন্নতা’ একটা সামাজিক ব্যাধি। আমরা ভুলে থেকেছি ব্যাধিগ্রস্ত সমাজের বিরুদ্ধে আদর্শবাদী তরুণদের স্বাভাবিক প্রতিবাদ, প্রতিরোধ এবং সংগ্রামও ‘বিচ্ছিন্নতা’।
কোনও জনগোষ্ঠীর বৃহত্তর অংশ যখন তাদের অধিকার ছিনিয়ে নিতে অথবা শোষণমুক্ত সমাজ থেকে বিযুক্ত হতে সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়ে, তখন সেই জনজাগরণকে সামাল দেওয়ার সাধ্য রাষ্ট্রশক্তির থাকে না।
যে আন্দোলনে শরিক হয়েছে একটি জনগোষ্ঠীর প্রায় প্রতিটি পরিবার, সেই আন্দোলনকে শেষ করতে হলে সেই জনগোষ্ঠীর প্রতিটি পরিবারকেই শেষ করতে হয়। যা সীমিত সেনা ও পুলিশের সাহায্যে সম্ভব নয়।
ওই জনগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে সর্বাত্মক যুদ্ধ ঘোষণা করে ধ্বংসের আগুনে প্রতিবাদী প্রতিটি পরিবারকে শেষ করে দিয়ে শ্মশানের স্তব্ধতা আনাও এ-যুগে সম্ভব নয়। আধুনিকতম যোগাযোগের কল্যাণে পৃথিবী অনেক ছোট হয়ে গেছে। এইভাবে একটি জনগোষ্ঠীকে নিশ্চিহ্ন করতে গেলে পৃথিবীর বহু প্রান্ত থেকেই এমন নৃশংসতার বিরুদ্ধে সোচ্চারে প্রতিবাদের ঝড় উঠবেই। আর তাই পৃথিবীর বহু দেশেই বিভিন্ন গোষ্ঠীর জনজাগরণের কাছে পিছু হটতে হয়েছে শাসক ও শোষকশ্রেণিকে।
এই বক্তব্যের সত্যতা প্রমাণে পৃথিবী জুড়ে ছড়িয়ে আছে বহু দৃষ্টান্ত । আমাদের খুব কাছের দেশ শ্রীলঙ্কার ক্ষেত্রেও দেখতে পাচ্ছি সংগ্রামী তামিল জনগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে পুলিশ, সেনা এমন কী, প্রতিবেশী দেশ ভারতের সেনা নামিয়ে সমস্ত রকম ভাবে দমননীতি চালিয়েও দমন করতে পারেনি তামিল জনগোষ্ঠীর সংগ্রামকে।
আমাদের দেশেও এমন উদাহরণ বিরল নয়। হাতের কাছেই দু’টি জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত পাঞ্জাব ও কাশ্মীর, সেখানে জনগোষ্ঠীর সিংহভাগের আন্দোলনের পক্ষে সমর্থন থাকায় আন্দোলন ধ্বংস করতে গিয়ে সর্বাত্মক চেষ্টা সত্ত্বেও সরকার এমন নিদারুণভাবে বারবার ব্যর্থ হচ্ছে। কারণ, ওসব জায়গায় আন্দোলন ধ্বংস করতে হলে প্রায় সমগ্র জনসমষ্টিকেই ধ্বংস করতে হয়, যা অসম্ভব। অসম, অন্ধ্রে একই ভাবে যত বেশি বেশি করে স্থানীয় মানুষরা আন্দোলনের সমর্থনে এগিয়ে আসছেন ততই এই আন্দোলন ধ্বংস করা সরকারের পক্ষে অর্থাৎ রাষ্ট্রশক্তির পক্ষে কঠিন কাজ হয়ে উঠছে।
শ্রীলঙ্কা, পাঞ্জাব, কাশ্মীর, অসম বা অন্ধ্রের আন্দোলনকে সমর্থন বা অসমর্থন করা এই উদাহরণ টেনে আনার উদ্দেশ্য নয়। উদ্দেশ্য— আন্দোলনকারীদের সামনে দৃষ্টান্ত টেনে এনে বোঝার ব্যাপারটা সহজতর করা। সঙ্গে সঙ্গে একথা মনে রাখাটাও প্রয়োজনীয়, বিচ্ছিন্নতার সুস্থ ও বলিষ্ঠ প্রকাশ শোষণমুক্ত সমাজ গঠনের প্রয়াসে। যখন কোনও জনগোষ্ঠীর যুক্তিবাদী চিন্তার সঙ্গে যুক্ত হবে আদর্শ-উদ্বুদ্ধ শোষণমুক্ত সমাজ গঠনের চেতনা, তখন রাষ্ট্রশক্তি ওই জনগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে দেশবাসীকে খেপিয়ে তুলতে জনগোষ্ঠীর বুকে বিচ্ছিন্নতাবাদীর লেবেল লাগাবে। ‘বিচ্ছিন্নতাবাদী’ শব্দটা ‘নাস্তিক’ শব্দের মতোই এমনই এক নেগেটিভ অ্যাপ্রোচ বা নেতিবাচক আবেদনে ভরা দীর্ঘ প্রচারের দৌলতে। ভাবুন তো, একটা শোষণযুক্ত সমাজ থেকে বেরিয়ে গিয়ে যে জনগোষ্ঠী শোষণমুক্ত সমাজ গড়তে চাইবে, নিজেদের শাসন কায়েম করতে চাইবে, তারা তো দেশের মূল জনগোষ্ঠী থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যেতেই বাধ্য। যে সমাজে শোষক ও শোষিতদের সহাবস্থান বিরাজ করছে, সে সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে তবেই কোনও জনগোষ্ঠী গড়ে তুলতে পারে শোষণমুক্ত সমাজ। একটি শোষণমুক্ত জনগোষ্ঠী বহুকে প্রভাবিত করতে পারবে এই পরম সত্যটি মাথায় রেখেই জনগোষ্ঠীকে তাঁবেতে রাখতে সচেষ্ট বা জনগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে আক্রমণকারীর ভূমিকায় অবতীর্ণ রাষ্ট্রশক্তি এমনভাবে প্রচার চালাতে থাকে যে সাধারণ মানুষ দেশ বলতে, দেশের বৃহত্তম নিপীড়িত জনসাধারণ, এই সত্যটি ভুলে গিয়ে দেশকে একটা ভূখণ্ড একটা ম্যাপ ভেবে ফেলে। ফলে শোষণমুক্ত সমাজ ব্যবস্থা থেকে মুক্তি পেতে চাওয়া রক্তাক্ত শোষিত মানুষগুলোর সংগ্রামকে অভিনন্দিত করার পরিবর্তে, নীতিগতভাবে সমর্থন জানাবার পরিবর্তে, আমরা শোষিত মানুষরাও ভুল করে অঙ্গহানির ব্যথা অনুভব করি। শোষক শ্রেণির খপ্পর থেকে কিছু মানুষ যে অন্তত মুক্তি পেয়েছে ম্যাপের ওই বিচ্ছিন্ন অংশটা কিছু কিছু মুক্তিকামী মানুষদের জয়েরই প্রতীক, যা আরও অনেক নিপীড়িত মানুষকে উদ্বুদ্ধ করবে, এ-কথা ভুলিয়ে রাখতেই রাষ্ট্রশক্তি বিচ্ছিন্নতাবাদীদের সঙ্গে জুড়ে দিতে সচেষ্ট একটা নেতিবাচক আবেদন ৷
বিচ্ছিন্নতার সঙ্গে আদর্শ ও পরিষ্কার স্বচ্ছ দৃষ্টিভঙ্গি যুক্ত হয়েই গড়ে ওঠে বিপ্লবী চেতনা। পরিষ্কার স্বচ্ছ দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তোলাই যুক্তির কাজ, যুক্তিবাদী আন্দোলনের কাজ ।
যুক্তিবাদী আন্দোলন, কুসংস্কার মুক্তির আন্দোলন আপাত
নিরীহ এক আন্দোলন, যার মধ্যে লুকিয়ে রয়েছে
এক অসাধারণ শক্তিশালী গণ-অভ্যুত্থানের
বীজ, ঠাসা রয়েছে শোষণমুক্তির
বিস্ফোরক বারুদ।
প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মঃ হানিমুনে বাঘ ডাকে
যুক্তিবাদ-বিরোধিতার প্রকৃত উৎস কোথায়—এই বিষয়ে আন্দোলনকারীদের স্পষ্ট ধারণা না থাকলে আন্দোলন ব্যর্থ হতে বাধ্য। যুক্তিবাদ আন্দোলনের পক্ষে জয় ছিনিয়ে আনতে হলে কে প্রধান শত্রু, কোন্ কোন্ শক্তি তার সহায়ক, কী তার শক্তিশালীতম অস্ত্র এসব বিষয়ে পরিষ্কার, স্পষ্টভাবে জানতে হবে।
যুক্তিবাদ বিরোধিতার প্রধান উৎস অবশ্যই শোষকশ্রেণি। তার সহায়ক শক্তি বহু। শোষক শ্রেণি কৃপাধন্য হওয়ার মতো মানুষের অভাব নেই এই সমাজে। তবে কৃপা পাওয়ার জন্য কিছু ক্ষমতা চাই বই কী, তা সে বুদ্ধিবলই হোক, কী বাহুবলই হোক। প্রধান সহায়ক শক্তি অবশ্যই রাষ্ট্রক্ষমতা, সরকার—যারা শোষকদের অর্থে নির্বাচন জিতে এসে গদিতে বসে মুখে গরিব-দরদী এবং কাজে ধনিক-তোষণের ভূমিকা গ্রহণ করে। শত্রু শিবিরে অমোঘ অস্ত্রটির নাম ধর্ম, প্রাতিষ্ঠানিক ধর্ম। হিন্দু, ইসলাম, খ্রিস্ট, বৌদ্ধ, শিখ, পাশি ইত্যাদি ধর্মীয় বিশ্বাসের ওপর পুরোপুরি নির্ভর করে দাঁড়িয়ে আছে ধর্মীয় বিশ্বাসীদের প্রাতিষ্ঠানিক রূপ বা সাংগঠনিক রূপ। ‘প্রাতিষ্ঠানিক ধর্ম’ হল এইসব ধর্মীয় বিশ্বাসীদের প্রাতিষ্ঠানিক রূপের ভিত্তিমূল। এই প্রাতিষ্ঠানিক ধর্ম বা তথাকথিত ধর্ম অবশ্যই যুক্তিবিরোধী, প্রগতির প্রতিবন্ধক, জ্ঞান ও মুক্তচিন্তার অন্তরায়, পুরুষকার বিরোধী, কুসংস্কারের স্রষ্টা এবং তাই শোষকশ্রেণির শ্রেষ্ঠতম হাতিয়ার।
(ঈশ্বর, পরমপিতা, পরমব্রহ্ম বা ওই জাতীয় চিন্তার ধারক-বাহক তথাকথিত ধর্ম যে আক্ষরিক অর্থেই যুক্তিবিরোধী, প্রগতির অন্তরায়, জ্ঞান ও মুক্ত চিন্তার প্রবন্ধক, পুরুষকার বিরোধী, কুসংস্কারের স্রষ্টা—এ বিষয়ে যে বিস্তৃত আলোচনা ও তথ্যপ্রমাণ হাজির করা প্রয়োজন, তা সবই নিয়ে হাজির হওয়ার ইচ্ছে রইল ‘অলৌকিক নয়, লৌকিক’ গ্রন্থের চতুর্থ খণ্ডে)।
‘ধর্ম’ ক্যানসারের চেয়েও মারাত্মক, পারমাণবিক বোমার চেয়েও
ধ্বংসকারী। শোষকশ্রেণির শ্রেষ্ঠতম এই হাতিয়ারকে ধ্বংস
করতে না পারলে চেতনা-মুক্তির যুদ্ধ জয় অধরাই
থেকে যাবে—এই পরম সত্য প্রতিটি
চেতনা-মুক্তির আন্দোলনকারীকে
বুঝতেই হবে।
মানব সমাজের প্রগতির দৃষ্টিকোণ থেকে ধর্মের এক বিপজ্জনক দিক হল ধর্মের ভিত্তিতে মানবসমাজ বহু গোষ্ঠীতে বিভক্ত। ফলে শোষিত মানুষগুলোও আর এককাট্টা থাকে না, বহু ভাগে বিভক্ত ও বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। এই গোষ্ঠী-ভাগের সুযোগ নেয় শঠ রাজনীতিকরা। শঠ রাজনীতিকরা ও রাজনৈতিক দলগুলো নিজ স্বার্থেই ধর্মান্ধতার অবসান চায় না। চাইতে পারে না। তারা নিপীড়িত মানুষদের বিক্ষোভ থেকে বাঁচতে অথবা ভোট কুড়োবার স্বার্থে বঞ্চিত মানুষগুলোকে ‘মুরগি লড়াই’তে নামায়। নিপুণ কুশলী প্রচারের ব্যাপকতায় সাধারণ মানুষ ভুলে যায়, যে কোনও ধর্মের, যে কোনও জাতপাতের কালোবাজারির একটাই পরিচয় হওয়া উচিত—কালোবাজারি, শোষক। যে কোনও ধর্মের, যে কোনও জাতপাতের দরিদ্র শ্রমিক-কৃষকদের একটিই পরিচয়—দরিদ্র, শোষিত। দরিদ্র নিপীড়িত মানুষগুলো যখন নিজেদের মধ্যে জাতপাত বা ধর্ম নিয়ে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়, তখন লাভের ক্ষীরটুকু জমা হয় শাসক ও শোষকের ঘরেই। গরিব মানুষের বিরুদ্ধে গরিব মানুষকে লড়িয়ে দেওয়ার জন্যে ধর্মের বিপুল প্রভাবের কথা মনে রেখেই শোষকশ্রেণি ধর্ম নামক অস্ত্রটিকে আরও শক্তিশালী করার গবেষণায় রত ।
ধর্মবিশ্বাসের মধ্য দিয়ে মানুষের মধ্যে যে পূর্বজন্ম, কর্মফল, ঈশ্বরবিশ্বাস, ঈশ্বর নির্ভরতা, অলৌকিক বিশ্বাস গড়ে উঠেছে তারই ফলে ধর্মবিশ্বাসী বঞ্চিত মানুষগুলো তাদের বঞ্চনার কারণ হিসেবে আসল খল-নায়কদের দায়ী না করে দায়ী করেছে কল্পনার ভগবানের অভিশাপকে, পূর্বজন্মের কর্মফলকে দুঃখে, অপমানে, সব হারাবার যন্ত্রণায়, ক্ষুব্ধতায় খানখান হতে গিয়েও ভেঙে না পড়ে পরমপিতা জাতীয় কারো চরণে সব ক্ষোভ, সব দুঃখ যন্ত্ৰণা ঢেলে দিয়ে প্রার্থনা করেছে— মোরে সহিবারে দাও শকতি।
ধর্মের সমর্থক অনেকেই বলেন—পরমপিতা জাতীয় কারো কাছে আত্মসমর্পণের মধ্যে রয়েছে অপার শান্তি, সহ্য করার শক্তি।
পুরুষকারহীন মানুষই জীবনের বিভিন্ন ঘাত-প্রতিঘাত থেকে
মুক্তি পাওয়ার আশায় পরমপিতাজাতীয়ের কারও কাছে
আত্মসমর্পণ করে পরিত্রাণ পেতে চায়। আপসপন্থী
মানুষই শান্তি খোঁজে আত্মসমর্পণে। কাদা-নরম
মেরুদণ্ডী মানুষই নিজ শক্তিতে প্রতিরোধ
না গড়ে আঘাত সহ্য করার শক্তি
খোঁজে পরের শ্রীচরণে।
ধর্মের সমর্থক অনেকে এ-কথাও বলেন-ধর্মই সমাজকে ধারণ করে রয়েছে, সমাজের শৃঙ্খলা বজায় রেখে চলেছে।
প্রাচীনকালে যখন রাজনৈতিক সংহতি, আইনের শাসন ছিল দুর্বল, তখন ধর্ম দিয়ে সামাজিক শৃঙ্খলা রক্ষার চেষ্টা হয়েছে, হয়তো বা তার কিছু প্রয়োজনও ছিল। কিন্তু আধুনিক রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাচ্ছি আইনের শাসন না থাকলে সামাজিক শৃঙ্খলা রক্ষাও অসম্ভব হয়ে পড়ে— তা সে দেশের মানুষ যতই ধর্মভীরু হোক না কেন?
এই প্রসঙ্গে একটি ছেট্টো উদাহরণ টানছি। ১৯৮৮ সালে আমাদের দেশে ১০০ জন অপরাধীর ওপর একটা অনুসন্ধান চালিয়েছিল ‘ভারতীয় বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী সমিতি’। বিভিন্ন ধরনের এই অপরাধীই বিশ্বাস করত ঈশ্বরের অস্তিত্বে, বিশ্বাস করত পাপ পুণ্যে। বিশ্বাস করত পাপের ফল নরক-যন্ত্রণা। এই বিশ্বাস কিন্তু অপরাধীদের অপরাধ থেকে নিবৃত্ত করতে পারেনি।
যে দেশে সর্বোচ্চ পদ থেকে সর্বনিম্ন পদে সাবলীলভাবে বয়ে চলেছে দুর্নীতির স্রোত, সে দেশে হত্যাকারী, নারী-ধর্ষক, গুন্ডা, ছিনতাইবাজ, চোর-চোট্টা-চিটিংবাজ রাজনৈতিক দলের ছত্রছায়ায় থাকলে সাত-খুন-মাপ হয়ে যায়। যে দেশে গুন্ডা-বদমাইশ পকেটে না থাকলে রাজনীতি করা যায় না, সে দেশের মানুষ দু-বেলা ঠাকুর প্রণাম সেরে, নামাজ পড়েও দুর্নীতি চালিয়ে যাবেই । এতক্ষণ উদাহরণ হিসেবে যে ধর্মপ্রাণ ভারতের কথা বললাম, এটা বুঝতে নিশ্চয়ই সামান্যতম অসুবিধা হয়নি সমাজসচেতন পাঠক-পাঠিকাদের।
প্রগতিবিরোধী চিন্তা এবং কুসংস্কারের উৎস ধর্ম, অধ্যাত্মচিন্তা। তাই কুসংস্কারমুক্ত সমাজ গড়তে গেলে ধর্মকে আঘাত দিতেই হবে। ধর্মকে আঘাত না দিয়ে যাঁরা কুসংস্কারমুক্ত সমাজ গড়ার স্বপ্ন দেখেন, শোষণমুক্ত সমাজ গড়ার স্বপ্ন দেখেন, তাঁরা হয় কল্পনাবিলাসী, নতুবা হুজুর-মজুর সম্পর্ককে বজায় রাখতে সচেষ্ট। এ তো বিষবৃক্ষের গোড়াকে বাঁচিয়ে রেখে আগা কাটতে কাঁচি চালানো। এই সত্যকে ভুললে তো চলবে না— শোষণমুক্ত সমাজ গড়ারই একটি পর্যায়, একটি ধাপ শোষিত মানুষদের কুসংস্কারমুক্তি, শোষিত মানুষদের চেতনা-মুক্তি, যার আর এক নাম— সাংস্কৃতিক বিপ্লব।
যেসব সংস্থা ও ব্যক্তি মানুষকে কুসংস্কারমুক্ত করতে, মানুষের ঘুম ভাঙাতে গান বাঁধছে, নাটক নিয়ে হাজির হচ্ছে, সভা করে বক্তব্য রাখছে, ফাঁস করছে ওঝা গুণিনদের নানা কারসাজি— তারা অবশ্যই খুব ভালো কাজ করছে। অবশ্যই এর প্রয়োজন আছে। কিন্তু সংস্কারের গোড়া ধরে টান দিতে হলে যে তথাকথিত ধর্মের প্রকৃত স্বরূপ শ্রমজীবী বঞ্চিত মানুষদের সামনে তুলে ধরতে হবে একথাও মনে রাখতে হবে। সঠিক রণকৌশলের স্বার্থে তত্ত্বগতভাবে ধর্ম বিষয়ে জেনে নিতে হবে। তারপর ঠিক করতে হবে রণনীতি। কোথায়, কখন, কী পরিস্থিতিতে তথাকথিত ধর্মকে কতটা আঘাত হানব, কাদেরকে কেমনভাবে বোঝালে তথাকথিত ধর্মের স্বরূপ ফলপ্রসূ হবে সেটা নিতান্তই কৌশলগত প্রশ্ন।
আমরা বঞ্চিত মানুষের দীর্ঘদিনের বহু অন্ধ-সংস্কার, বহু স্পর্শকাতর সংস্কার নিয়ে বোঝাতে গিয়ে উপলব্ধি করেছি, ওঁরা বোঝার চেষ্টা করেন, ওঁরা বোঝেন, ওঁরা বিষয়ের অনুধাবন করে সংস্কার-মুক্তির লড়াইতে আমাদের সঙ্গে এগিয়ে আসেন, আমাদের নেতৃত্ব দেন। ওঁরা দেশি-বিদেশি পুঁথি পড়ে, ভালো বলতে কইতে বা লিখতে পারার সুবাদে ছাত্রনেতা থেকে জননেতা হননি, ওঁরা বুদ্ধি-বেচা ও ডিগবাজি খাওয়া শেখেননি। ওঁরা লড়াই করতে করতে লড়াকু হয়েছেন, ওঁরা জানতে বুঝতে শিখতে অনেক বেশি আগ্রহী, অনেক বেশি আন্তরিক। মধ্যবিত্তসুলভ মানসিকতা নিয়ে ‘সব জানি’, ‘সব বুঝি’ করে ‘কুয়োর ব্যাঙ’ হয়ে থাকতে নারাজ। সংগ্রাম যখনই ময়দানে নেমে আসে, নেমে আসে রান্নাঘরে বেয়নেটের ফলা তখন মধ্যবিত্ত নেতাদের সীমাবদ্ধতা পচা ঘায়ের মতোই ফুটে ওঠে। বঞ্চনার শিকার শ্রমিক-কৃষক লড়াকুরাই তখন নিজেদের অভিজ্ঞতার মূল্যে সঠিক পথ নির্দেশ করেন। তাঁরা নেতৃত্বে চলে আসেন। তাঁরা ইতিহাস ঘেঁটে নজির খোঁজেন না, নজির তৈরি করে ইতিহাস সৃষ্টি করেন। ওঁদের হাতে নেতৃত্ব চলে যেতে থাকলে সবচেয়ে মুশকিল হয় শোষকশ্রেণির। ওঁদের নেতাদের কেনা যায় না মধ্যবিত্ত পরিবার থেকে বেরিয়ে আসা নেতাদের মতো। এখানেই শাসক শোষকদের মুশকিল।
আজ আমাদের সমিতির বহু শাখা সংগঠন ও সহযোগী সংস্থার নেতৃত্বে শ্রমিক কৃষক শ্রেণির বঞ্চিত বহু মানুষ এগিয়ে এসেছেন। ওঁদের লড়াইয়ের সাথী হিসেবে পেয়েছি, ওঁদের অন্ধ বিশ্বাস ভেঙে দেওয়ার ফলেই। সুতরাং যাঁরা মনে করেন বঞ্চিত মানুষদের ধর্মীয় ধারণাকে আঘাত করলে আমরা বঞ্চিত মানুষদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাব, তাঁরা একথা বলেন হয় ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার অভাব থেকে, নতুবা তাঁরা কুসংস্কারমুক্তির আন্দোলন-আন্দোলন খেলা খেলতে চান এবং বাঁচিয়ে রাখতে চান কুসংস্কারের গোড়াটিকেই ।
আমরা মনে করি, ধর্ম মানে শনি, শীতলার পুজো বা
দরগার সিন্নি নয়। আগুনের ধর্ম যেমন ‘দহন’,
তলোয়ারের ধর্ম যেমন ‘তীক্ষ্ণতা’,
মানুষের ধর্ম তেমনই মনুষ্যত্বের
চরম বিকাশ।
তাই মন্দিরে পুজো না করে, মসজিদে নামাজ না পড়ে, গির্জায় প্ৰাৰ্থনা না করেও মানুষের প্রগতিকামী যুক্তিবাদীরাই প্রকৃত ধার্মিক। এই স্বচ্ছতা নিয়ে নিজ স্বার্থেই শ্রমজীবী শোষিত মানুষদের আজ তথাকথিত ধর্ম ও সেই ধর্ম থেকে সৃষ্ট ধর্মান্ধতার বিরুদ্ধে সোচ্চার হওয়ার সময় হয়েছে।
ধর্মীয় মৌলবাদ ও ধর্মনিরপেক্ষতাঃ বুকে জড়াও আবেগভরে, পৃষ্ঠে বসাও ছুরি
এখানে ধর্ম বলতে আলোচনা সীমাবদ্ধ রাখব প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মে। ‘ধর্ম’ বলতে আরও অনেক কিছুকেই বোঝায় : যেমন, বস্তু-ধর্ম, জাত-ধর্ম, জীব-ধর্ম ইত্যাদি। কিন্তু এ-সব ধর্ম নিয়ে আলোচনার অবতারণা করতে এই প্রবন্ধ নয়। হিন্দু, ইসলাম, খ্রিস্ট, বৌদ্ধ, শিখ, পার্শি ইত্যাদি ধর্মীয় বিশ্বাসের ওপর পুরোপুরি নির্ভর করে দাঁড়িয়ে আছে ধর্মীয় বিশ্বাসীদের প্রাতিষ্ঠানিক রূপ বা সাংগঠনিক রূপ। ‘প্রাতিষ্ঠানিক ধর্ম’ হল এইসব ধর্মীয় বিশ্বাসীদের প্রাতিষ্ঠানিক রূপের ভিত্তিমূল। প্রতিটি প্রাতিষ্ঠানিক ধর্ম বা religion-এর মূলেই রয়েছে ঈশ্বর বা পরমপিতা অথবা অদৃশ্য নিয়ন্ত্রক শক্তির অস্তিত্বে বিশ্বাস; এবং এরই পাশাপাশি আত্মার অস্তিত্ব, পরলোক, পাপপুণ্য, অলৌকিক শক্তির অস্তিত্ব বিষয়ে আস্থা।
‘Fudamentalism’ এর প্রতিশব্দ হিসেবে বাংলায় যে শব্দটি বহুল ব্যবহৃত ও অতি-প্রচলিত, সেটি হল ‘মৌলবাদ।’ Fundamentalism – শব্দের অভিধানগত অর্থ কী ? SAMSAD ENGLISH-BENGALI DICTIO- NARY অনুসারে ‘বাইবেল বা অন্য ধর্মশাস্ত্রের বিজ্ঞানবিরুদ্ধ উক্তিতেও অন্ধবিশ্বাস।’ যাঁরা সংসদের মতো নির্ভরশীল প্রকাশকদের ভারতীয় প্রকাশক হওয়ার দরুন তেমন গুরুত্ব দিতে নারাজ, তাঁদের জন্য Oxford Dictonary থেকে অর্থ তুলে দিচ্ছি, “Strict maintenance of traditional scriptural beliefs”; Chambers Dictionary তে বলা হয়েছে, “Belief in the literal truth of the Bible, against evolution, etc” । অর্থাৎ দেখা যাচ্ছে সংসদ অভিধানে দেওয়া অর্থটি অন্য দুটি অভিধানগত অর্থের সঙ্গে সহমত পোষণ করছে।
এবার ‘মৌলবাদ’ শব্দটিকে একটু ভেঙে দেখা যাক। ‘মৌল’ শব্দের অর্থ ‘মূল থেকে আগত’ বা ‘মূল সম্বন্ধীয়’। ‘বাদ’ শব্দের অর্থ ‘মত’ বা ‘তত্ত্ব’ অর্থাৎ ‘theory’। অর্থাৎ মৌলবাদ শব্দের অর্থ দাঁড়াল ‘মূল থেকে আগত তত্ত্ব’। কোন্ মূল থেকে আগত তত্ত্ব? ধর্মীয় অন্ধ-বিশ্বাস, বিজ্ঞান-বিরোধী বিশ্বাসের মূল থেকে আগত তত্ত্ব। জ্ঞানের আলোকে জীবনকে উদ্ভাসিত করা যদি মনুষ্য-ধর্মের মূল লক্ষ্য বলে ধরে নিই, তবে স্বীকার করতেই হবে, অজ্ঞানের অন্ধকার থেকে আগত তত্ত্ব মনুষ্য-ধর্মের বিপরীতধর্মী।
ধর্মশাস্ত্রকে চরম সত্য বলে বিশ্বাস স্থাপনই যে ‘মৌলবাদ’,
এ বিষয়ে কোনওই সন্দেহের অবকাশ নেই। তাই
প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মের রমরমার সঙ্গেই নির্ভর
করে মৌলবাদের ভয়াবহ উত্থান।
আজ মৌলবাদ রোখার ব্যাপারে প্রায় প্রতিটি রাজনৈতিক দলই ভারতে মৌলবাদী চিন্তার একমাত্র রাজনৈতিক দল হিসেবে ভারতীয় জনতা পার্টিকেই দায়ী করে গাল পাড়ছে। ব্যাপারটা যেন এমনই যে, আর সব রাজনৈতিক দলগুলো মৌলবাদী চিন্তার ঊর্ধ্বে, ধোয়া তুলসীপাতা। এমন শোরগোল তোলার পিছনে রয়েছে রাজনৈতিক দলগুলোর সুস্পষ্ট অসাধু মতলব, যেন তেন প্রকারে বিজেপি-র বিরুদ্ধে একটা জনমত তৈরি করে উত্থিত জনসমর্থনের পাল থেকে হাওয়া কেড়ে নেওয়া। এইসব রাজনৈতিক দলগুলোর অনকেরই শাখাপ্রশাখা হিসেবে আছে ছাত্র-সংগঠন, বুদ্ধিজীবী-লেখক-শিল্পী সংগঠন, বিজ্ঞান আন্দোলনকর্মীদের সংগঠন, এমনি আরও সাত-সতেরো সংগঠন। মূলের আহ্বানে এইসব শাখা-প্রশাখা নিজস্ব চিন্তা বুদ্ধি বিসর্জন দিয়ে পথে-মাঠে-ময়দানে নেমে পড়েছে জনগণের মগজ ধোলাই করতে, জনগণের আবেগে উত্তাপ সৃষ্টি করতে। ‘হুম্-হুম্’ রবে এরা সব হাঁক ছেড়েছে— “শরীরের শেষ রক্তবিন্দু দিয়ে আমরা মৌলবাদ রুখছি, রুখব।”
যারা এমন তারস্বরে মৌলবাদ রোখার লড়াইতে ময়দানে নেমেছে, তারা আন্তরিক, কি ভণ্ড? বাস্তবিকই মৌলবাদ রুখতে চায়, কি এই সুযোগে প্রগতিবাদী ও সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের বন্ধু সেজে এক ঢিলে দুই পাখি মেরে রাজনৈতিক ফায়দা লুটতে চায়? এ-সব প্রশ্নের সঠিক উত্তর পেতে গেলে আমাদের শুধু দেখতে হবে, আন্দোলনকারীরা মৌলবাদী চিন্তার সঙ্গে সম্পর্কহীন কি না? মৌলবাদ বিরোধী, অর্থাৎ প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মবিরোধী কি না? কেউ আন্তরিকভাবে মৌলবাদ বিরোধী হলে প্রাতিষ্ঠানিক ধর্ম বিরোধী হতেই হবে।
বিভিন্ন ধর্মীয় গোষ্ঠীর সঙ্গে, ধর্মীয় নেতাদের সঙ্গে, মৌলবাদীদের সঙ্গে যেভাবে রাজনৈতিক দলগুলো বোঝাপড়া করছে, হাত মেলাচ্ছে, তাতে তাদের মৌলবাদ বিরোধী স্লোগান নেহাতই চূড়ান্ত ভণ্ডামি, শঠতা এবং রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত বই আর কিছুই মনে হওয়ার অবকাশ আছে কি? অবশ্যই নেই। পাড়ায় পাড়ায় মহল্লায় মহল্লায়, পুজো কমিটিতে পার্টি ক্যাডারদের ভিড়ে যেতে যারা বলে, তারাই তো স্পষ্টত মৌলবাদী চিন্তাধারার উত্থানের সহায়কশক্তি, মৌলবাদের পালক। মৌলবাদী শক্তি রুখতে যাঁরা শরীরের শেষ রক্তবিন্দু দেওয়ার প্রতিজ্ঞা ঘোষণায়, স্লোগানে আকাশ-বাতাস মথিত করেন, তাঁরা কি প্রতিজ্ঞা পালনের ক্ষেত্রে, স্লোগানকে বাস্তব রূপ দেওয়ার প্রয়োজনে পারবেন ওইসব মৌলবাদীদের ধারক-বাহক-পালক শঠ রাজনৈতিক নেতাদের বদমতলব রুখতে? তাদের ওইসব মৌলবাদী চিন্তার বিরুদ্ধে সোচ্চার হতে? না কি কিছু গুছিয়ে নেওয়ার ধান্দায় ওইসব রাজনীতিকদের কলটেপা পুতুলের ভূমিকায় অভিনয় করে যাবেন ?
আজ যে মৌলবাদের শক্তিবৃদ্ধির জন্য অনেকেই শঙ্কাপ্রকাশ করছেন, কিন্তু এই শক্তি তো একদিনে বেড়ে ওঠেনি। ধর্ম নিয়ে এমন উন্মত্ততা তো একদিনে গাছের পাকা ফলটির মতো টুপ করে এসে পড়েনি। ‘সাম্প্রদায়িক’, মৌলবাদী বলে আজ যাদের গাল পাড়ছে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল, সেই সাম্প্রদায়িক মৌলবাদী দলগুলো তো হঠাৎ করে উজ্জীবিত হয়ে ওঠেনি। ভারতবর্ষের মাটিতে সাম্প্রদায়িকতার চাষ, ধর্মের চাষ ও ধর্ম-ব্যবসা দীর্ঘ দিন ধরেই চলে আসছে। ঘোলা জলে মাছ ধরতে কে নামেনি? মানুষ তো জন্মেই সাম্প্রদায়িক ও ধর্মান্ধ হয়নি। ওদের একটু একটু করে এভাবে তৈরি করা হয়েছে। পাঠ্যক্ৰম, পরিচিত আপনজনের জীবন চর্যা থেকেই রস আহরণ করে শিশু মানুষ সাম্প্রদায়িক মানুষ ও ধর্মান্ধ মানুষে পরিণত হয়েছে। অধিকাংশ রাজনৈতিক দলের নেতারাই সংসদীয় নির্বাচনে আখের গোছাবার ধান্দায় ধর্মীয় নেতাদের আশীর্বাদ ভিক্ষা করে প্রকাশ্যে, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে গিয়ে ভক্তি গদগদ ভাব প্রদর্শন করে; কালীপুজো, দুর্গাপুজো, রামপুজো, গণেশপুজো, কৃষ্ণপুজো, শিবপুজো, ইত্যাদি পুজো উদ্বোধন করে, জগন্নাথের রথের রশিতে টান দেয়, ভেঙ্কটেশ্বরে মানত করে, দরগায় সিন্নি চড়ায়, গুরুদ্বারে ভক্তি নিবেদন করে, গির্জায় মোম জ্বালে। রাষ্ট্রীয় প্রচার যন্ত্রগুলো এইসব ধর্মীয় অনুষ্ঠানে প্রচার করে চলেছে অবিরল ধারায়। রাষ্ট্রনেতাদের ধর্মীয় অনুষ্ঠানে যোগদানও দেখানো হচ্ছে দূরদর্শনের পর্দায়, ঘোষিত হচ্ছে বেতারে, ছবিসহ প্রকাশিত হচ্ছে পত্র-পত্রিকায়। দিনের পর দিন এমন প্রচারে যে পরিমণ্ডল সৃষ্টি করা হচ্ছে, ‘তাতে সাধারণের মধ্যে ধর্মীয় বিশ্বাসই আরও বেশি শেকড় মেলে দিচ্ছে।
মৌলবাদ একটা বিশ্বাসের ব্যাপার ; ধর্মীয় অন্ধ বিশ্বাস।
রাজনৈতিক দলগুলোর কর্মকাণ্ডই এমন ধর্মীয় অন্ধ
বিশ্বাসকে আরও বেশি জোরদারই করছে,
আরও ব্যাপকতর অংশে ছড়িয়ে দিচ্ছে।
বামফ্রন্ট দীর্ঘ বছর পশ্চিমবঙ্গের শাসন ক্ষমতায় থেকে একটি লাগাতার প্রচার চালিয়ে যাচ্ছেন, ‘এখানে মৌলবাদীদের কোনও স্থান নেই’। কিন্তু বাস্তব যে বলে, এ-সবই আদ্যন্ত মিথ্যা প্রচার, প্রতারণা! এই বঙ্গে বারোয়ারি দুর্গাপুজো, কালীপুজো, জগদ্ধাত্রী পুজোর রমরমা বেড়েছে রাজনৈতিক ক্যাডারদের ও মাঝারি মাপের লিডারদের ব্যাপক অংশগ্রহণে। রাজনৈতিক নেতারা এইসব পুজো উদ্বোধনে হাজির থেকেছেন, বোম্বাই থেকে সুপার-স্টার অভিনেতা অভিনেত্রীদের উড়িয়ে নিয়ে এসে হাজির করেছেন তাঁদের স্নেহধন্যদের পুজোয়। যাঁরা মৌলবাদীদের চামড়া গুটিয়ে দেবেন বলে আস্তিন গুটিয়ে মাইক ফোঁকেন, মৌলবাদের বিরুদ্ধে পাঁচ কিলোমিটার পদযাত্রা করেন, তাঁরা কি পারবেন ওইসব ধান্দাবাজ স্ববিরোধী রাজনীতিকদের চামড়া গুটিয়ে দিতে? যদি না পারেন, প্রতিটি যুক্তিমনস্ক মানুষ অবশ্যই ধরে নেবেন, ওই সব উচ্চকণ্ঠ সংগ্রামী -সাজা বিভিন্ন সংগঠনগুলো আসলে কথায় ও কাজে ভিন্ন মেরুতে বিচরণ করা রাজনৈতিক দলগুলোরই লেজুড়, উচ্ছিষ্টভোগী ছাড়া কিছুই নয়।
‘মৌলবাদী রুখতে হবে’ স্লোগানের আড়ালে ভণ্ডামির যে প্রতিযোগিতায় নেমেছে ভারতের বিভিন্ন রাজনৈতিক দলগুলো, তাতে কে যে শেষ পর্যন্ত ‘ভণ্ড চূড়ামণি’র শিরোপা জিতে নেবে, আগাম অনুমান করা বেজায় কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছে। মার্কসবাদী অনেক দলকেই এই প্রতিযোগিতায় কেউ কেউ ‘আন্ডার ডগ’ ভাবলে বেজায় ভুল করবেন। ওরাই আসলে প্রতিযোগিতার ‘কালো ঘোড়া’। বিশাল এক মার্কসবাদী দলের সাম্প্রতিক ভূমিকার দিকে একটু মনোযোগী হলে প্রতিযোগিতায় তাদের সাফল্যের সম্ভাবনার রূপালি রেখা সমঝদার মাত্রেরই নজরে পড়বে। ওই দলটির দৈনিক মুখপত্রে আমরা একই সঙ্গে ‘মৌলবাদ রুখছি রুখব’ বিজ্ঞাপন ও অধ্যাত্ম জগতের মেগাস্টার ‘মা নির্মলাদেবীর’ বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হতে দেখেছি। ঈশ্বর দর্শনের ঠিকা-নেওয়া ‘মা নির্মলাদেবীর’ ঢাউস বিজ্ঞাপনটি একদিন হঠাৎ, আচমকা প্রকাশিত হয়নি। প্রকাশিত হয়েছে দিনের পর দিন।
মার্কসবাদী বেশ কিছু দলই তাদের ক্যাডার বাহিনীতে ঢুকিয়েছে এক নতুন পুজো কালচার; যে কালচার বিভিন্ন পুজো কমিটিকে বাজেট প্রতিযোগিতায় নামিয়েছে। বহু সর্বজনীন পুজো বাজেটই আজ লক্ষ ছেড়ে কোটির দিকে ধাবিত। পুজোর এই রমরমা প্রতিটি ক্ষেত্রেই রাজনৈতিক নেতাদের স্নেহচ্ছায়াতেই বর্ধিত হয়েছে। রাজনীতিকরাই প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মীয় বিশ্বাসের বিষবৃক্ষ জলসিঞ্চন করে চলেছেন, সার দিয়ে চলেছেন। এমন করার পিছনে অসাধু কুটিল উদ্দেশ্যের একটি, জনগণের আবেগকে কাজে লাগিয়ে তাদের আপনজন সেজে ভোট বাক্স পুষ্ট করা। আর তাতেই এঁরা স্ববিরোধিতার চূড়ান্ত নিদর্শন হিসেবে একই সঙ্গে রামপুজোর বিরোধিতা এবং দুর্গাপুজো, কালী পুজো, জগদ্ধাত্রী পুজোকে তোল্লা দেওয়া চালিয়ে যান। এঁরা পশ্চিমবঙ্গের রাজস্থানী ভোটারদের স্বল্পতার কথা চিন্তা করে নিরাপদ বিবেচনায় সতী মন্দিরের বিরুদ্ধে সোচ্চার হন, সতী মন্দির ও সতী পুজোর বিরুদ্ধে তীব্র ভাষায় বিবৃতি দেন, সতী মন্দিরের সামনে বিক্ষোভ সমাবেশ করেন। একটি মার্কসবাদী দলের রাজ্য সম্পাদক দীপ্ত ঘোষণা রাখেন—মৃতকে নিয়ে স্মৃতি সৌধ হতে পারে, কিন্তু মৃতকে পুজো? মৃতের স্মৃতিমন্দির? এমন কুসংস্কারাচ্ছন্ন চিন্তার বিষ আমরা পশ্চিমবাংলায় ছড়াতে দেব না। এঁরাই আবার লোকনাথ, রামকৃষ্ণ, স্বামী বিবেকানন্দ, অনুকূল ঠাকুর, অন্নদাঠাকুর, রামঠাকুরের পুজো নিয়ে, তাদের স্মৃতিতে গড়ে ওঠা মন্দির নিয়ে সোচ্চার হওয়ার পরিবর্তে অদ্ভুত রকম নীরবতা পালন করেন—নীতির চেয়ে ভোট-বাক্সে বেশি রকম গুরুত্ব দেওয়ার সুবাদে। ক্ষমতার মধুপানই যেখানে লক্ষ্য, সেখানে ছলের অভাব হওয়ার কথা নয়। এই সব রাজনৈতিক দলগুলোর নেতারা যে সব সময়ই নীরবতা পালন করে ধর্মশিকারিদের পরোক্ষ মদতই দিয়েছেন, এমন মিথ্যা কথা অবশ্য আমি বলছি না। অনেক সময়ই ওই সব কুশলী নেতারা ধর্মগুরু ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলোকে নিয়ে নাচন কোঁদন করে ধর্ম-ব্যবসায়ীদের প্রত্যক্ষ মদতও দিয়েছেন। আর এ-সবই করেছেন ধর্ম-ব্যবসায়ীদের শিষ্য শিষ্যাদের ভোটাধিকার আছে, এই কথাটি মাথায় রেখে।
একটি বড় মার্কসবাদী দলের বিজ্ঞান সংগঠন ‘পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞানমঞ্চ’ তাদের ১৯৮৯-এর বিশেষ সংখ্যায় তাদের সংগঠনের দৃষ্টিভঙ্গির কথা উপস্থিত করতে গিয়ে লিখছে, “মৌলবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের নামে ধর্মবিশ্বাসের বিরুদ্ধে জিগির তোলার অর্থ হচ্ছে জনসাধারণ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে কিছু ‘বিজ্ঞান প্রচারকে’র বীরদর্পে আস্ফালন” ?
কিছু কিছু কথা বারবার বলার প্রয়োজন হয়। তাই বলি, যে বিচ্ছিন্নতার অর্থ পচনধরা কুসংস্কারাচ্ছন্ন সমাজকে সংস্কার মুক্ত করা; যে বিচ্ছিন্নতার অর্থ শোষণের অবসানমুখী সংগ্রাম; যে বিচ্ছিন্নতার অর্থ সুস্থ সংস্কৃতি বিকাশমুখী চেতনা, সুস্থ আত্মবিকাশের চেতনা, সে বিচ্ছিন্নতা অবশ্যই মানুষের কাম্য, সভ্যতার কাম্য ।
বিজ্ঞান মঞ্চের আলোচ্য ওই প্রবন্ধটিতেই লেখা হয়েছে অদ্ভুত স্ববিরোধী দুটি লাইন, “সংগঠিত জনবিজ্ঞান আন্দোলন পারে ধৈর্য নিয়ে ধীর পদক্ষেপে সমাজের বেশির ভাগ মানুষের কাছে কুসংস্কার এবং মৌলবাদের মুখোশ খুলে দিতে। এখানেই প্রয়োজন জনবিজ্ঞান আন্দোলনের শত শত একনিষ্ঠ কর্মীর, যে কর্মীরা মানুষের বিশ্বাস এবং সংস্কৃতির ওপর আচমকা আঘাত করে নিজেদের বিচ্ছিন্ন করার ভুল রাস্তায় যাবেন না”।
মৌলবাদের অর্থাৎ ধর্মীয় বিশ্বাসের এবং কুসংস্কারের মুখোশ খোলার কর্মসূচি ঘোষণা করব, আবার মানুষের ধর্মীয় বিশ্বাস এবং অন্ধ-বিশ্বাসকে আঘাত হানা থেকে বিজ্ঞান আন্দোলনকারীদের বিরত থাকতে বলব। এ-সব কি অস্বচ্ছ চিন্তার ফসল? না কি আন্দোলনকর্মীদের মগজ ধোলাই করে তাদের মধ্যে অস্বচ্ছ চিন্তা ঢোকাতেই এমন অস্বচ্ছ চিন্তার ভণ্ডামি, কথার মারপ্যাঁচ?
সংস্কৃতির ওপর আঘাত হানায় তো অনীহা থাকার কথা নয়, যদি সেই সংস্কৃতি হয় অবক্ষয়ের সংস্কৃতি! কোন সংস্কৃতিকে আঘাত হানব না? সতীদাহের সংস্কৃতিকে? বাবু কালচারের সংস্কৃতিকে? ধর্মান্ধতার সংস্কৃতিকে ? অদৃষ্টবাদী চিন্তার সংস্কৃতিকে? জাত-পাতের সংস্কৃতিকে ? পণ-প্রথার সংস্কৃতিকে?
আজ গোটা দেশ জুড়ে ধর্মের রমরমা। আর এই রমরমার পিছনে রয়েছে ধনকুবের শ্রেণি ও তাদের অর্থে নির্বাচনে জেতা তল্পিবাহক সরকারের কূট পরিকল্পনা। ওরা চায় ধর্ম-বিশ্বাসের মধ্য দিয়ে, ধর্মীয় উন্মাদনার মধ্য দিয়ে মানুষের মধ্যে পূর্বজন্ম, কর্মফল, ঈশ্বরবিশ্বাস, ঈশ্বর-নির্ভরতা, অলৌকিক বিশ্বাস গড়ে উঠুক, দৃঢ়বদ্ধ হোক। এমনটি হলে বঞ্চিত মানুষগুলো তাদের ২৭৭ বঞ্চনার কারণ হিসেবে আসল খল নায়কদের দায়ী না করে দায়ী করবে কল্পনার ভগবানের অভিশাপকে, পূর্বজন্মের কর্মফলকে, অদৃষ্টকে। দুঃখে, যন্ত্রণায়, অপমানে খাখান্ হতে হতেও ওরা বঞ্চনাকারীদের বিরুদ্ধে রুখে না দাঁড়িয়ে, প্রতিরোধ না গড়ে তুলে, পরিত্রাণ পেতে চাইবে পরমপিতাজাতীয় কারও কাছে আত্মসমর্পণের মধ্যে।
ধর্ম আজ গরিবদের শত্রু শিবিরের শক্তিশালী অস্ত্র। ধর্মের নেশায় মাতিয়ে দিতে পারলে বঞ্চিত মানুষগুলোর প্রতিবাদের কণ্ঠকে স্তব্ধ করে রাখা যায়—অদৃষ্ট ও ঈশ্বরের ইচ্ছেকে বঞ্চনার কারণ হিসেবে চিহ্নিত করে। আর তাই পরিকল্পিতভাবেই সরকার নানা স্ববিরোধিতার মধ্য দিয়েই তার লক্ষ্যে স্থির রয়েছে। তারই পরিণতিতে মন্দির, মসজিদ ও নানা ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে সরকারি অর্থের বদান্যতার পরও সরকারি এবং বেসরকারি প্রচার মাধ্যমগুলো (যেগুলোর মালিক অবশ্যই ধনী, হুজুর শ্রেণি) ‘ধর্মনিরপেক্ষতা’ নামক ‘সোনার -পাথর-বাটি’টি ভাঙল ভাঙল বলে আর্ত-চিৎকারে আকাশ-বাতাস ভরিয়ে তুলে কুমিরের মতোই চোখের জল ফেলে। বিভিন্ন রাজনৈতিক দলগুলোর এমন চিৎকারের পিছনে যে কারণটি ক্রিয়াশীল তা হল, মুখোশহীন ধর্মীয় মৌলবাদী চিন্তার সমর্থক ভারতীয় জনতা পার্টির প্রচণ্ড উত্থানকে রোখার চেষ্টা। এতদিন যে বিষবৃক্ষে সকলে মিলিতভাবে জল সিঞ্চন করেছেন, সার ঢেলেছেন, তাতে এমনটা ঘটাই তো স্বাভাবিক। সকলে মিলে সাধারণের মধ্যে ধর্মীয় মৌলবাদী চিন্তা ঢুকিয়ে দেওয়ার পর সাধারণ মানুষ যদি মুখোশধারী মৌলবাদীদের ছেড়ে মুখোশহীন মৌলবাদীদের পক্ষে যান, তবে তার মধ্যে অস্বাভাবিকতা তো কিছুই দেখি না। এমন মৌলবাদী চিন্তার উত্থানের দায়িত্ব অস্বীকার করতে পারে না কোনও দল বা ব্যক্তি, যাঁরা ধর্মীয় চিন্তার বিরুদ্ধে নীরব থেকেছেন, নীরব থাকার উপদেশ বর্ষণ করেছেন।
বিপুল প্রচারে সাধারণ মানুষ পরিচিত হয়েছে ‘ধর্মনিরপেক্ষতা’ শব্দের সঙ্গে। জেনেছে—ধর্মনিরপেক্ষতা কথার অর্থ ‘সব ধর্মের সমান অধিকার। ‘ বিপুল সরকারি অর্থব্যয়ে ধর্মনিরপেক্ষতা শব্দের এই যে ব্যাখ্যা সর্বত্র হাজির করা হচ্ছে এবং এরই সঙ্গে সম্পর্কিতভাবে আমাদের দেশের মন্ত্রী, আমলা ও রাজনীতিকরা মন্দিরে মন্দিরে পুজো দিয়ে বেড়াচ্ছেন, গুরুদ্বারে নতজানু হচ্ছেন, মসজিদে, গির্জায় শ্রদ্ধা জানিয়ে আসছেন। দেওয়া, ঈদ, বড় দিন ইত্যাদিতে রাষ্ট্রনায়করা বেতার দূরদর্শন মারফত শুভেচ্ছা জানাচ্ছেন। ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের অর্থ সাহায্য দিলে আয়কর থেকে রেহাইয়ের ব্যবস্থা করে দিচ্ছেন।
সাধারণের ভালো লাগছে— ‘সব ধর্মের সমান অধিকার’ মেনে নিয়ে মন্ত্ৰী, আমলা, রাজনীতিকদের সমস্ত ধর্মের কাছে নতজানু হতে দেখে। উদার হৃদয়ের মানুষ হিসেবে নিজেদের ভাবতে ভালো লাগছে জনসাধারণের—হুঁ হুঁ বাবা, আমাদের দেশ ধর্ম নিরপেক্ষ। এখানে সব ধর্মই সমান অধিকার ও শ্রদ্ধা পায় মন্ত্রী আমলার। মন্ত্রীরা এরই মাঝে বুঝিয়ে দেন সমস্ত ধর্মের সমান অধিকার বজায় রাখতে, দেশের ধর্মনিরপেক্ষতা মশাল জ্বালিয়ে রাখতে রাজনীতি থেকে ধর্মকে আলাদা রাখতে হবে।
‘ধর্মনিরপেক্ষতা’ শব্দটিকে নিয়ে কী নিদারুণভাবে অপব্যাখ্যা করে সাধারণ মানুষের মগজ ধোলাই করা হচ্ছে, ভাবা যায় না! ‘নিরপেক্ষ’ শব্দের অর্থ— কোনও পক্ষে নয়। ‘ধর্মনিরপেক্ষ’ শব্দের অর্থ কোনও ধর্মের পক্ষে নয়। অর্থাৎ সমস্ত ধর্মের সঙ্গে সম্পর্ক বর্জিত। Secularism শব্দের আভিধানিক অর্থ—একটি মতবাদ, যা মনে করে—রাষ্ট্রনীতি, শিক্ষা প্রভৃতি ধর্মীয় শাসন থেকে মুক্ত থাকা উচিত।
একী! এদেশে ধর্ম নিরপেক্ষতার নামে আমরা কী দেখছি? সেকুলার রাষ্ট্রীয় অনুষ্ঠানেও এদেশে ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান পালন করা হয়। কোনও প্রকল্পের উদ্বোধন বা শিলান্যাস হয় মন্ত্রোচ্চারণের মধ্যে প্রদীপ জ্বালিয়ে, পুষ্পার্ঘ্য নিবেদন করে, নারকেল ফাটিয়ে।
সেকুলার রাষ্ট্রে ধর্ম কেবল ব্যক্তিগত বিশ্বাস ও আচরণের
ব্যাপার হতে পারে। রাষ্ট্রীয় জীবনে বা রাষ্ট্রীয় নীতিতে
এই ব্যক্তিগত ধর্মীয় বিশ্বাস যেন প্রকাশ্যে না
এসে পড়ে এ বিষয়ে অতি সতর্ক থাকা
‘সেকুলার’ বা ‘ধর্মনিরপেক্ষ’
রাষ্ট্রের কর্তব্য।
কিন্তু ভারতে মন্ত্রী, রাজনীতিক ও আমলারা প্রকাশ্যেই বিশেষ সম্প্রদায়ের ধর্মাচার পালন করেন। প্রয়োজনে এইসব রাজনীতিকরা সব ধর্মকেই সমান প্রশ্রয় দেয়। ফলে এইসব রাজনীতিকরাই যখন ধর্ম নিরপেক্ষতার বড় বড় বুলি কপচায় ও রাজনীতি থেকে ধর্মকে পৃথক করার কথা বলে তখন এদের দ্বিচারী, ধান্দাবাজ চরিত্রই প্রকাশ পায়।
শ্রমজীবী মানুষের আজ তাই সচেতন হওয়ার সময় এসেছে। সাম্প্রদায়িকতা ও ধর্মান্ধতার বিষবৃক্ষটিকে তুলে ফেললেই কিন্তু আমরা বিপদমুক্ত হতে পারব না। আমাদের দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হতে হবে—কাউকেই বিষবৃক্ষের বীজ বপনের, জলসিঞ্চনের ও সার প্রয়োগের সুযোগ কোনও ভাবেই দেব না। সময় এসেছে স্ববিরোধী, কথায় ও কাজে সম্পর্কহীন আখের গুছোন চরিত্রগুলোকে সুস্থ, প্রগতিশীল চিন্তার বিরোধী শিবিরের মানুষ হিসেবে চিহ্নিত করার; নিরন্ন, অত্যাচারিত, হতদরিদ্র মানুষগুলোর বন্ধুবেশী শত্রু হিসেবে চিহ্নিত করার; যারা একই কণ্ঠে উচ্চারণ করে, “ধর্মীয় ধারণাকে আঘাত নয়”, এবং “মৌলবাদ রুখতে হবে।”
যে শক্তি ৬ ডিসেম্বর ‘৯২ হিন্দু মন্দির গড়ার নামে অযোধ্যায় বিতর্কিত বাবরি মসজিদ ভেঙেছে সেটা যেমন অশুভ, ধর্মান্ধ, ফ্যাসিস্ট, তেমনই যে শক্তি জামিয়া মিলিয়া ইসলামিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের সহ-উপাচার্য মুশিরাম হাসানকে প্রহার করেছে “স্যাটানিক ভার্সেসের মতো বই নিষিদ্ধ করে কোনও লক্ষ সাধিত হয় না” বলার অপরাধে সেটাও তেমনই অশুভ, ধর্মান্ধ, ফ্যাসিস্ট। যে শক্তি বাবরি মসজিদ ভাঙার বদলা নিতে মন্দিরের পর মন্দির ধুলোয় মিশিয়ে দিয়েছে সেটা যেমন অশুভ, ধর্মান্ধ, ফ্যাসিস্ট, তেমনই যে শক্তি বাংলাদেশের যুক্তিবাদী লেখক আহমদ শরীফের যুক্তিনিষ্ঠ কথা বলার অপরাধে তাঁর মৃত্যুদণ্ড ঘোষণার দাবিতে উন্মত্ততা প্রকাশ করে, সেটাও তেমনই অশুভ, ধর্মান্ধ, ফ্যাসিস্ট। এই ধর্মান্ধ ফ্যাসিস্ট শক্তির বিরুদ্ধে একটা কঠিন ও জটিল সার্বিক লড়াই দিতে না পারলে এই ক্রান্তিকালকে অতিক্রম করে ধর্মনিরপেক্ষতার বাতাবরণ সৃষ্টি করা যাবে না। এই লড়াই হবে মৌলবাদের বিরুদ্ধে, অন্ধ-ধর্মবিশ্বাসের বিরুদ্ধে মানবিকতার লড়াই, যুক্তিনিষ্ঠার লড়াই, ধর্মনিরপেক্ষতার লড়াই।
রাজনীতির ব্যবসায়ীরা নানা ধর্মকে তোল্লাই দিয়ে সর্বধর্মের সমন্বয় ও সংহতির বাঁধা গৎ এতদিন বাজিয়েই এসেছেন। দূরদর্শনের পর্দায় নানা মনীষীর ধর্ম-সার, ধর্ম-সমন্বয় ও সংহতির কথা প্রচারিত হয়েছে। কিন্তু এতে যে কোনও কাজই হয়নি তা বাবরি মসজিদ ধূলিসাৎ, ও মন্দিরে পাল্টা একগাদা মন্দির ও তার পাল্টা একগাদা মসজিদের ধূলিসাৎ-এর ঘটনাতেই প্রমাণিত হয়েছে।
কিন্তু কার সঙ্গে সংহতি? এটা স্পষ্ট করে বুঝে না নিলে ধর্মনিরপেক্ষতা বা সেকুলারিজমকে শব্দ-গণ্ডির বাইরে নিয়ে এসে কখনওই বাস্তবরূপ দেওয়া যাবে না, বাঁধা গৎ-ই শুধু ঘুরে মরবে। ‘ধর্মনিরপেক্ষ’ শব্দের প্রকৃত অর্থ ও তাৎপর্য এবং সুসংস্কৃতির ক্ষেত্রের তার অসামান্য অবদার কথা নিজে বুঝতে হবে, অপরকে বোঝাতে হবে, সাধারণকে বোঝাতে হবে। এই বোধ থেকেই তৈরি হবে ধর্মনিরপেক্ষ মানুষ। ধর্মনিরপেক্ষ মানুষদের সংহত করতে পারলেই ‘ধর্মে আছি, মৌলবাদে নেই’ বলা ধর্মনিরপেক্ষতার ছদ্মবেশী শত্রুদের বিচ্ছিন্ন করে ফেলা যাবে।
বাবরি মসজিদ গুঁড়িয়ে দেওয়ার ব্যাপারটা ‘পূর্ব-পরিকল্পিত’ নয় ঠিকই, তবে করসেবকদের এই কাজ দীর্ঘ-দিনের অবরুদ্ধ হিন্দু আবেগেরই বহিঃপ্রকাশ। পাল্টা মন্দির গুঁড়িয়ে দেওয়ার ঘটনাগুলোও মুসলিম আবেগেরই বহিঃপ্রকাশ। এই ধর্মীয় আবেগের বাস আমাদের মনের গভীরে। এই আবেগ আমাদের সামাজিক পরিবেশের, আমাদের সাংস্কৃতিক পরিবেশেরই ফলশ্রুতি। একবার পর পর ঘটে যাওয়া ঘটনাগুলোর দিকে ফিরে তাকালেই স্পষ্টতর হবে কীভাবে সমস্ত রাজনৈতিক দল একটু একটু করে আমাদের চূড়ান্ত সাম্প্রদায়িক করে তুলেছে, আর তারই পরিণতিতে এই জাতিদাঙ্গা। দূরদর্শনে শত কিস্তি ‘রামায়ণ’ ‘মহাভারত’ হাজির করে সুপরিকল্পিতভাবে হিন্দু আবেগকে উসকে দিয়েছে কেন্দ্রের কংগ্রেস সরকার। এই উসকে দেওয়া আবেগকে কাজে লাগিয়ে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধি রামায়ণ টি ভি সিরিয়ালের রাম চরিত্রের অভিনেতাটিকে রাম সাজিয়ে নিজের দলের পক্ষে ভোটের প্রচারে নামিয়েছেন। ১৯৪৯ সাল থেকে অযোধ্যার যে বিতর্কিত কাঠামো ছিল তালাবন্ধ এবং মানুষের স্মৃতিতেও ছিল তালাবন্দি, সেই তালা রাজীব গান্ধির আমলে উত্তরপ্রদেশের তৎকালীন কংগ্রেস সরকারই খুলে দিয়েছিল হিন্দু মনে রামভক্তির জোয়ার আনতে। তার কিছুদিন পরেই নির্বাচনী ফায়দা তুলতে কংগ্রেস সরকার আর এক দফা হিন্দুত্ববোধের ধর্মান্ধতা জাগিয়ে তোলার পরিকল্পনায় রাজকীয় প্রচারের মধ্য দিয়ে রামমন্দিরের শিলান্যাস করল অযোধ্যায়। অযোধ্যায় অদূরে ফৈজাবাদে রাজীব গান্ধি নির্বাচনী প্রচার অভিযান শুরু করলেন আবেগকম্পিত গলায় সোচ্চার ঘোষণার মধ্য দিয়ে-‘প্রতিশ্রুতি দিচ্ছে ভারতে রামরাজ্য স্থাপন করব।’ হিন্দু ভোটারদের আবেগকে উত্তাল করার রাজীব পরিকল্পনা সার্থক হল। শ্রোতারা ‘জয় শ্রীরাম’ ধ্বনিতে সে-দিন ফৈজাবাদের আকাশ-বাতাস কাঁপিয়ে দিল।
কংগ্রেসকে এমন ধর্ম দিয়ে রাজনীতি করতে দেখে ভারতীয় জনতা পার্টি প্রমাদ গুনল। কংগ্রেসের পাল থেকে হাওয়া কাড়তে, আবেগ-তাড়িত হিন্দু ভোটারদের কাছে ভারতীয় জনতা পার্টি আরও দু চার ধাপ বেশি এগিয়ে গেল। প্রতিশ্রুতি দিল— আমরা বাবরি মসজিদ ভেঙে রামমন্দির প্রতিষ্ঠা করবই। আমরা কংগ্রেসের মত সামনে ‘রাম’ ও পিছনে ‘রহিম’ বলি না। রামরাজত্ব ও হিন্দুরাজত্ব সমার্থক এবং একমাত্র আমাদের দলই হিন্দুরাজত্ব অর্থাৎ রামরাজত্ব প্রতিষ্ঠা করতে পারে, কারণ একমাত্র আমাদের দলই হিন্দুত্বের প্রতীক। কথাগুলো আবেগে হাবুডুবু খাওয়া পাবলিক দারুণ খেল।
শঙ্কিত কংগ্রেস ভারতীয় জনতা পার্টির অগ্রগতি রোধে ব্যর্থ হল। এই সময় ভারতীয় জনতা পার্টির আর এক প্রতিদ্বন্দ্বী জনতা দল হিন্দি বলয়ে ভারতীয় জনতা পার্টির অগ্রগতি রোধে বিশাল এক পরিকল্পনা নিয়ে লড়াই দিতে ময়দানে নামল। জনতা দল তখন দিল্লির তখত-এ আসীন। সংরক্ষণের নামে মণ্ডল কমিশনকে শিখণ্ডী খাড়া করে হিন্দু সমাজে বিভেদ সৃষ্টি করে দলিত, নিপীড়িতদের ভোট কাটিয়ে আনতে চাইল ভি. পি. সিং সরকার । ভি. পি. সিং-এর অবশ্য একথা মোটেই অজানা ছিল না -এই সমাজ ব্যবস্থায় ‘সংরক্ষণ’ কখনওই নিপীড়িত, শোষিত মানুষদের মুক্তি আনবে, না আনতে পারে না। শোষিত মানুষদের শোষণ-মুক্ত করার জন্য শোষকরা তার দলকে নির্বাচনে জেতাতে কোটি-কোটি টাকা ঢালেনি, ঢেলেছে শোষণের কাজে সহায়ক হবে জেনে নেওয়ার পরই। ভি. পি. সিং-এর জনতা দল ভারতীয় জনতা পার্টির পাল থেকে হাওয়া কাড়তে পারল না পাল্টা চালে। ভারতীয় জনতা পার্টি আডবানীর নেতৃত্বে বের করল ‘রামরথ’। হিন্দি বলয়ে রামরথ প্রচণ্ড রাম উন্মাদনার সৃষ্টি করল। অযোধ্যায় রামমন্দির বানাবার প্রতিশ্রুতির বিনিময়ে ভারতীয় জনতা পার্টি উত্তর ভারতের চারটি রাজ্যে নির্বাচন জিতে প্রমাণ করল, হিন্দু ধর্মীয় উন্নাদনার যে বাতাবরণ কংগ্রেসের রাজীব গান্ধি গড়ে তুলতে শুরু করেছিলেন, তাকেই তাদের দল আরও সার্থক পরিণতির দিকে নিয়ে গিয়েছে মাত্র। ভারতের রাজনৈতিক দলগুলো ভারতীয় জনতা পার্টির অগ্রগতির রথ থামাতে যতই সাম্প্রদায়িকতার অভিযোগ এনে বিরোধিতা করেছে ততই ধর্মান্ধ হিন্দুরা এই বিরোধিতাকে রাম-বিরোধিতারই সমার্থক বলে ধরে নিয়েছে।
রাজনৈতিক দলগুলো যে ভাবে নিজেদের মতো করে আমাদের চেতনায়, আমাদের সংস্কৃতিতে সাম্প্রদায়িকতার বীজ পুঁতেছে, সার দিয়েছে, জল সিঞ্চন করেছে, তারই ফলশ্রুতিতে হিন্দু আবেগের বিস্ফোরণ ঘটল অযোধ্যায়। ভারতীয় জনতা পার্টি তাই বাবরি মসজিদ অক্ষুণ্ণ রাখার কথা দিয়েও কথা রাখতে পারেনি। আবেগ যখন গণহিস্টিরিয়ার রূপ নেয়, তখন সেই আবেগ সৃষ্টিকারীর ক্ষমতা থাকে না, তাকে সামাল দেওয়ার। মনোবিজ্ঞানের এই পরম সত্য ভুলে ব্যক্তি স্বার্থে ও দলীয় স্বার্থে আমাদের দেশে বার-বার এ-ভাবেই বহু আবেগকে বাড়তে দেওয়া হয়েছে। বাড়তে দেওয়ার পরিণতিতে যখনই আবেগতাড়িতরা গণহিস্টিরিয়ার শিকার হয়েছে ও বিস্ফোরিত হয়েছে, তখনই আবেগের স্রষ্টারা তাকে সামাল দিতে ব্যর্থ হয়েছে।
অতি আবেগ অনেক সময়ই হিস্টিরিয়ার কারণ। বহু মানুষের অতি আবেগ থেকে বহুর মধ্যে যে হিস্টিরিয়া দেখা দেয় তাই গণ-হিস্টিরিয়া, যা আরও বহুতে সংক্রামিত হয়। এমনটাই ঘটেছিল অযোধ্যা কাণ্ডের ক্ষেত্রে। হিন্দু-ধর্মান্ধতার অতি আবেগ চালিত হয়ে করসেবকরা হয়ে পড়েছিল গণ-হিস্টিরিয়ার শিকার। সেই গণহিস্টিরিয়াই সংক্রামিত হয়েছিল বাবরি মসজিদ রক্ষার দায়িত্বে থাকা সরকারি বাহিনীর মধ্যে।
বাবরি মসজিদ রক্ষার দায়িত্বে ছিল সেন্ট্রাল রিজার্ভ পুলিশ ও প্রাদেশিক সশস্ত্র বাহিনী (পি.এ.সি)। এই বিশাল বাহিনীর হাতে ছিল করসেবকদের ছত্র-ভঙ্গ করার মতো নানা ধরনের সাজ-সরঞ্জাম। হিমাংকের কাছাকাছি নেমে আসা শীতে করসেবকদের জব্দ করার জন্য ছিল পাইপের সাহায্যে জল ছোড়ার ব্যাপক ব্যবস্থা। ছিল কাঁদুনে গ্যাস, আধুনিক আগ্নেয়াস্ত্র, ঢাল ছিল, লাঠি ছিল। কিন্তু করসেবকদের ‘শ্রীরাম’ ধ্বনি তুলে প্রতিরোধের বেড়া টপকে মসজিদের দিকে এগোতে দেখেও মসজিদ রক্ষাকারীদের হাতের কোনও অস্ত্রই সেদিন করসেবকদের বিরুদ্ধে ব্যবহৃত হয়নি। এমনকী, উপরওয়ালার ‘ফায়ার’ আদেশকে পর্যন্ত তারা তুচ্ছ করেছে করসেবকদের সঙ্গে একাত্মতা অনুভব করে।
এই ধর্মান্ধতা থেকে সৃষ্ট গণহিস্টিরিয়া ও ধর্মীয়-ফ্যাসিবাদ স্পষ্টতই সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিবেশ দূষণেরই ফল, অপসংস্কৃতিরই ফল, যুক্তিহীনতার ফল। যুক্তি, তথ্য ও তত্ত্বের ভিত্তিতে বিচার করলেই দেখতে পাবেন, এমন আত্মঘাতী সামাজিক পরিবেশ সৃষ্টির জন্য প্রধানতম ঘাতকের ভূমিকায় আবেগচালিত হওয়ার ফলে অনেক হিন্দুদের সামনেই হিন্দু-রাজত্ব প্রতিষ্ঠার সুখ-স্বপ্নের হাতছানি, সমস্যাহীন, দারিদ্রহীন, শোষণহীন ‘রামরাজ্য’ প্রতিষ্ঠার হাতছানি। অতি-আবেগ তাদের সরিয়ে রেখেছে যুক্তিনিষ্ঠ চিন্তার থেকে দূরে। তারা ‘শ্রীরাম’ নামের গণহিস্টিরিয়ার শিকার হয়ে ভুলে গেছে সাধারণ যুক্তিটুকু—গরিবদের ক্ষুধার আগুনের কাছে একান্তই অর্থহীন, —রাজত্ব হিন্দু চালাচ্ছে, কি অহিন্দু। গরিবদের তীব্র প্রয়োজন বেঁচে থাকার, ভাত-রুটির, মাথা গোঁজার ঠাঁইয়ের ও পরনের কাপড়ের। হিন্দু রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠাই যে গরিবদের সমস্ত সমস্যা সমাধানের চাবিকাঠি হতে পারে না, তারই প্রমাণ হিসেবে লক্ষ লক্ষ অর্ধভুক্ত, নিপীড়িত, শোষিত মানুষদের সঙ্গে সোনার চামচ মুখে তোলা শোষক মানুষদের একই অঙ্গে ধারণ করে দাঁড়িয়ে থাকা একমাত্র হিন্দুরাষ্ট্র নেপাল। এক ধর্ম শাসিত কোনও রাষ্ট্রশক্তিই গরিব শোষণ বন্ধ করেনি, গরিবদের হাল পাল্টে দেয়নি, ইসলামিক রাষ্ট্রগুলোই তার প্রমাণ। শুধু তাই বা বলি কী করে? দক্ষিণ আফ্রিকায় সাদা খ্রিস্টীয়দের হাতে কালো খ্রিস্টীয়দের নিপীড়নের টাটকা কাহিনি তো কম কানে আসছে না মানুষের।
হিন্দুস্থানে মুসলিমদের অবস্থানই জাতিদাঙ্গার কারণ, এমন
কুযুক্তি ধোপে টেকে না। আমাদের এই দেশেই
বহু জাতিদাঙ্গা হয়েছে ভাষার ভিত্তিতে,
জাত-পাতের ভিত্তিতে।
এ-দেশে ফি বছর বর্ণ হিন্দুদের নিষ্ঠুর আক্রমণে বহু অচ্ছুত হিন্দু উজাড় হয়ে গেছে, উজাড় হয়েছে ওদের ঝুপড়ি-ইজ্জত প্রাণ। একই ধর্মতে অবস্থান কি কুয়েত, ইরাক, ইরান ইত্যাদি দেশগুলোর মধ্যে যুদ্ধ বন্ধ করতে পেরেছে? পেরেছে পৃথিবীর বহু দেশে একই ধর্মীয়দের মধ্যে জাতিদাঙ্গা বন্ধ করতে?
নির্বাচন-নির্ভর সব রাজনৈতিক দলই সাম্প্রদায়িকতার তাস খেলে চলেছে, ভারতীয় জনতা পার্টিও খেলছে। ধারাবাহিকভাবে রয়েছে দুর্নীতিবাজ, স্বার্থান্ধ, ‘মানুষ’ নামের অনুপযুক্ত রাজনীতির ব্যবসায়ীরা।
‘অযোধ্যা-কাণ্ড’ ঘটে যাওয়ার পর প্রায় সমস্ত রাজনৈতিক দলই এমন ভান করছে, যেন ভারতীয় জনতা পার্টি ও তার পরিবারভুক্ত এবং দোসর দলগুলোকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করে দিলেই ‘ভারত’ নামক দেশটি থেকে সাম্প্রদায়িকতাকে ঝেঁটিয়ে বিদায় করা যাবে। না যাবে না, যেতে পারে না। কারণ ‘সাম্প্রদায়িকতার তাস’, ‘জাত-পাতের তাস’ এ-সব হাতে না থাকলে রাজনীতির ব্যবসায়ীরা খেলবে কী নিয়ে? দেশে অর্থনৈতিক সংকট থাকলে এ-সব তাস নিয়ে ওদের খেলতেই হবে। একটু চোখ খুললেই দেখতে পাবেন অযোধ্যা কাণ্ডের দৌলতে ভারতের চরমতম আর্থিক সমস্যা, বিশ্বের বৃহত্তম আর্থিক দুর্নীতি-শেয়ার কেলেংকারি এবং তার সঙ্গে জড়িয়ে পড়া গোটা দেশের তা-বড় মন্ত্রী, রাজনীতিবিদ, আমলা, ব্যাঙ্ক চেয়ারম্যানদের নিয়ে দুর্নীতির কেচ্ছা, পশ্চিমবাংলায় পুলিশ ও সরকারের বিরুদ্ধে স্বতঃস্ফূর্ত জনবিক্ষোভ – এমনকী, বহু কিছুই আড়ালে চলে গেল। তীব্র আর্থিক সমস্যা ও গণবিক্ষোভের গন্ধ পেলে সব দেশের শাসকশ্রেণি যা করে ভারতের শাসকরাও তাই করে—দুটি তুরুপের তাস ব্যবহার করে। এক-সাম্প্রদায়িকতার, দুই-ধর্মান্ধতার সমস্যা মিটে যাবে না। দেশে অর্থনৈতিক সমস্যা থাকলে, দেশে জনবিক্ষোভ থাকলে ধর্মান্ধতার জিগির তুলতে নতুন-নতুন মন্দির-মসজিদ বেছে নিতে শাসকদের অসুবিধে হবে না, জাত-পাতের জিগির তুলতেও অজুহাতের অভাব হবে না।
দেশের ক্রান্তিকালেও রাজনীতির ব্যবসায়ীরা যে ভোটের ফায়দা লোটার লোভ ভুলতে পারে না, তাও আর একবার দেখতে হল দেশবাসীকে অযোধ্যায় ঘটনাবলির পরিপ্রেক্ষিতে ইন্ডিয়ান ইউনিয়ন মুসলিম লিগ জানাল কেন্দ্রীয় সরকারের উপর থেকে সমর্থন তুলে নিচ্ছে, সমর্থন তুলে নিচ্ছে কেরল জোট সরকারের উপর থেকেও। কংগ্রেস সাংসদদের একটা বড় অংশকে মুসলিম ভোটের কথা খেয়াল রাখতেই হয়। বিশেষ করে দক্ষিণ ভারতের কংগ্রেস এখনও মুসলিম ভোটের বেশিটাই টানে। অর্থাৎ মুসলিমদের মধ্যে কংগ্রেসের ‘ভোট-ব্যাঙ্ক’ উল্লেখযোগ্য। এমন অবস্থায় মুসলিম লিগ-সহ বিভিন্ন মুসলিম গোষ্ঠীর কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতি সমর্থন তুলে নিলে তার প্রভাব পড়বেই, এই কথা চিন্তা করে কেন্দ্রের কংগ্রেস সরকার বাবরি মসজিদ ভেঙে ফেলার প্রতি তীব্র নিন্দা প্রকাশ করে ভেঙে ফেলা মসজিদ পুনর্নির্মাণের প্রতিশ্রুতি ঘোষণা করলেন ৬ ডিসেম্বরই। বইয়ের এই অংশটি যখন লিখছি তখন অযোধ্যা-কাণ্ডের দশ দিন অতিক্রান্ত। ইতিমধ্যে বহু মন্দির ধুলোয় মিশেছে, কিন্তু সে ব্যাপারে কোনও তীব্র নিন্দা বা মন্দির পুনর্নির্মাণের প্রতিশ্রুতি ঘোষিত হয়নি কেন্দ্রীয় সরকারের তরফ থেকে।
এই দৃষ্টান্তটি হাজির করার উদ্দেশ্য ভেঙে ফেলা মসজিদ বা মন্দির নির্মাণে কেন্দ্রীয় সরকারের সহযোগিতা বা অসহযোগিতার পক্ষে বা বিপক্ষে কিছু বলা নয়। এই দৃষ্টান্ত হাজির করে দেখাতে চাইছি, এমন দুঃসময়েও এরা কী ভাবে দেশের মানুষের চেয়েও দলের স্বার্থ, ভোটের ফায়দার কথা বিচার করে নিজেদের ঘোষিত মানদণ্ডের ধর্মনিরপেক্ষতাকেও প্রয়োজনে লাথি কথায়।
বাবরি মসজিদ ভেঙে ফেলার পরিপ্রেক্ষিতে ৭ নভেম্বর ‘৯২ রাষ্ট্রপতি ভবনে বাম ও জনতা দলের নেতাদের সঙ্গে মুসলিম নেতাদের কথা হয়েছিল। তখন মুসলিম নেতারা বলেন, প্রধানমন্ত্রী তো বটেই, অন্য রাজনৈতিক নেতাদের উপরেও তাঁরা আস্থা হারিয়ে ফেলেছেন। তাঁরা ‘আজই’ ভারত বন্ধ ডাকবেন বলে জানিয়ে দেন। সে সময় বাম ও জনতা নেতারা মুসলিম নেতাদের বোঝান, বাবরি মসজিদ ভেঙে ফেলা শুধু মুসলমানদের উপর আক্রমণ নয়, দেশের সমস্ত ধর্মনিরপেক্ষ মানুষের উপরও আক্রমণ। মুসলিম নেতাদের ধৈর্য ধরতে অনুরোধ করে তাঁরা বলেন, আমরাও বিষয়টা দেখছি। আপনাদের সঙ্গে আমরাও ভারত বন্ধ ডাকতে চাই। সারা ভারত বাবরি মসজিদ সংগ্রাম কমিটির নেতারা একদিন বন্ধ পিছোতে রাজি হন। ফলে ৮ নভেম্বর ভারত বধের ডাক দিল সারা ভারত বাবরি মসজিদ সংগ্রাম কমিটি আর বাম দল ও রাষ্ট্রীয় মোর্চা। ৭ নভেম্বর প্রায় মধ্যরাতে কংগ্রেসের মুখপাত্র ভি. এন. গ্যাডগিল জানালেন, বাবরি মসজিদ ভাঙাকে আমরা দেশের সমস্ত ধর্মনিরপেক্ষ মানুষের উপরও আক্রমণ বলে মনে করি, তাই কংগ্রেস এই বন্ধকে সমর্থন করছে।
ওই বন্ধের দিনেই কত মন্দির ধূলিসাৎ হল ধর্মান্ধ মুসলিমদের আক্রমণে, কিন্তু ভারত বন্ধ ডাকা একটি রাজনৈতিক দলও একবারের জন্যও সোচ্চারে বলার প্রয়োজন অনুভব করল না— মন্দির ভেঙে ফেলা শুধু হিন্দুদের উপর আক্রমণ নয়, দেশের সমস্ত ধর্মনিরপেক্ষ মানুষের উপরও আক্রমণ। এই আক্রমণের প্রতিবাদে তারা ভারত বন্ধ ডাকতেও এগিয়ে এল না। এই তো তাদের ভোটের কথা মাথায় রাখা ধর্মনিরপেক্ষতা! তাদের হিসেব মতো, ধর্মান্ধ হিন্দুরা যখন উল্লেখযোগ্যভাবে ভারতীয় জনতা পার্টির ভোট বাক্সকেই স্ফীত করবে, তখন ভোট-যুদ্ধে টক্কর দিতে হলে ধর্মান্ধ মুসলিমদের ভোট সপক্ষে আনতেই হবে। আর তারই জন্য এই মুসলিম তোষণ।
আমার এই বক্তব্যের মধ্য দিয়ে আমি মসজিদ বা মন্দির ভাঙা বা পাল্টা ভাঙার প্রতি কোনও রকমের সমর্থন বা অসমর্থন জ্ঞাপন করতে চাইছি না, শুধু ভোটনির্ভর রাজনৈতিক দলগুলোর মেকি ধর্মনিরপেক্ষতার প্রতি আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাইছি।
ধর্মান্ধতার তমসায় আজ কে আচ্ছন্ন নয়? রাজনীতিক, পুলিশ, প্রশাসন, সরকারি অফিসার, বুদ্ধিজীবী, শিক্ষক, অধ্যাপক, লেখক, শিল্পী, ব্যবসায়ী, কে নয়? এই ধর্মান্ধতার অপসংস্কৃতিকে দূর করতে হলে এই ধর্মীয় মৌলবাদীদের হাত ধরে ফ্যাসিবাদের যে আগমন, তাকে রুখতে হলে প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মকেই আঘাত হানতে হবে। নতুবা সাম্প্রদায়িক দলগুলোকে নিষিদ্ধ করে দেওয়ার মধ্য দিয়ে কিছুতেই এই সমস্যার সমাধান করা যাবে না। ধর্মীয় ফ্যাসিবাদ হল সেই ব্যাধি, অত সহজে নিষেধাজ্ঞা জারির মধ্য দিয়ে যার হাত থেকে পরিত্রাণ পাওয়া যায় না। বাঁচতে গেলে গোটা ব্যাধিটাকেই নির্মূল করতে হবে, গোড়া থেকে উপড়ে ফেলতে হবে। আর তারই জন্য প্রয়োজন ব্যাধি ও ভাইরাস’কে ভালোমতো চিনে নেওয়া। ব্যাধিটা হল ‘ধর্মান্ধতা’, ব্যাধিটা হল ‘ধর্মীয় মৌলবাদ’। ভাইরাস বা ধ্বংসকারী জীবাণু হল ‘প্রাতিষ্ঠানিক ধর্ম ।
বাবরি মসজিদ ভাঙার ঘটনাকে কেন্দ্র করে জাতিদাঙ্গা শুরু হওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে ১০ ডিসেম্বর ‘৯২ কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক ১৯৬৭ সালের ‘বেআইনি কার্যকলাপ নিরোধ আইন’ অনুসারে নিষিদ্ধ ঘোষণা করল বিশ্ব হিন্দু পরিষদ, বজরং দল, রাষ্ট্রীয় স্বয়ং সেবক সংঘ, জামাত ই-ইসলামি-হিন্দ ও ইসলামিক সেবক সংঘকে। ওই একই আইনে ইসলামিক মুজাহির সংঘ, আগম সেনা, সারা ভারত বাবরি মসজিদ সংগ্রাম কমিটি, আলি সেনা, জিহাদ লস্করের মতো মুখোশহীন, সাম্প্রদায়িক সংগঠনগুলোকেও নিষিদ্ধ ঘোষণা করা যেত, করা উচিতও ছিল। এমনকী, শিবসেনা, ভারতীয় জনতা পার্টি ও মুসলিম লিগের মতো মুখোশহীন সাম্প্রদায়িক রাজনৈতিক দলগুলোকেও ভারতীয় সংবিধান মেনেই অর্ডিন্যান্স জারি করে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা যেত । ব্যাপারটা রাজনৈতিকভাবে কঠিন হলেও সম্ভব ছিল। কিন্তু কোন্ আইনে মনের গভীরে প্রোথিত ধর্মান্ধতাকে, ধর্মীয় মৌলবাদকে নিষিদ্ধ করা যাবে? আইনের প্রয়োজনীয়তাকে স্বীকার করে নিয়েও বলছি—শুধুমাত্র আইন দিয়ে মানুষকে ধর্মনিরপেক্ষ করা যায় না, যাবে না।
তবে কি এই অবক্ষয় থেকে উত্তরণের কোনও পথ নেই? আছে, এই পথ ধর্মনিরপেক্ষ মনকে গড়ে তোলার পথ। ব্যক্তিজীবনে এবং রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে শুধুমাত্র কথায় নয়, কাজেও সততার সঙ্গে ধর্মনিরপেক্ষতার চর্চা চালাতে হবে। ধর্মনিরপেক্ষতার সংস্কৃতি গড়ে তুলতে হবে।
আমরা অনেকেই ধর্মনিরপেক্ষতার পক্ষে প্রচুর কথা বলি, প্রচুর কথা লিখি, ভারত নামক রাষ্ট্রটির ধর্মনিরপেক্ষতার মুকুট কাদার ছিটেতে মলিন হল বিদেশিদের চোখে—এই ভেবে আর্তনাদে বুক চাপড়াই কিন্তু আমরা দেখেও দেখি না, বুঝেও বুঝি না, এ-দেশের কি বিপুল সংখ্যক মানুষ বাবরি মসজিদ ভাঙার খবরে খুশিতে ঝলমল হয়ে ওঠে, কি বিপুল সংখ্যক মানুষ ক্রিকেট বা হকি খেলায় ভারতের বিরুদ্ধে পাকিস্তানের জয়ে পাকিস্তানি পতাকা উত্তোলন করে উল্লসিত হয়, মন্দিরের পতনের খবরে মনে খুশির জোয়ার ডাকে।
এই পুরো অবস্থাটার জন্য, এমনই একটা অপসংস্কৃতির পরিবেশ সৃষ্টির জন্য অবশ্যই সবচেয়ে বড় দায়ী আমাদের শাসকগোষ্ঠী ও রাজনীতি- ব্যবসায়ীরা। এরা ধর্ম-ব্যবসায়ীদের সঙ্গে গাঁটছড়া বেধে বিভিন্ন ধর্মীয় চেতনা ও অন্ধ-বিশ্বাসকে সাধারণের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে নিরন্তর প্রয়াস চালিয়েই চলেছে, আর চূড়ান্ত মিথ্যাচারিতার সঙ্গে দল, সরকার ও রাষ্ট্রের গায়ে ধর্মনিরপেক্ষতার ছাপ মারতে সমস্ত রকমের মগজ-ধোলাই চালিয়েই যাচ্ছে। আমরা প্রচারে বাজিমাত করে যতই প্রতিষ্ঠা করতে চাই না কেন— ‘ভারত একটি ধর্মনিরপেক্ষ দেশ’ অর্থাৎ আমরা রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে ধর্মনিরপেক্ষ, বাস্তব চিত্র যে তার সম্পূর্ণ বিপরীত, সে নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা করে আগেই তা দেখিয়েছি। সুতরাং তাত্ত্বিক স্তরে, যাকে বলে অ্যাকাডেমিক নিরিখে বিচার করলেও আমাদের দেশকে নৈতিকতা ও ঔচিত্যের দিক থেকেই ‘ধর্মনিরপেক্ষ’ হিসেবে কিছুতেই চিহ্নিত করতে পারি না ।
এ-বার আমরা বিশুদ্ধ যুক্তির স্তরে একটু আলোচনা করে দেখাতে চাইছি, আমাদের রাষ্ট্রশক্তি, আমাদের সরকার দলের স্বার্থেই, ভোটের মুখ চেয়েই ঠিক করে, কখন ভারতের সর্বোচ্চ আদালত সুপ্রিম কোর্টের আদেশ মানবে, কখন মানবে না। উদাহরণ বহু। বাস্তবিকই এই দ্বিচারিতার উদাহরণ টানতে টানতে একটা পুষ্ট-বই লিখে ফেলা যায়। বহু থেকে একটি উদাহরণ এখানে টানছি, যা থেকে প্রতিটি সৎ যুক্তিনিষ্ঠ পাঠক-পাঠিকা অবশ্যই বুঝতে পারবেন, আমাদের সরকার শুধু দ্বিচারিতা দোষেই দুষ্ট নয়,
যখনই আমাদের রাষ্ট্রীয় জীবনে ধর্মনিরপেক্ষতার প্রশ্ন বিশাল
হয়ে হাজির হয়েছে, তখনই আমাদের সরকার রাষ্ট্রীয়
ধর্মনিরপেক্ষতার প্রশ্নটিকেও বিচার করেছে
দলীয় স্বার্থের কথা ভেবে,
ভোটের কথা ভেবে।
উদাহরণ হল— শাহ বানুর মামলা। শাহ বানুর মামলায় সুপ্রিম কোর্ট যে সুচিন্তিত রায় দিয়েছিলেন, সেই রায়কে ভারতের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধি পার্লামেন্টের ভোটে নস্যাৎ করে দিয়েছিলেন, মৌলবাদী মুসলিম ভোটারদের পায়ে তেল মাখিয়ে ভোট-বাক্স স্ফীত করার ধান্দায়। বাবরি মসজিদ সমস্যা রাজনৈতিক ভাবে সমাধান করতে গিয়ে ধর্মান্ধ হিন্দু বা ধর্মান্ধ মুসলিম ভোটাররা দলের উপর পাছে চটে, এই ভেবে কংগ্রেস সরকারই এই মসজিদ সমস্যাকে নিয়ে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হয়েছে। এ কি. দ্বিচারিতারই দৃষ্টান্ত নয়? ভোটের ফায়দা লোটার অপচেষ্টায় দেশবাসীর সঙ্গে প্রতারণাপূর্ণ ব্যবহারেরই জ্বলন্ত উদাহরণ নয়?
একই সঙ্গে নিন্দনীয় বামদলগুলো সহ বিভিন্ন রাজনৈতিক দলগুলোর শাহ বানু মামলার ক্ষেত্রে সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গির দ্বারা পরিচালিত ভূমিকা । রাজীব গান্ধির এমন দৃষ্টিকটু মৌলবাদীদের তুষ্ট করার প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে এরা প্রবলতম আন্দোলন গড়ে তোলার চেষ্টা করলেন না মৌলবাদী সংখ্যালঘুরা অসন্তুষ্ট হবে ভেবেই।
আসুন, এ-বার আমরা তত্ত্বের নিরিখে বিচার করে দেখি কোনও সংগঠনকে নিষিদ্ধ করে তার শক্তিকে নিঃশেষ করা যায় কি না? আমরা তাত্ত্বিক স্তরে বিষয়টিকে বিচার করলে দেখতে পাব যে-সব দলের সাংগঠনিক শক্তি জোরাল ভিতের উপর দাঁড়িয়ে নেই, অর্থাৎ যে-সব দল মানুষের আবেগের উপর নির্ভর করে অস্তিত্ব রক্ষা করছে, অথবা যে-সব দল ক্ষয়িষ্ণু, দুর্বল, কাগুজে, তাদের ক্ষেত্রে সরকারি নিষেধাজ্ঞা মৃত্যুই বয়ে আনে। কিন্তু যে-সব দল জোরাল সাংগঠনিক শক্তির উপর দাঁড়িয়ে, তাদের ক্ষেত্রে এমন নিষেধাজ্ঞা বড় জোর প্রকাশ্য কাজ-কর্মকে অন্তরালে নিয়ে যেতে বাধ্য করে। অনেক ক্ষেত্রে এমন সরকারি নিষিদ্ধ ঘোষণা দলকে সাধারণ মানুষের চোখে মহত্তর ও আকর্ষণীয় করে তোলে।
এই তত্ত্ব কতটা যুক্তিগ্রাহ্য, এটুকু জানতে আমাদের ভবিষ্যতের অপেক্ষায় না থেকে ইতিহাসের দিকে তাকালেই চলবে। ব্রিটিশ শাসকদের দমননীতি ও নিষেধাজ্ঞা দেশের স্বাধীনতাকামী মানুষদের দৃঢ় প্রতিজ্ঞাকে ভাঙতে পারেনি। স্বাধীন ভারতে এর আগেও রাষ্ট্রীয় স্বয়ং সেবক সংঘ দু’বার ও জামাত ই-ইসলামি একবার নিষিদ্ধ হয়েছে। নিষেধ উঠে যাওয়ার পর ওরা আরও বেশি শক্তি নিয়ে আত্মপ্রকাশ করেছে। এই ঐতিহাসিক ঘটনাগুলো আমাদের এমন সিদ্ধান্তেই পৌঁছে দেয়—রাজনৈতিক জীবন থেকে নির্বাসিত করে কোনও দল বা সংগঠনকে শক্তিহীন করা যাবে, বা তাদের চিন্তার হাত থেকে সমাজজীবনকে আগলে রাখা যাবে, এ-কথা সর্বক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। নিষিদ্ধ ঘোষিত দলটির সাংগঠনিক শক্তি ও তাদের চিন্তাধারা ও কর্মধারার প্রতি মানুষের শ্রদ্ধা বা অশ্রদ্ধা, তাদের বিরুদ্ধে সরকারি প্রচারে মানুষের প্রভাবিত হওয়া বা না হওয়া ইত্যাদি বিষয়ের উপর বহুলাংশে নির্ভর করে দলটি নিষিদ্ধ ঘোষিত হওয়ার পর শক্তি বজায় রাখতে পারবে কি না, শক্তি ক্ষয়িত হবে কি না অথবা শক্তি বৃদ্ধি ঘটাতে পারবে কি না, চিন্তাধারা জনগণের মধ্যে প্রসারিত হবে, কি বন্ধ হবে। নিষিদ্ধ দল নাম পাল্টে সিদ্ধ হলে যেখানে আইনের কিছুই করার নেই, সেখানে সংগঠিত সংগঠনকে শুধু নিষিদ্ধ ঘোষণা করে তার উত্থান ঠেকাবার চেষ্টা ব্যর্থ হওয়াটা কোনও অস্বাভাবিক ঘটনা নয়।
কয়েকটি মুখোশহীন সাম্প্রদায়িক দলকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করার মধ্য দিয়ে কোনওভাবেই সর্বগ্রাসী এই সাম্প্রদায়িক চিন্তার হাত থেকে আমাদের সমাজ-জীবনকে, আমাদের সংস্কৃতিকে বাঁচানো যাবে না, কারণ প্রায় প্রতিটি নির্বাচন-নির্ভর রাজনৈতিক দলই স্পষ্টতই সাম্প্রদায়িক। ভোট আদায়ের স্বার্থে এরা ধর্ম-ভাষা-জাত-পাত সব কিছু নিয়েই বিভেদ সৃষ্টি করে, রাজনীতি করে। একটা স্পষ্ট কথা বলি, প্রায় সমস্ত রাজনৈতিক দলই আজ ভারতীয় জনতা পার্টিকে নিষিদ্ধ ঘোষণার দাবিতে সোচ্চার, কিন্তু কই-এরা তো একবারের জন্যেও মুসলিম লিগকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করার দাবিতে সোচ্চার হচ্ছে না? এমনতর অদ্ভুত ব্যবহারের, দ্বিচারিতার কারণ অন্তর্নিহিত রয়েছে সাম্প্রদায়িক মুসলিম ভোটারদের খুশি করার চেষ্টার মধ্যেই।
অযোধ্যার বিতর্কিত বাবরি মসজিদকে রক্ষা করা কেন ভারতের ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রনীতির অগ্নি-পরীক্ষার প্রতীক হয়ে দাঁড়াল? কেন বিশ্ববিদ্যালয়ের সহ-উপাচার্য মুশিরুম হাসানকে ধর্মান্ধদের বর্বরোচিত আক্রমণের হাত থেকে রক্ষা করাকে ভারতের ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রনীতির অগ্নিপরীক্ষার প্রতীক করা হল না? কেন তথাকথিত ধর্মনিরপেক্ষ, প্রগতিশীল রাজনৈতিক দলগুলো এই ধৰ্মীয় মৌলবাদ, ধর্মীয় ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে গর্জে উঠল না? কথায় ও কাজে রাজনৈতিক দলগুলোর কেন এমন ‘আশমান-জমিন’ ফারাক? ভোটের কথা মাথায় রেখে মুসলিম মৌলবাদীদের তুষ্ট করতেই কি এই নীরবতা? শ্রদ্ধেয় পাঠক-পাঠিকা, চোখ-কান খোলা রাখলে এর উত্তর অবশ্যই আপনাদের অজানা, অধরা থাকবে না। আপনাদের সচেতনতাই পারে রাজনৈতিক ব্যবসায়ীদের এমন দ্বিচারিতা, অসততা ও শয়তানি বন্ধ করতে।
ভ্রাতৃদাঙ্গায় জড়িয়ে পড়া সাম্প্রদায়িকতার বিষে জর্জরিত দেশের এমন এক ক্রান্তিকালে সাংস্কৃতিক আন্দোলনকর্মী ও সংগঠনগুলোর ভূমিকা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। সভা-সমিতি-মিছিল-প্রচার-পুলিশ-প্রশাসন-সেনাটহল ইত্যাদির সম্মিলিত প্রয়াস দ্বারা হয়তো একটা আত্মহননকারী জাতিদাঙ্গার লেলিহান শিখা স্তিমিত করতে পারে, কিন্তু মানুষের মনে তুষের আগুনের মতো ধিকি ধিকি জ্বলতে থাকা সাম্প্রদায়িকতার আগুন নেভাতে পারে না, যাতে থাকে আবারও ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড ঘটে যাওয়ার সম্ভাবনা। এমন গোপন-আগুন সর্বদলীয় মিটিং-মিছিল বা সেনা-পুলিশের গুলির মুখে নেভার নয়। এ-আগুন নেভানোর কোনও শর্টকাট রাস্তা নেই। এ-পথ অত্যন্ত দীর্ঘ, এর প্রক্রিয়া অত্যন্ত দীর্ঘস্থায়ী। এক ধর্মনিরপেক্ষ সাংস্কৃতিক পরিবেশ তৈরির দীর্ঘস্থায়ী প্রচেষ্টার মধ্য দিয়েই মানুষের মনের ধর্মান্ধতার তুষের আগুন নেভাতে হবে। মানুষের মনে ধর্মনিরপেক্ষতার চিন্তা-ভাবনা প্রোথিত করতে পারলে আপনা থেকেই উপড়ে আসবে ধর্মীয় উন্মত্ততার শিকড়। ধর্মনিরপেক্ষ মানুষ গড়াতে এই পদ্ধতির কোনও বিকল্প নেই।
পশ্চিমবঙ্গে সাম্প্রদায়িকতার কোনও স্থান নেই”–মুখ্যমন্ত্রীর এমনতর ঘোষণাটি যখন বিভিন্ন ঋতুতে ঘুরে-ফিরে বসন্তের হাওয়ার মতোই প্রশান্তি ও তৃপ্তি বয়ে আনছিল নাগরিক মনে, ঠিক তখনই তাঁরই মন্ত্রিসভার রাজচক্রবর্তী মন্ত্রীরা তাঁদের স্নেহভাজন মাম্যানদের মহা ধুম-ধামে পুজো-আর্চা চালিয়ে যাওয়ার প্রতিযোগিতার মধ্য দিয়ে সৃষ্টি করে চলেছিলেন ধর্মান্ধতার ঘুণ-পোকা, যারা নিঃশব্দে আপন কাজ চালিয়েই গিয়েছিল। তারই ফলে অযোধ্যাকাণ্ডের পরে-পরেই তামাম বঙ্গবাসী অবাক বিস্ময়ে দেখলেন ধর্মান্ধতার এক ফুৎকারে বঙ্গবাসীদের সযত্নে লালিত ধারণা ও মুখ্যমন্ত্রীর গর্বের দুর্গ ভেঙে চুরমার হয়ে গেল। যে ক্যাডার বাহিনীকে কথায় কথায় আন্দোলন রোধে ডান্ডা হাতে রাস্তায় নামতে দেখা যেত, সাম্প্রদায়িকতা রোধে তাদের টিকির দেখা মিলল না। বরং বহু অঞ্চলে রাজনৈতিক মাস্লম্যান ও ক্যাডাররাই সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বাধাল। দাঙ্গায় ক্ষতিগ্রস্তরা দাঙ্গাকারীদের পরিচয় জানালেন পুলিশকে, পত্র-পত্রিকার সাংবাদিকদের। সব-জেনে শুনেও পুলিশ রাজনীতির ব্যবসায়ীদের সন্তুষ্ট রাখতে আশ্চর্য রকম নিস্পৃহতা দেখাল দাঙ্গার যত পালের গোদাদের গ্রেপ্তার করার ব্যাপারে।
যখন কলকাতায় রাজনীতির ব্যবসায়ীদের আশ্রিত গুন্ডারা লুট-তরাজ, অগ্নিকাণ্ড ও হত্যার বিভীষিকা চালিয়ে যাচ্ছে, ঠিক সেই সময় পশ্চিমবাংলার গ্রাম-শহরের চিত্র ছিল কিছুটা ভিন্নতর। জাতীয় জীবনের এমন এক চরম মুহূর্তে গ্রামে-শহরে শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষদের পাশে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষার কাজে জীবনকে বাজি রেখে কাজে নেমেছিলেন সমাজ সচেতন মানুষরা, যুক্তিবাদীরা। কলকাতার মতো গ্রামে-গঞ্জে দাঙ্গা না ছড়াবার একটা বিরাট কারণই হল, নাওয়া-খাওয়া-ঘুম শিকেয় তুলে রাখা কিছু সমাজসচেতন ও যুক্তিবাদীদের ভূমিকা।
কলকাতা থেকে কার্ফু বিদায় নেওয়ার আগেই ভারতীয় বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী সমিতির জরুরি ভিত্তিতে কলকাতা-সহ পশ্চিমবাংলায় ৩০০ সহযোগী সংস্থা ও শাখা সংগঠনের মাধ্যমে ধর্মনিরপেক্ষ মানুষ গড়ার কাজে সর্বত্র মিটিং-মিছিল শুরু করল। সে-সব মিটিং-মিছিলে যুক্তিবাদী সমিতির পক্ষ থেকে দাবি রাখা হতে লাগলঃ
(১) ভারতীয় সংবিধানের ‘ধর্মনিরপেক্ষ (Secular)’ শব্দটির অর্থ করা হয়েছে-ধর্মের ক্ষেত্রে ভারত থাকবে নিরপেক্ষ। রাষ্ট্রনীতি, রাজনীতি ও শিক্ষা নীতি ধর্মীয় অনুপ্রবেশ থেকে মুক্ত থাকবে। সংবিধানকে মর্যাদা দিতে সরকারকে ধর্মনিরপেক্ষতার যথাযথ প্রয়োগ করতে হবে। অর্থাৎ,
(ক) রাষ্ট্রীয় সমস্ত রকম কার্যকলাপে ধর্মীয় অনুপ্রবেশ বন্ধ করতে হবে। (খ) শিক্ষায়তনগুলোতে কোনও ধর্মীয় অনুষ্ঠান, ধর্মীয় প্রার্থনা, ও পঠন-পাঠনে ধর্মীয় নেতাদের জীবনী এবং প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মচেতনা বৃদ্ধিকারী বিষয়ের অন্তর্ভুক্তিকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করতে হবে।
(২) ধর্মীয় কার্যকলাপে রাজনৈতিক নেতাদের পৃষ্ঠপোষকতা ও সহযোগিতা নিষিদ্ধ করতে হবে।
(৩) যে রাজনৈতিক দলের নেতা ধর্মীয় কার্যকলাপে পৃষ্ঠপোষকতা করবেন অথবা প্রকাশ্যে ধর্মীয় অনুষ্ঠানে অংশ নেবেন, সেই নেতাকে দল থেকে বহিষ্কার করতে হবে, নতুবা গোটা দলকেই সাম্প্রদায়িক হিসেবে নিষিদ্ধ ঘোষণা করতে হবে।
(৪) সরকরি প্রচার-মাধ্যমে ধর্মীয়-প্রচারকে নিষিদ্ধ করতে হবে।
(৫) কোনও আবেদন পত্রে আবেদনকারীর ধর্ম জানতে চাওয়া চলবে না ।
কোনও রাজনৈতিক দল সাম্প্রদায়িক কাজ-কর্মের সঙ্গে জড়িত থাকলে বা সাম্প্রদায়িকতাকে পালন করার কাজে বা উস্কে দেওয়ার কাজে যুক্ত থাকলে সংবিধানের ১৯৮৯ সালের রিপ্রেজেন্টেশন অফ দ্য পিপল্ (অ্যামেন্ডমেন্ট) অ্যাক্টের ২৯(এ) ধারা বলে ওই রাজনৈতিক দলের স্বীকৃতি খারিজ করার বিধান আছে।
উপরোক্ত ধারা মতে, দেশের সংবিধানে যে মৌলিক নীতিগুলি আছে, প্রতিটি রাজনৈতিক দলকে সেই মৌলিক নীতিগুলির প্রতি লিখিতভাবে আস্থাজ্ঞাপন করতে হবে নির্বাচন কমিশনের কাছে। কোনও ক্ষেত্রে কোনও দল এই নীতিগুলি অমান্য করলে নির্বাচন কমিশন ২৯(এ) ধারা বলে সেই রাজনৈতিক দলের রেজিস্ট্রেশন কেড়ে নিতে পারে।
এই মৌলিক নীতিগুলি কী? সংবিধানের মুখবন্ধের (Preamble) প্রথম অনুচ্ছেদেই বলা হয়েছে, ‘WE THE PEOPLE OF INDIA, having solemnly resolved to constitute India into a SOVEREIGN SOCIALIST SECULAR DEMOCRATIC and to secure to all its citizens:’ অর্থাৎ সার্বভৌম গণতান্ত্রিক, ধর্মনিরপেক্ষ, সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র হল দেশের সংবিধানের মৌলিক নীতি।
আমাদের সমিতি স্পষ্টতই চায়-সরকার সাম্প্রদায়িকতার প্রশ্নে সংবিধানকে মান্য করে চলুক। একটি সংগঠনের দাবির ধাক্কাতেই সরকার ও রাজনৈতিক দলগুলো তাদের সাম্প্রদায়িক চরিত্র ত্যাগ করে অসাম্প্রদায়িক মানুষ গড়ার কাজে নিবেদিত প্রাণ হবে, এমনটা কখনওই প্রত্যাশা করি না। আর তাই আমরা চাই উপরের দাবির পক্ষে জনমত গড়তে। এই চিন্তাকে সার্থক রূপ দিতে এই দাবির পক্ষে দ্রুত জনমত গড়ে তুলতে ভারতীয় বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী সমিতি একদিকে যেমন সভা-সমিতিকে কাজে লাগাতে লাগল, তেমনই এই পাঁচটি দাবি সংবলিত স্মারকলিপি পেশ করল ভারতের রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী, কেন্দ্রীয় আইনমন্ত্রী, কেন্দ্রীয় মানবসম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রী, সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী এবং পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রীকে।
স্মারকলিপিতে আরও দাবি করা হল, ‘কথায় ও কাজে, এতাবৎকাল যে বিপরীত মেরুতে আপনারা অবস্থান করেছেন, তারই পরিণতিতে মানুষ ধর্মনিরপেক্ষ না হয়ে সাম্প্রদায়িক হয়েছে। দেশকে বাস্তবে ‘ধর্মনিরপেক্ষ’ রূপ দিতে চাইলে এই দাবিগুলির প্রত্যেকটিকে কার্যকর করতে সমস্ত রকম পদক্ষেপ নিন।”
এই দাবিকে আরও ব্যাপকতর আকার দিতে, আন্দোলনে রূপান্তরিত করতে ভারতীয় বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী সমিতি এক শ্বেতপত্র প্রকাশ করে শুভবুদ্ধিসম্পন্ন, সমাজ-সচেতন ব্যক্তি ও সংগঠনের কাছে আবেদন রাখল—“দেশে প্রকৃত ‘ধর্মনিরপেক্ষ’ মানুষ গড়ার স্বার্থে এই দাবিগুলোর পক্ষে বৃহত্তর জনমত গড়ে তুলতে সর্বশক্তি নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ুন, গণআন্দোলন গড়ে তুলুন। আপনারা প্রত্যেকেই ব্যক্তিগতভাবে অথবা সংগঠনের তরফ থেকে উপরের পাঁচটি দাবিকে পেশ করুন আমাদের দেশের রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী, কেন্দ্রীয় আইনমন্ত্রী, মানবসম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রী, সংসদ বিষয়ক মন্ত্ৰী এবং নিজ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীকে। আপনারা সভা-সমিতিতে, নিজেদের প্রকাশিত পত্র-পত্রিকায়, লিফলেটে ও আলাপ-আলোচনায় এই দাবির পক্ষে শক্তিশালী জনমত গড়ে তুলতে সচেষ্ট হোন। তারই সঙ্গে সচেষ্ট হোন, কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের কাছে আরও বেশি বেশি করে দাবিপত্র পেশ করার কাজে জনগণকে শামিল করতে। সকল শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষের সম্মিলিত প্রচেষ্টা অবশ্যই পারে সরকার ও রাজনৈতিক দলগুলোকে ধান্দাবাজি ছেড়ে বাস্তবে ‘ধর্মনিরপেক্ষ’ দেশ গড়ার কাজে শামিল করতে, আইন মানতে বাধ্য করতে। কারণ শেষ কথা বলে জনগণই।
একটা গভীর দুঃখ ও শঙ্কার কথা জানাই—অযোধ্যাকাণ্ড ও সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা নিয়ে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় যে সমস্ত প্রথিতযশা বুদ্ধিজীবী সম্প্রীতির পক্ষে কলম ধরেছিলেন কোনও রকম দিশা দেখাতে, স্বচ্ছ সমাধান বার করে আনতে পারেননি তাঁরাও। বরঞ্চ ব্যতিক্রমহীনভাবে প্রত্যেকেই সাম্প্রদায়িকতার প্রশ্নে সরকারি মগজ-ধোলাই নীতিকেই সার্থক করতে যেন উঠে-পড়ে লেগেছিলেন। প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মকে সর্বস্তরে সরাসরি আক্রমণের বদলে সর্বধর্ম-সমন্বয়ের সাত-বাসী কীর্তন জনগণের কানের পাশে গেয়ে গেছেন তাঁরা। সাম্প্রদায়িকতার বিষবৃক্ষটির ডাল-পাতা ছেঁড়া-ছেঁড়ির হুটোপুটিতে মত্ত হলেও শিকড় ধরে টান দেবার চেষ্টা করেননি বুকের পাটার অভাবে। একটু ভুল বললাম? বরং বলি, অনেক বুদ্ধিজীবী শিকড়ে হাত দিতে চাননি রাজনীতির ব্যবসায়ীদের সঙ্গে নিজেদের দেওয়া-নেওয়ার’ সুমধুর সম্পর্ককে অটুট রাখতে, অনেকে বোধবুদ্ধির অভাবে।
‘ধর্মনিরপেক্ষ’ মানুষ সৃষ্টির মধ্য দিয়ে ধর্মনিরপেক্ষ দেশ গড়ার কাজে বুদ্ধিজীবীরা যে দিশা দেখাতে ব্যর্থ হলেন, সেই দিশাই দেখাল যুক্তিবাদী সমিতি। ‘ধর্মীয় মৌলবাদ’ ও ‘ধর্মনিরপেক্ষতা’ বিষয়ে যে ব্যাখ্যা আজ থেকে বছর তিনেক আগে হাজির করেছিলাম আমার লেখায়, তা আমাদের সমিতি গ্রহণ করার সঙ্গে সঙ্গে জনগণকে আন্দোলিত করার ক্ষেত্রে নতুন মাত্রা যুক্ত হয়েছিল। সমিতির শ্বেতপত্রে এই ব্যাখ্যাগুলোই হাজির করা হয়েছিল। সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল পাঁচ দফা দাবি। অযোধ্যাকাণ্ডের পর আমাদের হাজির করা ব্যাখ্যা ও দাবি সর্বসাধারণের মধ্যে বিপুল গ্রহণ-যোগ্যতা পেল। পূর্ব-ধারণা থেকে সরে এসে আমাদের সুরে সুরে সুর মেলালেন দুই-বাংলার অনেক সাহিত্যিক ও বুদ্ধিজীবীই। ধর্মীয়-মৌলবাদ রুখতে যুক্তিবাদী আন্দোলনের প্রতি সমর্থন জানিয়ে সম্পাদকীয় প্রকাশিত হল আনন্দবাজার, আজকাল, বর্তমান ও গণশক্তিতে। বিজ্ঞান আন্দোলনকে বিজ্ঞানমনস্ক মানুষ গড়ার আন্দোলনে রূপান্তরিত করার কথা বলে তাঁদের দলের এতদিনকার চালানো বিজ্ঞান আন্দোলনের ব্যর্থতা ও জন-বিচ্ছিন্নতার কথা স্বীকার করলেন জ্যোতি বসু এবং পৃথকভাবে সি.পি.এম-এর রাজ্য নেতৃত্ব। ২ জানুয়ারি ‘৯৩ পশ্চিমবঙ্গ সরকার আয়োজিত পশ্চিমবঙ্গ গ্রন্থমেলায় আমাদের সমিতি ‘অলৌকিক নয়, লৌকিক’ শিরোনামে যে অনুষ্ঠান করল তাতে গ্রন্থমেলার ইতিহাসে অনুষ্ঠান শ্রোতাদের ভিড়ের সর্বকালীন রেকর্ড স্থাপিত হল। আর তা হয়েছিল, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা প্রসঙ্গে আমরা কী বলি— তাই শুনতে। জনদাবিতে গোটা মেলা প্রাঙ্গণের মাইকেই আমাদের বক্তব্য প্রচারিত হল। মেলার শেষ শনিবারে দোকানে প্রত্যাশিত বিপুল বিক্রি মার খেল। মেলা জুড়ে মানুষের ঢল— সকলে আমাদের কথা শুনতে চান। সেদিনের শ্রোতাদের মধ্যে ছিলেন অনেক মন্ত্রী রাজনৈতিক নেতা ও বুদ্ধিজীবী। অনুষ্ঠান চলাকালীন সি.পি.এম-এর কিছু নেতা যেমন গ্রিনরুমে এসে আমাদের বক্তব্য লাগাম পরাতে সচেষ্ট হলেন, তেমনই সি.পি.এম-এর প্রথম সারির কিছু নেতা গ্রিনরুমে এসে আমাদের বক্তব্যের প্রতি জোরালো সমর্থন জানিয়ে গেলেন। এই ঘটনা থেকে বুঝলাম–আমরা যদিও কোনও রাজনৈতিক দলের শাখা-প্রশাখা নই, তবু আমাদের বক্তব্যের সূত্র ধরে একটি সংগঠিত রাজনৈতিক দলের মধ্যে কতকগুলো প্রশ্ন, মূল্যবোধ-সম্পর্কিত-প্রশ্ন উঠে আসতে শুরু করেছে।
রাষ্ট্রের ধর্ম-নিরপেক্ষতা বজায় রাখার পক্ষে আমাদের সমিতির হাজির করা পাঁচ দফা দাবি ইতিমধ্যেই যথেষ্ট আলোড়ন সৃষ্টি করেছে। বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় দাবিগুলো যথেষ্ট গুরুত্ব সহকারে প্রকাশিত হয়েছে। এবং তারপর পত্রিকাগুলোর পাঠকদের মতামত জ্ঞাপনকারী কলমে বহু চিঠি প্রকাশিত হয়েই আসছে, দাবির সমর্থনে। সুদূর গ্রাম বাংলার খবরের কাগজ ‘গাঁয়ের কথা’ ও ‘গ্রামীণ সংবাদ’-এ প্রকাশিত হল আমাদের শ্বেতপত্রের প্রথম-লাইন থেকে শেষ লাইন পর্যন্ত। ১৯ জানুয়ারি ’৯৩ দূরদর্শনের জাতীয় কার্যক্রমে ‘পরখ’ অনুষ্ঠানে বিনোদ দুয়ার সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে কেন্দ্ৰীয় ‘হেভি-ওয়েট’ মন্ত্রী বসন্ত শাঠে আমাদের সমিতির হাজির করা ‘ধর্মনিরপেক্ষ শব্দের ব্যাখ্যার প্রসঙ্গ টেনে তার বিরোধিতা করতে গিয়ে এ-কথা অবশ্য স্বীকার করলেন, আমাদের সমিতির হাজির করা ব্যাখ্যা ইতিমধ্যেই ভারতের বুদ্ধিজীবী মহলে যথেষ্ট প্রভাব ফেলেছে। একটি বিশিষ্ট বাম-রাজনৈতিক দল আমাদের হাজির করা পাঁচ-দফা দাবিকে পরিপূর্ণ সমর্থন জানিয়ে ওই দাবির সমর্থনে জনমত সৃষ্টি করতে বিভিন্ন সভায় বক্তব্য রাখছেন। আরও একটি সর্ব-ভারতীয় রাজনৈতিক দল আমাদের এই দাবির সমর্থনে জনমত গড়ার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে, এই জনমত গড়ার কাজে কাঁধে-কাঁধ মিলিয়ে কী ভাবে চলা যায়, সে বিষয়ে আমাদের সঙ্গে আলোচনা চালাবার দায়িত্ব দিয়েছেন তাঁদের দলের প্রথম সারির একাধিক নেতাকে। আমরা কোনও রাজনৈতিক দলের শাখা-প্রশাখা নই ঠিকই, কিন্তু আমরা, আমরাই মিছরি তৈরির আগের সেই মিছরির দানা, যাকে ঘিরে মিছরি জমাট বাঁধে, মিছরির ‘ক্রিস্টাল’ তৈরি হয়। মাত্র কয়েক দিনের মধ্যেই বহু সংস্থা ও ব্যক্তি এগিয়ে এলেন পাঁচ দফা দাবির সমর্থনে জনমত গড়ার কাজে, অবক্ষয়ী—সংস্কৃতির বিরুদ্ধে প্রগতিশীল—সংস্কৃতি গড়ার কাজে। সেই সঙ্গে সচেতন প্রতিটি মানুষের কাছে যুক্তিবাদী সমিতি আরও একবার প্রতিষ্ঠা করল তাদের যুক্তির সারবত্তা—সব দেশে, সব ঋতুতেই সাংস্কৃতিক আন্দোলনের, যুক্তিবাদী আন্দোলনের কোনও বিকল্প নেই।
একটি সত্যিকারের আন্দোলনঃ দিন বদলের খিদে ভরা চেতনার
যুক্তিবাদী আন্দোলনকে যাঁরা জীবনের শ্বাস-প্রশ্বাস করে নিয়েছেন, যাঁদের কাছে সাংস্কৃতিক আন্দোলন বেঁচে থাকার ভাত রুটি, যাঁরা আদর্শের বারুদ ঠেসে শরীরের খোল ভরিয়ে রেখেছে, যাঁরা বঞ্চিত মানুষগুলোর প্রেমে লায়লা কী মজনু—প্রেমের মূল্য তো তাঁদের দিতে হবেই। প্রেম করব কিন্তু মূল্য দেব না; এ হয় না, হতে পারে না। সে মানব-মানবীর প্রেমই হোক আর দেশপ্রেমই হোক । আদর্শের প্রতি এই প্রেম, বঞ্চিত মানুষদের প্রতি এই প্রেমই আত্মোৎসর্গে অনুপ্রাণিত করে,
আদর্শের বারুদে বিস্ফোরণ ঘটিয়ে ছিন্নভিন্ন করে দেয় নিজের
শরীরের সঙ্গে সঙ্গে শত্রু শরীরও। এমন আদর্শে নিবেদিত
প্রাণ সারা শরীরে বারুদ ঠাসা মানুষ ইতিহাসের
পাতা থেকে হঠাৎ উঠে আসে না। এরা
তৈরি হয়। আদর্শ এদের
তৈরি করে।
এরা আবেগতাড়িত হিস্টিরিয়াগ্রস্ত অবস্থায় টপ করে প্রাণ দিয়ে ফেলে না। এরা উত্তেজনাহীন, আবেগহীন অবস্থাতেও নিজ আদর্শে অবিচল। আবারও বলি এমন মানুষ তৈরি হয়েছে আদর্শকে সামনে রেখেই । আত্মোৎসর্গ ব্যাপারটা এইসব আদর্শবাদীদের কাছে দৈনন্দিন আর দশটা কাজকর্মের মতো এতই স্বাভাবিক যে, এর মধ্যে তারা কোনও বিশেষ বীরত্ব বা বিশেষ মাত্রা আছে বলে মনে করে না। নিছক কল্পনা থেকে এসব কথা লিখছি না। এসব কথা কলম থেকে উঠে এসেছে বাস্তব অভিজ্ঞতার ফসল হিসেবে। আন্দোলন করব, শাসক শ্রেণি ও রাষ্ট্রক্ষমতাকে আক্রমণ করব, অথচ আক্রান্ত হব না এমন বোকার মতো প্রত্যাশা রাখি না। আক্রান্ত হয়েছি, হচ্ছি, হব।
আজ এক চরম যুগ-সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে স্পষ্ট বুঝে নেবার প্রয়োজন আছে যুক্তিবাদ নিয়ে আন্দোলন আন্দোলন খেলায় শামিল না হয়ে সত্যিকারের গণআন্দোলন গড়ে তুলতে থাকলে আঘাত আসবেই। এই আন্দোলন যাদের স্বার্থকে আঘাত করবে, যাদের অস্তিত্বকেই বিপন্ন করে তুলবে, তারা যে আঘাত হানবেই এবং সে আঘাত হবে অবশ্যই নিষ্ঠুর ভয়ংকর। এই আন্দোলনে প্রয়োজন ব্যাপক জনসমর্থন। শোষিত জনগণ যে-দিন তাঁদের নিজেদের যুক্তিতে বুঝতে পারবেন কুসংস্কারের সঙ্গে শোষণের সম্পর্কটা, সে-দিন যে গণ-আন্দোলন গড়ে উঠবে, তাতে বর্তমান সমাজ-ব্যবস্থার ভিত্তিমূল পর্যন্ত আন্দোলিত হবে। সেই আন্দোলনকে ধ্বংস করতে হুজুরের তল্পিবাহক সরকার ময়দানে নামবেই নানাভাবে । নামবে অত্যাচার, কুৎসা, চরিত্রহনন, ব্ল্যাকমেইলিং ইত্যাদি অস্ত্র নিয়ে। আজকাল সরকার আর শত্রুদের বিরুদ্ধে শুধু মাইনে করা সেনা, পুলিশ নামায় না। হাজির করে গোয়েবেলস- এর মিথ্যেকে লজ্জা পাইয়ে দেওয়া নানা ফন্দিফিকির, ষড়যন্ত্র। ফলে আন্দোলনের নেতৃত্বে আপনি এগিয়ে এলে হঠাৎই এক রাতে দেখতেই পাবেন পুলিশ আপনার আস্তানায়। তারপর ভ্যানে তোলা। গুলির শব্দ, আর্তনাদ, সব শেষ। তার ওপর রাত দুপুরে পুলিশের কোনও বড়কর্তা পত্রিকার অফিস ও সংবাদ মাধ্যমগুলোকে ফোনে দারুণ একটা খবর শোনাবেন; কোনও পতিতার ঘরে এক সমাজবিরোধীর সঙ্গে ঝগড়ায় লিপ্ত হয়ে গুলিবিদ্ধ হয়ে আপনার মারা যাওয়ার খবর। অথবা ছড়ানো হতে পারে অন্য কোনও গপ্পো যা সাধারণ মানুষ চেটে পুটে খবেন, সেই সঙ্গে খাওয়া হবে আন্দোলনেরও কিছুটা। ষড়যন্ত্রের শিকারে কত রকমভাবেই না খেলে বিশাল-প্রভাবশালী রাষ্ট্রক্ষমতা। সরকারের একান্ত ইচ্ছেয় সাধুকে চোর বানানো কঠিন কী?
আপনার আমার দাবি জানানোর গণতান্ত্রিক অধিকার, আপনার আমার বেঁচে থাকার গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা করতে পুলিশ ও প্রশাসন এগিয়ে আসবে এবং পুলিশ ও প্রশাসনের দেওয়া নিরাপত্তার ঘেরাটোপের ওপর নির্ভর করে আমাদের আন্দোলন এগোবে এমন অদ্ভুত চিন্তা করলে এখনই সচেতন হওয়ার প্রয়োজন আছে। আন্দোলনকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হলে বাস্তব সত্যকে বুঝতেই হবে। বুঝতে হবে হুজুরের দলের সঙ্গে হুজুরদের অর্থে জেতা সরকার গঠনকারী রাজনৈতিক দলগুলোর সম্পর্ক এবং সরকারের সঙ্গে পুলিশ ও সেনার সম্পর্ক । একই সঙ্গে মনে রাখতে হবে যাঁদের জন্য আন্দোলন, যাঁদের নিয়ে আন্দোলন, তাঁরাই আমাদের আন্দোলনের শক্তি। আমরা আন্দোলনের প্রাথমিক পর্যায়ে যখনই আক্রান্ত হয়েছি জনরোষ আক্রমণকারীদের ভাসিয়ে নিয়ে গেছে, তারা পিছু হটতে বাধ্য হয়েছে। আজ যুক্তিবাদী আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত এমন বহু মানুষ তৈরি হয়েই গেছেন, যাঁরা প্রয়োজনে অবলীলায় নিজের হৃৎপিণ্ড পেতে দিতে পারেন শত্রুর গরম সীসায় বিদীর্ণ হতে। দেশপ্রেমই তাঁদের এমন করে গড়েছে।
তবু এরপরও একটা অতি প্রয়োজনীয় কথা বলার থেকেই যায়, সেটা হল—আন্দোলন এগোয় উত্থান পতনের পথ ধরে, আন্দোলন অনেক উত্থান পতনের সমষ্টি। আন্দোলনের সংকট মুহূর্তে, প্রয়োজনে পিছু হঠার মুহূর্তে এই সত্যটা স্মরণে রাখলে লড়াই করার প্রেরণা পাওয়া যায়, উজ্জীবিত হওয়া যায়, হারতে হারতেও হারাকে জেতায় রূপান্তরিত করা যায়।
আন্দোলনে যতই বেশি বেশি করে বঞ্চিত মানুষরা অংশ নেবে ততই আন্দোলন ধ্বংসে আক্রমণ তীব্রতর করবে রাষ্ট্রশক্তি। খেটে খাওয়া মানুষদের বিরুদ্ধে খেটে খাওয়া মানুষদের কাজে লাগাতে ‘উগ্রপন্থী’ ছাপও মারা হবে লড়াকু আপসহীন আন্দোলনকর্মীদের বুকে-পিঠে। উগ্রপন্থীদের নির্মূল করার প্রশ্নে ভারতের প্রায় সমস্ত রাজনৈতিক দল ও তাদের পকেটের বুদ্ধিজীবীরাই প্রচণ্ড সোচ্চার। বিপজ্জনক মতৈক্যের জোয়ারে বলিষ্ঠ সত্যটুকু প্রকাশ করতে ভয় পায় অনেকেই। জেনে-বুঝেও এইসব শঙ্কিত কণ্ঠগুলো যা বলতে পারে না, তা হল— উগ্রপন্থীরা তো উল্কার মতন আকাশ থেকে এসে খসে পড়েনি। অবহেলিত বঞ্চিত মানুষগুলোর অধিকার দাবির ক্ষেত্র থেকে উঠেছে এই সমস্যা । উগ্ৰপন্থী মারতে হবে শুনলে জনসাধারণের অর্থে পোষ্য সরকারি পুলিশ ও সেনাবাহিনীর চোখে মুখে ফুটে ওঠে একটা জিঘাংসা, কিলার ইনস্টিংক্ট। তারপর তারা আন্দোলনকারী জনগোষ্ঠীর ওপর যে অত্যাচার চালায় তা নাৎসি অত্যাচারকেও হার মানায়। ভুক্তভোগী জনগোষ্ঠীর সঙ্গে যাঁরা যুক্ত নন, তাঁদের একথা শুধু কলমে লিখে বোঝানো যাবে না।
এখানে একটা ছোট্ট উদাহরণ টানছি, ৯১-এর অক্টোবরে হারারে তে মিলিত হয়েছিলেন কমনওয়েলথভুক্ত দেশগুলোর রাষ্ট্র-প্রধানেরা। বহু দেশেই প্রধানরাই ছিলেন ঋণভিক্ষু। ব্রিটেন ও কানাডা প্রস্তাব আনতে চেয়েছিল- ঋণপ্রার্থী দেশগুলোর মানবাধিকার রক্ষার রেকর্ড দেখে ঋণ দেওয়া হবে। এই প্রস্তাবের তীব্র বিরোধিতা করেছিল ভারত সহ তৃতীয় বিশ্বের প্রায় সব দেশই । কারণ একটাই—রেকর্ড ঘাঁটলে দক্ষিণ আফ্রিকার মানবাধিকার রক্ষিত হচ্ছে না বলে চোখের জলে বুক ভাসানো এইসব দেশের ঋণ পাওয়া অসম্ভব হয়ে যায়-মানবাধিকারকে অতি বর্বরতার সঙ্গে নিষ্পেষিত করার অপরাধে।
যুক্তিবাদী আন্দোলনে যাঁরা নেতৃত্ব দিচ্ছেন ও দেবেন তাঁদের তাই সচেতন থাকতে হবে, বুঝতে হবে আন্দোলনের শত্রু-মিত্রকে। আন্দোলনকর্মী ও নেতাদের আন্তরিকতা, তাঁদের নিপীড়িত মানুষদের প্রতি সমুদ্র-গভীর প্রেমই দিতে পারে আন্দোলনের অসামান্য সাফল্য। এই আন্তরিকতার ও প্রেমের মাঝখানে কখনও আসতে পারে না আপসমুখী কোনও চিন্তা। এই আপসমুখী মানসিকতা দ্বিধাই আপনাকে হিসেবি পা ফেলতে শেখাবে, ক্যারিয়ার গোছাতে শেখাবে। প্রেম কখনও হিসেবি পা ফেলতে শেখায় না।
সাংস্কৃতিক আন্দোলনকর্মী ও বিজ্ঞান আন্দোলনকর্মীদের সচেতন
থাকতেই হবে তাঁদের নেতাদের কাজকর্মের বিষয়ে,
যাতে চ্যুতি ঘটলে নজর না এড়ায়।
আন্দোলনকে বিপথে চালিত করতে শোষক ও শাসকরা নানাভাবে প্রতিটি সাংস্কৃতিক সংগঠন, বিজ্ঞান ক্লাব এবং কুসংস্কার-মুক্তির কাজ-কর্মের সঙ্গে জড়িত সংস্থাতে থাবা বসাতে চাইবেই। চাইবেই তাদের মতো করে।
কুসংস্কার-মুক্তির আন্দোলন খেলায় সাংস্কৃতিক কর্মীদের মাতিয়ে রাখতে । সাধারণ মানুষের চেতনা রোধ করতে ওরা এমনটা করবেই। আর সেইজন্য অতি সরলীকৃত পদ্ধতিটি হল– সংস্থার নেতাদের চিহ্নিত করো, তাদের কিনে পকেটে পুরে ফেলো।
যে নেতা নিজেকে বিকিয়ে দিয়েছে, তাকে আপনারা—আন্দোলনকর্মীরাই চিহ্নিত করুন, বিচ্ছিন্ন করুন আন্দোলন থেকে। আপনার আমার যদি লক্ষ্য সম্বন্ধে সঠিক ও স্বচ্ছ ধারণা থাকে, তবেই বুঝতে পারব নেতৃত্ব আমাদের অন্য দিকে ঠেলে নিয়ে যেতে চাইছে কি না।
কোনও অপছন্দের আন্দোলনকে ধ্বংস করতে রাষ্ট্রশক্তি সেই আন্দোলনে ঢুকিয়ে দেয় ট্রয়ের ঘোড়া। যাদের অন্তর্ঘাতে আন্দোলন ধ্বংস হয়ে যায়। সব দেশের ইতিহাসেই ছড়িয়ে রয়েছে এমন বহু উদাহরণ। বহু থেকে একটিকে তুলে দিচ্ছি। নকশালপন্থী রাজনৈতিক আন্দোলনের সঙ্গে যে কোনও কৌশলেই হোক মিশে গিয়েছিল সমাজবিরোধী গোষ্ঠী। আর সমাজবিরোধীদের প্রয়োগ করা হয়েছিল ওই আন্দোলন ধ্বংস করার কাজে। এ বিবরণ রঞ্জিত গুপ্তেরই দেওয়া, যিনি নকশাল দমনকারী পুলিশ কমিশনার হিসেবে পরিচিত।
নকশালপন্থার সমর্থন বা অসমর্থন আমার এই উদাহরণ টেনে আনার উদ্দেশ্য নয়। উদ্দেশ্য আন্দোলনকারীদের সামনে দৃষ্টান্ত এনে বোঝার ব্যাপারটা আরও ‘জল-ভাত’ করে দেওয়া।
কুসংস্কার-মুক্তির আন্দোলনকে এগিয়ে নিয়ে যেতে যে-সব বিষয়গুলো মাথায় রাখা প্রাথমিকভাবে প্রয়োজনীয় সেগুলো হলঃ
১. সাংস্কৃতিক জগতে শাসক ও শোষকদের একচেটিয়াপনা বন্ধ করতে হবে। নতুন সাংস্কৃতিক পরিবেশ গড়ে তুলতে আমাদেরও সমস্ত রকমভাবে চেষ্টা করতে হবে প্রতিটি গণমাধ্যম ও প্রচার মাধ্যমকে কাজে লাগাতে। যে-সব গণমাধ্যম ও প্রচারমাধ্যম মানুষকে আকর্ষণ করে, তার প্রতিটিকে কাজে লাগিয়েই আমরা আমাদের চিন্তা-চেতনাকে পৌঁছে দেব, প্রতিটি মানুষের মধ্যে। মানুষ যেখানে, সেখানেই আমাদের পৌঁছতে হবে আমাদের চিন্তাধারাকে পৌঁছে দেবার স্বার্থেই। পরিষ্কারভাবে মাথায় রাখতে হবে, আমরা গণমাধ্যম ও প্রচারমাধ্যমগুলোকে আন্দোলনের স্বার্থে কাজে লাগাব, কিন্তু গণমাধ্যম ও প্রচার মাধ্যমগুলো যেন হুজুর শ্রেণির স্বার্থে আমাদের কাজে না লাগাতে পারে।
যাঁরা মনে করেন বৃহৎ পত্র-পত্রিকায় না লেখাটাই বুঝি লড়াকু মানসিকতার পরিচয়, তাঁরা ভুল করেন, সাধারণ মানুষের কাছে নিজেদের বক্তব্য পৌঁছে দেবার লক্ষ্য থেকেই সরে যান। সাধারণ মানুষের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে একটি ক্ষুদ্র গোষ্ঠী মাত্র হয়ে পড়েন। সব সময় এমন চিন্তা যে ভুল ধারণা থেকে উঠে আসে, তাও নয়। অনেক তথাকথিত লড়াকু মানুষকে চিনি, যাঁরা বড় পত্রিকায় লেখা প্রকাশ করাটা প্রতিক্রিয়াশীলতার লক্ষণ বলে সোচ্চারে ঘোষণার পাশাপাশি গোপনে বড় পত্রিকায় ‘লাইন’ করার চেষ্টা করেন স্রেফ নিজের লেখা ছাপাতে। এঁদের অনেকেই নিজের বিবেক বিক্রি করছেন লেখা ছাপানোর প্রতিশ্রুতি কিনতে। যাঁদের লেখায় ধার নেই, পাঠক-পাঠিকাদের প্রথম পাতা থেকে শেষ পাতা পর্যন্ত টেনে নিয়ে যাওয়ার আকর্ষণী ক্ষমতা নেই, তাঁরা বিবেক জামিন রাখতে চাইলেও কেনার খদ্দের জোটে না। এই অক্ষমতা থেকেও অনেক সময় আসে বড় প্রচার মাধ্যমগুলোর প্রতি বৈরাগ্য। এ যেন ভিখারির বৈরাগ্য, নপুংসকের ব্রহ্মচর্য।
বড় পত্রিকায় লেখার সুযোগ পেলে আমরা নিশ্চয়ই নেব। কিন্তু তা বিবেক জামিন রেখে অবশ্যই নয়। সুযোগ নেব আমাদের দর্শন, আমাদের আদর্শকে পৌঁছে দেওয়ার স্বার্থেই। বড় পত্রিকার মধ্য দিয়ে আদর্শ প্রচারের ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধতা অবশ্যই আছে, এটুকু মাথায় রেখেই বলছি সাধারণ মানুষের ধোলাই করা মগজকে পাল্টা ধোলাই করার সামান্যতম সুযোগ ছাড়াও উচিত হবে না।
এরই পাশাপাশি আমাদের নিজস্ব লেখক তৈরি করতে, সম্পাদক তৈরি করতে স্থানীয়’ মানুষদের সঙ্গে নিবিড় যোগাযোগ বাড়াতে, স্থানীয় মানুষদের সঙ্গে ভাব বিনিময় করতে, তাঁদের ভাববাদ-বিরোধী লেখা-পত্তরের সঙ্গে পরিচিত করাতে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক সংস্থাগুলোকে এগিয়ে আসতে হবে। সাংস্কৃতিক সংস্থাগুলো আন্তরিকভাবে সচেষ্ট হলে নিশ্চয়ই তারা পারবে ভাববাদ-বিরোধী, কুসংস্কার বিরোধী বুলেটিন, পত্র-পত্রিকা, বই ইত্যাদি প্ৰকাশ করতে; তা সে যতই অকিঞ্চিৎকরই হোক না কেন, যত কৃশ কলেবরেই হোক না কেন। এখান থেকেই আমরা জ্বালাব মনুষ্য চেতনায় জ্ঞানের আলো। এখান থেকেই আমরা তৈরি করব আমাদের নিজস্ব ‘রবীন্দ্রনাথ’, আমাদের নিজস্ব ‘সত্যজিৎ’।
সাধারণ মানুষের কাছে আমাদের লেখাপত্তর, বক্তব্য, নাটক ইত্যাদিকে গ্রহণযোগ্য করতে হলে সাধারণ মানুষের সঙ্গে আমাদের কমিউনিকেশন বা যোগাযোগ বাড়াতে হলে আমাদের লেখাপত্তরকে এতটাই আকর্ষণীয় করে তুলতে হবে যাতে পাঠক-পাঠিকারা আপন তাগিদে ওইসব লেখাপত্তর পড়তে উৎসাহিত হন। যে মানুষদের সামনে পৌঁছতে চাইছি, যাদের সঙ্গে যোগাযোগ গড়ে তুলতে চাইছি, তাদের ভালোলাগা না লাগার খবরও আমাদের রাখতে হবে; বুঝতে হবে তাদের মনস্তত্ত্ব।
রাজনৈতিক স্লোগানধর্মী নাটক, গল্প, উপন্যাস মানুষকে সাধারণভাবে টানতে পারছে না। পুজো প্যান্ডেলে মার্কসবাদী সাহিত্যের স্টলে রাজনৈতিক দলের কর্মীদের ভিড় যতটা থাকে ক্রেতাদের ভিড় ততটা থাকে না। এর একটাই কারণ, সাধারণ মানুষকে এসব আকর্ষণ করতে পারছে না। এই জাতীয় অনেক বইই ভারী ভারী শব্দে এতই ভারাক্রান্ত যে সাধারণ মানুষ সভয়ে ও-সব লেখাপত্তর এড়িয়ে চলেন।
আমরা ‘ছোটি-বড়ি বাতেঁ’-এর মতন অতি সফল টি.ভি. সিরিয়াল দেখেছি, যেখানে হাঁচি কাশি টিকটিকির ডাকের মতন নানা কুসংস্কারের বিরুদ্ধে বক্তব্য এসেছে জমাটি কাহিনির সঙ্গে। আমরা ‘রজনী’ হিন্দি টি. ভি. সিরিয়ালের প্রচণ্ড জনপ্রিয়তা অর্জনের ইতিহাসও জানি। রজনীর বিপুল জনপ্রিয়তায় নায়িকা প্রিয়া তেণ্ডুলকরকে তাঁর পরিচিত মানুষরাও ডাকতে শুরু করেছিলেন ‘রজনী’ নামে। সেখানেও এসেছে বুজরুকের ভান্ডাফোড় করার কাহিনি। ‘জ্ঞান দিচ্ছে’ বলে মানুষ, মুখ ফিরিয়ে নেয়নি। গ্রহণ করেছে। বিষয়বস্তুর আকর্ষণীয়তাই এগুলোকে সাধারণের কাছে গ্রহণযোগ্য করেছে।
ঢাল তলোয়ারহীন নিধিরাম সর্দারের গল্প আমরা জানি, আমাদের ভাববাদ-বিরোধী সাংস্কৃতিক আন্দোলনকর্মীদের অবস্থাও অনেকটা ঢাল তলোয়ারহীন নিধিরাম সর্দারের মতো। আমাদের না আছে একজন মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, না একজন বিভূতি বাঁড়ুয্যে। ফলে আমাদের অনেকের হাতেই নিপীড়িত মানুষের কথা বেরিয়ে আসছে স্লোগান হয়ে। পরমান্ন রাঁধতে গিয়ে আমরা যদি লঙ্গরখানার খিচুড়ি রেঁধে বসি, তাহলে মানুষ মুখে তুলবে কেন?
শহরে গ্রামে যেদিকেই তাকান দেখতে পাবেন সিনেমা ও ভিডিওর রমরমা ব্যবসা। শহরের বস্তিবাসী থেকে গ্রামের গরিব চাষার প্রধান বিনোদন এই সিনেমা, ভিডিও। ওরা হলে এসে ভুলে যেতে চায় ওদের সমস্ত বঞ্চনার কথা, দৈনন্দিন দুঃখ-দারিদ্র্যের কথা। ওরা আসে সব কিছু ভুলে কিছুক্ষণের আনন্দে ডুবে থাকতে। হতদরিদ্র মানুষগুলোকে নিয়ে তোলা সিনেমা তাই গরিব মানুষদের তেমন টানে না।
‘রজনী’তে গরিবদের নিয়ে আকর্ষণীয় কোনও প্যানপ্যানানি ছিল না, ছিল সমাজের নানা সমস্যা এবং সেইসব সমস্যাকে এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা না করে মোকাবিলা করার শিক্ষা।
‘ছোটি বড়ি বাতেঁ’ তে পাঁজি-পুঁথি-মঘা ত্র্যহস্পর্শ-বারবেলা মান্য করা, বৃহস্পতিবার ও শনিবার ক্ষৌরকর্ম না করা, পিছু-ডাক, হাঁচি, টিকটিকির ডাক ইত্যাদি মেনে চলাকে হাসির খোরাক করা হয়েছে এবং দর্শকরা তা দারুণভাবে উপভোগ করেছে। এই সিরিয়ালের চরিত্রগুলো কিন্তু শোষিত মানুষদের প্রতিনিধিত্ব করেনি। কিন্তু সিরিয়াল থেকে উঠে এসেছিল আমাদেরই কথা। এই ধরনের কুসংস্কার মেনে চলাটা নেহাতই হাসির খোরাক হওয়া—এই প্রচার লাগাতারভাবে চালাতে পারলে এই সব কুসংস্কার না মানাটাই বহু মানুষের ‘স্ট্যাটাস সিম্বল’ হয়ে দাঁড়াত।
আমার এই বক্তব্যের মধ্যে দিয়ে গল্পে উপন্যাসে নাটকে গরিব অত্যাচারিত মানুষদের চরিত্রগুলোকে নিয়ে আসা নিয়ে সামান্যতম বিরোধিতা করছি না। এই সব চরিত্র-চিত্রণ করতে গিয়ে বিষয়বস্তু আকর্ষণ হারালে আমাদের উদ্দেশ্য সাধিত হবে না—এই সত্যটুকুর দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করাতে চাইছি শুধু। বলতে চাইছি— লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বিষয়ে স্পষ্ট ধারণা থাকলে নানা আকর্ষণীয় ভাবেই হাজির করা যেতে পারে আমাদের বক্তব্য।
২। সাধারণ মানুষের সঙ্গে কমিউনিকেশন বা যোগাযোগ গড়ে তোলার ক্ষেত্রে প্রচার ব্যবস্থার গুরুত্ব অপরিসীম। আমাদের দেশের জনসমষ্টির সিংহভাগই বই পড়ার মতো লেখা-পড়ার সুযোগলাভে অক্ষম। এদের কাছে আমরা আমাদের লেখাপত্তর নিয়ে হাজির হতে পারব না। আমরা সাধারণ মানুষের চেতনাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য শুধুমাত্র আমাদের লেখাপত্তরের ওপর নির্ভর করলে দেশের বৃহত্তম জনসমষ্টি পিছিয়েই থেকে যাবে। সাধারণ মানুষের সঙ্গে যোগাযোগ গড়ে তুলে আদর্শ প্রচারের ক্ষেত্রে আমরা কাজে লাগাতে পারি নাটক, যাত্রা, গান, এবং ‘অলৌকিক নয়, লৌকিক’ শিরোনামে বিভিন্ন অলৌকিক ক্ষমতার রহস্য ফাঁস করে।
আমরা সকলের কাছেই হাজির হব। যেখানেই মানুষ সেখানেই হাজির হব। যে সংস্থাই আমন্ত্রণ জানাক, আমরা যাব—তা সে দক্ষিণ, অতিদক্ষিণ, বাম, অতিবাম—যেই ডাকুক না কেন। যুক্তিবাদ প্রসারে ব্রতী সংস্থাগুলোর একটি জরুরি কাজ হবে তাদের এলাকার বিভিন্ন স্কুল, কলেজ ও ক্লাবগুলোর সঙ্গে যোগাযোগ করে তাদের সহায়তায় নানা অনুষ্ঠানের আয়োজন করে জন-চেতনাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করা এবং একই সঙ্গে এই আন্দোলনকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য আরও নতুন নতুন মানুষকে এই আন্দোলনের শরিক করা, দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ করা।
৩। ভাববাদী বইপত্তরের তুলনায় ভাববাদ-বিরোধী বা যুক্তিবাদী বইপত্তরের সংখ্যা অতি নগণ্য। ভাববাদী মানসিকতা ঠেকাতে ও যুক্তিবাদী চেতনা বাড়াতে সাধারণ মানুষের মধ্যে হাজির করতে হবে যত বেশি করে সম্ভব যুক্তিবাদী বইপত্তর। এই দায়িত্ব পালন করতে হবে আপনাকে আমাকে প্রতিটি দেশপ্রেমিককে। আসুন আমরা আজই কেন প্রতিজ্ঞা করি না— শোষণমুক্ত সমাজ গড়তে যে সংস্কার-মুক্তির প্রয়োজন তারই স্বার্থে আমরা বেঁচে থাকার জন্যেই প্রয়োজন ভেবে সংস্কার-মুক্তির বই কিনব, বই পড়াব, বই পড়ব, এবং বই উপহার দেব।
৪। যুক্তিবাদী আন্দোলনে শামিল সংস্থা ও গণসংগঠনগুলোর একান্ত কর্তব্য হওয়া উচিত কর্মীদের তৈরি করে তোলার জন্য নিরন্তর ‘স্টাডি ক্লাস’ করা। কীভাবে স্টাডি ক্লাসগুলো চালাতে হবে, এই নিয়ে ‘অলৌকিক নয়, লৌকিক’ দ্বিতীয় খণ্ডে আলোচনা করেছি বলে আবার বিস্তৃত আলোচনায় গেলাম না।
৫। কোনও সাংস্কৃতিক বা যুক্তিবাদী সংস্থা কোনও ধরনের কঠিন সমস্যার মুখোমুখি হলে বা কোনওভাবে আক্রান্ত হলে তাঁরা সমমনোভাবাপন্ন মানুষ ও সংস্থাগুলোর সঙ্গে দ্রুত যোগাযোগ করে তাদের পরামর্শ, সাহায্য ও সহযোগিতা গ্রহণ করুন। একইভাবে কোনও আক্রান্ত সংস্থা যোগাযোগ করলে সমস্ত রকমভাবে আপনারা প্রত্যেকে তাদের পাশে দাঁড়িয়ে লড়াই-এ জয় ছিনিয়ে নিয়ে আসুন। যদি সংস্কারের শেকল ভাঙতে গিয়ে আক্রান্ত হন— অঙ্গীকারবদ্ধ রইলাম আমাদের সমিতি তার সমস্ত শাখা সংগঠন ও সহযোগী সংস্থাকে সঙ্গে নিয়ে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে লড়বে।
৬। গণ-সংগঠনগুলোর কর্মীদের এমনভাবে তৈরি করতে হবে, এবং এমন প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে এগুতে হবে যাতে নেতৃত্বের চ্যুতি, ভ্ৰান্তি বা বিপথগামিতার ক্ষেত্রে সদস্যরা নেতাদের সমালোচনা করতে পিছু-পা না হয় ৷
৭। সমালোচনা যিনিই করবেন তাঁকে অবশ্যই সতর্ক থাকতে হবে সমালোচনার লক্ষ্য যেন হয় সংগঠনের উন্নতি এবং আন্দোলনের শ্রীবৃদ্ধি।
সমালোচনা হবে খোলাখুলি এবং অবশ্যই সংগঠনের মধ্যে। কোনও বিষয়ে আলোচনায় মতপার্থক্য অবশ্যই থাকতে পারে। শেষ পর্যন্ত সংগঠনের সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যদের মতামতই প্রত্যেককে মেনে চলতে হবে সংগঠনের স্বার্থে। সংগঠনে সিদ্ধান্ত গ্রহণের আগেই শুধু নিজস্ব মতামত থাকতে পারে। কিন্তু সিদ্ধান্ত গৃহীত হওয়ার পর সংগঠনের বাইরে কেউ এই বিষয়ে সমালোচনা করলে সেটা সংগঠন-বিরোধী কাজ হিসেবেই বিবেচিত হওয়া উচিত। সংগঠনের বাইরে সমালোচনাকারীকে প্রয়োজনে সংগঠনের স্বার্থেই সংগঠন থেকে বের করে দিতে হবে, তা সেই সমালোচক সংগঠনের যত উচ্চ-পদাধিকারীই হোন না কেন।
মধ্যবিত্তসুলভ মানসিকতার দরুন অনেক সময়ই সমালোচনা হয়ে পড়ে দায়িত্বজ্ঞানহীন, কখনও সমালোচনা উঠে আসে ব্যক্তিত্বের সংঘাত থেকে, কখনও ঈর্ষাপরায়ণতা থেকে। সমালোচনা হওয়া উচিত সংগঠনের স্বার্থে ইতিবাচক। শুধুমাত্র নেতিবাচক বা নাকচ করে দেবার সমালোচনা অর্থহীন হয়ে পড়ে, যদি না পরিবর্ত পথনির্দেশ দেওয়া হয়। দায়িত্বজ্ঞানহীন সমালোচনা সংস্থায় বিশৃঙ্খলাই শুধু টেনে আনতে পারে।
৮। উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য বিষয়ে স্পষ্ট ধারণা থাকলে কোনও শক্তির সাধ্য নেই মগজ ধোলাই করে বিপথে চালিত করে। সংগঠনের প্রয়োজনেই নেতৃত্বের অবশ্য কর্তব্য আন্দোলনকর্মীদের ধাপে ধাপে শিক্ষিত, নিবেদিত প্রাণ করে তুলে প্রত্যেককে এক একজন সংগঠক, সংগ্রামী করে তুলে তাঁদের দৃঢ় মতাদর্শগত ভিতের ওপর দাঁড় করিয়ে দেওয়া। মতাদর্শগত ভিতই উদ্দেশ্য এবং লক্ষ্যের দিকে আন্দোলনকর্মীদের চালিত করবে।
৯। সংগঠন যাঁদের নিয়ে গড়ে উঠবে তাঁরাই সংগঠনকর্মী বা আন্দোলনকর্মী। আর নেতা তিনি, যিনি নিজে যে কোনও ঘটনার চুলচেরা বিশ্লেষণ করতে পারেন এবং আন্দোলনকর্মীদের বিশ্লেষণ-পরবর্তী করণীয় বিষয়ে সঠিক নির্দেশ দিতে সক্ষম। এরই পাশাপাশি নেতাকে হতে হবে সৎ, আবেগহীন, আত্মবিশ্বাসী, বিনয়ী, জনসাধারণের সঙ্গে আন্তরিকভাবে মিশতে সক্ষম, আন্দোলনের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য বিষয়ে সচেতন ও কৌশলগত দিক বিষয়ে ওয়াকিবহাল।
ভারী ভারী নাম বা বড় বড় ডিগ্রি দেখে নেতা বাছবেন না। নেতা বাছুন কাজের মানুষ বিচার করে। যে যত বেশি দায়িত্ব পালনে এগিয়ে আসবে, যত বেশি আন্তরিক হবে, ততই সে অভিজ্ঞতা অর্জনের মধ্যে দিয়েই নেতৃত্বের গুণগুলোকে অতি স্বাভাবিকভাবেই অর্জন করে নেবে।
১০। আন্দোলনকর্মীদের মধ্যে অনেক সময়ই এই জিজ্ঞাসা দেখা দিতে পারে— আমাদের আন্দোলনকে আঘাত করতে যদি রাষ্ট্রশক্তিই হাজির হয়, তবে কি আমরা আন্দোলনকে শেষ জয় এনে দিতে পারব? অথবা কখনও যদি এমন প্রশ্ন হাজির হয়, গোটা ভারত বা গোটা পৃথিবীর মানুষ কুসংস্কারমুক্ত হয়ে তাদের শোষণের পদ্ধতিগুলো ধরে ফেলে বর্তমান সমাজ-কাঠামোই পাল্টে দিতে লড়াইয়ে শামিল হবে, অধিকার ছিনিয়ে নিতে সোচ্চার হবে— এ এক অবাস্তব কল্পনা নয় তো? তখন প্রশ্নকর্তাদের দৃষ্টির কুয়াশা কাটিয়ে আলো দেখাতে দৃষ্টান্ত হিসেবে তুলে ধরুন আমাদেরই দেশের বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর সংগ্রামী ইতিহাস। বুঝিয়ে দিন আন্দোলনের শরিক যেখানে কোনও জনগোষ্ঠীর বৃহত্তর অংশ, সেখানে আন্দোলন শেষ করার সাধ্য পৃথিবীর কোনও রাষ্ট্রশক্তিরই নেই। একটি অঞ্চলের জনগোষ্ঠীকে যুক্তিবাদী চেতনার আলোকে আলোকিত করা নিশ্চয়ই অসম্ভব কোনও কাজ নয়। কর্মীদের উদ্বুদ্ধ করুন, আন্দোলনকর্মীরা উদ্দীপ্ত হলে জনগণকে সচেতন করা, সংগঠিত করার কাজটা অতি সহজ হয়ে যায়।
১১। সাধারণভাবে ‘ধর্ম’, ‘ধর্মনিরপেক্ষতা’, ‘দেশপ্রেম’, ‘বিচ্ছিন্নতাবাদ’, ‘জাতীয়তাবাদ’ ইত্যাদি বিষয়ে যেসব ধ্যান ধারণা শোষকশ্রেণি তাদের তাঁবেদার রাজনীতিক, বুদ্ধিজীবী ও প্রচার মাধ্যমগুলোর সাহায্যে প্রচার করে চলেছে, সেগুলোর বিরুদ্ধে পাল্টা যুক্তি হাজির করুন। ওদের যুক্তিকে সুযোগ পেলেই আক্রমণ চালিয়ে সাধারণ মানুষের কাছে সঠিক চিন্তাগুলো পৌঁছে দেবার চেষ্টা করুন। এতদিনকার কুযুক্তির বিরুদ্ধে কোনও সুযুক্তি হাজির হয়নি বলেই সাধারণ মানুষ মগজ ধোলাইয়ের শিকার হয়েছেন। সুযুক্তি পেলে সাধারণ মানুষ তা অবশ্যই গ্রহণ করেন, আমাদের সমিতির অভিজ্ঞতা তাই বলে।
১২। শুধু নাকচ বা বর্জনের ওপর কোনও কিছুর স্থায়ী ভিত গড়ে উঠতে পারে না। বর্তমান সমাজের নেতিবাচক দিকগুলোর নিশ্চয়ই সমালোচনা করতে হবে, এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে হবে, জনমত গড়তে হবে। আমাদের সমিতির অভিজ্ঞতা তাই বলে।
আমাদের অশ্রদ্ধা পুরনো সবকিছুর প্রতি নয়, অশ্রদ্ধা
যুক্তিহীনতার প্রতি। আমাদের শ্রদ্ধা যা
নতুন তার প্রতি নয়, আমাদের
শ্রদ্ধা যুক্তির প্রতি।
১৩। যুক্তিবাদী আন্দোলন সঠিক পথে চললে যাদের স্বার্থে এই আন্দোলন আঘাত করবে তারা হাত গুটিয়ে বসে থাকবে না। তারা প্রত্যাঘাত হানবেই। এই প্রত্যাঘাত রোখার সবচেয়ে বড় শক্তি মানুষ। তারই পাশাপাশি একথাও মনে রাখতে হবে সংগঠন যদি বাস্তবিকই সংগ্রামী মানুষদের নেতৃত্ব দিতে তবে সেই সংগঠনের অনেক কিছুর ক্ষেত্রে অবশ্যই গোপনীয়তা রক্ষা করতে হবে।
গোপন সংগঠন সম্পর্কে একটা অদ্ভুত ধারণা সাধারণের মধ্যে প্রচলিত রয়েছে। অনেকেই মনে করেন সংগঠনের কয়েকজন নেতা আত্মগোপন করলেই বুঝি ‘গোপন সংগঠন’ হয়। গোপন সংগঠন চোরের মতো লুকিয়ে লুকিয়েও করতে হয় না। সংগঠনের গোপনীয়তা রক্ষার জন্য এসব কোনও কিছুরই প্রয়োজন হয় না। বরং সাধারণভাবে আন্দোলনে নেতৃত্বদানকারীরা আত্মগোপন করলে সাধারণ কর্মীদের থেকে তাঁরা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েন।
সাধারণ মানুষের সঙ্গে মিশে গিয়ে শ্রমিক, কৃষক, বুদ্ধিজীবী, সাংবাদিক সাহিত্যিক ইত্যাদি বহু পেশার মানুষের সঙ্গে যোগাযোগ গড়ে তুলতে হবে । এর জন্য একদল কর্মী তৈরি করতে হবে। এঁরা বিভিন্ন পেশার মানুষ হতে পারেন, এঁদের আদর্শে উদ্বুদ্ধ করতে পারলে প্রতিটি লড়াইয়ে জনসমর্থন পাওয়া সহজতর হবে।
১৪। গণ-সংগঠনসর্বস্ব আন্দোলনের ক্ষেত্রের যে-সব অসুবিধে দেখা দিতে পারে, সেগুলো নিয়েও অবশ্যই সচেতন থাকা প্রয়োজনঃ
ক) আন্দোলন তীব্রতর হলে শোষক ও শাসকশ্রেণি সমস্ত গণ-সংগঠনগুলোকেই চরবৃত্তির কাজে লাগাতে চেষ্টা করে। গণ-সংগঠন নেতাদের লোভ, ভয়, ইত্যাদির দ্বারা কিনে ফেলার চেষ্টা চলে।
খ) গণ-সংগঠনের অনেক নেতৃত্বই কম ত্যাগ ও কম ঝুঁকি নিয়ে বেশি রকম আত্মপ্রচারে উৎসাহী হয়ে পড়ে।
গ) সরকারি-বেসরকারি সাহায্য ও প্রচারের মোহে বাঁধা পড়ে অনেক নেতৃত্বই কথায় ও কাজে দুই মেরুতে অবস্থান করতে শুরু করেন। নেতা বিক্রি হয়ে যাওয়ায় সংগঠন ভুল পথে চালিত হতে থাকে, প্রকৃত আন্দোলনের শত্রুতা করতে থাকে।
ঘ) গণ-সংগঠনের নেতারা অনেক সময় যুক্তিবাদী আন্দোলনের আদর্শগত দিকটা আন্তরিকতার সঙ্গে গ্রহণ না করে কিছুটা হুজুগে আন্দোলনে ঢুকে যা খুশি তাই করে ফেলতে পারে।
১৫। আন্দোলনে শামিল সমমনোভাবাপন্ন সাংস্কৃতিক সংগঠন, বিজ্ঞান ক্লাব, যুক্তিবাদী আন্দোলনে শামিল সংস্থাগুলোর উচিত নিজেদের মধ্যে সমন্বয় গড়ে তোলা। সংগঠনগুলোর মধ্যে সমন্বয় সাধিত হলে প্রতিটি আক্রমণের, প্রতিটি সমস্যার, মোকাবিলায় সমস্ত সংগঠন একত্রিত হতে পারবে অতি দ্রুত। সকলে কাঁধে-কাঁধ মিলিয়ে লড়লে লড়াই জেতা, সমস্যা ডিঙিয়ে যাওয়া সহজতর হয়।
ভারতীয় বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী সমিতি বহু সংগঠনের সমন্বয়কারীর ভূমিকা পালন করে আসছে। আরও বেশি বেশি করে সংগঠন এগিয়ে এলে প্রত্যেকের কাছেই উদ্দেশ্য পৌঁছনো সহজতর হবে।
কোনও সংগঠনের স্বাধীনতায় হাত না দিয়েই যুক্তিবাদ প্রসার, কুসংস্কারমুক্তি, মানবাধিকার, মরণোত্তর দেহদান, স্বাক্ষরদান, প্রগতিশীল নাটক, গান এবং আরও কিছু ‘কমন’ কর্মসূচির ভিত্তিতে আমরা একত্রিত হয়েছি। আমাদের সম্মিলিত ও পরিকল্পিত প্রয়াসই এমন একটা আন্দোলন গড়ে তুলতে পারে, যাতে বর্তমান সমাজের মূল কাঠামোই আন্দোলিত হতে পারে, নাড়া খেতে পারে। আর তারপর—আন্দোলনে শামিল জনগণই সৃষ্টি করবে এক নতুন ইতিহাস, জাগরণের ইতিহাস।
১৬। যুক্তিবাদী আন্দোলনকে জোরদার করতে আসুন না কেন, প্রতিটি যুক্তিবাদী আন্দোলন প্রসারকামী মানুষ ও সংস্থা বছরের একটি দিনকে, ১ মার্চ দিনটিকে ‘যুক্তিবাদী দিবস’ হিসেবে পালন করে যুক্তিবাদী আন্দোলনে নতুন মাত্রা যুক্ত করি। এই দিনটিতে আমরা প্রত্যেকে অন্তত সংস্কার মুক্তির সহায়ক, যুক্তিনির্ভর কিছু লিখি, কিছু পড়ি, অথবা কিছু আলোচনা করি। সাংস্কৃতিক আন্দোলনে অগ্রণী সংস্থাগুলো ১ মার্চ দিনটি ‘যুক্তিবাদী দিবস’ হিসেবে পালনে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। আপনি আমিই পারি ১ মার্চকে আক্ষরিক অর্থে ‘আন্তর্জাতিক যুক্তিবাদী দিবস’ করে তুলতে।
আন্দোলনে জোয়ার আনতে আন্দোলনকর্মীদের এইসব বিষয়ে সচেতনতা ও আন্তরিকতার কোনও বিকল্প নেই ।
ভাঙা ও গড়াঃ এই খেলা ভাঙার খেলা শুধু নয়
মানুষ সামাজিক জীব। বহু মানুষকে নিয়েই একসঙ্গে চলতে হয় প্রতিটি সুস্থ-স্বাভাবিক মানুষকে। এই একসঙ্গে চলার প্রয়োজনেই গড়ে উঠেছে নানা নিয়ম-নীতি-আইন। এই গড়া কখনওই শুধু ‘নির্মাণ’ নয়। অনেক-ভাঙা-গড়ার মধ্য দিয়েই বর্তমান অবস্থায় পৌঁছনো।
মানবসভ্যতার ইতিহাসের দিকে সতর্ক নজর দিলে দেখতে পাব অতীতে সমাজের নিয়ম-নীতি-আইন তৈরি করেছে গোষ্ঠীপতি, রাজা, শাসককুল। গোষ্ঠীপতি, রাজা ও শাসককুল শুধু শাসনই চালাত না, বিশেষ সুবিধাভোগী শ্রেণির মানুষ হয়ে উঠে শোষণও চালিয়েছে। এই শোষণ প্রক্রিয়ায় তাদের সহযোগীর অভাব হয়নি। অর্থ ও ক্ষমতার লোভে এরা শাসকদের চাটুকারে পরিণত হয়েছে, শাসকদের সঙ্গে মিলে- জুলে শোষণ চালিয়েছে। এ-ভাবে এক সময় সমাজ দুটি শ্রেণিতে বিভক্ত হয়ে পড়েছে-শোষক ও শোষিত। এই শ্রেণিবিভক্ত সমাজে শোষক ও শাসক মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে। কখনও শোষকরা তাদের পুঁজিকে কাজে লাগিয়ে শাসন ক্ষমতায় বসিয়েছে এমন মানুষদের, যারা শোষকদের স্বার্থ রক্ষা করবে। কখনও বা শাসকগোষ্ঠীর সঙ্গে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়ে উভয়ে উভয়ের স্বার্থ রক্ষাকারীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছে। ফলে এই শ্রেণিবিভক্ত সমাজে শাসকশ্রেণি ও শোষকশ্রেণির স্বার্থরক্ষার জন্য বহু নিয়ম-নীতি-আইন সমাজের উপর চাপিয়ে দিয়েছে। ফলে অনেক নিয়ম-নীতি-আইনই শৃঙ্খলভার হয়ে চেপে বসেছে শোষিত শ্রেণির উপর। এই শৃঙ্খলভার মুক্ত হতে ব্যক্তিগতভাবে কেউ নিয়ম-নীতি-আইনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতেই পারে, প্রতিবাদ করার অধিকার তার নিশ্চয়ই আছে। এই প্রতিবাদই সার্থক রূপ পেতে পারে, সমাজ অগ্রবর্তীর ক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা নিতে পারে, যদি প্রতিবাদী পরিবর্ত কোনও সুন্দর নিয়ম-নীতি-আইনের হদিশ দিতে পারে এবং তার প্রতি জনসমর্থন ব্যাপকতা পেতে থাকে। এ-ভাবে পুরোনো আইন ভেঙে নতুন আইন হয়েছে— এমন দৃষ্টান্ত কম নেই।
আমরা যখন নিয়ম ভাঙার নেশায় মাতি তখন সমাজের নিয়মের উপর মানুষের প্রতিভার দ্বান্দ্বিক প্রয়োগ থেকেই ঘটে অগ্রগতি। আবার প্রকৃতির উপর মানুষের প্রতিভার দ্বান্দ্বিক প্রয়োগ থেকেই ঘটে বৈজ্ঞানিক অগ্রগতি। আর একটু ব্যাখ্যা করে বলতে পারি মানুষ এক সময় প্রকৃতির নিয়মকে ভেঙে নিজেদের প্রয়োজনে ব্যবহার করতে চেয়েছে। প্রকৃতির অস্ত্র দিয়েই প্রকৃতির নিয়মকে ভাঙতে চেয়েছে। নিজের প্রজ্ঞা দিয়ে প্রকৃতির নিয়মকে ভাঙতে চেয়েছে। এই ভাঙার প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়েই বিজ্ঞান এগিয়েছে, প্রজ্ঞা এগিয়েছে, মানুষ এগিয়েছে। এই ভাঙা-গড়ার সংগ্রামে সুফলের সঙ্গে কুফলও এসেছে কখনও কখনও। মানুষ এ নিয়ে চিন্তা করেছে প্রকৃতির পরিবর্তন এতদূর ঘটানো ঠিক হয়েছে কি না, এখানেই নতুন করে ভাবনা-চিন্তার জন্য বিশ্রাম নেবে কি না, অথবা ছেদ টানবে কি না। এ জিজ্ঞাসা থেকে, এ দ্বন্দ্ব থেকে গতিশীল মানুষের মুক্তি নেই। একই ভাবে সমাজের নানা নিয়ম নানা ছক পাল্টে দিয়ে নতুন নিয়ম নতুন ছক গড়ার চেষ্টাতেও সমান সচেষ্ট মানুষ। সমাজ তাই নিয়ত গতিশীল। সে গতিশীলতা কোন্ গোষ্ঠীর পক্ষে সুফল ও কোন্ গোষ্ঠীর কুফল কখন বয়ে আনবে সে কথা স্বতন্ত্র। কিন্তু সমাজবিন্যাস পাল্টায়, ইতিহাস এগোয়—এ চূড়ান্ত সত্য। শোষক ও শোষিত উভয়েই নিয়ম-নীতি-আইন ভাঙা-গড়ার খেলায় মাতে। কেউ জেতে কেউ হারে। কেউ এগোয়, কেউ পিছোয়। মানুষ অনেক সময়ই নিয়ম ভাঙে সুন্দর নিয়ম গড়ার স্বপ্ন নিয়ে। মানুষেরই তৈরি সমাজের নিয়মকে মানুষের অগ্রগমনের স্বার্থে ভাঙার, পাল্টে দেবার অধিকার ও ক্ষমতা মানুষেরই আছে। কিন্তু ভাঙার পর যা গড়ে উঠবে বা পড়ে থাকবে, তা সুন্দর কি অসুন্দর হবে সেটা নির্ভর করবে বিদ্রোহী বা বিপ্লবী মানুষদের দক্ষতা- শৃঙ্খলাবোধ বা অদক্ষতা-উচ্ছৃঙ্খলার উপর, দর্শনের উপর ।
আমাদের এই সমাজ ব্যবস্থায় এমন অনেক রীতি-নীতি-নিয়মশৃঙ্খলা রয়েছে যার সুযোগ নিয়ে দেশের পুলিশরা আজ সবচেয়ে সংগঠিত মস্তান বাহিনী, রাজনীতিকরা ‘অসৎ’-এর সমার্থক শব্দ, দুর্নীতি আজ সর্বগ্রাসী, ন্যায়হীনতা ও মূল্যবোধের অবক্ষয় সমাজে একগাদা কাদা-নরম-মেরুদণ্ডী প্রাণী সৃষ্টিতে তৎপর। এমন এক সুষমাহীন সমাজে কিছু মানুষ গ্লানির শিকার। কিছু মানুষ বিদ্রোহের আগুন জ্বালে, কিছু মানুষ রক্তপাত, আত্মত্যাগ ও দাঁতে দাঁত চেপে লড়াই চালাতে চালাতে অপেক্ষায় থাকে ক্রান্তির মুহূর্তের। এই ক্রান্তি আসতে পারে কিছু শর্ত পূরণের পথ ধরেই। এই শর্ত পূরণের জন্যেও প্রয়োজন কিছু নিয়ম-নীতির—হোক না সে নতুন নিয়ম-নীতি। এই নিয়ম-নীতি ও শৃঙ্খলার অভাব হলে ক্রান্তির প্রস্তুতি হবে ব্যর্থ। আবার আর এক দিক থেকে এও সত্য—নতুন নিয়ম-নীতি গড়তে গেলে পুরোনো নিয়ম-নীতি ভাঙতেই হয়।
গড়ার নিয়ম জানা না থাকলে শুধু ভাঙার খেলা খেলে
কখনওই কোনও আন্দোলন, কোনও সমাজ
অগ্রগতি ধরে রাখা সম্ভব নয়।
এই বক্তব্যের সমর্থনে বহু দৃষ্টান্ত ছড়িয়ে রয়েছে ইতিহাসের পাতায় পাতায়। বহু থেকে একটিকে বেছে নিতে আমরা আমাদের দেশের সত্তর দশকের ইতিহাসের দিকে নজর দিতে পারি। ইন্দিরা গান্ধি জরুরি অবস্থা জারি করে চরম স্বৈরাচারিতা চালিয়ে যাচ্ছেন তখন। ইন্দিরা গান্ধির অপশাসনের বিরুদ্ধে সংগঠিত হয়েছে জনতা পার্টি। জনতা পার্টির নেতৃত্বে গড়ে ওঠা আন্দোলনের আলোতে ইন্দিরা গান্ধির অন্ধকারময় দিকগুলোর কথা জনতার কাছে উদ্ভাসিত হতে লাগল। পরিণতিতে যা ঘটল তাকে অবশ্যই বলতে হয়-ইন্দিরা গান্ধিকে ক্ষমতায় ফিরতে না দেবার জন্য তীব্র গণ-প্রতিরোধ । পুলিশ, মিলিটারি ও গুন্ডাবাহিনী দিয়ে বুথ দখল করে ‘নির্বাচন’ নামক প্ৰহসন চালাতে গিয়ে বিপুল জন-প্রতিরোধে সে প্রহসন ফুৎকারে ছত্রখান্ হয়ে গেল। অসম্ভব জেদি এক জন-প্রতিরোধের মুখে ইন্দিরার দিল্লির তখতে বসার স্বপ্ন অধরাই থেকে গেল। লোক সভায় এমন বিপুল সংখ্যাধিক্যতার কথা দিবাস্বপ্নেও ভাবেনি জনতা পার্টি। কিন্তু ইন্দিরা গান্ধির অন্ধকারময় রাজনীতিতে ভাঙন ধরিয়ে কী গড়তে পেরেছিল সে দিনের জনতা সরকার? কিছু নয়। ওরা ভাঙার নিয়মটাই শুধু জানত। গড়ার নিয়ম ছিল অজানা। ফলে জনতা পার্টির ইন্দিরা বিরোধী জঙ্গি কথা-বার্তায় মুগ্ধ জনগণ যে রঙিন স্বপ্ন দেখতে শুরু করেছিল জনতা পার্টি ঘিরে সে স্বপ্নের রং দ্রুত ফিকে হয়ে গিয়েছিল জনতা সরকারের গঠনমূলক কাজকর্মের অভাবে।
পৃথিবীর ইতিহাসে এমন দৃষ্টান্ত অবিরল ধারায় স্থাপিত হয়েই চলেছে যেখানে বিরোধী দল সরকারের বিরুদ্ধে নেতিবাচক সমালোচনার ঝড় তুলে ক্ষমতা দখল করেছে। কিন্তু তারা ইতিবাচক কিছু করার অক্ষমতায় জনতার ভালোবাসা থেকে নির্বাসিত হয়েছে।
জনগণের মনে স্থায়ী শ্রদ্ধার ছাপ ফেলতে হলে, সমাজের সর্বক্ষেত্রে ভাঙা-গড়ার মধ্য দিয়ে অগ্রগামিতা বজায় রাখতে হলে ভাঙার বিশৃঙ্খলার পর গড়ার শৃঙ্খলার প্রয়োজন, শিক্ষাক্ষেত্রে-কর্মক্ষেত্রে-লেখায়-রেখায়-বিপ্লবে সর্বত্র প্রয়োজন। অ্যাবস্ট্রাক্ট বা বিমূর্ত ছবি আঁকিয়ে হতে গেলে ‘রিয়ালিস্টিক’ ছবি আঁকায় সিদ্ধহস্ত হতে হয়।
এই প্রসঙ্গে এক পত্র- লেখকের কথা মনে পড়ছে, যিনি বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদকে ভিত্তি করে অবিরল ধারায় সুতীক্ষ্ণ আক্ৰমণ চালিয়েই চলেছেন। ওঁর শাণিত আক্রমণগুলো নেমে এসেছে রাজনৈতিক দল, রাজনীতিক, অভিনেতা, গায়ক, নাট্যকার, চিত্র-পরিচালক, বিজ্ঞানী, চিকিৎসক, লেখক ইত্যাদি বিভিন্ন ও বিচিত্র পেশার সঙ্গে যুক্ত মানুষ ও সংস্থার উপর । এইসব প্রকাশিত পত্রের অসাধারণ শ্লেষাত্মক ভাষা ও যুক্তির অবতারণায় তিনি বহু পাঠক-পাঠিকার কাছেই আজ প্রজ্ঞার প্রতীক। ঝড় তোলা এইসব চিঠি-পত্ৰ পড়ে একাধিক পত্র-পত্রিকা তাঁকে দিয়ে প্রবন্ধ লেখাতে উৎসাহিত হয়েছে। সম্পাদকের অনুরোধকে সম্মান জানাতে লিখতে বসে কখনও অনেক পৃষ্ঠা ও সময় নষ্টের পর ওই পত্র-লেখক সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন- বিষয়টি নিয়ে প্রবন্ধ লিখতে যে ইতিবাচক স্বচ্ছ দৃষ্টিভঙ্গির প্রয়োজন, লেখায় সেই ঘাটতি অতিমাত্রায় প্রকট হয়ে উঠেছে। কখনও বা লেখা সম্পাদকের হাতে তুলে দেবার পর সম্পাদকই বাতিল করেছেন ইতিবাচক সারবস্তুর অভাবে। নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে কোনও কিছুর বিরুদ্ধে সমালোচনার ঝড় তুলে বহু মানুষকেই হয়তো আবেগতাড়িত করা সম্ভব, কিন্তু ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গির অভাব থাকলে সেই আবেগকে সমাজের অগ্রগতির পক্ষে গতিশীল করা অসম্ভব।
সাধারণ মানুষের মধ্যে সমাজ সচেতনতা গড়ার প্রয়োজনে সমাজের পচন-ধরা বহুতর দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করতে কোনও ব্যক্তি বা গোষ্ঠী যখন সচেষ্ট হন তখন সচেতনতার আলোয় সদ্য উদ্ভাসিত মানুষগুলো তাঁদের চিন্তা-চেতনার মধ্যে ভাঙা-গড়ার খেলা চালিয়ে নিজেরাই গড়ে তুলতে থাকে শোষকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের ব্যূহ—আক্রমণ হানার কৌশল—এ কথা আমরা শিখেছি ইতিহাস থেকে।
কিন্তু এ কথাও আমরা ইতিহাস থেকেই শিখেছি—জনগণ তীব্র
শোষণের শিকার হলেও নেতৃত্বের ইতিবাচক ভূমিকার
অভাবে বহু আদর্শে উদ্বুদ্ধ মানুষের প্রাণদান
সত্ত্বেও একটা সংগ্রাম কী ভাবে
ব্যর্থ হয়ে যায়।
কমিউনিস্ট পার্টিগুলো-সহ সবকটি বামপন্থী দল রাজ্যস্তরে শাসন ক্ষমতা দখল করার পর স্লোগান তুলেছিল-সীমিত রাষ্ট্রক্ষমতা কাজে লাগানো হবে সমাজতান্ত্রিক আন্দোলন গড়ে তোলার স্বার্থে। দীর্ঘদিনের প্রচলিত চিন্তার রাজ্যের ভিত্তিভূমিতে আঘাত করে সব কিছু ওলট-পালট করে দিয়ে ষাটের দশকে শুরু হল নকশালবাড়ির কৃষক সংগ্রাম। রাজনৈতিক দিক থেকে শুধু নয়, ভারতীয় সমাজ জীবনকেও এই সংগ্রাম প্রভাবিত করেছিল। উজ্জীবিত করেছিল অনেক আদর্শবাদী তরুণ-তরুণীকে ও নিপীড়িত বহু মানুষকে। নকশালবাড়ি আন্দোলনের নেতৃত্ব স্পষ্ট ঘোষণায় জানাল, ক্ষমতাসীন কমিউনিস্ট দলগুলোর প্রগতিশীল মুখোশের আড়ালে রয়েছে বিপ্লব বিমুখ, মধ্যবিত্ততার গ্লানিতে আচ্ছন্ন মুখের সারি। ঘোষিত হল মেকি বামপন্থীর বিরুদ্ধে, রাষ্ট্রশক্তির বিরুদ্ধে সংগ্রাম, রক্তাক্ত সংগ্রাম। আছড়ে পড়ল এক অভাবনীয় ভাঙার প্রক্রিয়ার ঢেউ। বিপ্লবকে ত্বরান্বিত করতে শাসক ও শোষকদের স্বার্থরক্ষাকারী প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থাকে ভেঙে ফেলার ডাক দেওয়া হল। না ভেঙে তৈরি করা যাবে না নিপীড়িত মানুষদের স্বার্থে, শ্রেণিহীন সমাজের স্বার্থে বৈপ্লবিক নতুন শিক্ষাধারা—এই ঘোষণাকে সামনে রেখে আঘাত হানা শুরু হল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোতে। কিন্তু শুধুমাত্র শিক্ষাব্যবস্থাকে ভেঙে চুরমার করে দিলেই তো চলবে না, পরিবর্তে কেমন ধাঁচের শিক্ষাব্যবস্থা কী ভাবে গড়ে তোলা হবে— এই সরল প্রশ্নটির কোনও উত্তর পেল না সাধারণ মানুষ।
আমাদের সাংস্কৃতিক চেতনাকে প্রভাবিত করতে শাসকশ্রেণি ও শোষকশ্রেণি যাদের কর্মকাণ্ডকে মহান বলে প্রচার চালিয়েই চলেছে নিজেদের স্বার্থে, সেই হুজুরের চাপানো সংস্কৃতির পরিবর্তে মজুরদের সংস্কৃতি সমাজে প্রতিষ্ঠিত করতে হলে হুজুরদের চাপানো সংস্কৃতিতে ভাঙন ধরাতেই হবে। এ যেন জঙ্গলে বাঘের মুখোমুখি হওয়া। হয় বাঘ আমাকে খাবে, নতুবা আমি বাঘকে। একজনের মৃত্যুর মধ্যেই রয়েছে অন্যজনের জীবন । শাসকশ্রেণি যাঁদের মহান মনীষী বলে প্রতিষ্ঠা করতে চাইছে সেই সব মনীষীদের সীমাবদ্ধতা, যুক্তিহীনতা, প্রতিক্রিয়াশীলতা কোথায়, এই বিষয়ে জনসাধারণকে বোঝাবার চেষ্টা না করে, বিকল্প হিসেবে সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে কারা সাধারণের কাছে শ্রদ্ধেয় হবেন এই বিষয়ে কোনও মতামত গড়ে তোলার চেষ্টা না করে আন্দোলনকারীরা রামমোহন-বিদ্যাসাগর-রবীন্দ্রনাথের যে মূর্তিভাঙার আন্দোলন শুরু করেছিলেন, তা মানুষ ভালো চোখে দেখেনি। হাটে-মাঠে- কারখানায় সর্বত্রই যে নিয়ম ভাঙার ঢেউ আছড়ে পড়েছিল, তাতে পরিবর্ত গড়ার দিশার অভাব ছিল। স্বভাবতই আর প্রতিটি নেতিবাচক আন্দোলনের ক্ষেত্রে যে পরিণাম, এ ক্ষেত্রেও তাই ঘটেছিল। অনেক রক্ত ঝরানো অনেক আত্মোৎসর্গের পরও এই সংগ্রাম ব্যর্থ হয়েছিল নেতৃত্বের নিয়ম গড়ার ব্যাকরণ জানা না থাকায়।
এরপর যে প্রশ্ন স্বতঃস্ফূর্ততার মধ্য দিয়ে বহু মুখ থেকে বেরিয়ে আসার সম্ভাবনা, তা হল—নেতিবাচক ভূমিকা গ্রহণ করার পরও পশ্চিমবঙ্গে বামফ্রন্ট সরকারের দীর্ঘকাল গদি দখলে রাখা কি এই লেখকের বক্তব্যকে মিথ্যে প্রমাণ করার পক্ষে যথেষ্ট নয়?
আর প্রতিটি সৎ, সমাজ-সচেতন, রাজনীতি-সচেতন, মুক্ত-মনের মানুষের মতো এই লেখকও সত্যের দিক থেকে মুখ ঘুরিয়ে রাখতে নারাজ। সত্যের খাতিরে প্রশ্নকর্তাদের সঙ্গে সহমত পোষণ করতেই হয়—কমিউনিস্ট পার্টিগুলো সহ বামপন্থী দলগুলো রাজ্যস্তরে শাসন ক্ষমতা দখল করার পর সীমিত রাষ্ট্রক্ষমতাকে কাজে লাগিয়ে সমাজতান্ত্রিক আন্দোলন গড়ে তোলার, শোষণমুক্তি ঘটানোর সার্বিক কোনও প্রচেষ্টা অতীতেও করেনি, বর্তমানেও করছে না। রাষ্ট্রক্ষমতাকে কাজে লাগিয়ে জনচেতনাকে সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনমুখী করার চেষ্টা করলে কতটা কার্যকর হত, তা বিচারে বসার সুযোগই আমাদের নেই—যেহেতু জনচেতনাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার সামান্যতম চেষ্টাই বামপন্থীদের তরফ থেকে হয়নি।
এমন কথা বলার পরিপ্রেক্ষিতে কেউ কেউ বলতে পারেন—এই দেশের সাংবিধানিক কাঠমোর মধ্যে থেকে জনচেতনাকে শোষণমুক্তির আন্দোলনমুখী করার চেষ্টা একান্তই অবাস্তব।
কথাগুলোকে নিপাট মেনে নেওয়া বেজায় মুশকিল, যেহেতু এই লেখকের ঘাসে পা দিয়ে চলার অভিজ্ঞতা অন্য কথাই বলে। আমার মতোই বহু সাংস্কৃতিক আন্দোলনকর্মীর কাছে একটি অভিজ্ঞতালব্ধ সত্য যুক্তিবাদী সমিতি উদ্ভাসিত করেছে, এই দেশের সংবিধানের সীমাবদ্ধতার মধ্যেও বহু মানুষের মধ্যে চেতনার আগুন জ্বালাবার ক্ষমতার পরিচয় দিয়ে। যুক্তিবাদী সমিতির নেতৃত্ব জানে দেশের সংবিধান রচিত হয়েছে শাসক ও শোষকদের স্বার্থরক্ষার চিন্তাকে প্রধানত মাথায় রেখে। এও জানে— শেষ কথা বলে জনগণ । জনচিন্তাকে সঠিকভাবে চালিত করতে পারলে যে অসাধারণ শক্তির সৃষ্টি হয় তা শুধু সংবিধান কেন, রাষ্ট্রশক্তির শিকড় ধরেই টান মারার ক্ষমতা রাখে।
সাংবিধানিক সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও যে কাজ যুক্তিবাদী সমিতি করতে পারছে, সে কাজ করতে কমিউনিস্ট পার্টিগুলো-সহ বামপন্থী দলগুলোর অসুবিধে হওয়ার তো কথা নয়। বরং তারা যুক্তিবাদী সমিতির চেয়ে শত-সহস্রগুণ বেশি গতি সঞ্চারিত করতেই পারত, পারত জনচেতনাকে সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনমুখী করতে, যদি বাস্তবিকই করার ইচ্ছাটা আন্তরিক হত। রাজ্যের ক্ষমতা দখলের পর বামপন্থী দলগুলো যখনই কোনও ডাক দিয়েছে, গ্রাম-শহর থেকে স্বতঃস্ফূর্ততার সঙ্গেই মানুষ এসেছে সভায় মিছিলে-আন্দোলনে । এ-ভাবে যতই বছর গড়িয়েছে বঞ্চিত মানুষদের সুখস্বপ্নকে সরিয়ে দিয়ে দখল নিয়েছে নিরাশা-আর কত সহযোগিতা করতে হবে যাতে দেখা যাবে সমাজতন্ত্রের আলোক মিনার? এই প্রশ্ন জেগেছে বামপন্থী সরকারের সঙ্গে এককালে সমস্ত রকম সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেওয়া বঞ্চিত মানুষদের মধ্যে।
রাজ্যের কমিউনিস্ট পার্টিগুলো-সহ বামপন্থী দলগুলো কথা দিয়েও কথা রাখেনি, ক্ষমতার গদিতে বসে ক্ষমতার মধু খেতে আগ্রহী নেতার সংখ্যাধিক্য হেতু। ওই নেতারা কখনওই চাননি বঞ্চিত মানুষদের জনচেতনা সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবমুখী করে গড়ে তোলার চেষ্টার মধ্য দিয়ে নিজের কবর নিজে খুঁড়তে। দুর্নীতির শাঁসে-জলে পরিপুষ্ট নেতারা এক সময় হয়ে পড়েছে শোষক দলের সঙ্গী রাষ্ট্র-শক্তি।
এরপর আবার সেই প্রশ্নটাই ঘুরে আসবে—শাঁসে-জলে পরিপুষ্টদের ভিড়ে ঠাসা এই দল নেতিবাচক রাজনীতির খেলা চালিয়েও কী করে ক্ষমতায় টিকে আছে? জনগণ তো এই প্রাবন্ধিকের সূত্র মতো ওদের ছুড়ে ফেলে দিচ্ছে না?
কারণ দুটি। একঃ বামপন্থীদের সব চেয়ে কাছের প্রতিদ্বন্দ্বী কংগ্রেসিরা নেতিবাচকতায় বামপন্থীদেরই তুল্যমূল্য; অর্থাৎ সাধারণের চোখে দুই প্রতিদ্বন্দ্বীর অবস্থান যেন টাকার এপিঠ-ওপিঠ। ফলে নিরাশার গভীরে ডুবে থাকা বঞ্চিত মানুষরা আজ এক পক্ষকে হঠিয়ে অন্য পক্ষকে ক্ষমতায় আনার উৎসাহ হারিয়েছে, ভোটে উৎসাহ হারিয়েছে। দুইঃ সর্বগ্রাসী দুর্নীতির বাইরে আমাদের নির্বাচন-প্রক্রিয়াও নয়। ফলে জনগণের সঠিক মতামত নির্বাচনে প্রতিফলিত হওয়ার সম্ভাবনা অসম্ভবের চেয়েও কিছু বেশি। ভালো হিসেব জানা থাকলে এবং হুজুরের দলের সহযোগিতায় নির্বাচন তহবিল পুষ্ট থাকলে প্রকাশ্যে ‘বুথ জ্যাম’ না করেও জনগণের প্রকৃত ইচ্ছেকে ওলট-পালট করে দেওয়া যায় শতকরা মাত্র দশ থেকে কুড়ি ভাগ জাল ভোট বাক্সে ঢেলে। আর তেমনটা পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রে ঘটছেও। নির্বাচনের মধ্য দিয়ে যেহেতু প্রকৃত জনমত আদৌ বেরিয়ে আসছে না, তাই আদৌ এমন সিদ্ধান্তে পৌঁছনো যায় না-এই লেখকের সূত্র অসার। বরং এ-কথা মিলিয়ে নেবেন—যেদিন ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে, ভাঙার পর গড়ার আদর্শ সামনে রেখে কোনও রাজনীতির অভ্যুত্থান ঘটবে এ-দেশে, সেদিন নেতিবাচক রাজনীতি করা, হুজুরের দালাল প্রতিটি রাজনৈতিক দলের খেলা হবে শেষ। ওদের কফিনে শেষ পেরেক ঠুকবে জনগণই।
ভাঙা-গড়ার এই খেলায় যে কোনও আন্দোলনকে সাময়িক
জয়ের পরিবর্তে দীর্ঘস্থায়ী বা স্থায়ী জয়ে পরিবর্তিত
করতে চাইলে নেতাদের জানতেই হবে গড়ার
নিয়ম, যে নিয়মের কোনও বিকল্প নেই।
দ্বিচারিতাঃ অপ্রিয় কিছু কথা, কিছু প্রশ্ন
এই লেখা কোনও রাজনৈতিক দল, প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তিকে নিছক বিরোধিতা করার জন্য নয়। কোনও রাজনৈতিক দলের প্রপাগান্ডার জন্যও নয়। সহানুভূতিশীল পাঠক-পাঠিকাদের কাছে বিনম্র অনুরোধ – আপনার রাজনৈতিক আনুগত্য ও ব্যক্তিশ্রদ্ধাকে কিছুক্ষণের জন্য ছুটি দিয়ে সৎ-মূল্যবোধ ও শাণিত-যুক্তির নিরিখে লেখাটিকে বিচার করুন। আপনার এই ক্ষণিক নিরপেক্ষতার মধ্যেই লুকিয়ে রয়েছে সুন্দর পৃথিবী গড়ার অমোঘ শক্তি।
রাজনীতি = দুর্নীতি—এই ধরনের একটা সরল সমীকরণের শিকার সাধারণ মানুষ। কারণ, এটা তো ঠিক, প্রায় সমস্ত রাজনৈতিক দলই কম-বেশি দুর্নীতির সঙ্গে জড়িত। এই অবস্থায় এমন একটা লেখা লিখে ফেলা এবং প্রকাশ করার প্রয়োজনীয়তা যেমন বেশি ঝুঁকিও তেমনই বেশি। কারণ লক্ষ করেছি, অনেক দ্বিচারিতা, অনেক দুর্নীতি, অনেক অপসংস্কৃতির প্রশ্ন ভেসে যায় জনপ্রিয়তা ও সাফল্যের উন্মাদনার স্রোতে—একই সঙ্গে বানভাসি হয় যুক্তির, আদর্শের এবং শোষণ মুক্তির ভিত্তিমূলের।
কেন সমাজকে সুস্থ রাজনীতি দেওয়া যাবে না? নিশ্চয়ই যায়। আমরাই তা পারি, আমাদের সচেতনতাই পারে সমাজকে দ্বিচারিতামুক্ত ও দুর্নীতিমুক্ত করতে। আর সেই চিন্তাই এই লেখার উৎস। “ফরোয়ার্ড ব্লক মার্কসবাদী দল নয়” বলে কমিউনিস্ট পার্টি অফ ইন্ডিয়া (মার্কসিস্ট)-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক হরকিষেণ সিং সুরজিৎ মন্তব্য করেন ৯ মে ’৯৩ নয়াদিল্লিতে অনুষ্ঠিত ‘কিউবা সংহতি কমিটি’র বৈঠকে। এক কিউবান কমিউনিস্ট পার্টির পলিটব্যুরোর নেত্রীর উপস্থিতিতে এমন বেমক্কা বাক্যবাণে মর্মাহত ফরোয়ার্ড ব্লকের কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক চিত্ত বসু বলেন, “কোনও দলের নাম কমিউনিস্ট পার্টি হলেই সেই দল কমিউনিস্ট বা মার্কসবাদী হয়ে যায় না। সবকিছুই নির্ভর করে একটি দলের কাজকর্মের উপর।”
এই খবর ১০ মে’র বিভিন্ন দৈনিক পত্রিকার পাতায় পড়ে বুঝলাম, চিত্তবাবু খুবই কোমল-চিত্তের মানুষ। অপ্রিয় সত্য বলে কাউকে ব্যথা দেওয়ার কথা ভাবতেই পারেন না। তাই সে-দিনের অমন মহতী সভায় সোচ্চারে বলতে পারেননি—একটি মানুষের মার্কসবাদী হয়ে ওঠার প্রাথমিক ও আবশ্যিক শর্ত, তাকে যুক্তিবাদী হতেই হবে। নাস্তিক হতেই হবে। অন্ধ-বিশ্বাসের কাছে নতজানু হওয়া চলবে না। (এই প্রসঙ্গে অবশ্য এইটুকুও বলে রাখা ভালো— একটি মানুষকে যুক্তিবাদী হতে হলে মার্কসবাদী হতে হবে—এমন কোনও পূর্বশর্ত নেই)।
এইসব আলটপকা অপ্রিয় সত্য কথাগুলো ছুড়ে দিলে শিখধর্মাচরণে নতজানু ধর্মীয় অনুশাসন মেনে পাগড়ি ও বালাধারী সফেদ-দাড়ির হরকিষেণ সিং সুরজিৎ এবং তাঁকে দলের সর্বোচ্চ পদে বসান সি পি এম পার্টি নিশ্চয়ই যথেষ্ট চেয়ে বেশি অস্বস্তিতে পড়তেন। অবশ্য যেটুকু মুখ চিত্তবাবু খুলেছেন, একটু সচেতনদের কাছে সেই ইশারাই ‘কাফি হ্যায়’।
সি.পি.এম-এর কাছে অবশ্য আশার কথা এই যে–চিত্ত বসুর এ হেন বাক্যবাণেও কিউবান কমিউনিস্ট নেত্রীর কাছে সি.পি.এম-এর সম্মান একটুও টস্কায়নি। কারণ কিউবার কমিউনিস্ট পার্টির এক নম্বর জাঁদরেল নেতা ফিদেল কাস্ত্রোও আর এক হরকিষেণ সিং সুরজিৎ। আর তাইতেই তো খ্রিস্টধর্মের জয়গানে মুখরিত কাস্ত্রো রচিত পুস্তকের উদ্বোধন অনুষ্ঠিত হল সি.পি.এম-এর শ্রমিক সংগঠন সিটুর সদর দপ্তরে।
ধর্মের বিরুদ্ধে যে মার্কস ছিলেন চির-সংগ্রামী, দৃঢ়তার সঙ্গে
লিপিবদ্ধ করলেন শ্রেণিশোষণের সঙ্গে ধর্মের সম্পর্ক
কত নিবিড়, কত দৃঢ়বদ্ধ-সেই মার্কসের তথাকথিত
অনুগামী ভণ্ড মার্কসবাদীরা সমস্ত বঞ্চনার কারণ
হিসেবে অদৃষ্ট বা ঈশ্বরীয় অলীক কোনও
কিছুকে দায়ী করে নিজেদের দুর্নীতিকে,
শ্রেণিশোষণকে আড়াল করে আখের
গোছাতে চায় বলেই ধর্মের সঙ্গে
মার্কসকে জড়িয়ে এক সংশোধিত
মার্কসবাদকে হাজির
করতে চাইছে।
‘মার্কসবাদেও আছি, ধর্মেও আছি’ নীতি নিয়ে যাঁরা চলেন, তাঁরা একে ‘কৌশল’ বা ‘যুগোপযোগী’ বলে যতই সোচ্চার হোন না কেন, মোদ্দা কথায় এই নীতি দুর্নীতি, স্ববিরোধিতা, দ্বিচারিতা। ধর্মকে আঘাত না করার ফিকির হিসেবে প্রচার করতে চাইছে— ‘ধর্মকে আঘাত করলে জনগণের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যেতে হবে।’ এ-দেশে মার্কসবাদীরা ধর্মে আঘাত হানল কবে? এমন পরীক্ষাহীন সিদ্ধান্ত কি তথাকথিত মার্কসবাদীদের অন্তঃসারশূন্যতা, ও দেউলেপনাকেই প্রকট করে না? রামকৃষ্ণ মিশনের বিশ্বধর্মসম্মেলন উপলক্ষে সরাসরি রাজনীতিকে নাক গলানোর বিরোধিতায় আমরা যুক্তিবাদী সমিতি, নেমেছিলাম। আমরা ধর্ম থেকে রাজনীতিকে বিচ্ছিন্ন করার দাবিতে আন্দোলন গড়ে তুলতে চেয়েছিলাম। আমরা জানতাম পশ্চিমবঙ্গ তথা কলকাতায় দাঁড়িয়ে রামকৃষ্ণ মিশনের বিরুদ্ধে কিছু করা বা বলতে যাওয়া ভোট-নির্ভর রাজনৈতিক দলগুলোর কাছে বিজেপি বিরোধিতার চেয়ে হাজারোগুণ কঠিন। এই অবস্থানগত জায়গাতে দাঁড়িয়েও আমরা পেরেছিলাম দেশব্যাপী রাজনীতিকদের মানসকে আমাদের দাবির অনুকূলে সংগঠিত ও সমাবেশিত করতে। ‘ধর্মনিরপেক্ষতা’ শব্দটি ভারতের সংবিধানে যে অর্থহীন আবর্জনার মতোই পড়ে ছিল, সেই শব্দটির সুষ্ঠু ও সুস্থ প্রয়োগের দাবি তুলে আমরা পেরেছিলাম সে-দিকে আন্তর্জাতিক জনমতের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে। আমরা এই প্রত্যয় বহুতে প্রোথিত করতে পেরেছি—ধর্ম কখনওই প্রগতি ও সুচেতনার ধারক নয়, বরং মনুষ্যত্বের বিকাশকামিতার পক্ষে বাধা-স্বরূপ।
দ্বিচারিতা অবশ্যই দুর্নীতি। কিন্তু সকল দুর্নীতিই দ্বিচারিতা নয়।
একজন ঘুষখোর, চোর, ডাকাত বা গুন্ডা-মস্তানদের মতো
দুর্নীতি-পরায়ণদের চিহ্নিত করা যতটা সোজা,
ততটাই কঠিন দ্বিচারীদের মুখোশের
আড়ালের মুখগুলোকে
চিহ্নিত করা।
দ্বিচারিতা ও সীমাবদ্ধতা একই নিঃশ্বাসে উচ্চারিত হওয়ার মতো বিষয় নয় ৷ সীমাবদ্ধতা দুর্নীতি নয়। ফুটবলের প্রসূন ব্যানার্জির সীমাবদ্ধতা ছল—ডান পা তেমন চলত না। হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের সীমাবদ্ধতা ছিল—রাগাশ্রয়ী গানে গলা তেমন খুলত না। কল্প-বিজ্ঞানের গল্প লেখার ক্ষেত্রে সত্যজিৎ রায়ের সীমাবদ্ধতা ছিল— গল্পগুলো বিজ্ঞানের আবিষ্কৃত সূত্রের উপর মোটামুটি ভাবে নির্ভর করার পরিবর্তে প্রায়শই সে-সব গল্প হয়ে উঠেছে বিজ্ঞান-বিরোধী। এমনকী এও বলা যায়- সত্যজিৎ যতটা শিল্পমনস্ক ছিলেন ততটা বিজ্ঞানমনস্ক ছিলেন না। কিন্তু এঁদের এই সীমাবদ্ধতার বাইরে এঁরা এমন অনেক কিছুই সৃষ্টি করে গেছেন, যে সৃষ্টির জন্য আমাদের অন্তর থেকে প্রবাহিত হয়েছে ভালোবাসা, শ্রদ্ধা শুধুমাত্র সীমাবদ্ধতার কারণে দুর্নীতির কালিমার দ্বারা ওইসব চরিত্রকে আমরা তাই কলঙ্কিত করতে পারি না।
‘দ্বিচারিতা’ অবশ্যই দুর্নীতির চেয়ে বাড়তি কিছু, সংস্কৃতির পরিবেশকে ধ্বংস করার ক্ষেত্রে ব্লাড-ক্যানসারের মতোই নিঃশব্দ বিধ্বংসী শক্তি। হর্ষদ মেহেতা, দাউদ ইব্রাহিম, রশিদ বা বীরাপ্পানের মতো মুখোশহীন দুর্নীতির রথীমহারথীরাও একবার ফেঁসে গেলে ভুস ভুস করে ডুবতে থাকে। কিন্তু ডোবেন না আম্বানি, বিড়লা, চন্দন; ডোবেন না সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি, পুলিশ-প্রশাসন ও সেনাবিভাগের ক্রিম মানুষগুলো; ডোবেন না সমাজের ক্রীম বুদ্ধিজীবী বা সুপারস্টার অভিনতা, ডোবেন না দু-তিন হাজারি মাস-মাইনের ধনকুবের বিধায়ক, কি গায়ক, সাংসদ ও মন্ত্রীমশাইয়েরা। এঁদের ভাসিয়ে রাখে ভালোমানুষের মুখোশ, জনদরদী মুখোশ, প্রতিবাদী মুখোশ, উন্নাসিক বুদ্ধিজীবীর মুখোশ।
দুর্নীতি আজ এতই সর্বত্রগামী এবং এতই পরস্পরের সঙ্গে সম্পর্কিত হয়ে উঠেছে যে এ-দেশের মানুষ আজ গভীর নিরাশায় মানসিক রোগের শিকার হয়ে পড়ছে। এই অবস্থায় ভরসা যাঁরা জাগাচ্ছেন তাঁরা কতটা নির্ভরযোগ্য এটা আজ অতি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন হয়ে দাঁড়িয়েছে। আমরা যদি মুখোশধারী দ্বিচারীদের মুখোশ দেখে ভরসা রাখি, তাহলে সে হবে যুদ্ধহীন আত্মসমৰ্পণ, আত্মহনন।
মস্কোয় লেনিনের মূর্তি ‘হেঁইয়ো–মারো—হেঁইয়ো’ করে টেনে ভূলুণ্ঠিত করা হল। কোনও প্রতিবাদ বা প্রতিরোধ দেখা গেল না। কারণ এই ধরনের মানসিকতার সপক্ষে একটা সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল গড়ে তোলা হয়েছিল বিউটি কনটেস্ট, ক্যাবারে নাচের মতো নানা ভোগবাদী চিন্তার অফুরন্ত জোগান দিয়ে, ভাগ্যফল ও যিশু-বিবেকানন্দের মতো নানা ভাববাদী চিন্তার আমদানি ঘটিয়ে।
আজ আমাদের এই পোড়া দেশে মানুষের অধিকার ভূলুণ্ঠিত, ‘গণতন্ত্র’ একটা ‘তামাশা’, দুর্নীতির সহাবস্থান বেঁচে থাকার আবশ্যিক শর্ত। এ-সব থেকে যারা ফয়দা লুটছে, সেই বণিক-রাজনীতিক-আমলা-পুলিশ-প্রশাসন ফয়দা অব্যাহত রাখার স্বার্থে ব্যক্তি-লোভ ও দুর্নীতির পরিমণ্ডল গড়ে তুলেছে এবং তাকে প্রতিনিয়ত- পুষ্ট করতে সচেষ্ট রয়েছে। শাসক ও শোষকদের স্বেচ্ছাচারিতা, স্বজনপোষণ, রাজনৈতিক বিরোধীদের জানে বা পেটে মারার প্রয়াসের বিরুদ্ধে জনরোষ যেন দাউ-দাউ আগুনে পরিণত হয়ে বণিক- রাজনীতিক-আমলাদের অশুভ চক্রকে পুড়িয়ে না মারে, সে কথা চিন্তা করেই শিল্প-সাহিত্য-সংগীত ইত্যাদি জগতের বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বদের নানাভাবে কাজে লাগানো হয়েছে। এঁদের কেউ স্বার্থান্ধ, ভোগসর্বস্ব উত্তেজক সংস্কৃতির গন্ধ তৈরি করে মানুষের চেতনায় পৌঁছে দিচ্ছেন। কেউবা ‘ঈশ্বর’ জাতীয় সেরা গুজবের ঘাস-বিচুলিকে কুশলী হাতে পরিবেশন করে মানুষকেও ‘হাম্বা’ রবের চতুষ্পদীতে পরিণত করছেন। ফলে বঞ্চনার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ না গড়ে এইসব তৃণভোজীরা পরমপিতা-জাতীয়ের কাছে আত্মসমর্পণের মধ্যে মুক্তি ও শান্তি পেতে চাইছে। এইসব ভোগবাদী বা ভাববাদী চিন্তার প্রসারকামী লেখক হিসেবে অমুক গাঙ্গুলি বা তমুক চট্টোপাধ্যায়কে চিনতে কোনও অসুবিধে হয় না । এই চিনে ফেলার দরুন যাঁরা এঁদের সৃষ্ট ভাইরাস-আক্রমণ থেকে নিজেদের চিন্তাকে রক্ষা করতে পারেন, তাঁদের চিন্তাকে বিনাশ করতেই মুখোশধারী প্রতিবাদী বাজারে ছাড়া হয়েছে। এঁরা বাস্তবে চিন্তার প্রোটিনের ছদ্মবেশে চিন্তার বিনাশকারী ভাইরাস। একটু লক্ষ করলেই দেখবেন এই তথাকথিত শিল্পী, সাহিত্যিক বা বুদ্ধিজীবীদের স্পনসরের ভূমিকায় রয়েছে রাষ্ট্রশক্তি, ধনকুবের বণিকশ্রেণি বা প্রচারমাধ্যম— যার মালিকও অবশ্যই বণিক-শ্রেণিই ৷
আমাদের সমাজের চিত্রটাই এই রকম— ‘নামী’ হওয়ার একটা
পর্যায় অতিক্রম করে আরও নাম কিনতে সাধারণভাবে
বিভিন্ন স্পনসরকারী প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে আপস করা
প্রায় অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়ে। আর এইসব
স্পনসর দানকারী প্রতিষ্ঠানগুলো অন্যের
স্বাতন্ত্র্যকে পিষে মেরে নিজের
ছাঁচে ঢালাই করতে চায়।
এ দেশের অপসাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলের বিরুদ্ধে সুসংস্কৃতির পরিমণ্ডল গড়ে তুলতে অগ্রণী ভূমিকা অবশ্যই নিতে পারতেন সাহিত্যিক শিল্পী বুদ্ধিজীবীরা।
পৃথিবীর ইতিহাসে এমন দৃষ্টান্ত তো কম নয় যেখানে একটি গ্রন্থ অনেক বিপ্লব, অনেক ওলট-পালট ঘটিয়ে দিয়েছে। ভলতেয়ারের লেখা ‘ক্যানডিড’ ঘটিয়ে ছিল ফরাসি বিপ্লব। পত্রিকা ও প্রচারমাধ্যমগুলোর স্বাধীনতার পক্ষে (Pressfreedom) বিশাল ও ঐতিহাসিক ভূমিকা নিয়েছিল মিলটনের ‘আরিয়ো প্যাজিটিকা’ গ্রন্থটি। রুশ বিপ্লবে ম্যাকসিম গর্কির ‘মাদার’ প্রেরণা জুগিয়েছিল বিপ্লবীদের। শরৎচন্দ্রের ‘পথের দাবি’ ব্রিটিশ শক্তির বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে বহু বাঙালি যুবককেই প্রেরণা জুগিয়েছিল। কিন্তু আজ? এমন একটা প্রয়োজনীয় মুহূর্তেও সিংহভাগ সাহিত্যিক-শিল্পী-বুদ্ধিজীবীরা সুন্দর সমাজ গড়ার জন্য মানুষের চেতনাকে উদ্বুদ্ধ করতে এগিয়ে এলেন না। এঁরা হয় নিশ্চুপ হয়ে রয়েছেন, নতুবা স্পনসরদের চাটুকারের ভূমিকা পালন করে চলেছেন। এইসব স্পনসররা অনুগতদের জনপ্রিয় করতে অতিমাত্রায় সচেষ্ট এবং একইভাবে সচেষ্ট অনুগত স্রষ্টাদের সাহায্যে এমন এক পরিমণ্ডল গড়ে তুলতে, যেখানে প্রতিবাদ থাকবে না, প্রতিরোধ থাকবে না, থাকবে শুধু আপস।
যে কোনও পেশায় নিযুক্ত লোকের মতো শিল্পী-সাহিত্যিক-বুদ্ধিজীবীদেরও ব্যক্তিগত জীবনে মতাদর্শগত বিশ্বাস বা রাজনৈতিক আনুগত্য থাকতেই পারে । কিন্তু সরকার, বৃহৎ-পত্রিকাগোষ্ঠী জাতীয় স্পনসরদের পরাক্রমে বেশিরভাগ বুদ্ধিজীবীই তার আদর্শগত বিশ্বাস বা সততাপূর্ণ আনুগত্য দ্বারা পরিচালিত হন না। এমন দৃষ্টান্ত প্রায় বিরল যেখানে কেউ স্পনসর বা প্রচার মাধ্যমের কাছে নীতিকে বন্ধক রাখা আপসে না গিয়েও বিশাল জনপ্রিয়তা অর্জন করেছেন।
ব্যাপকতর মানুষদের মধ্যে একটা বিপদজনক ধারণা গ্রহণযোগ্যতা অর্জন করেছে—অমুক পত্রিকা প্রতিক্রিয়াশীল, অমুক পত্রিকা প্রগতিবাদী। ধারণাটা একেবারে আগাপাছতলা ভুল। বৃহৎ পত্রিকাগোষ্ঠীর কাছে পত্রিকা প্ৰকাশ স্রেফ একটি ব্যবসা মাত্র, যেমন ব্যবসা করেন শেয়ার দালাল, বিল্ডিং প্রমোটার অথবা ফিল্ম প্রডিউসার কিংবা ক্লথ মিলের মালিক। পত্রিকাগুলোর কেউ সি. পি. এম-এর প্রতি জনগণের ক্ষুব্ধতাকে পুঁজি করে খদ্দের ধরতে পত্রিকার একটা চরিত্র’কে খাড়া করে। কেউ বা সি. পি. এম-এর জনসমর্থনকে পুঁজি করে খদ্দেরদের মনোরঞ্জন করে। কেউ বা জনপ্রিয় রাজনৈতিক নেতা বা নেত্রীকে সমর্থনের মধ্য দিয়ে এবং তারই সঙ্গে পরিচ্ছন্ন রাজনীতির ইমেজ বা সরকার বিরোধী, ইমেজ তৈরি করে কাগজের বিক্রি বাড়িয়ে চলেন। এইসব পত্রিকাগুলোর সম্পাদক থেকে সাংবাদিকদের অবস্থান মোহনবাগান, ইস্টবেঙ্গল, মহামেডানের ফুটবল টিমের কোচ ও খেলোয়াড়দের মতোই— যখন যে দলে খেলেন, সেই দলকে জয়ী করতেই সচেষ্ট থাকেন। প্রতিক্রিয়াশীল পত্রিকা বলে যাকে আপনি গাল পাড়েন, তারই অতিক্ষমতা সম্পন্ন দুদে বার্তাসম্পাদক কিংবা ঝানু সাংবাদিক আপনার মনে হওয়া প্রগতিবাদী পত্রিকায় যোগ দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে জীবিকার স্বার্থে কলম থেকে ঝরাতে থাকেন বিপ্লবী আগুন। একই ভাবে বিপরীত ঘটনাও ক্রিয়াশীল। প্রগতিশীল পত্রিকার বিপ্লবী কলমও টিম পাল্টাবার সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবিপ্লবী কলম হয়ে ওঠে। এই জাতীয় উদাহরণ কিন্তু ব্যতিক্রমী দৃষ্টান্ত নয়, বরং সাবলীল গতিশীল। এইসব বিপ্লবী, প্রতিবাদী, প্রতিবিপ্লবী, বুর্জোয়া প্রভৃতি প্রতিটি বাণিজ্যিক পত্রিকার মালিকরাই আসলে এক একটি ধনকুবের। এইসব পত্রিকা মালিকদের মধ্যে অবশ্যই প্রতিদ্বন্দ্বিতা রয়েছে। একজনকে ধনসম্পদে আর একজনের টপকে যাওয়ার প্রতিদ্বন্দ্বিতা। কিন্তু নিজেদের অস্তিত্বের পক্ষে বিপজ্জনক কোনও শক্তির বিরুদ্ধে মোকাবিলার ক্ষেত্রে ওরা দারুণ রকম এককাট্টা।
কখনও কখনও বিশাল বাণিজ্য সাম্রাজ্যের অধিকারীরা রাজনীতিকদের উপর প্রভাব বিস্তার করে নিজের ক্ষমতা রক্ষা ও বর্ধিত করতে পত্রিকা প্রকাশে উদ্যোগী হয়। এখানেও কিন্তু বাণিজ্য-সম্রাটের পক্ষে পত্রিকার বাণিজ্যিক সাফল্যের দিকে মুখ ঘুরিয়ে থাকা সম্ভব হয় না। যে পত্রিকা বিক্রি হয় না, তাকে কোনও রাজনীতিক পাত্তা দেবে?
যে-সব সাংবাদিক বা সংবাদপত্রকর্মী সমাজের প্রতি দায়বদ্ধতা অনুভব করেন, দুর্নীতির শিকল ভেঙে সুসংস্কৃতির সমাজ গড়তে চান, তাঁদের পক্ষেও কলমকে হাতিয়ার করে পত্রিকাকে রণভূমি করা সম্ভব হয় না। কারণ পত্রিকায় ব্যক্তি ইচ্ছে বা ব্যক্তি আবেগের স্থান সীমাবদ্ধ। পত্রিকার পলিসির সঙ্গে মানিয়ে নিয়েই একজন সাংবাদিককে কলম চালাতে হয়। কোনও সাংবাদিকের পক্ষে একজন ব্যক্তি বা একটি প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে ততক্ষণই সহযোগিতা করা সম্ভব যতক্ষণ না পেপার পলিসি ওই ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের বিপক্ষে যায় ।
পেপার পলিসি কাউকে ব্ল্যাক আউট করতে চাইলে বা কারও বিপক্ষে গেলে তাকে পত্রিকার প্রচারে আনা বা তার পক্ষে লেখা কোনও সাংবাদিকের পক্ষেই সম্ভব হয় না। কিন্তু পত্রিকা মালিক যদি দেখেন কাউকে ব্ল্যাক আউট করার ফলে অথবা কারও বিপক্ষে লেখার ফলে জনগণের মধ্যে ব্যাপক বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা যাচ্ছে, পত্রিকা ব্যবসা ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার মুখে, তখন ব্যবসার স্বার্থেই তাঁরা পলিসি পাল্টে ফেলেন, ডিগবাজি খান। এই ডিগবাজি খাওয়াটাও ততক্ষণই সম্ভব, যতক্ষণ না ওই ব্যক্তি বা সংস্থা পত্রিকা মালিকের অস্তিত্বের পক্ষে চূড়ান্ত সংকট হিসেবে হাজির হচ্ছে।
বাণিজ্যিক পত্র-পত্রিকার বাস্তব কাঠামো বিষয়ে স্পষ্ট ধারণা না থাকলে বিভ্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা বেশি থাকে, ভুল বোঝার অবকাশ বেশি থাকে। আর এই ভুলই বহু সৎ ও গতিশীল আন্দোলনে ধস নামাতে পারে। সত্যিকারের আন্দোলনের পাল থেকে জনসমর্থনের হাওয়া কেড়ে নিতে মেকি আন্দোলনকারী খাড়া করে তথাকথিত প্রগতিশীল পত্রিকা যখন ময়দানে নামে, তখন পত্রিকা-চরিত্র বিষয়ে ভ্রান্ত ধারণা বহু সমর্থককে, বহু আন্দোলন-কর্মীকে, বহু নেতাকে আন্দোলন থেকে দূরে সরিয়ে দেয়।
বিভিন্ন প্রচার-মাধ্যম বা পত্র-পত্রিকা যেমন বিভিন্ন শিল্পী, সাহিত্যিক, বুদ্ধিজীবী ও সংগঠনের নেতৃত্বকে ‘পেপার পলিসি’র পক্ষে কাজে লাগায়, নিজস্ব ছাঁচের সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল গড়ার পক্ষে কাজে লাগায়, তেমনই শিল্পী, সাহিত্যিক, বুদ্ধিজীবী ও সংগঠনের নেতৃত্ব বা আন্দোলনের নেতৃত্ব কেন পারবে না পত্র-পত্রিকা ও প্রচার-মাধ্যমগুলোকে যতদূর সম্ভব কাজে লাগাতে? কাজে লাগানো সম্ভব। অবশ্যই সম্ভব। সৎ, নিষ্ঠাবান, নির্লোভ ও লক্ষ্য সচেতন বুদ্ধিদীপ্ত ব্যক্তিত্ব চেষ্টা করলে দুর্নীতির সঙ্গে আপস না করে, প্রচার-মাধমে দ্বারা ব্যবহৃত না হয়ে প্রচার-মাধ্যমকেই ব্যবহার করতে পারেন।
যে পত্রিকার পাঠক সংখ্যা যত বেশি, জনগণকে প্রভাবিত করার ক্ষমতাও তার তত বেশি।
বাংলা ভাষার সবচেয়ে জনপ্রিয় পত্রিকার দিকে একটু সচেনততার
সঙ্গে ফিরে তাকান, দেখতে পাবেন ওই পত্রিকা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে
নানাভাবে মানুষের মাথায় ঢোকাতে চায়, সমাজের সেরা
লেখক, সেরা শিল্পী, সেরা বুদ্ধিজীবীরা তাদের পত্রিকায়
লেখেন, আঁকেন। ফলে ওই পত্রিকায় স্থান পাওয়া,
জনগণের কাছে শ্রেষ্ঠত্বের ISI ছাপ পাওয়া হয়ে
দাঁড়ায়। এর পর ওরা ইচ্ছে মতন একজনকে
প্রচারের তুঙ্গে তুলে নিয়ে যায়, একজনকে
ব্ল্যাক আউট করে জনগণ থেকে নির্বাসিত
করে। জনপ্রিয় সব পত্রিকাই কম-
বেশি একই মানসিকতার দ্বারা
পরিচালিত হয়।
আর এক দল বুদ্ধিজীবী, সাহিত্যিক, শিল্পী আছেন, যাঁরা নিজেদের ‘বাজারি বুদ্ধিজীবীদের সঙ্গে মেশাতে রাজি নন। সমাজের প্রতি যাঁদের দায়বদ্ধতার কথা সোচ্চারে প্রচারিত হয়, প্রতিবাদী চরিত্র হিসেবে এঁদের প্রজেক্ট করা হয়। প্রজেক্ট করেন তথাকথিত প্রগতিশীল পত্রিকা (আসলে যে প্রগতিশীলতা খদ্দের ধরার বাণিজ্যিক কৌশল মাত্র)। এঁরা যদি ভণ্ড, প্রগতিশীলতার মুখোশ পরা, লোভী বা দ্বিচারী হন তবে আমরা এঁদের বিরুদ্ধে সবচেয়ে বেশি সোচ্চার হব। কারণ, এঁরা আমাদের সমাজ-সংস্কৃতিকে দূষিত করার পক্ষে প্রথম আলোচিত বুদ্ধিজীবীদের চেয়ে অনেক বেশিগুণ ভয়ংকর শক্তির অধিকারী।
আমরা এই আলোচনায় সেই সব নরসিমাজাতীয় পচা রাজনীতিবিদদের কথা আনতে চাই না, যাঁরা কথায় ও কাজে সর্বদা বিপরীত মেরুতে অবস্থান করার সুবাদে ‘রাজনীতি’কে ‘দুর্নীতি’র সমার্থক শব্দ হিসেবে জনমানসে দৃঢ়বদ্ধ করেছেন। সেইসব সর্বহারার নেতাদের কথাও আলোচনায় আনব না, যাঁরা কোটিপতি এবং যাঁদের সন্তান ও আত্মীয়-পরিজনেরা কোটি-কোটিপতি। কারণ বেশির ভাগ মানুষই এইসব মানুষদের “চোর-চোট্টা-চিটিংবাজ’ হিসেবেই চেনেন। কিন্তু সেইসব রাজনীতিকদের ভিতর থেকে দু একজন ব্যক্তিকে উদাহরণ হিসেবে টেনে আনাটা নিশ্চয়ই অসঙ্গত হবে না, যাঁরা স্বার্থান্ধ ও অন্ধ স্তাবকের দল ছাড়াও অনেকেরই শ্রদ্ধা আকর্ষণ করলেও বাস্তবে তাঁরা স্ববিরোধী, দ্বিচারী, কথায় ও কাজে বিপরীত মেরুতে অবস্থানকারী।
আসুন রাজনীতিক দিয়ে শুরু করে সমাজশীর্ষের দু-চারজন বহুরূপীর রূপ চিনিয়ে দিই। তারপর আমরা সকলে মিলে দ্বিচারীদের চিহ্নিতকরণের খেলায় মেতে উঠলে নাম কিনতে বা আখের গোছাতে দ্বিচারী হওয়ার অসুস্থ প্রবণতা বন্ধ হবেই।
চোদ্দোশো বঙ্গাব্দে পা দিতেই বুঝলাম, আমাদের জন্য অপেক্ষা করে আছে অনেক কৌতুক যাকে ‘নির্মল কৌতুক’ না বলে ‘রোমহর্ষক কৌতুক’ বললে যথার্থ হবে। কট্টর মার্কসবাদী, শ্রেণি সংগ্রামে দৃঢ় প্রত্যয়ী সোমনাথ চট্টোপাধ্যায় তাঁর দুই নাতির উপনয়ন উপলক্ষে প্রীতিভোজে অনেক মার্কসবাদী বন্ধুকে আমন্ত্রণ জানালেন। আর সেইসব মার্কসবাদীরা একটা রাতের জন্য শ্রেণি সংগ্রামকে শীতের শেষের লেপের মতোই গুটিয়ে তুলে রেখে ব্রাহ্মণ্যবাদের ধারাকে স্বাগত জানিয়ে মার্কসীয় ভোজ সমাধা করলেন। একটু গোদা বাংলায় বলা যায়— মার্কসবাদীরা সেই ভোজসভায় মার্কসবাদকেই উদরসাৎ করেন।
১৩ জুন ‘৯৩ মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টির দৈনিক মুখপত্র ‘গণশক্তি’র দু’য়ের পাতায় প্রকাশিত একটি বিজ্ঞাপন এখানে তুলে দিচ্ছি—
‘মাকর্সবাদী পরিবারের মেয়ে পূঃবঃ (ঢাকা বিক্রমপুর) ব্রাহ্মণ, ৫–১, বি এ মান, সুশ্রী, ঘরোয়া, গৃহকর্মে নিপুণা, রন্ধনে পারদর্শী, টাইপ জানা, গৃহশিক্ষয়িত্রী ও শাড়ি ব্যবসায়ী। মাসিক আয় দু’হাজার। সহৃদয় স্নাতক কেন্দ্রীয়/রাজ্য সরকারি পদস্থ কর্মচারী, অফিসার, প্রফেসর, ব্যাঙ্ক, রেল, ইঞ্জিনিয়ার, ডাক্তার, ব্রাহ্মণ/কায়স্থ প্রগতিশীল পাত্র অগ্রগণ্য।’
পাত্রীর পিতা প্রয়াত দীনেশ মজুমদার ছিলেন মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টির প্রথম সারির নেতা, যাঁর নামাঙ্কিত এক বিশাল সৌধ দাঁড়িয়ে রয়েছে কলকাতার মৌলালিতে। প্রয়াত কমিউনিস্ট নেতার মেয়ের জন্য কমিউনিস্ট পার্টির দৈনিক বিজ্ঞাপন দিয়ে মার্কসবাদী পাত্রীর জন্য ‘ব্রাহ্মণ অথবা কায়স্থ প্রগতিশীল’ পাত্ৰ চাওয়া হচ্ছে।
জাত-পাতের বিরুদ্ধে সংগ্রামী, শ্রেণি সংগ্রামে বিশ্বাসী একটা রাজনৈতিক দলের নেতাদের অবস্থা এই বলেই ‘রণে বনে জঙ্গলে’ স্মরণ নিলেই রক্ষাকারীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হওয়ার অঙ্গীকারবদ্ধ লোকনাথবাবার ঘটা করে পুজো হয় মাঝারি মার্কসবাদী নেতাদের ঘরে, লক্ষ্মীর ঘট ও নানা দেব-দেবীর মূর্তিতে আচ্ছন্ন থাকে মার্কসবাদীদের কুলুঙ্গি, আর পাত্র বা পাত্রী খোঁজার সময় জাত-পাতের বিরুদ্ধে সংগ্রাম ইত্যাদিকে ক্ষণিক বিশ্রাম দেয়। পরিণতিতে ১৬ বছর মার্কসীয় শাসনে মার্কসীয় চেতনায় উদ্বুদ্ধ হওয়ার মতো কোনও সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল গড়ে না উঠে গড়ে উঠেছে ভণ্ডের সংস্কৃতি, দুর্নীতির সংস্কৃতি, লুম্পেনের সংস্কৃতি। আমরা পেয়েছি ব্রাহ্মণ মার্কসবাদী, কায়স্থ মার্কসবাদী, ঈশ্বরজাতীয় বিশ্বাস নতজানু মার্কসবাদী, অদৃষ্টবাদী মার্কসবাদী, হুল্লোড়বাজ নাচ-গানের প্রমোটার মার্কসবাদী, বিল্ডিং-প্রমোটার মার্কসবাদী, শেয়ার দালাল মার্কসবাদী, লটারি ও সাট্টা ব্যবসায়ী মার্কসবাদী, মস্তান মার্কসবাদী, ধর্ষক মার্কসবাদী, ওয়াগন ব্রেকার মার্কসবাদী, রিগিং মাস্টার মার্কসবাদী, ব্যক্তি-স্বার্থে এবং দলীয় স্বার্থে মার্কসবাদের আন্দোলনকে পদদলিত কর মার্কসবাদী, দ্বিচারী মার্কসবাদী।
ব্যক্তিগত আখের গোছানোর স্বার্থে, দুর্নীতি ও শোষণকে বজায় রাখার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে ওইসব ‘হাঁসজারু’ মার্কা মার্কসবাদী তৈরির লাগাতার প্রক্রিয়া চালিয়েই চলেছে ভারতের বৃহত্তম তথাকথিত মার্কসবাদী দলের নেতৃত্ব । এরই ফলস্বরূপ, আমরা মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টির দৈনিক মুখপত্র ‘গণশক্তি’তে শেয়ার দর ছাপতে দেখলাম। আর কখন ছাপা হল? না, যখন আন্তর্জাতিক মার্কসবাদী সম্মেলন হচ্ছে সি. পি. এম -এরই ব্যবস্থাপনায়। আমরা ‘গণশক্তি’তে সাট্টার বিজ্ঞাপন ছাপতে দেখেছি, দেখেছি ‘মা নির্মলাদেবী’ নামের জনৈকা অলৌকিক ক্ষমতার দাবিদারের ছবিসহ ঢাউস বিজ্ঞাপন ছাপতে। অথচ যখন এই ‘গণশক্তি’ সান্ধ্য দৈনিক ছিল বা ’৬৭তে যখন প্রভাতী সংবাদপত্রের রূপ নিল তখন প্রথম পৃষ্ঠার একেবারে উপরের দু’পাশে ছাপা হত মার্কস ও লেনিন-এর বাণী।
কমিউনিটি পার্টিতে এমন একটা দিন ছিল যখন দলের নেতা বিনয় চৌধুরী স্ত্রীর সঙ্গে ধর্মস্থানে যাওয়ার জন্য দলের নেতৃত্ব তাঁর কাছে কৈফিয়ত তলব করেছিলেন। তখন ছিল বিনয় চৌধুরীর যৌবনকাল। তারপর অনেক জল গড়িয়েছে । আজ বালক ব্রহ্মচারীর শিষ্য সুভাষ চক্রবর্তী, শান্তি ঘটক বীর-বিক্রমে দলের উচ্চপদে বিরাজ করেন। জ্যোতি বসু কোমরের ব্যথা সারাতে বালক ব্রহ্মচারীর ঝাড়-ফুঁকের সাহায্য নেন। সর্বহারাদের মুক্তির স্বপ্ন দেখানো বড় মেজ মার্কসবাদী দলগুলোর বর্তমান অবস্থান সর্বহারাদের মধ্যে স্বপ্নভঙ্গের নিরাশাই শুধু সৃষ্টি করে চলেছে, সৃষ্টি করে চলেছে ভণ্ড সুবিধাভোগী এক বিশেষ শ্রেণি।
ষাটের দশকের যে সব উজ্জ্বল নাম এক সময় এই সব ভণ্ড নেতৃত্বের বিরুদ্ধে এগিয়ে এসেছিলেন, যাঁদের প্রতি একদা বহু মানুষ প্রত্যাশা রেখেছিলেন, স্বপ্ন দেখেছিলেন, যাঁদের আহ্বানে পরম অবহেলায় শত-সহস্র যুবক-যুবতী সীসার গুলি বুকে নিয়ে শুয়ে আছে মাটির গভীরে, তাঁদের অনেকেই আজ রাজার বাজনদরের বাজনার তালে তালে দিব্বি নাচন-কোঁদন করছেন, ডিগবাজিও খাচ্ছেন। ‘মৃতেরা এ পৃথিবীতে ফেরে না কখনও’। ডিগবাজিকরেরা বুঝে গেছেন সীসার গুলি বুকে নিয়ে শুয়ে থাকা হীরে-মানিকরা মাটি ফুঁড়ে উঠে এসে কোনও দিনই এমন অবস্থা পাল্টানোর জন্য জবাবদিহি চাইতে আসবে না। তারই সুযোগ নিয়ে জেল খাটার বছরগুলোকে অপূর্ব করিশ্মার সঙ্গে ইউনিট ট্রাস্টের ডিভিডেন্ড করে অনেকেই দিব্বি ভাঙিয়ে খাচ্ছেন।
কমরেড কাকা ওরফে অসীম চ্যাটার্জি ’৯০-তে এসে আবিষ্কার করলেন এবং সোচ্চার হলেন, “রাজ্যের বাম ও গণতান্ত্রিক আন্দোলন বামফ্রন্টের নেতৃত্ব ও শাসনের মধ্য দিয়ে যে অতীতের তুলনায় শক্তিশালী হয়েছে তা অস্বীকার করতে পারি না।” অসীমবাবু, আপনার ‘ভোট বয়কটের রাজনীতি’তে একদা অবস্থান বা ‘ভোটের রাজনীতি’তে ফিরে আসা, এই দুটি প্রসঙ্গের প্রতি সম্পূর্ণভাবে নিস্পৃহ থেকেও অবশ্যই যুক্তিকে মর্যাদা দিতে প্রশ্ন তুলতে পারি, অসীম চ্যাটার্জি— সত্যিই কি আপনি মনে করেন বামফ্রন্ট শোষণ মুক্তির আন্দোলন করছে? সর্বহারাশ্রেণির মুক্তির পক্ষে সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল তৈরির আন্দোলন করছে? আন্দোলন বলতে আপনি কী বোঝেন আসীমবাবু? আগের মতো করে বোঝেন? না, অবস্থান পাল্টে আন্দোলন বলতে লোক জড়ো করার ক্ষমতাকেই গুরুত্ব দিতে চান বা ভয় দেখিয়ে বর্তমান রাজনৈতিক দলগুলোর লোক জড়ো করার ক্ষমতাকেই আন্দোলনের ক্ষমতা বলে মনে করেন? এই বক্তব্যের মধ্য দিয়ে কোনওভাবেই ভোট বয়কটের রাজনীতি বা ভোটের রাজনীতিকে সমর্থন অথবা অসমর্থন করতে চাইছি না। বলতে চাইছি, অসীমবাবুর এমনতর বক্তব্যের মধ্য দিয়ে তাঁর স্পষ্ট কোনও রাজনীতির দিশা আমরা লাভ করি না। বরং তাঁর বক্তব্য থেকে একটা আন্দোলনবিমুখ সুবিধাবাদী রূপই স্পষ্টতর হয়ে ওঠে। ‘৯০-এর জানুয়ারিতে বিভিন্ন প্রভাতী দৈনিক সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়েছিল, আপনি সি.পি.এম মঞ্চে যেতে রাজি হওয়ার পক্ষে যুক্তি দেখিয়েছেন, “ওদের মানুষ জড়ো করার ক্ষমতা আমাদের থেকে অনেক বেশি।” অসীমবাবু আপনার কাছে আরও একটি খোলা প্রশ্ন- আপনি কি সত্যি এ-জাতীয় কথা বলেছেন? সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে কংগ্রেস এবং বি.জে.পি’র মানুষ জড়ো করার ক্ষমতা তো সি.পি.এম-এর চেয়েও বহুগুণ বেশি; আপনারই যুক্তি মেনে আপনি কি সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে কংগ্রেস বা বি.জে.পি’র মঞ্চে হাজির হবেন ?
আসলে আপনার মতো নেতারা সৎ থেকে অবস্থান পাল্টে চতুর হয়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে গুণে নয়, পরিমাণে শ্রদ্ধাশীল হয়ে পড়েছেন। ফলে আপনারা সংখ্যাগুরু জনগণকে সঙ্গে পেতে পিছিয়ে পড়া জনচেতনার স্তরে নিজেদের নামিয়ে নিয়ে আসতে শুরু করেছেন। আপনারা চাইছেন মানুষের চেতনার অগ্রগামিতা থামাতে। কারণ, আপনাদের মতন পোড়খাওয়া চতুর নেতাদের মোটেই অজানা নেই-বিজ্ঞানমনস্কতা, যুক্তিমনস্কতা গড়ে তোলার আন্দোলন, সার্বিক সাংস্কৃতিক আন্দোলন, সমাজ ব্যবস্থা আমূল পরিবর্তনকারী আন্দোলনেরই ভিত্তিভূমি। আপনারা চাইছেন এমন এক সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল সৃষ্টি করতে, জিইয়ে রাখতে, যেখানে ধান্দাবাজদের আখের গোছানোর খেলাটা চলমান থাকে।
’৯৩-এর পঞ্চায়েত নির্বাচনের মুখে আজিজুল হকের প্রকাশিত লেখাগুলো পড়ে বুঝতে অসুবিধে হয়নি তিনি গ্রাম-গঞ্জের এক সোনালি চিত্র এঁকে বামফ্রন্টের ভোট বাক্সকে স্ফীত করতে চেয়েছিলেন। যে কোনও রাজনৈতিক দলকে সমর্থন বা অসমর্থন করার পূর্ণ অধিকার আপনার নিশ্চয়ই আছে। এক সময় আপনার নিশ্চয়ই অধিকার ছিল সি.পি.এম’কে শোষকদের সহযোগী শাসক ভাবার। আজ আপনার নিশ্চয়ই অধিকার আছে এমন ভাবার— অনেক রক্ত ঝরানো সংগ্রামের মধ্য দিয়ে রাজ্যের বাম সরকার সর্বহারা শ্রেণির জন্য অনেক দিয়েছে—যেমনটি এখন ভাবছেন। কিন্তু আপনি সত্যিই কি এমনটা ভাবছেন? না কি ভাবনার সঙ্গে সম্পর্কহীনভাবে এমনটা লিখতে বাধ্য হয়েছেন ও হচ্ছেন—পেট চালাবার তাগিদে?
আজিজুল সাহেব, জানি আপনার শারীরিক অক্ষমতা আপনাকে গ্রাম-গঞ্জে ঘুরতে দেয় না, শহুরে কিছু মধ্যবিত্তদের ঘিরে আপনার বর্তমান গণ্ডি । আপনার শারীরিক সীমাবদ্ধতার কথা জেনেও বলছি-সৎ সাংবাদিকতার স্বার্থে গ্রামে-গঞ্জে ঘুরে গ্রামবাংলাকে জেনে লিখুন। কুড়ি বছর আগের জানা ভাঙিয়ে খাবেন না। এই পরিক্রমার পর আপনার যদি মনে হয়, সর্বহারা শ্রেণির শোষণ মুক্তির কাজে বামফ্রন্ট সরকার দৃঢ় পদক্ষেপে এগিয়ে চলেছে—লিখুন। যদি মনে হয়, বাণিজ্যিক সিনেমায় দেখানো শান্ত সুন্দর গ্রামগুলোর মতোই আমাদের গ্রামবাংলার বর্তমান সামগ্রিক চিত্র—তাই লিখুন। যদি দেখেন ক্ষুধা, দুর্নীতি, অবক্ষয়, রাজনৈতিক ফ্যাসিবাদের বাঁধনে গ্রাম বাংলা আজ মুমূর্ষু—তাই লিখুন ৷ গণ-আন্দোলনের স্বার্থে, নিপীড়িত-বঞ্চিত মানুষদের স্বার্থে ধর্মীয় ফ্যাসিবাদের পাশাপাশি রাজনৈতিক ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধেও সোচ্চার হোন।
আপনি বি.জে.পি’র ধর্মীয় ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে সোচ্চার-আপনাকে অভিনন্দন। যে কোনও ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধেই যুক্তিবাদী মানুষরা সোচ্চার হবেন, সৎ মানুষরা সোচ্চার হবেন, সোচ্চার মানুষদের অভিনন্দন জানাবেন—এমনটাই প্রত্যাশিত। বি.জে.পি’র ধর্মীয় ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে সব্বাইকে এক হয়ে লড়াইতে নামতে হবে বলে যেমনটি ভাবছেন, আহ্বান রাখছেন, সি. পি. এম-এর রাজনৈতিক ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে তেমনই আহ্বানে সোচ্চার হতে পারবেন কি আজিজুল সাহেব? গণতন্ত্রে যে কোনও নাগরিকের যে কোনও রাজনৈতিক দলকে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সমর্থন অথবা অসমর্থন করার পূর্ণ অধিকার যেখানে স্বীকৃত, সেখানে বিরোধী রাজনৈতিকদলের সমর্থকদের প্রাণে বা ভাতে মারার অধিকার কোনও রাজনৈতিক দলেরই থাকতে পারে না। কিন্তু আজ প্রায় সব রাজনৈতিক দলের মধ্যেই কম-বেশি এই ফ্যাসিবাদী মানসিকতা মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে। এই রাজনৈতিক ফ্যাসিবাদ বন্ধের ক্ষেত্রে এ রাজ্যে যে রাজনৈতিক দল সবচেয়ে অগ্রণী ভূমিকা নিতে পারত, সে হল বৃহত্তম ও শাসক রাজনৈতিক দল সি. পি. এম। কিন্তু তাদের এ-বিষয়ে ভূমিকা কী? তারা কি স্কুলে-কলেজে ভর্তি হওয়া থেকে প্রাইমারি স্কুলের কেরানি, কলেজের অধ্যাপক, সরকারি চাকরি, বেসরকারি চাকরি সর্বত্রই একচ্ছত্র নিয়ন্ত্রক, ফ্যাসিবাদীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়নি? তৃণমূল পর্যায়ের জনগণের সঙ্গে আজও কি আপনি তেমনই মেশেন, যেমন মিশতেন কারাজীবনের আগের লালটুকটুকে দিনগুলোতে? সত্যকে জানতে মিশতে শুরু করুন আজিজুল সাহেব, মিশতে শুরু করুন ৷ মাঠে ময়দানে এইসব মানুষগুলোর সঙ্গে ওদের মতো করে মিশলে অবশ্যই দেখতে পাবেন, কী বিপুল সংখ্যক মানুষ আজ বিশ্বাস করেন ‘মার্কসবাদ’ ও ‘ফ্যাসিবাদ’ সমার্থক শব্দ । এই বিশ্বাসীদের সংখ্যা যে প্রতিটি দিনই বেড়ে চলেছে ! এই বিশ্বাস থেকে জন্ম নেওয়া ঘৃণাই কি একদিন তথাকথিত মার্কসবাদীদের এই বাংলা থেকে উৎপাটিত করার ক্ষেত্রে প্রবলতর ভূমিকা নেবে না? মার্কসবাদের বিরুদ্ধে জনমানসে এমন একটা অ্যালার্জি, বিতৃষ্ণা ও ঘৃণা সৃষ্টির জন্য শাসক ও মার্কসবাদীদের ফ্যাসিবাদী চরিত্র, ভণ্ডামি ও দুর্নীতির একটা বিশাল ভূমিকা রয়েছে বলে কি আপনাদের মনে হয় না?
আজিজুল সাহেব, ’৯৩-এর পঞ্চায়েত নির্বাচনের সময়-সময় আপনার সঙ্গে আমার কিছু কথা হয়েছিল ফোনে। আপনি তখন ছিলেন জ্যোতির্ময় দত্তের বাড়িতে, আমি আমার বাড়িতে। মার্কসবাদী দলে সমাজবিরোধী ও ভণ্ডদের বর্তমান অবস্থানকে সমর্থন জানিয়ে আপনি বলেছিলেন, “বি.জে.পির ধর্মীয় ফ্যাসিবাদ রুখতে আমি সমাজবিরোধীদেরও সঙ্গে নেবার পক্ষে।”
সমাজবিরোধীরা তো প্রথাগতভাবে গত ষোলো বছর ধরেই শাসক দলের সঙ্গে রয়েছে, তাতে কি বিজেপি’র উত্থান রুখতে পারা যাচ্ছে? আপনি কি রাজনৈতিক ফ্যাসিবাদের সাহায্যে ধর্মীয় ফ্যাসিবাদ রুখতে চাইছেন? তারপর রাজনৈতিক ফ্যাসিবাদ রুখবেন কী দিয়ে? শেষ পর্যন্ত বোতল থেকে বের করা সমাজবিরোধীদের ভূতকে বোতলে পুরবেন কী করে? সমাজবিরোধীরা স্বভাব না পাল্টানো সত্ত্বেও অর্থাৎ অবস্থান না পাল্টানো সত্ত্বেও তাদের পালন ও পুষ্ট করলে কাদের স্বার্থ রক্ষিত হবে আজিজুল সাহেব? সমাজের? না ভণ্ড রাজনৈতিক দলের ও তাদের পালক বণিক শ্রেণির? একজন সৎ মানুষ অবস্থান পাল্টে অসৎ হলে পূর্ব সম্পর্ক থাকলেও তা ছিন্ন করে তার অসততার বিরোধিতা করাটা যে কোনও মূল্যবোধ-সচেতন যুক্তিনিষ্ঠ মানুষ সমর্থন করলেও আপনি সমর্থন করবেন কি না আমি নিশ্চিত নই—আপনার বর্তমান অবস্থানের জন্যই নিশ্চিত নই। বালক ব্রহ্মচারীর ‘নির্বিকল্প সমাধি’ নিয়ে পথনির্দেশ দিয়ে আপনি কখনও বলেছেন, ‘মৃতদেহ পুড়িয়ে দিতে হবে, আবার কখনও বা বলেছেন, ‘মৃতদেহ পচতে দাও’। স্থান-কাল-পাত্র দেখে আপনি দু’রকম কথাই বলেছেন। এই দ্বিচারিতার জন্যই আপনার সম্বন্ধে নিশ্চিত নই।
আমি যে পাড়ায় থাকি, সে পাড়ায় মধ্যবয়স্ক ও বয়স্কদের একটি তাসের আড্ডা আছে। সন্ধ্যার আড্ডায় তাঁরা আসেন, তাস খেলেন, রাতে বাড়ি ফেরেন। বদলি, স্থায়ী অসুস্থতা ও মৃত্যু ছাড়া আড্ডার কোনও সদস্য বিদায় নেননি আমার দেখা পনেরোটি বছরের মধ্যে। এই একই চিত্রের পুনরাবৃত্তি দেখতে পাবেন অন্যান্য পাড়ার তাস বা দাবার আড্ডার ক্ষেত্রে। কিন্তু আমাদের যুক্তিবাদী সমিতির সভ্যদের ক্ষেত্রে এমন অবস্থা আমরা গত আট বছরে আদৌ দেখিনি। যখনই কোনও সদস্য লোভ বা ভয়ের দ্বারা চালিত হয়ে সমিতির আদর্শ থেকে চ্যুত হয়েছে অথবা যুক্তিবাদ এবং সাংস্কৃতিক আন্দোলনের প্রতি দায়বদ্ধতার কথাগুলো নিতান্তই মেকি বলে আমাদের দৃষ্টিতে ধরা পড়েছে, তখন আমাদের সমিতির সদস্যদের সঙ্গে চ্যুত বা মেকি মানুষটির তীব্র দ্বন্দ্ব দেখা দিয়েছে ৷ আজ আমার প্রতি যে গভীর বিশ্বাস ও ভালোবাসা সমিতির সভ্য-সভ্যাদের আছে, আমি বিচ্যুত হলে সেই বিশ্বাস ও ভালোবাসায় ভাঙন ধরতে বাধ্য। এরপর সমিতির সদস্যদের সঙ্গে আমার অতীত সম্পর্ক অটুট থাকা যেমন অসম্ভব, তেমনই নীতিহীন। তাসের আড্ডায় সদস্য এবং আমাদের সমিতির সদস্যদের মধ্যে মতাদর্শগত চেতনার পার্থক্যের দরুনই দ্বন্দ্ব দেখা না দেওয়া এবং দ্বন্দ্ব দেখা দেওয়ার পার্থক্য আমরা লক্ষ করি। তাস-দাবার আড্ডায় কোনও মতাদর্শগত সংগ্রাম নেই বলেই দ্বন্দের সম্ভাবনাও নেই। আর আমাদের সমিতির ক্ষেত্রে তীব্রভাবে মতদর্শগত সংগ্রাম আছে বলেই দ্বন্দ্বেও তীব্রতর হয়ে ওঠে। মাত্র তিনটি উদাহরণে বিষয়টি পরিষ্কার করতে চাইছি।
নারায়ণ সান্যাল বিভিন্ন বিষয়ে সাবলীল এক গ্রন্থকার এবং প্রগতিশীল হিসেবে চিহ্নিত। অন্যায় ও দুর্নীতির বিরুদ্ধে অনেক উপন্যাস লিখেছেন। লিখেছেন ‘পয়োমুখম’-এর মতো অলৌকিকতা বিরোধী গ্রন্থ। বিভিন্ন সভায় যুক্তিবাদের পক্ষে সোচ্চার বক্তব্য রেখেছেন। আমাদের আন্দোলনের প্রতি তাঁর সরব সমর্থন হেতু আমরা তাঁকে আমাদের সমিতির উপদেষ্টার পদে বসিয়েছি।
কেটে গেছে কয়েকটা বছর। এল ১৯৯৩ সাল। ঘটল ঘটনাটা। পুরুলিয়া থেকে প্রকাশিত ‘সাহিত্য মন্দির পত্রিকা’র ১৩৯৮ বঙ্গাব্দের সংখ্যাটি জনপ্রিয় যুক্তিবাদী লেখক নারায়ণ সান্যালকে পাঠিয়েছিলেন শ্রদ্ধাবনত সম্পাদক অশোক আগরওয়াল। পত্রিকাটি পড়ে ‘কুসংস্কার ও বিজ্ঞান’ শিরোনামের একটি লেখার প্রসঙ্গ টেনে সম্পাদককে এক পত্রাঘাত করলেন নারায়ণ সান্যাল। নারায়ণবাবুর চিঠিটি সম্পাদক ছেপে দিলেন ‘সাহিত্য মন্দির’-এ ১৩৯৯ বঙ্গাব্দের সংখ্যায়। সাহিত্য মন্দিরের দু’টি সংখ্যাই আমাদের দপ্তরে এল, সঙ্গে একটি চিঠি। বক্তব্য—আপনাদের সুস্পষ্ট মতামত চাই, নারায়ণ সান্যালের এমন দ্বিচারিতার বিরুদ্ধে কী করছেন?
নারায়ণবাবুর প্রকাশিত পত্রের একটা অংশে আছে, লেখিকার বন্ধু বলেছিল, “যুগ যুগ ধরে কত মানুষ সংসার ত্যাগ করেছেন, কৃচ্ছ্রসাধন করেছেন—কীসের জন্য?… তাঁরা সবাই কি ভুল করেছিলেন?” লেখিকা জবাবে বলেছিলেন, “সবাইও তো ভুল করতে পারেন।” লেখিকা কি সচেতন ভাবে খেয়াল করেছেন এ ‘সবাই” এর মধ্যে পড়েন গৌতম বুদ্ধ, আদি শঙ্করাচার্য, চৈতন্যদেব, শ্রীরামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ এবং শ্রীঅরবিন্দ?
শেষোক্ত ব্যক্তি যিনি ‘সাবিত্রীর’ মতো গ্রন্থরচনায় সক্ষম তিনি কী কারণে জীবনের পঁচিশটা বছর কাটিয়ে দিলেন রুদ্ধদ্বার কক্ষে একান্ত সাধনায়? এবং কোন্ বৈজ্ঞানিক হেতুতে তাঁর মৃত্যুর পর সতেরো দিন মৃতদেহে পচনকার্য শুরু হয়নি (সার্টিফিকেট দিয়েছিলেন ভারত বিখ্যাত ডাক্তার প্রভাত সান্যাল এবং পণ্ডিচেরির ফরাসি সিভিল সার্জেন) এ তো ইতিহাস নয়। আমার জীবদ্দশায় ঘটা ঘটনা !
নারায়ণবাবু, এ আপনি কী লিখলেন? এ কি আপনার স্মৃতিভ্রংশের ফলশ্রুতি? না, মফস্বলের অনামী এক পত্রিকার সম্পাদককে যা খুশি লেখার স্পর্ধা? শ্রীঅরবিন্দ সম্পর্কে আপনার জীবন দশায় যা ঘটেছে বলে দাবি করেছেন, তা তো আদৌ ঘটেনি! এ তো ইতিহাস নয়! এ হল বিকৃতি অরবিন্দের মৃত্যু ৫ ডিসেম্বর ১৯৫০ রাত ১টা ২৬ মিনিটে। তাঁকে সমাধিস্থ করা হয় ৯ ডিসেম্বর ১৯৫০ বিকেল ৫টায়। যদি বাস্তবিকই তেমনটা ঘটে থাকে, তবে বলতে হয় বালক ব্রহ্মচারীর মৃতদেহ দেখে সার্টিফিকেট দিয়ে ফেঁসেছেন ডাঃ অমলেন্দু সাঁতরা, কিন্তু ডাঃ প্রভাত সান্যাল ও সিভিল সার্জেন ফাঁসেননি। কারণ হল সময়টা ‘৯৩-এর পরিবর্তে ছিল’৫০; স্থান–কলকাতার পরিবর্তে পণ্ডিচেরি এবং ওখানে ছিল না ‘আজকাল’, ‘ভারতীয় বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী সমিতি’ ও যুক্তিবাদী আন্দোলনের হাওয়া; থাকলে একই ভাবে ফাঁসত ৫০-এর বুজরুকি।
কিন্তু ডাক্তার প্রভাত সান্যালের সার্টিফিকেট দেওয়া নিয়ে নারায়ণ সান্যালের বক্তব্য কতটা সত্যি- সে বিষয়েও যথেষ্ট সন্দেহের অবকাশ আছে। পণ্ডিচেরিতে শ্রীঅরবিন্দের মৃতদেহ দেখে ফিরে এসে ডাক্তার প্রভাত সান্যাল কলকাতায় একটি সভায় এই প্রসঙ্গে বক্তব্য রাখতে গিয়ে বলেছিলেন- শ্রীঅরবিন্দের মৃতদেহে তিনি জ্যোতির কোনও নিদর্শন দেখতে পাননি। বরং স্পষ্টতই এ-কথা বলেছিলেন—শ্রীঅরবিন্দর মৃতদেহে তিনি বিকৃতি ই দেখেছিলেন এবং অবিলম্বে সৎকারের পরামর্শ দিয়েছিলেন। সে সভার বহু শ্রোতা আজও বিদ্যমান। ১৯ জুলাই ’৯৩-এর আজকাল পত্রিকায় এমনই এক শ্রোতা কলকাতার রাজ্যেশ্বর মিত্রের বক্তব্য প্রকাশিত হয়েছে, যা আমার বক্তব্যের সত্যতাকেই সমর্থন করে। তবুও এর পরেও আমার শ্রদ্ধেয় ও প্রিয় লেখক নারায়ণ সান্যালের কাছে একটি বিনীত ও যুক্তিসঙ্গত অনুরোধ—ডাক্তার প্রভাত সান্যালের সার্টিফিকেটটা বাস্তবিকই কি আপনি চর্মচক্ষে দেখেছেন? আমাকে দেখাতে পারবেন নিদেন তারই একটা ফোটো কপি? সত্যকে প্রকাশের স্বার্থেই একবার দেখান না।
নারায়ণ সান্যাল ওই পত্রে আরও লিখেছেন, লেখিকার যা বক্তব্য তা অনুজপ্রতিম প্রবীর ঘোষ ‘অলৌকিক নয় লৌকিক’ গ্রন্থে বিস্তারিতভাবে বলেছেন, আমিও আমার সাধ্যমতো বলার চেষ্টা করেছি ‘পয়োমুখম’ গ্রন্থে। কিন্তু তাই বলে বিজ্ঞানের বাইরে কোনও Supe- rior reason Power নেই একথা মেনে নেওয়া তো ছার মনেও নিতে পারি না।
অরবিন্দের মৃতদেহ ঘিরে অলৌকিক ঘটনা ঘটে যাওয়ার সপক্ষে প্রমাণ যখন একটু চেষ্টা করলেই নারায়ণবাবুর সহযোগিতায় পাওয়া যেতে পারে এবং অলৌকিকত্বের অস্তিত্বের পক্ষে প্রমাণ পাওয়ার পর অস্তিত্বের বিরোধিতা যেহেতু যুক্তিহীনতারই নামান্তর, তাই সমিতির পক্ষ থেকে নারায়ণবাবুকে অনুরোধ করেছি—এ বিষয়ে প্রমাণ দিতে। এমনকী, অন্য কোনও অলৌকিক ঘটনা বা শক্তির প্রমাণ থাকলে তাও হাজির করতে অনুরোধ করেছি। আমার নিরীহ ও বিনীত অনুরোধের বিনিময়ে তথাকথিত যুক্তিবাদী লেখক সহযোগিতার হাত প্রসারিত না করে তীব্র উষ্মা প্রকাশ করে বলেছেন—আমার ব্যক্তিগত চিঠি ছেপে অশোক আগরওয়াল অত্যন্ত গর্হিত ও বে-আইনি কাজ করেছেন। ‘চানঘরে গান’ বইতে সত্যজিৎ রায়ের চিঠি প্রকাশ করা নিয়ে আইনি-লড়াইয়ের প্রসঙ্গ টেনে বলেছিলেন—আমি অশোক ও সাহিত্য মন্দির পত্রিকার বিরুদ্ধে কেস করতে পারি। আর এমন বেআইনি প্রসঙ্গ নিয়ে আমি কারও সঙ্গেই আলোচনা করতে রাজি নই। তোমার সঙ্গেও না।
এমনতর সুবিধাবাদী, মেকি যুক্তিবাদী চরিত্রটি খোলামেলাভাবে প্ৰকাশ পেতে এমন চরিত্রকে ‘সুসংস্কৃতির ক্যানসার’ বিবেচনায় আমরা ছেঁটে ফেলেছি আমাদের উপদেষ্টা পদ থেকে শুধু নয়, সমিতি থেকেও।
সুমন চট্টোপাধ্যায় একাধারে গীতিকার, সুরকার ও গায়ক। বাংলা গানে নতুন কথা, নতুন সুর এনে এবং গানের মাঝে ঝক্ঝকে কথা বলে নিজেকে সমাজের প্রতি দায়বদ্ধ ও প্রতিবাদী হিসেবে প্রতিষ্ঠা করেছেন। সুমনের গানে এসেছে ‘যুক্তিবাদ’, এসেছি ‘আমি’। আমাদের সমিতিকে উৎসর্গ করে গান বেঁধে মঞ্চ মাতিয়েছেন— সে খবর শুনে পুলকিত হয়েছি। এল তারপর ‘৯৩-এর ১ মার্চ। আন্তর্জাতিক যুক্তিবাদী দিবসে আমাদের সমিতির কেন্দ্রীয় অনুষ্ঠানের মধ্যে তাঁর গানকেও আমরা হাজির করেছিলাম। সেই অনুষ্ঠানেও সুমন আমাদের সমিতিকে কৃতজ্ঞতা জানিয়েছেন, অভিনন্দিত করেছেন এবং একটি গানও আমাদের সমিতির উদ্দেশে উৎসর্গ করে গেয়েছেন। তাঁর গানে আমাদের সমিতির বহু দর্শকের শ্রবণ-ইন্দ্রিয়কে পীড়িত করেছে, যে গানে আমরা অনুপ্রাণিত হয়েছি, বিপুলভাবে অভিনন্দিত করেছি। এরই মাঝে তাঁর একটা গান তিনি মানুষকে ভরসা রাখতে আহ্বান জানিয়েছেন ‘আজানে ও শাঁখের সুরে’। তাঁকে কাছাকাছি থেকে দেখতে পাওয়ার সুযোগ যাদের ঘটল তাঁদের অনেকেই ধাক্কা খেলেন বুক বাজিয়ে মার্কসবাদী বলে ঘোষিত এই মানুষটিকে অদৃষ্টবাদে পরম বিশ্বাস রেখে গ্রহরত্নের আংটি ধারণ করতে দেখে।
এরই মাঝে আরও একটি ঘটনা আমাদের সমিতির স্বেচ্ছসেবকদের খুবই খারাপ লেগেছে। সুমনের গানের আগে যখন বক্তব্য রাখছিলেন শ্রদ্ধেয় চলচ্চিত্র পরিচালক ও আমাদের সমিতির উপদেষ্টা মৃণাল সেন, যখন তাঁর অননুকরণীয় বৈঠকিচালের বক্তব্যে শ্রোতারা সম্মোহিত, ঠিক তখনই কিছু শ্রোতা ছন্দপতন ঘটিয়ে চিৎকার শুরু করেন, “বসে পড়ুন, বসে পড়ুন । আমরা সুমনের গান শুনব।” গোলমালকারীরা সংখ্যায় জনা কুড়ি। এবং আমাদের স্বেচ্ছাসেবকরা সবিস্ময়ে আবিষ্কার করলেন, এঁরা কেউই আমাদের সমিতির সদস্য নন। এঁরা বসেছিলেন সেই আসনগুলোতে যেগুলো সুমন ‘গেস্ট কার্ড’ হিসেবে পেয়েছিলেন অথবা যে সাধারণ কার্ডগুলো সুমন সংগ্রহ করেছিলেন।
এই প্রসঙ্গে অভিনেতা অশোককুমারের স্মৃতিচারণমূলক প্রবন্ধ ‘জীবন- নাইয়া’র কথা মনে পড়ে গেল। অশোককুমার জওহরলাল নেহরু ও সুভাষচন্দ্র বসু সম্পর্কে দু’টি ঘটনার উল্লেখ করেছিলেন। নেহেরু একবার সপার্ষদ অশোককুমারের সঙ্গে অশোককুমার অভিনীত ‘অচ্ছুৎকন্যা’ সিনেমা দেখছেন। ছবি দেখতে দেখতে নেহরু মাঝে মাঝেই একটা হাত তুলছেন। আর হাত তোলামাত্র পিছনে বসা তার সাঙ্গোপাঙ্গরা নেহরুর নামে ‘জিন্দাবাদ’ ধ্বনি তুলছিল। বিস্মিত অশোককুমার জিজ্ঞেস করেছিলেন, “এটা কী হচ্ছে?” নেহরুর এক পার্শ্বচর নিচু গলায় জানালেন, “পাবলিসিটি”।
সুভাষচন্দ্র সম্পর্কে অশোককুমার তাঁর তিক্ত অভিজ্ঞতার কথা লিখতে গিয়ে জানাচ্ছেন, খোলা বাসে নেতাজি দাঁড়িয়ে, নেতাজির ঠিক পিছনের সিটে বসে অশোককুমার। পিছনে বিশাল মিছিল। রাস্তার দু’ধার থেকে জনতা নেতাজির উদ্দেশে ছুড়ে দিচ্ছে ফুল। বার বার আকাশ কাঁপিয়ে জয়ধ্বনি উঠছিল নেতাজির নামে। অশোককুমার অবশ্য চুপ। তারপর হঠাৎ শোনেন সুভাষচন্দ্র নিচু গলায় অশোককুমারকে বলছেন, “জয় বলো, জয় বলো।’ এই নির্লজ্জতায় বিরক্ত হয়ে সুভাষ-সঙ্গই পরিত্যাগ করেছিলেন অশোককুমার ।
‘পাবলিসিটি’র জন্য সুমনের ভাড়াটে নটুয়া ব্যবহারের নির্লজ্জতায় আমরাও বিরক্ত হয়েছিলাম। আমাদের স্বেচ্ছাসেবকরা গোলমালকারীদের কড়া ভাষায় জানিয়ে দিয়েছিলেন, “কারও পাবলিসিটি দিতে গিয়ে অনুষ্ঠানে আবার বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির চেষ্টা করলে হল থেকে বের করে দেব, এবং কান ধরে।” কথায় কাজ হয়েছিল।
ঈশ্বরে ভরসা রাখা অদৃষ্টবাদে বিশ্বাসী এই সুমনই পরবর্তীকালে প্রতিবাদে মুখর হয়ে আর এক মঞ্চে ‘ভগবান’কে রশিদের বাড়ির মতোই ধূলিসাৎ করলেন। তারপর আর এক মঞ্চে আবারও আহ্বান জানালেন ঈশ্বর ও আল্লায় ভরসা রাখতে।
‘৯৩-এর ১৫ মার্চ। স্থান কলকাতার নজরুল মঞ্চ। এইচ. এম. ভি-র দেওয়া ‘গোল্ডেন ডিস্ক’ পেয়ে আপ্লুত সুমন বাড়তি উচ্ছ্বাসে ওই সম্মান উৎসর্গ করলেন তাঁর পিতাকে, কিংবদন্তি গায়ক-গায়িকাদের, তাঁর ও রেকর্ড কোম্পানির সহযোগী কর্মীদের, অগণিত অনুরাগীদের।
এর মাত্র ছ’দিন পর অর্থাৎ ২১ মার্চ ওই নজরুল মঞ্চেই সুমন তাঁর সমস্ত রুচিবোধ ও সাংস্কৃতিক চেতনাকে চূড়ান্ত জলাঞ্জলি দিয়ে গর্বভরে ঘোষণা করলেন “গোল্ডেন ডিস্ক-এ পেচ্ছাপ করি”। উৎসর্গ করার পর উৎসর্গীকৃত ডিস্কে পেচ্ছাপ করে তিনি নিজেরই পিতা, পরম সম্মানীয় কিংবদন্তি গায়ক-গায়িকা, সহকর্মী ও অনুরাগীদের চূড়ান্তভাবে অপমান করলেন। এমনভাবে প্রত্যেকের সম্মানকে পেচ্ছাপে ডুবিয়ে দেবার স্পর্ধা কেউ দেখালে তাঁর ধিক্কার ও ঘৃণা ছাড়া আর কিছু প্রাপ্য হতে পারে কি?
কিন্তু এখানেই শেষ নয়। সেই সন্ধ্যাতেই নজরুল মঞ্চে ইতর মস্তানের মতোই বারবার মঞ্চ দাপিয়ে একটি ইংরেজি দৈনিক ও সেই পত্রিকার এক সাংবাদিককে ‘মাদার-ফাকার’ অর্থাৎ ‘মাকে সঙ্গমকারী’ বলে খিস্তি দিলেন। ধিক্কার জানাই সুমনের এই ধরনের পূতিগন্ধময় সংস্কৃতিকে আমদানি করার বদমতলবকে। পর পরই সুমন যখন আর এক মঞ্চে গান ধরেন, “পাল্টে দেবার স্বপ্ন আমার এখনো গেল না”, তখন স্বভাবতই প্রশ্ন জাগে পাল্টে কোন সংস্কৃতিকে আনতে চান সুমনবাবু? খিস্তি দিয়ে শ্রোতাদাদের মধ্যে এক ধরনের বিকৃত আবেগ ও সে থেকে সৃষ্ট উত্তেজনাকে কাজে লাগিয়ে শ্রোতাদের সঙ্গে একটা ‘র্যাপট’ বা ‘বিশেষ সম্পর্ক’ গড়ে তুলে জনপ্রিয়তা অর্জনের এই ভয়াবহ প্রচেষ্টায় সুমন সার্থক হলে কী হত ভাবা যায়? বহু গায়ক-গায়িকাই জনপ্ৰিয়তা অর্জনের আশায় এমন অশ্লীল-কদর্য-খেউড় গানের সঙ্গে যুক্ত করে শ্রোতাদের সঙ্গে ‘র্যাপট’ বা ‘বিশেষ সম্পর্ক’ গড়ে তুলতে সচেষ্ট হতেনই। সুমনের এই অশ্লীলতা কি নেহাতই এক ধরনের বিকৃত রুচির পাগলামি? না, প্রগতিশীলতার মুখোশের আড়ালে দ্বিচারিতা ও অশ্লীলতার ভাইরাস বহু গায়ক-গায়িকাদের মধ্যে ছড়িয়ে দিয়ে এক ব্যাপক সাংস্কৃতিক দূষণ গড়তেই বিদেশ থেকে এদেশে চালনো করা হয়েছে একটি প্রতিভাকে, যার সৃষ্টির মধ্যে অনেক সম্ভাবনা ছিল, যার মধ্যে মিলেমিশে ছিল অনেক মধ্যবিত্তর স্বপ্ন। কিন্তু কী পেলাম? একটি ভালো গান গাওয়া খারাপ মানুষ অসৎ মানুষ। অতীতে সুমন আমাদের কতটা প্রশংসা করেছেন, কতটা তোল্লাই দিয়েছেন, সেই সমস্ত আবেগ ও কৃতজ্ঞতা বিদায় করে দিয়ে সুমনের বর্তমান সুচতুর অবস্থান বঙ্গ-সংস্কৃতির পক্ষে বেশি ক্ষতিকারক বিবেচনায় তাঁর কদর্য অশ্লীল ধ্বংসাত্মক শক্তির গতি রুদ্ধ করতে আমরা জনচেতনাকে সচেতন করতে সচেষ্ট হয়েছিলাম। কারণ, আমরা বিশ্বাস করি—শেষ কথা বলেন জনগণ। আর সে কথা বলেন বলেই পুলিশ, প্রশাসন, স্বেচ্ছাসেবক এবং মস্তানদের বিপুল সমাবেশ ঘটিয়েও পৃথিবী কাঁপানো মরিস সেরুলো শেষ রক্ষা করতে পারেননি; সুমন তো কোন ছার! মার্কেট রাখতে খিস্তি নয়, খিস্তি ছাড়তে ঘাড় ধরে বাধ্য করাতে পারেন শ্রোতারাই।
সুমন কিন্তু শুধুমাত্র ভোগবাদসর্বস্ব, উচ্ছৃঙ্খলতা ও অশ্লীলতাকে গানের ফাঁকে ফাঁকে গুঁজে দিয়ে, জীবনচর্যার মধ্যে প্রকাশ করে ও কথায়-বার্তায় প্রতিফলিত করে এবং একশ্রেণির সংগীত শিল্পী ও সংগীত প্রেমিকদের প্ররোচনা জুগিয়ে নতুন ধরনের সাংস্কৃতিক দূষণ সৃষ্টি করার মধ্যেই তাঁর জনপ্রিয়তাকে সীমাবদ্ধ রাখেননি, তিনি ঘুষের ও দুর্নীতির পক্ষে জোরালো সওয়াল করে অনুগামী ও আপ্লুত শ্রোতাদের নিজের বক্তব্যের অনুকূলে সমাবেশিত করতে চেয়েছেন। ‘দৈনিক বসুমতী’র ১৯৯৩-এর মহালয়ার বিশেষ ক্রোড়পত্র-তে প্রকাশিত সাক্ষাৎকারে সুমন জানাচ্ছেন, “আপনি যদি আমাকে প্রশ্ন করেন, আপনি ঘুষ নেবেন? আমি কী করে বলি ‘না’। যদি দেখি আমার বউ, আমার বাচ্চা খেতে পাচ্ছে না বা যাকে ভালবাসি সে খেতে পাচ্ছে না, আমার তখন কোনও উপায় নেই। ঘুষ নেব, বেশ করব।”
বঞ্চনার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ, প্রতিরোধ, আন্দোলন, আক্রমণের পরিবর্তে ঘুষের দুর্নীতির অনুশীলন বঞ্চিত মানুষকে চটজলদি স্বার্থফল দিতে পারে বটে, কিন্তু বঞ্চিত মানুষদের সমুন্নত লক্ষ্যে পৌঁছে দিতে পারে না, পারে না, মুক্তি ঘটাতে। বরং বঞ্চিত মানুষদের ঘুষের দুর্নীতির আবর্তে পদভ্রষ্ট করে আখেরে লাভবান হন শোষকশ্রেণি, রাষ্ট্রশক্তি। এর পরও কি বুঝতে হয় সুমনের সাজানো গানের কথাগুলো শুধুমাত্র কথারই কথা এবং তারই আড়ালে লুকিয়ে আছে রক্তলোলুপ একটা বাঘ।
পি সি সরকার (জুনিয়র) ভারতের এক জনপ্রিয় জাদুকর। তাঁর জাদুতে অনাবিল আনন্দ পাওয়া ও মুগ্ধ হওয়া মানুষের সংখ্যা প্রচুর। যতজন দেখেছেন, তারচেয়ে বেশি মানুষ দেখেননি, কিন্তু শুনেছেন তাঁর অসাধারণ জাদুশৈলীর কথা। শ্রী সরকার কোটি কোটি মানুষের কাছে জীবন্ত কিংবন্তি—আস্ত একটা অমৃতসর এক্সপ্রেস ভ্যানিস করে দিয়ে। লক্ষ লক্ষ মানুষ দূরদর্শনের পর্দায় দেখেছেন ট্রেন ভ্যানিস, পত্র-পত্রিকায় পড়েছেন সেই রোমাঞ্চকর মুহূর্তের বর্ণনা। ট্রেন ভ্যানিসের ঘটনাটা ঘটেছিল এই তো সে’দিন—১২ জুলাই ’৯২ খানা স্টেশনের কাছে।
সমস্ত জাদুর পিছনেই কৌশল থাকে। যে’টা ঘটেছে বলে দেখেন, সেই ঘটার পিছনে থাকে কৌশল বা কার্য-কারণ-সম্পর্ক। কিন্তু এই ট্রেন ভ্যানিসের ক্ষেত্রে অমৃতসর এক্সপ্রেস সেদিন সে’সময় খানা স্টেশনের কাছে ছিল না। কোনও কৌশলের সাহায্যেই ট্রেনটিকে ভ্যানিস করা হয়নি। এটা ছিল একটা মিথ্যে প্রচার। প্রচারমাধ্যমগুলোর সঙ্গে বোঝাপড়ার ভিত্তিতে ব্যাপক আকারের মিথ্যে প্রচার। ব্যাপারটি ছিল জাদুকর ও প্রচারমাধ্যমগুলোর সাদা-সাপটা মিথ্যে—দ্বিচারিতা নয়।
কিন্তু ’৯৩-এর ডিসেম্বরে পি সি সরকার (জুনিয়র) যখন কুসংস্কারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করলেন ও কলকাতায় মেয়র বাহবা দিয়ে সমস্ত রকম আশ্বাসের কথা ঘোষণা করলেন এবং সেই খবর বিশাল প্রচার পেল, তখন ব্যাপারটা হয়ে গেল দ্বিচারিতার এক দুর্দান্ত যুগলবন্দি। কারণ পি. সি. সরকার (জুনিয়র) নিজেই ভূতে, ভাগ্যে ও ঈশ্বরে পরম বিশ্বাসী। এই বিশ্বাসের কথা বার-বার সোচ্চারে উচ্চারণ করেছেন সাক্ষাৎকারে ও লেখায়৷ এমনকী আগামী দিনে এ-সব “পরিষ্কার বিজ্ঞান বলে পরিচিত হবে” এমন প্রত্যাশাও ব্যক্ত করেছেন। আদ্যন্ত কুসংস্কারাচ্ছন্ন একটি মানুষ নিজেকে ‘কুসংস্কার মুক্তিতে আন্তরিক’ বলে প্রচারে সচেষ্ট হওয়াটা যেমন দ্বিচারিতা, ঠিক তেমনই দ্বিচারিতার স্পষ্ট প্রকাশ কলকাতার মেয়র তথা মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টির নেতা প্রশান্ত চট্টোপাধ্যায়ের একই সঙ্গে কুসংস্কারের বিরোধিতা এবং কুসংস্কারের পক্ষে ডুবে থাকা মানুষটিকে কুসংস্কার মুক্তির অগ্রণী মানুষ হিসেবে ‘প্রজেক্ট’ করা।
শুধুমাত্র ম্যাজিক দিয়ে তাবৎ অলৌকিক কাণ্ডকারখানার ব্যাখ্যা দেওয়া যায় না, কুসংস্কার থেকে জনমানসকে মুক্ত করা যায় না। ভর, ভাগ্যে বিশ্বাস, ঈশ্বরে বিশ্বাস এ’সব কুসংস্কারের ব্যাখ্যা কি ম্যাজিকের সাহায্যে দেওয়া সম্ভব? এর জন্য প্রয়োজন তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা। কুসংস্কার ও ভাববাদী চিন্তার মূলস্রোত আত্মার অস্তিত্ব, কর্মফল, ভাগ্য, ঈশ্বর ইত্যাদিতে বিশ্বাস। রাষ্ট্রশক্তি তার শোষণ প্রক্রিয়াকে মসৃণ রাখতে কুসংস্কার ও ভাববাদী চিন্তার এই মূলস্রোতকে গতিশীল রাখতে সব সময়ই সক্রিয়। আর তাই ভূত, ভাগ্য ও ঈশ্বরে বিশ্বাস জনমানসে বদ্ধমূল করা রাষ্ট্রশক্তির কাছে অনিবার্যভাবেই প্রয়োজনীয়।
জাদুকর সরকারের মতো কুসংস্কারে আচ্ছন্ন মানুষটি জনসাধারণের কাছে কুসংস্কারের বিরুদ্ধে এক সংগ্রামী চরিত্র হিসেবে গ্রহণযোগ্যতা পেলে সাধারণ মানুষ তাঁর কথায় ভূত, আত্মার অবিনশ্বরতা, কর্মফল, ভাগ্য, ঈশ্বর ইত্যাদির অস্তিত্বেও বিশ্বাস করবে—এটাই স্বাভাবিক। তাই শোষক-শাসক-বুদ্ধিজীবীদের আঁতাঁত বুঝে-সমঝেই শ্রীসরকারকে কুসংস্কারবিরোধী ব্যক্তিত্ব হিসেবে ‘প্রজেক্ট’ করতে চাইছে। চাওয়াটা স্বাভাবিক। এক হাতে যুক্তিবাদী আন্দোলনকে রোখা অন্য হাতে কুসংস্কারের চাষের জন্যই স্বাভাবিক। কিন্তু যাঁরা না বুঝেই শ্রীসরকারকে সমর্থন করতে এগিয়ে এসেছেন তাঁদের প্রতি বিনীত অনুরোধ—একটু ভেবে দেখুন—ভিক্ষাপাত্র ধরা হাতে কি গাণ্ডীব মানায় ? ও হাতে বরং মানায় ঘাতকের ছুরি।
‘স্পনসর’ নামধারী অভিভাবক, ভণ্ড ও দ্বিচারীদের ভিড়ে, অসুস্থ সাংস্কৃতিক গ্রাস-ক্ষমতা যখন সর্বগ্রাসীতার রূপ পেতে উন্মুখ, তখনই একঝলক টাটকা হাওয়া নিয়ে হাজির হয়েছে হাজার-হাজার তরুণ-তরুণী, যাদের বয়স বারো থেকে বিরাশি—যাই হোক । চতুর্দশ শতাব্দীর অন্তিম লগ্নে ইউরোপে যুক্তিবাদের যে প্রথম আগমন বার্তা ঘোষিত হয়েছিল, তারই সূত্র ধরে সোনার বাংলা গড়ার অনেক সুখ-স্বপ্ন আজ লক্ষ কোটি মানুষের চোখে যদি ভেসে ওঠে, সেটা কি শুধুই স্বপ্ন থেকে যাবে?
না। এ দেশ পঞ্চদশ শতাব্দীর নবজাগরণের অলোকে যে উদ্ভাসিত হবে, সংঘর্ষ ও নির্মাণের উৎসবে মেতে ওঠা সাংস্কৃতিক যোদ্ধারা সেই প্রত্যয়ই জাগিয়ে তুলেছে। এমনই এক যুগসন্ধিক্ষণে দুর্নীতি ও ভণ্ডামির পাশাপাশি আদর্শের ক্ষেত্রে আপসহীন মানুষও উঠে আসতে শুরু করেছে।
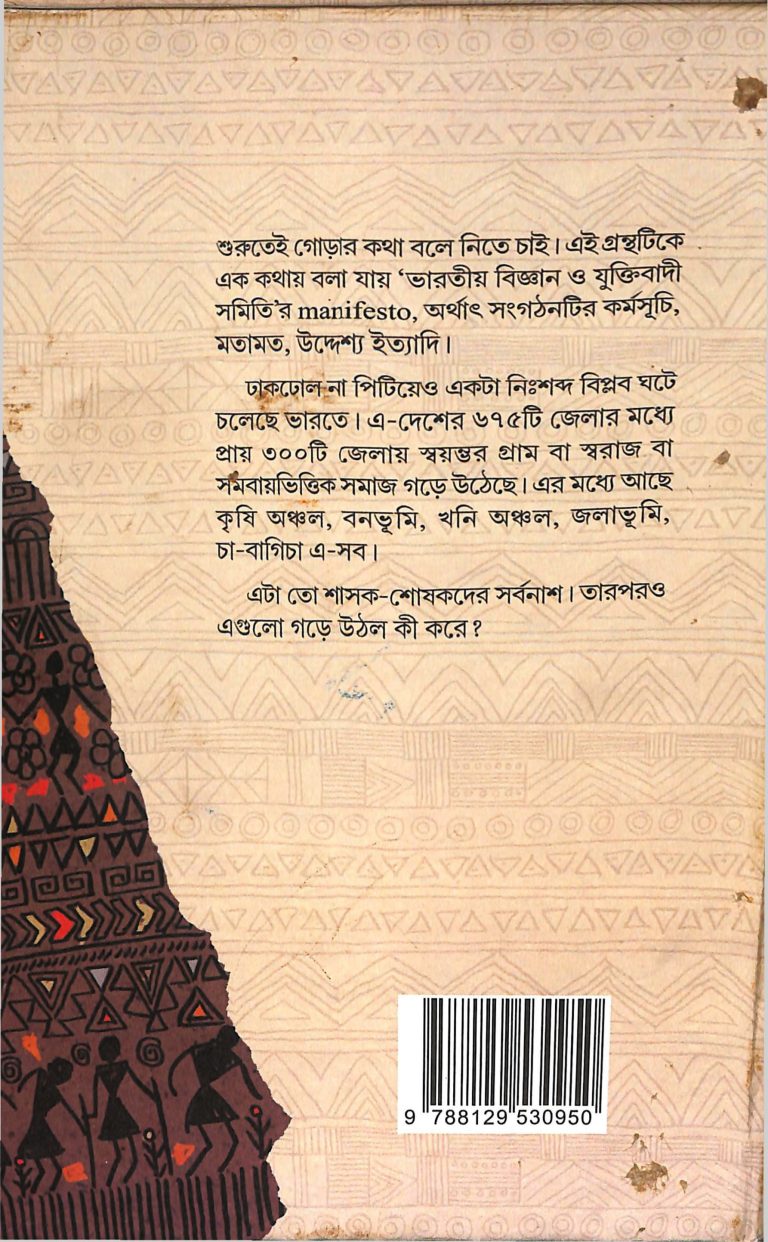
অধ্যায়ঃ এক
♦ বিভ্রান্তির সংস্কৃতিঃ বাঁচাও তাহারে মারিয়া
অধ্যায়ঃ দুই
♦ অপসংস্কৃতি ও সুস্থ সংস্কৃতিঃ পৃথিবীর ক্রমমুক্তি হোক সুচেতনার পথে
অধ্যায়ঃ তিন
♦ সাংস্কৃতিক বিপ্লবঃ পৃথিবীর পথে হাজার বছর হাঁটা
অধ্যায়ঃ চার
♦ ভারতবর্ষে সাংস্কৃতিক আন্দোলনঃ কেউ কথা রাখেনি
অধ্যায়ঃ পাঁচ
♦ নকশালবাড়ির সংগ্রামে উব্ধুদ্ধ সাংস্কৃতিক আন্দোলন
অধ্যায়ঃ ছয়
♦ যুক্তিবাদী আন্দোলন, সার্বিক সাংস্কৃতিক আন্দোলনঃ এসো আমরা আগুনে হাত রেখে প্রেমের গান গাই
অধ্যায়ঃ সাত
অধ্যায়ঃ আট
♦ যুক্তির পথচলাঃ লোভের অন্ধকারে ঢোকে না দিনের আলো
অধ্যায়ঃ নয়
♦ অতি ব্যবহৃত কিছু শব্দঃ সিন্দুকেতে মন ভরেছে ভেতরে তার কি আছে কেই বা রাখে খোঁজ?
“সংস্কৃতিঃ সংঘর্ষ ও নির্মাণ” বই সম্পর্কিত আপনার মন্তব্যঃ